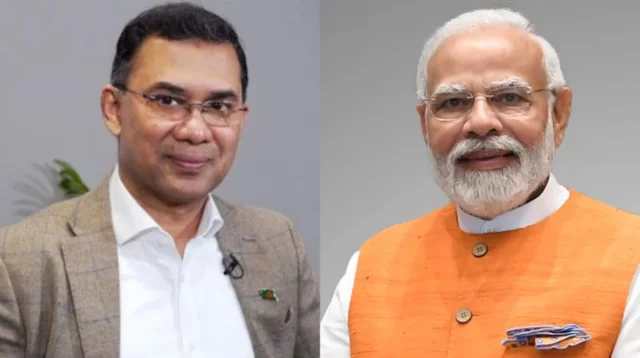শহরে—বা বলা ভালো, অঞ্চলে—একটি নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তি এসেছে।
পাকিস্তান ও সৌদি আরব আড়ম্বরের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, আর এ ঘোষণাকে ঘিরে দেশে–বিদেশে (কিছু স্থানে) বেশ শোরগোল পড়ে গেছে। মন্তব্য, বিশ্লেষণ, গান আর আলোচনা, করতালি—সবই চলছে।
আলোচনা এখনো শেষ হয়নি; উচ্ছ্বাসীদের প্রশংসা আর সংশয়প্রবণদের সামান্য সমালোচনার মাঝেও একটি বিষয়ে সবার ঐকমত্য—এই মুহূর্তে তথ্য খুবই সীমিত। মনে হচ্ছে, গম্ভীর ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্যের জন্য অপেক্ষাই করতে হবে।
আসলেই, পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের আগে আরও বিস্তারিত তথ্য এবং একটি সম্যক চিত্র দরকার। তাই অপ্রত্যাশিত নয় যে, আপাতত উত্তর কম, প্রশ্নই বেশি; তথ্যের চেয়ে অনুমানই প্রধান—এই চুক্তি কার্যত কী বোঝায়, দুই দেশ একে–অপরকে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এটি কি কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রকে মাথায় রেখে সই করা হয়েছে কি না, কিংবা আরও দেশ কি এতে যুক্ত হবে, নাকি একের পর এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হবে—এসব প্রশ্ন ঘুরছে।

তবু উত্তরহীনতার মাঝেই পাকিস্তানে যে উচ্ছ্বাস, তা তাৎপর্যপূর্ণ। আশাবাদ, অনুমান, এমনকি বিশ্বাসও দেখা যাচ্ছে—এই চুক্তি নাকি দেশকে ‘ভালো’ সময়ে নিতে পারে। আর এই আশাবাদ কেবল সরকারি মহল থেকে আসছে, তা নয়; ব্যক্তিগত আলাপেও তা শোনা যাচ্ছে।
আংশিকভাবে এটি বোধগম্য, কারণ সৌদি আরব অতীতে বারবার পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছে—মুলতুবি অর্থে তেল সরবরাহ থেকে শুরু করে ঋণ, যা আমাদের চিরকালীন সংকট—কম বৈদেশিক মজুত—সামাল দিতে সাহায্য করেছে। এখনও তারা আমাদের বৈদেশিক মজুদের অন্যতম বড় উৎস; ঋণ যখনই পরিশোধের সময় আসে, সেটি আবার (বারবার) পুনর্গঠিত হয়।
দেশের ভেতরে পাকিস্তান–সৌদি চুক্তিটিকে অনেকটা আগের কিছু মুহূর্তের পুনরাবৃত্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে।
এখন যখন একটি আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা চুক্তি হলো—যেখানে যে দেশ আক্রমণের শিকার হবে, অন্যটি তাকে সাহায্য করবে—তখন সকলের টানা উপসংহারে যাওয়া স্বাভাবিক। বোঝাই যাচ্ছে, এই সম্পর্কের পেশিশক্তি পাকিস্তানই দেবে, তার সুবিদিত সামরিক সক্ষমতা দিয়ে; আর রিয়াদ ইসলামাবাদকে কিছু আর্থিক রেয়াত বা সহায়তা দেবে। ‘ভালো সময়’ যেন দোরগোড়ায়।
কিন্তু এই অনুমানগুলোই বহু দশকে গড়ে ওঠা যে এলিট ঐকমত্য, তা উন্মোচন করে—যা এখনো অটুট। সেই ঐকমত্যে দেশের এলিটরা বাইরের তহবিল দিয়ে অর্থনীতি চালাতে চায়; সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে মানতে রাজি যে, এসব তহবিল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীই প্রধান এবং দেশীয় রাজনীতিতেও তারাই মুখ্য খেলোয়াড়। রাজনীতিকরা তাতে রাজি—জুনিয়র অংশীদারের ভূমিকায়, ক্ষমতায় এবং টাকার ভাগে। টাকাগুলো তারাও গোপনে সরিয়ে রাখে; সামান্য একটু খরচ করে জনসাধারণের উপর।
গত কয়েক বছরে ভূ-রাজনৈতিক ভাড়ার সুযোগ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এলেও ক্ষমতাসীন এলিট তাদের বেখেয়ালি, ক্ষতিকর অভ্যাস পাল্টাতে চাননি, চাইছেনও না। আগের পিএমএল-এন সরকার ভরসা করেছিল সিপিইসি’র ওপর; পিটিআই আশা করেছিল প্রবাসী পাকিস্তানিদের বিনিয়োগে; ২০২২-এর বন্যার পর জলবায়ু-সম্পর্কিত সহায়তার কথা উঠেছিল; তারপর এল উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে বিনিয়োগের আলাপ। সবকিছুর অন্তর্লীন সুর এক—কোনো না কোনো বাহ্যিক প্রবাহ এসে সংকট কাটাবে, দেশকে বাস্তব সংস্কার ও কষ্টকর সমন্বয়ের পথ মাড়াতে হবে না।

উল্লেখযোগ্য যে, এই ‘আশা’ সত্য ছিল, যদিও একই সময়ে অর্থনীতির জটিল সংকট নিয়ে জনপরিসরে নির্ণয় ও প্রস্তাবের বিশদ আলোচনা চলছিল—করভিত্তি বাড়ানো থেকে শুরু করে কেন্দ্রের সরকারি ব্যয় কমানো, এমনকি এনএফসি সংশোধন পর্যন্ত। এই আলোচনাগুলো যে গভীরতায় হয়েছে, তা নজিরবিহীন। কিন্তু ক্ষমতায় থাকা লোকজন—যারা এই আলোচনায় অংশও নিয়েছেন—রাজনৈতিক সদিচ্ছা দেখাননি। বছরের পর বছর গড়ে ওঠা ‘খারাপ অভ্যাস’ই একমাত্র ব্যাখ্যা নয়, তবে বড় কারণ।
আরেকটি কারণ বৈধতার সঙ্কটও। ক্ষমতাসীনরা—হোক তা ক্ষমতায় থাকা পিটিআই সরকার বা বর্তমান ব্যবস্থা—এতটাই অনিরাপদ যে, তারা দীর্ঘমেয়াদি, কষ্টকর সংস্কারের পথে না গিয়ে তাৎক্ষণিক স্বস্তির প্রতিশ্রুতি দিতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, তা যতই অস্থিতিশীল হোক।
এই তাৎক্ষণিক স্বস্তির আশাই এই চুক্তির দেশীয় প্রভাব নিয়ে ‘চর্চা’র জন্ম দিয়েছে। আলাপের বড় অংশটি ইতিবাচক হলেও পাকিস্তান নিজেকে সস্তায় ‘বিকিয়ে’ দিচ্ছে—এমন আশঙ্কার কথাও শোনা গেছে। এর পেছনে নিশ্চয়ই ৯/১১-পরবর্তী সময়ে পারভেজ মোশাররফের দ্রুত যুক্তরাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন অভিযানে যোগ দেওয়া এবং যথেষ্ট দরকষাকষি না করা—এমন ধারণার প্রভাব আছে। এই মতের সঙ্গে কেউ একমত হন বা না হন, তাতে সন্দেহ নেই যে, ওই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জেনারেল এক ধরনের মায়া-মরীচিকার মতো অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরতে পেরেছিলেন এবং নিজের শাসনকে বাফার দিয়েছিলেন।
তাই আশ্চর্যের কিছু নেই—বিশ্ব ও বিশ্বে পাকিস্তানের অবস্থান বদলালেও—দেশের ভেতরে এই চুক্তিকে অনেকটাই আগের কিছু মুহূর্তের মতোই দেখা হচ্ছে: বর্তমান ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল ও টিকিয়ে রাখার, এবং যে ক্ষমতার ভারসাম্য গড়ে তোলা হয়েছে তা বজায় রাখার সুযোগ হিসেবে।
তবে প্রশ্ন তোলা যায়—এবার যে অর্থপ্রবাহের আশায় আছে সবাই, তা কি আগের সময়গুলোর সমপর্যায়ের হবে?—এ প্রশ্নের উত্তর অর্থনীতিবিদদের জানা। কিন্তু টাকার অঙ্ক উদার হলেও তা সাধারণ মানুষের জন্য কী অর্থ বহন করবে? কারণ এ ‘এলিট ঐকমত্য’ বেশির ভাগ সময়েই মানুষের উন্নয়নের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, না হলে ইচ্ছাকৃত অবহেলার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই জনঅবহেলাই ক্ষমতাসীন এলিটদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে—যদিও তারা বর্তমান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হন এবং গণতন্ত্রের মানগত প্রশ্নে সমালোচনা এড়াতেও পারদর্শী বলে প্রমাণ করেন। উদ্যাপনের মাঝেই এ বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার।
লেখিকাসাংবাদিক।
ডন পত্রিকায় প্রকাশিত: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

 আরিফা নূর
আরিফা নূর