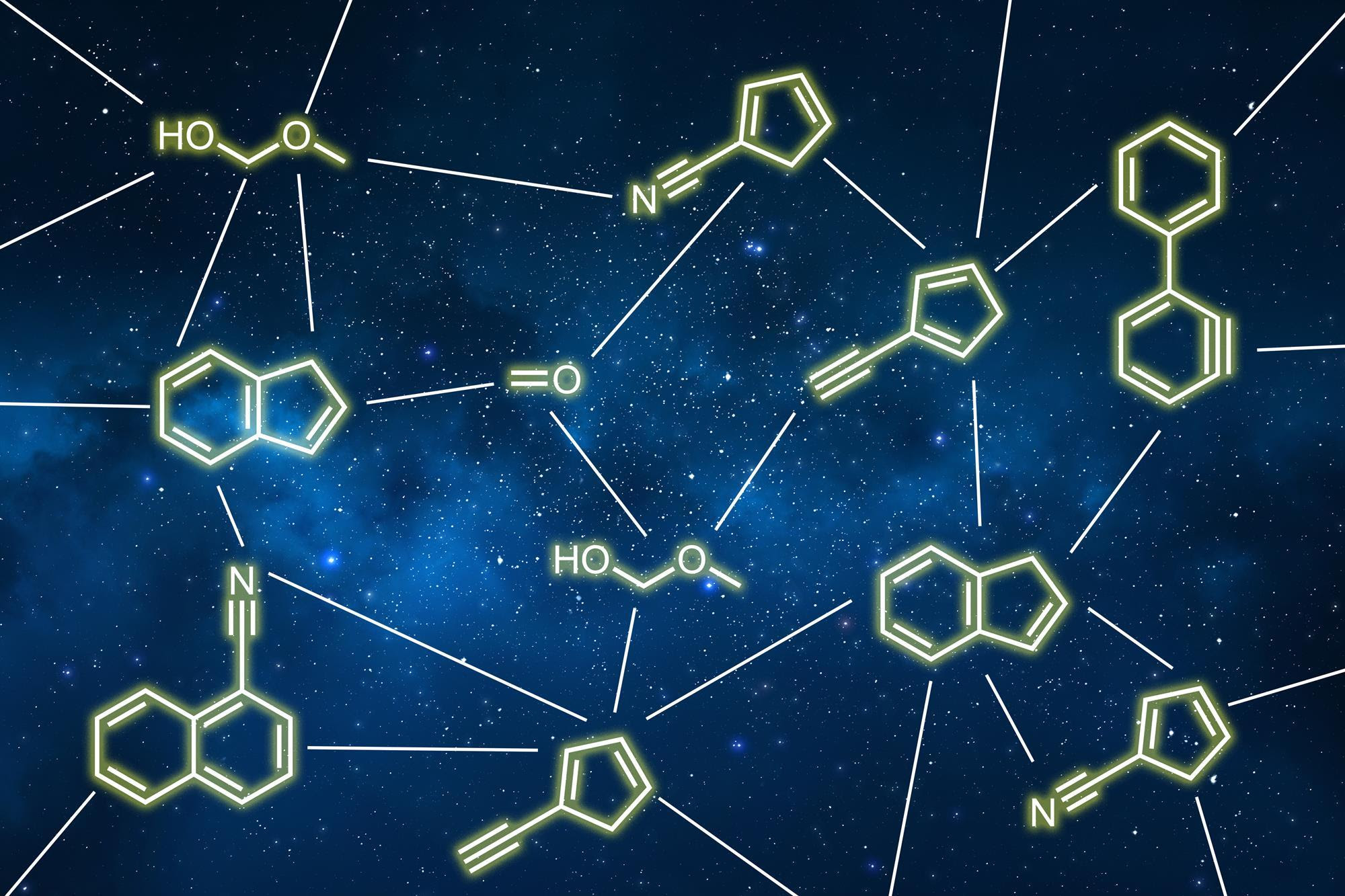শুরুতেই ধাক্কা
পৃথিবীর নানা দেশে বাংলাদেশের শিক্ষা সনদ আর আগের মতো মর্যাদা পাচ্ছে না। একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হতো ‘প্রাচ্যের অক্সফোর্ড’। কিন্তু এখন সেই প্রতিষ্ঠানসহ দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি বিদেশে মূল্যায়নের সময় অপ্রতুল বা নিম্নমানের হিসেবে গণ্য হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, এশিয়া—সবখানেই দেখা যাচ্ছে, স্নাতকোত্তর ডিগ্রিকে অনেক জায়গায় কেবল স্নাতক সমমানের ধরা হচ্ছে, আর স্নাতক ডিগ্রিকে নামিয়ে আনা হচ্ছে ফাউন্ডেশন বা ডিপ্লোমা স্তরে। ফলে বিদেশে চাকরি বা উচ্চশিক্ষার জন্য আবেদন করা বাংলাদেশিদের পক্ষে প্রতিযোগিতা করা কঠিন হয়ে পড়ছে।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য সংকট
শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক প্রতিষ্ঠানের সনদও বিদেশে স্বীকৃতি সংকটে পড়ছে। এসব সনদকে অনেক জায়গায় ‘ডিপ্লোমা’ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এতে আবেদনকারীরা নির্ধারিত যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, ভিসা নবায়ন ঝুঁকিতে পড়ছে, আবার বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়াতেও জটিলতা তৈরি হচ্ছে।

শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন
শিক্ষাবিদদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা রাজনৈতিক বিবেচনায় দ্রুত বেড়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক মান ধরে রেখে পাঠক্রম তৈরি হয়নি। গবেষণার সুযোগ সীমিত, আর আন্তর্জাতিক অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থার সঙ্গে চুক্তিও যথেষ্ট হয়নি। এর ফলেই বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা বিশ্বমঞ্চে ধীরে ধীরে মর্যাদা হারাচ্ছে।
ঢাবির শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. এস এম হাফিজুর রহমান বলেন, “আমাদের শিক্ষার্থীরা বিশ্বজুড়ে ভালো করছে। তবে গবেষণায় বিনিয়োগ নেই, অবকাঠামোগত ঘাটতি রয়ে গেছে। ওয়েবসাইটে পাঠক্রম বা গবেষণার তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ হয় না। এগুলো না বদলালে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া কঠিন।”
বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে
বাংলাদেশে বর্তমানে ১৭১টি বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও কোনোটি বিশ্বের সেরা ৫০০ তালিকায় নেই। ২০২৫ সালের কিউএস র্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৫৮৪তম স্থানে। টাইমস হায়ার এডুকেশন র্যাঙ্কিংয়েও প্রথম ৫০০-তে কোনো বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয় জায়গা পায়নি। গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ ৮০০-১০০০-এর মধ্যে অবস্থান করেছে।

অ্যাক্রেডিটেশনের ধীরগতি
২০১৮ সালে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হলেও সাত বছরেও কোনো সনদ দেওয়া হয়নি। কেবল পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন এখনো প্রক্রিয়াধীন। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ মনে করেন, বাধ্যতামূলক অ্যাক্রেডিটেশন ব্যবস্থা চালু হলে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে।
বিদেশে শিক্ষার্থীদের মান নিয়ে উদ্বেগ
ডেনমার্কের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক জরিপে বলা হয়েছে, দেশটিতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও তারা স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না এবং ফলাফল তুলনামূলকভাবে দুর্বল। অনুরূপ অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অন্যান্য দেশেও শোনা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে তাই বাংলাদেশিদের জন্য আরও কঠোর ভিসা ও ভর্তি শর্ত আরোপ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সংকটের শিকড়
ঢাবির সাবেক উপাচার্য ড. এস এম এ ফায়েজ বলেন, “বিশ্বজুড়ে ঢাবির শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। তবে রাজনৈতিক বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোয় অনেক প্রতিষ্ঠান মানহীন হয়ে পড়েছে। এখন তাদের উন্নত করা কঠিন, আবার বন্ধ করাও সম্ভব নয়।”
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃতি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়ন, গবেষণায় বিনিয়োগ এবং অ্যাক্রেডিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া এই সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট