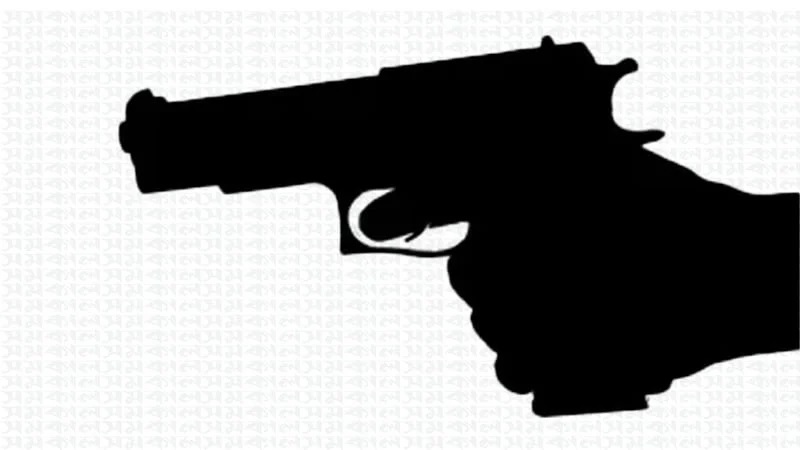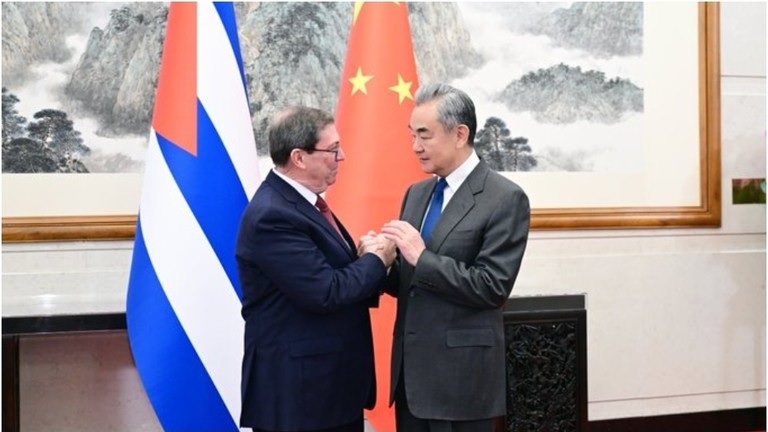প্রস্তাবনা
একসময় প্রযুক্তিনির্ভর সিনেমা জগতের পথিকৃৎ ছিল ‘ট্রন’। ১৯৮২ সালের সেই প্রথম চলচ্চিত্রে মানুষ ও মেশিনের সম্পর্ক, ভার্চুয়াল জগত ও বাস্তবতার সীমারেখা—সবকিছুই ছিল নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত। কিন্তু ২০২৫ সালের নতুন সংযোজন ‘ট্রন: অ্যারিস’ সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেনি। বরং এটি অনেকাংশে দেখা যায় একটি ‘প্রথম দিকের সিনেমাপ্রেমীর’ কাঁচা পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা হিসেবে।
ভিজ্যুয়াল জাঁকজমক বনাম দুর্বল কাহিনি
সিনেমার কিছু দৃশ্য ‘ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস’-এর মতো চমকপ্রদ অ্যাকশন দৃশ্যের অনুকরণে তৈরি। কিন্তু গল্পের গভীরতা অনুপস্থিত। বৈচিত্র্য দেখানোর প্রচেষ্টা এতটাই কৃত্রিম যে চরিত্রগুলো যেন কোটা পূরণের অংশ—একজন কৃষ্ণাঙ্গ, একজন শ্বেতাঙ্গ, একজন এশীয়, একজন ভারতীয়—সব জাতির প্রতিনিধিত্ব থাকলেও ব্যক্তিত্বের অভাব প্রকট।
সঙ্গী চরিত্রটি হাস্যরস আনার চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ; বরং তার অস্থির কথাবার্তা গল্পের গতি কমিয়ে দেয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) নিয়ে যে সংলাপগুলো এসেছে, সেগুলো বাস্তব বিশ্বের আলোচনার প্রতিফলন হলেও মৌলিকত্বহীন। সব মিলিয়ে, পুরো সিনেমাটি যেন “ফেলড প্রোগ্রামিং”—ত্রুটিপূর্ণ এক কোডিংয়ের ফল।

পুরোনো মহিমা ও নতুন বাস্তবতা
১৯৮২ সালের ‘ট্রন’ ছিল প্রযুক্তির নতুন যুগের প্রতীক। সেখানে মানুষ সরাসরি কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ করে এক ভার্চুয়াল দুনিয়ায় যাত্রা করত। আজকের ‘ট্রন: অ্যারিস’-এ সেই ধারণাকে নতুনভাবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ফলাফল ম্লান।
গল্পে ইভ কিম (গ্রেটা লি) এনকম কোম্পানির প্রধান, যিনি তাঁর বোনের মৃত্যুর পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও দায়িত্ব নেন। মূল প্রতিষ্ঠাতা কেভিনের ছেলে স্যাম এখন এই দুনিয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে, প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি ডিলিঙ্গার সিস্টেমসের প্রধান জুলিয়ান (ইভান পিটার্স), যিনি তৈরি করেছেন ‘বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত AI’—অ্যারিস (জ্যারেড লেটো অভিনীত)।
ইভ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চান মানবকল্যাণে, আর জুলিয়ান তা অস্ত্রে পরিণত করতে চান।
২৯ মিনিটের সীমা ও ‘পারম্যানেন্স কোড’
গল্পে দেখা যায়, AI প্রোগ্রামগুলোকে বাস্তব জগতে আনা সম্ভব হলেও তাদের আয়ুষ্কাল মাত্র ২৯ মিনিট। এরপর তারা ‘হ্যারি পটার’-এর ভলডেমর্টের মতোই ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যায় ও নিশ্চিহ্ন হয়।
এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে উভয় কোম্পানি লড়াই করছে ‘পারম্যানেন্স কোড’ পাওয়ার জন্য। নায়ক পক্ষ নিজেদের সীমিত শক্তি নিয়ে সংগ্রাম করছে, আর খলনায়ক পক্ষ প্রেরণ করেছে রোবট সৈনিকদের।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিবেক
চলচ্চিত্রের শেষভাগে গল্পটি রূপ নেয় ক্ষমতার লোভে অন্ধ হওয়ার নাটকে। তবে সেখানে হাজির হয় এক ‘অপ্রত্যাশিত’—আসলে বেশ অনুমানযোগ্য—নায়ক: এক AI, যে নিজের প্রোগ্রামিংয়ের বিরুদ্ধেও লড়ে মানবতার পাশে দাঁড়ায়।
কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়: গ্রিক দেবতাদের নামে প্রোগ্রামগুলোর নামকরণ কেন? কেন জ্ঞানের দেবতা ধ্বংস ডেকে আনে, আর যুদ্ধের দেবতা শান্তির জন্য কাজ করে? এই প্রতীকী উপমা দর্শকদের বিভ্রান্তই করে বেশি।
অতীতের সেরা উদাহরণগুলোর ছায়া
মানুষের রূপ ধারণ করা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ইতোমধ্যেই অসাধারণ কিছু সিনেমা হয়েছে—রবিন উইলিয়ামস অভিনীত Bicentennial Man কিংবা The Matrix সিরিজ, যেখানে AI মানুষের বাস্তবতাকেই নিয়ন্ত্রণ করে। ‘ট্রন: অ্যারিস’ সেই গভীর দার্শনিক প্রশ্নগুলো তুলতে ব্যর্থ হয়েছে।
এছাড়া জীবন্ত সত্তা 3D প্রিন্ট করার ধারণা বাস্তব বিজ্ঞানীদের কাজের প্রতি অসম্মানজনকও বটে। পরিচালক জোয়াকিম রনিং (যিনি Pirates of the Caribbean ও Maleficent: Mistress of Evil পরিচালনা করেছেন) চলচ্চিত্রটিকে দৃষ্টিনন্দন করলেও, কাহিনির মেরুদণ্ড তৈরি করতে পারেননি।
অভিনয় ও প্রযুক্তির সীমা
খ্যাতনামা অভিনেত্রী গিলিয়ান অ্যান্ডারসন, যিনি ‘এক্স-ফাইলস’ ও ‘দ্য ক্রাউন’-এ দারুণ পারফরম্যান্স দিয়েছেন, এখানে পরিণত হয়েছেন এক পরিত্যক্ত নেত্রীর ভূমিকায়—যার চরিত্র রচনায় গভীরতার অভাব স্পষ্ট।
চলচ্চিত্রে উড়ন্ত মহাকাশযান, লেজার ধারবিশিষ্ট চাক্রা, আপগ্রেডেড বাইক—সবই চিত্তাকর্ষক দৃশ্যমান প্রভাব তৈরি করেছে। কিন্তু দুর্বল কাহিনি ও পুনরাবৃত্ত গল্প এই ভিজ্যুয়াল জাঁকজমককেও অর্থহীন করে তোলে।

সংগীতই একমাত্র সফল উপাদান
সিনেমার প্রকৃত নায়ক হলো এর সংগীত। ‘নাইন ইঞ্চ নেলস’-এর ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর গল্পের দুর্বলতাকে ঢেকে রাখে, প্রমাণ করে যে সংগীত সত্যিই এক সার্বজনীন ভাষা। কিন্তু এটাই যদি হয় সিনেমার একমাত্র শক্তি, তাহলে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।
‘ট্রন’ ফ্র্যাঞ্চাইজির উত্তরাধিকার বহু দশকের—ভিডিও গেম ও চলচ্চিত্রের সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে এর পেছনে। কিন্তু ‘ট্রন: অ্যারিস’ সেই উত্তরাধিকারের মর্যাদা রাখতে পারেনি। দৃষ্টিনন্দন প্রভাব, বড় বাজেট ও জাঁকজমকপূর্ণ কাস্টিং সত্ত্বেও গল্পের দুর্বলতা, অপ্রাণ সংলাপ ও কৃত্রিম বার্তা সিনেমাটিকে বাঁচাতে পারেনি।
হয়তো এইবার সত্যিই বলা যায়—গেম ওভার।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট