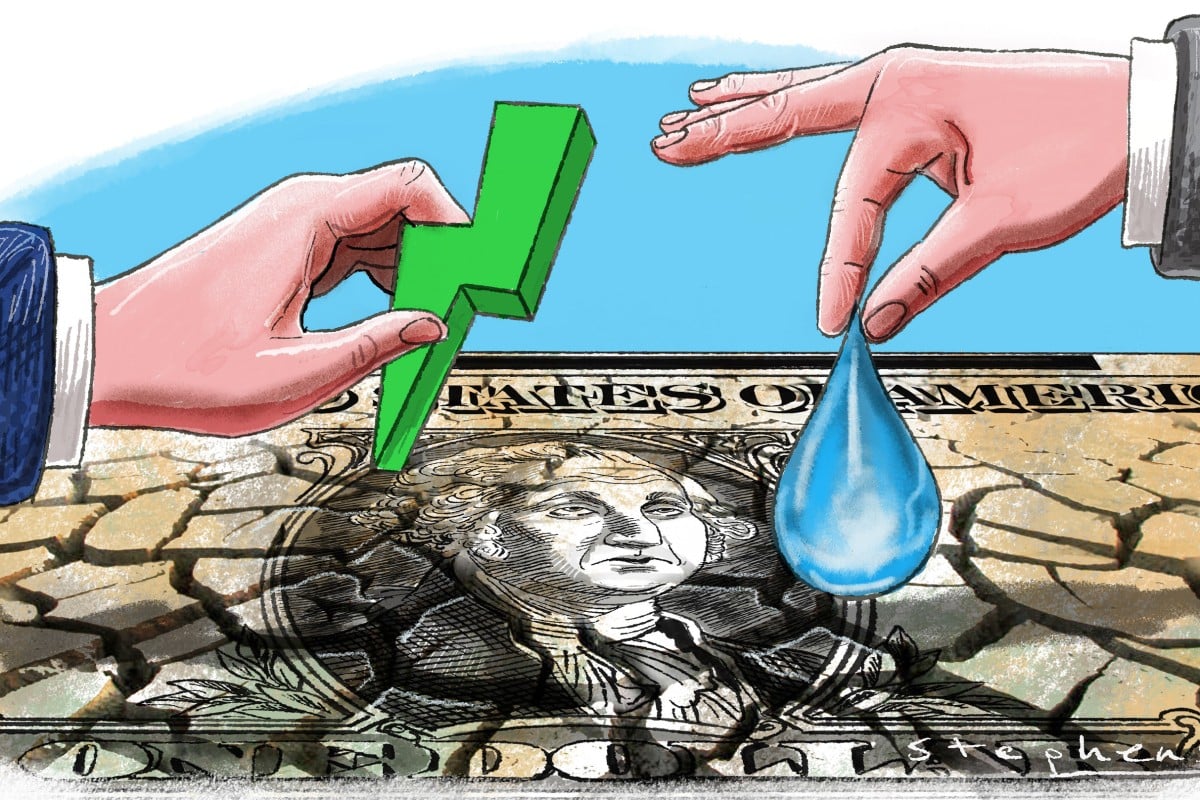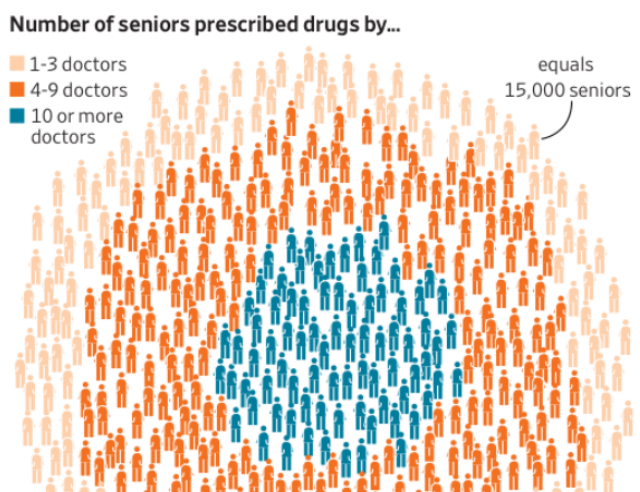১৯৮৯ সালে বার্লিন প্রাচীর ভেঙে পড়েছিল—যা ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান ও উদার গণতন্ত্রের জয়ের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু তিন দশক পর, ২০০৫ সালের পর থেকে পৃথিবী যেন আবার পিছনের দিকে হাঁটছে। স্বাধীনতা, মতপ্রকাশ ও ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে, আর এক নতুন ধরণের স্বৈরতান্ত্রিক ঢেউ পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে।
ইতিহাসের সমাপ্তি থেকে পুনর্জাগরণ
‘ইতিহাসের সমাপ্তি’—এই ধারণাটি প্রথম হেগেলের দর্শন থেকে আসে, যা পরে ১৯৮৯ সালে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা জনপ্রিয় করে তোলেন। তখন মনে হয়েছিল, কমিউনিজম ও ফ্যাসিবাদ পরাজিত, রাজতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্র হারিয়ে গেছে, আর গণতন্ত্রই মানবজাতির একমাত্র পথ।
সেই সময় পূর্ব ইউরোপ, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার বহু দেশ সাংবিধানিক গণতন্ত্র গ্রহণ করে। স্বাধীনতার সেই ‘সংক্রমণ’ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।
গণতন্ত্রের মন্দা: ২০০৫–এর পরের বাস্তবতা
কিন্তু ২০০৫ সাল ছিল শেষ বছর, যখন গণতন্ত্রের প্রসার সংকোচনের চেয়ে বেশি ছিল। ফ্রিডম হাউসের তথ্য অনুযায়ী, এরপর প্রতি বছরই গণতন্ত্র থেকে পিছিয়ে পড়া দেশের সংখ্যা বেড়েছে। রাজনীতি বিজ্ঞানী ল্যারি ডায়মন্ড একে বলেছেন “গণতান্ত্রিক মন্দা” (Democratic Recession)। আমরা এখনো সেই মন্দায় আছি।

গণতন্ত্র ভাঙে ভেতর থেকেই
আজকের সংকেতগুলো স্পষ্ট—
- • আইনের শাসন দুর্বল হয়ে পড়ছে।
- • স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত।
- • মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত।
- • নির্বাচন হয়েও বিশ্বাস হারাচ্ছে।
- • রাজনৈতিক দলগুলো ফলাফল মানতে চায় না।
গণতন্ত্র সাধারণত বাইরের শত্রুর হাতে নয়, নিজের হাতেই ধ্বংস হয়। জনগণ নিজেরাই এমন নেতাকে বেছে নেয় যারা গণতন্ত্র ভাঙে—শক্তিশালী, রাগী, বিভাজনমূলক, এবং দায় অন্যের ঘাড়ে চাপাতে অভ্যস্ত।
ন্যায়বিচারের দিকে ইতিহাস বেঁকে যায়?
বারাক ওবামা প্রায়ই মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের একটি লাইন উদ্ধৃত করতেন: “নৈতিক মহাবিশ্বের ধনুক দীর্ঘ, কিন্তু তা ন্যায়বিচারের দিকে বেঁকে যায়।”
কিন্তু এই ধারণা ধরে নেয় যে ইতিহাসের গতি সরল ও অগ্রগামী। অথচ সেই বাঁকটা নিজেকেই তৈরি করতে হয়।

স্বৈরশাসকেরা ইতিহাসকে উল্টোদিকে বাঁকায়
শি জিনপিং ও ভ্লাদিমির পুতিনের মতো নেতারা মনে করেন না যে ইতিহাস ন্যায়বিচারের দিকে এগোয়। তারা বিশ্বাস করেন, মানবসভ্যতা বৃত্তাকারে ঘোরে—যেখানে শক্তিই একমাত্র নীতি। হোবস যেমন বলেছিলেন, জীবন “নোংরা, নিষ্ঠুর ও স্বল্পস্থায়ী।”
আজ আমরা ‘নরম ফ্যাসিবাদ’-এর উত্থান দেখছি—অতি-জাতীয়তাবাদ, বিদেশি-বিদ্বেষ, কর্তৃত্ববাদ ও বিষাক্ত অতীত-নস্টালজিয়ার মিশ্রণ।
‘মেক কান্ট্রি গ্রেট এগেইন’: আসলে ‘হোয়াইট এগেইন’
এই উল্টোদিকে যাত্রার মূল কারণ একটিই—দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে উত্তর গোলার্ধে অভিবাসন, বিশেষ করে অ-শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর আগমন।
“মেক কান্ট্রি এক্স গ্রেট এগেইন” স্লোগানটি প্রায়ই আসলে অর্থ বহন করে—“দেশটিকে আবার শ্বেতাঙ্গদের দেশ বানাও।”
১৯শ শতাব্দীর রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রত্যাবর্তন
আজ ইতিহাসের চাকা আবার ফিরে গেছে শক্তিমান নেতা, ক্ষমতার রাজনীতি, ‘স্ফিয়ার অব ইনফ্লুয়েন্স’ এবং বাণিজ্যিক জাতীয়তাবাদের যুগে।
আমেরিকান রক্ষণশীলরা অতীতকে মহিমান্বিত করে দেখে—তাদের মতে, অভিবাসনের সুফল শেষ হয়ে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, আর মুক্তবাণিজ্যের সুফল শেষ হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। তারা মনে করে, যুক্তরাষ্ট্রকে উচ্চ প্রাচীর তুলে বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত রাখতে হবে এবং সার্বভৌমত্ব ‘রক্ষা’ করতে হবে।

নাগরিক শিক্ষা হারানোর মূল্য
লেখক একসময় ফিলাডেলফিয়ার ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন সেন্টারের প্রধান ছিলেন। সেখানে তিনি প্রথম নারী বিচারপতি স্যান্ড্রা ডে ও’কনরকে বোর্ডে নিয়োগ দেন। একদিন ও’কনর বলেছিলেন, “আমরা নাগরিক শিক্ষা বন্ধ করে ভয়াবহ মূল্য দিচ্ছি।”
আজ সেই কথার সত্যতা আরও স্পষ্ট—মানুষ জানে না, গণতন্ত্র কিভাবে টিকে থাকে।
স্বাধীনতার আত্মা মানুষের হৃদয়ে
১৯৪৪ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন, বিচারক লার্নড হ্যান্ড “দ্য স্পিরিট অব লিবার্টি” নামে এক বিখ্যাত বক্তৃতায় বলেছিলেন:
“আমরা হয়তো সংবিধান, আইন ও আদালতের ওপর অতিরিক্ত ভরসা করি। কিন্তু এগুলো ভ্রান্ত আশা। স্বাধীনতা বাস করে মানুষের হৃদয়ে; যখন তা সেখান থেকে মরে যায়, তখন কোনো সংবিধান বা আদালত তাকে বাঁচাতে পারে না।”
স্বাধীনতার বৃত্ত বড় করো
তবু সব শেষ নয়। নাগরিক শিক্ষা আমাদের শেখায়—ভোট ও প্রতিবাদ গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি।
তাই আমাদের উচিত রাস্তায় নামা, ভোট দেওয়া, আওয়াজ তোলা—এবং স্বাধীনতার বৃত্তকে আরও বড় করে তোলা।
#গণতন্ত্র #ফ্যাসিবাদ #ইতিহাস #স্বাধীনতা #রাজনীতি #সারাক্ষণরিপোর্ট

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট