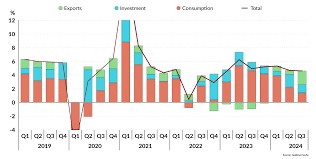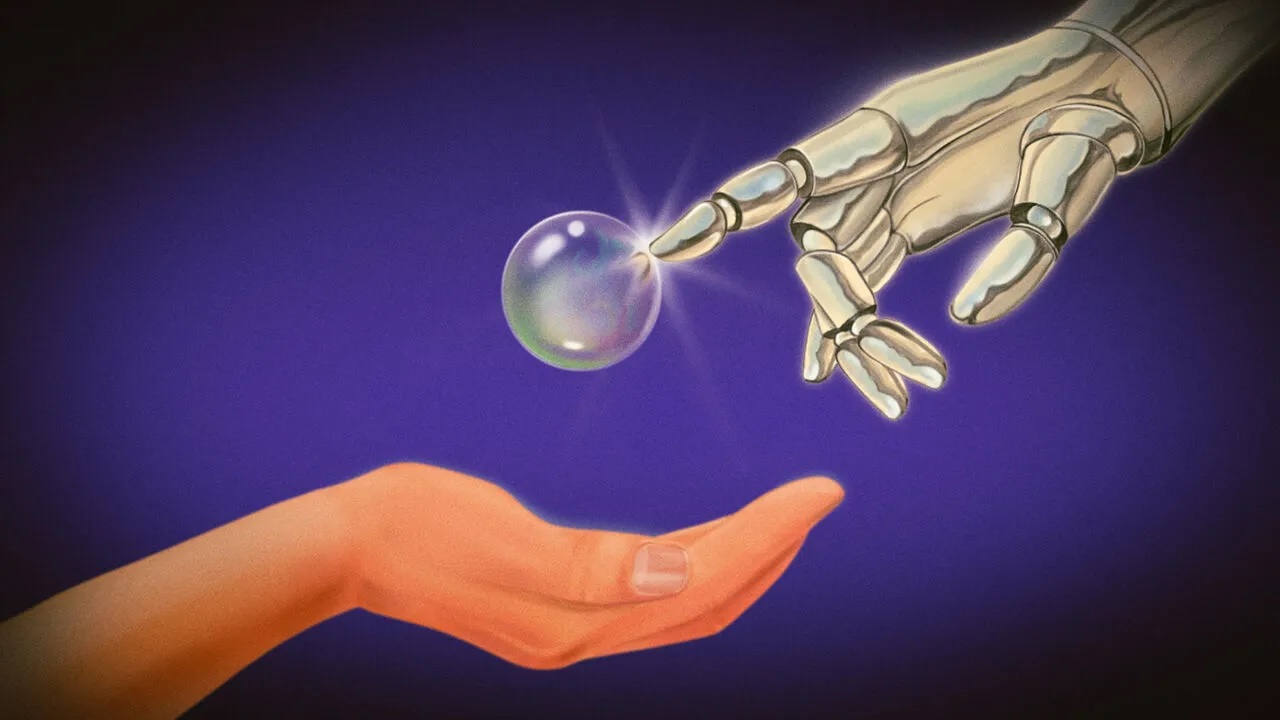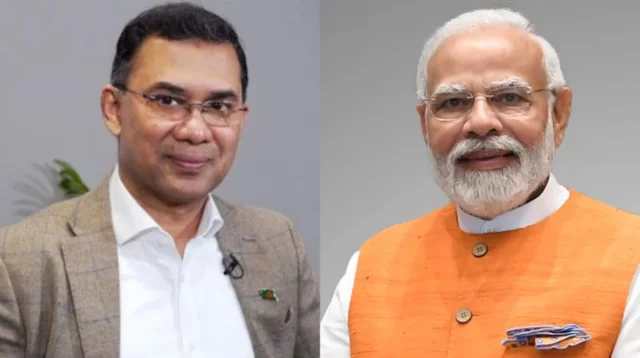আরেকটু হলেই খাদে পড়ে যেত ফাঁকা শেয়ারবাজার। না, আগারগাঁওয়ের সুউচ্চ অভিজাত সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ ভবন বা নিকুঞ্জের ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ভবন থেকে নয়, মনস্তাত্ত্বিক শেষরেখা সূচকে পাঁচ হাজারের নিচে নামতে নামতে কোনো রকমে ঝুলে আছে। আর এর সঙ্গে দৈনিক গড় লেনদেন যে নেমেছে তিনশ কোটির ঘরে, তাতেই শেয়ারবাজারে ধ্বস না বলার কোনো কারণ আছে কি? বিশ্লেষকরা নানান ব্যাখ্যা দিতেই পারেন, কিন্তু ঐ যে দেশের সবচেয়ে দুর্বল পাঁচ ব্যাংকের তিনটিই যদি থাকে টপ টেন গেইনারের তালিকায়, সেও কি অস্বাভাবিক নয়? ধরুন ঐ এক্সিম ব্যাংকের কথাই। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি যার দাম উঠেছিল ৪ টাকা ৪০ পয়সা, এক সপ্তাহেই তা যখন আবার নেমে যায় ৩ টাকা ৭০ পয়সায়, ভাবুন তো—ঝাঁপ দিয়ে পড়ে একটি সম্ভাব্য “ইউনাইটেড ইসলামিক ব্যাংকের” শেয়ারহোল্ডার হওয়ার আশা যদি কেউ এক লাখ শেয়ার চার লাখ চল্লিশ হাজারে কিনেছিল, তার শেয়ারের দাম কিন্তু হয়ে গেল তিন লাখ সত্তর হাজার। লোকসানটা পাঠক, আপনি হিসেব করে নিন। আর সেই টপ টেনে কিন্তু আরও ছিল এসআইবিএল আর ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংকের নামও।
শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার ৪৬৮ কোটি টাকা লেনদেনে সপ্তাহ শেষ হলেও এর আগের দিন কিন্তু তা নেমেছিল ৩৫৫ কোটিতে, যা ছিল চার মাস আগে। কিন্তু মাসখানেক আগেও হাজার কোটি টাকা লেনদেনের প্রদীপটা বলা যায় ধপ করেই প্রায় নিভন্ত! ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো আর গ্রামীণফোনের মতো কোম্পানির শেয়ারের দাম ক্রমশ নিম্নমুখী থাকলে কিন্তু সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বুক ধড়ফড়ই করতে থাকে। গত মাসের শেষ সপ্তাহে ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির প্রতিটি শেয়ারের দাম ২৮০ টাকার ঘরে থাকলেও গত সপ্তাহে তা নেমেছে ২৫৫ টাকায়। একই সময়ে যে জিপি ছিল ৩০০ টাকা, তাও কমে গেছে প্রায় ২০ টাকার মতো। ব্যাংক খাতের বেশির ভাগ শেয়ারের দাম কমেছিল, এক্ষেত্রে বরং ২ টাকা বা ৩ টাকার শেয়ারগুলোর দাম এবং কেনাবেচার সংখ্যা যখন বাড়তে থাকল, সেটাও কম অস্থিরতার প্রকাশ নয়।
কি বুঝে বিনিয়োগকারীরা বা কোন ধরনের শেয়ার ব্যবসায়ী ন্যাশনাল ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক বা এসআইবিএল এমনকি আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের শেয়ার কিনছিল, সেটা নিয়েও অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন হতে পারে। যা হোক, সপ্তাহের শেষে যে লেনদেন তিনশ কোটির নিচে আর সূচক পাঁচ হাজার থেকে কমে যায়নি, সেটাই আপাত রক্ষা। এখন দেখা যাক, কি হয় সামনের সপ্তাহে।

তবে হঠাৎ করেই শেয়ারবাজারের পতনের জন্য অনেকেই আবার দায় চাপাচ্ছেন খোদ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশনের কাঁধে। গণমাধ্যমে খবরও প্রকাশিত হয়েছে। মার্জিন ঋণ বিধিমালার সংশোধন ইস্যু লেনদেন কমার অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন বিভিন্ন ব্রোকারেজ হাউসের কর্মকর্তারা। তারা সাংবাদিকদের জানান, গত কয়েক মাস ধরে মার্জিন ঋণ বিধিমালা সংশোধনের প্রক্রিয়া চলছে। বাজারে এর প্রভাব রয়েছে। বিনিয়োগকারীদের এ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। ফলে দ্রুত এ প্রক্রিয়া শেষ করা উচিত।
বিএসইসির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো না হলেও শেয়ারবাজার-সংশ্লিষ্ট অনেকেই জানাচ্ছেন, সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন বিধিমালাটি চূড়ান্ত করেছে। এরই মধ্যে বাজার অংশীজনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় বিএসইসির চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে, যা কার্যকর হলে ১৬০ কোম্পানির শেয়ার মার্জিনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যদিও এমন সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। এ নিয়ে নানা গুজবও ছড়াচ্ছে। কমিশন প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে দিলে গুজব ছড়াত না বলেও মত দেন একটি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ এক কর্মকর্তা।
সমন্বয় সভা শেষে বিএসইসি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, সভায় বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ অতিসত্বর মার্জিন ঋণ বিধিমালার গেজেট প্রকাশ হবে বলে জানিয়েছেন। শঙ্কার কারণ নেই—এমন আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, ‘চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট সবার মতামত ও পরামর্শের আলোকে নতুন মার্জিন বিধিমালা করা হয়েছে। কার্যকরের পরও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের জন্য ছয় মাস থেকে এক বছর সময় থাকবে। এ বিষয়ে আগামী সপ্তাহে শীর্ষ ১০ ব্রোকারের সঙ্গে বৈঠক করা হবে।’
অর্থনীতিবিদরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, বাজারের অস্থিরতা সাময়িক। বিনিয়োগকারীদের উচিত আতঙ্কিত না হয়ে ধৈর্য ধরে থাকা। অযৌক্তিক ভয়ে শেয়ার বিক্রি করলে ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ে; বিপরীতে ধৈর্য ধরে বিনিয়োগ ধরে রাখলে ভবিষ্যতে ভালো মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একজন শীর্ষ ব্রোকারেজ হাউসের কর্মকর্তা বলেন, “আমরা বিনিয়োগকারীদের অনুরোধ করছি আতঙ্কিত হয়ে ‘প্যানিক সেল’ করবেন না। সাময়িক মন্দার পর বাজারে নতুন গতি আসবেই।”
বিশ্লেষকরা মনে করছেন, চলমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় কিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও বড় ধরনের পতনের আশঙ্কা নেই। বরং সরকারের নীতিগত সহায়তা ও আসন্ন বিনিয়োগবান্ধব উদ্যোগ পুঁজিবাজারে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে।
অবশ্য এসব মন্তব্য যারা গণমাধ্যমে করেন, তাদের মধ্যে তাত্ত্বিক জ্ঞানের মানুষই বেশি বলে মনে করেন সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। অবশ্য বাজার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে। অস্থির সময়ে ঠান্ডা মাথার সিদ্ধান্তই ভবিষ্যতে বড় মুনাফার পথ তৈরি করতে পারে।
এসব কথা কি কথা! যারা ৪০০ টাকার ওপরে ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো বা ৪৫০ টাকায় ওয়ালটন আর ৫০০ টাকার ঘরে রেনেটা কিনে বসে আছেন, তাদের কি হবে? আবার উল্টো এমন কথাও অনেকে বলেন, যে কে কার পরামর্শে বেশি দামে শেয়ার কিনবে, তার দায়িত্ব তো এসইসি বা ডিএসই নিতে পারবে না।

 সারাক্ষণ বিশ্লেষণ
সারাক্ষণ বিশ্লেষণ