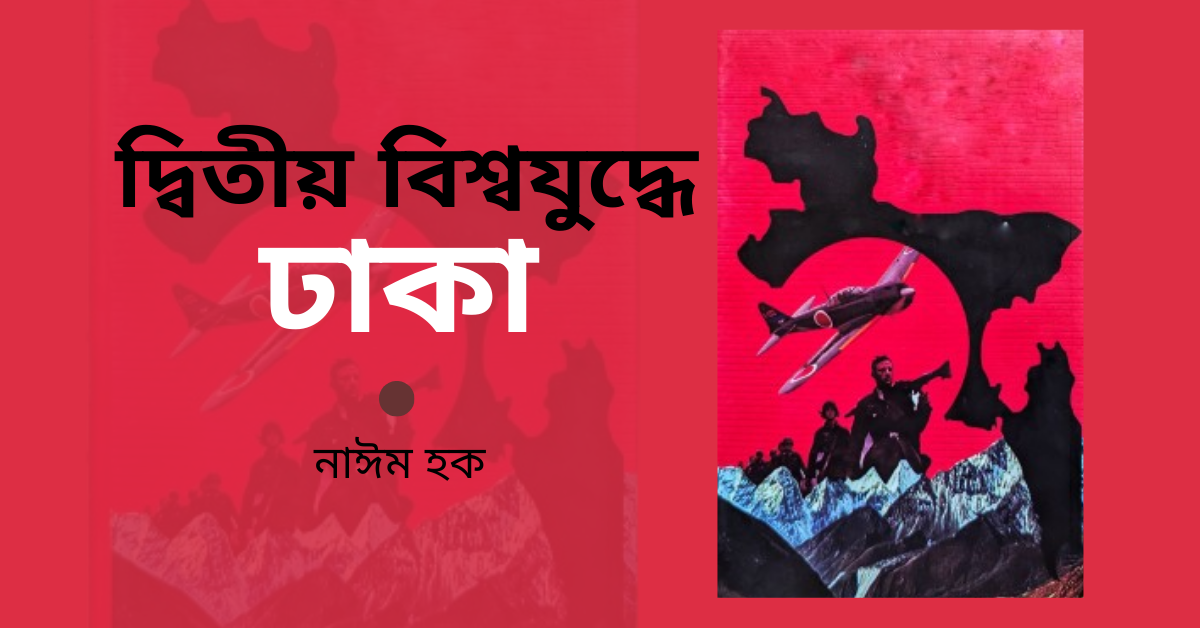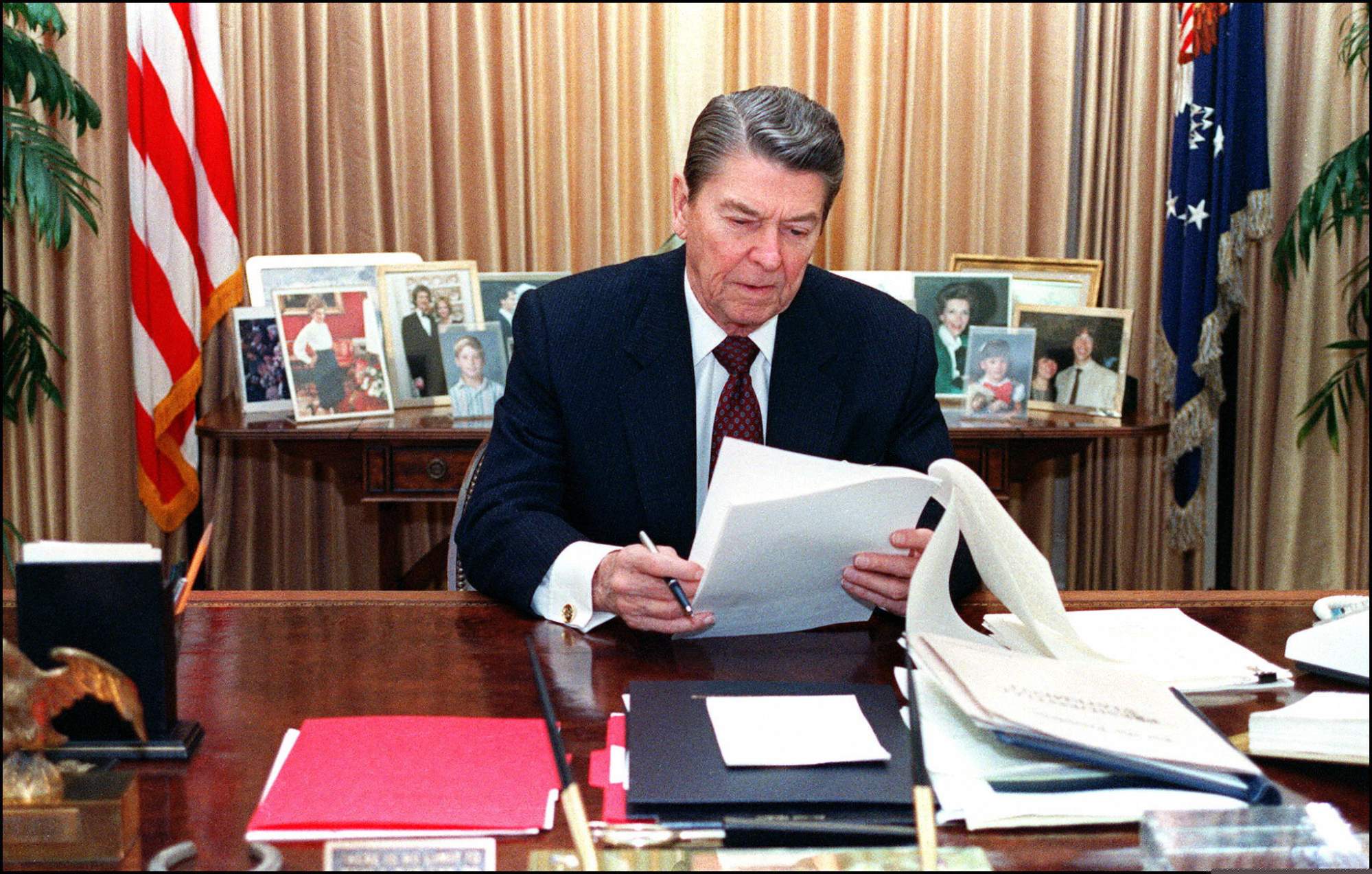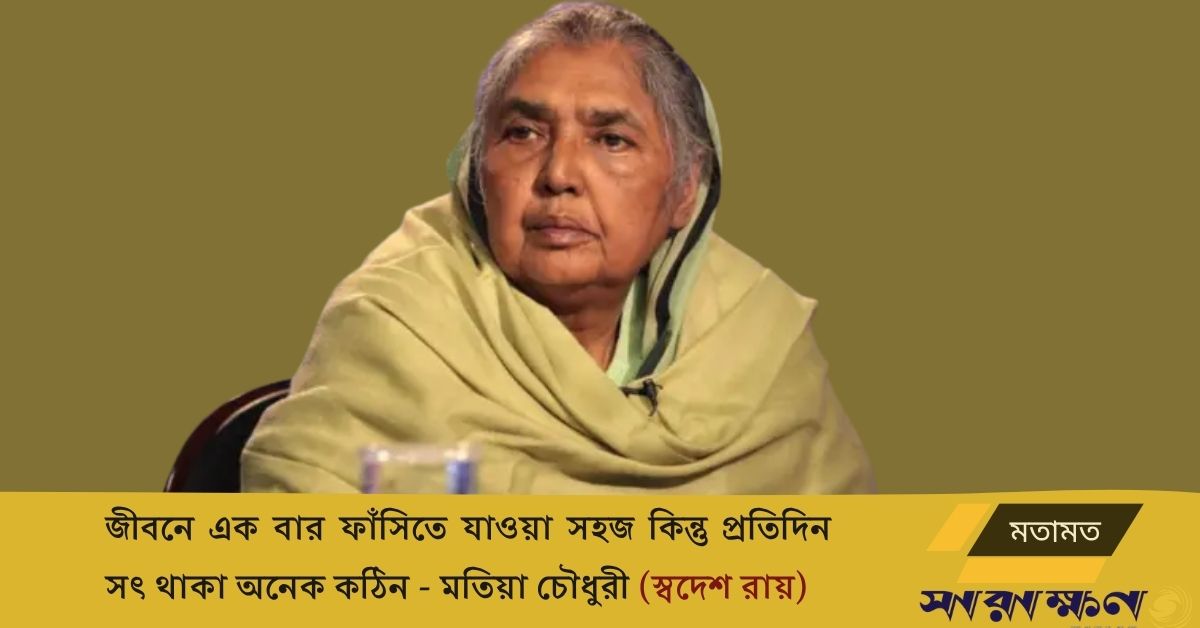ছোট বড় বিভিন্ন প্রজাতির গাছের সমারোহ। মাঝ দিয়ে পায়ে হাঁটা সরু পথ। এত কাছাকাছি গাছ আর লতা-গুল্মের ঝোপ, সূর্যের আলোও যেন ঠিকমতো মাটিতে পড়ছে না। দেখে মনে হচ্ছে, কয়েকশ বছর ধরে গড়ে ওঠা ঘন জঙ্গল।
একসময় দেশের গ্রামাঞ্চলে এমন দৃশ্য হরহামেশা চোখে পড়লেও এখন যেন দেখা মেলা ভার। খাদ্যপণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি সড়ক, কলকারখানা আর বসতবাড়ির চাহিদা মেটানোই যেন এখন মূখ্য। যাতে অনেকটাই হারিয়ে যেতে বসেছে এমন ক্ষুদ্র বনাঞ্চল।
সুন্দরবন কিংবা পার্বত্য এলাকার গহীন পাহাড়ি অরণ্যে এমন দৃশ্য চোখে পড়লেও নগর জীবনে এগুলো এখন আর খুব একটা চোখে পড়ে না। উল্টো কংক্রিটের চাহিদা মেটাতে গাছপালা কেটে পোড়ানো হচ্ছে ইটভাটায়।
এমন প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি উদ্যেগে চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে গড়ে উঠেছে একটি কৃত্রিম বন। যেখানে মাত্র চার হাজার ৪০০ বর্গফুট জায়গায় ছোট-বড় ১২০ প্রজাতির গাছ ও লতাগুল্মে মাত্র তিন বছরেই ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে।
এই প্রকল্পের উদ্যোক্তারা বলছেন, ‘মিয়াওয়াকি ফরেস্ট’ পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলকভাবে দেশের প্রথম কৃত্রিম বন তৈরিতে সফল হয়েছেন তারা।
এর মাধ্যমে কেবল সবুজের সমারোহই নয়, ওই এলাকার প্রকৃতি ও জীববৈচিত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলেও মনে করেন তারা।
প্রাকৃতিক কৃষি কেন্দ্রের উদ্যোক্তা ও পরিচালক দেলোয়ার জাহান বিবিসি বাংলাকে বলছেন, বিশেষ উপায়ে মাটি প্রস্তুত করে কোনো ধরনের রাসায়নিকের ব্যবহার ছাড়াই খুব কম সময়ে কৃত্রিম বন তৈরি সম্ভব মিয়াওয়াকি পদ্ধতিতে।
“যা ঘন করে রোপন করার কারণে দশ বছরেই একশ বছরের একটি ঘন বনের আকার ধারণ করে,” বলেন মি. জাহান।
তিনি বলছেন, “দেশের প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষায় বণাঞ্চল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পর্যায়ে ‘মিয়াওয়াকি ফরেস্ট’ অবশ্যই কার্যকর একটি উপায় হতে পারে। তবে আমাদের দেশে কয়েক বছর আগেও বাড়িঘরের আশপাশে যে ঝোপঝাড় বা ছোট বন প্রাকৃতিক উপায়েই তৈরি হতো সেগুলোও তো এখন নেই।”
বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে রিফরেস্টেশন বা অরণ্যায়ন করার ক্ষেত্রে ‘মিয়াওয়াকি ফরেস্ট’ পদ্ধতি ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক মো. দানেশ মিয়া।
তিনি বলছেন, “জাপানের একটা কনসেপ্ট এখানে বলা হচ্ছে । কিন্তু এই ধরনের বনাঞ্চল বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে কিন্তু ঐতিহ্যগতভাবে অনেক আগে থেকেই ছিল, কিন্তু অতিরিক্ত মানুষের কারণে এটা রাখা যায়নি।”

‘মিয়াওয়াকি ফরেস্ট’ আসলে কি
‘মিয়াওয়াকি ফরেস্ট’ মূলত বনায়নের একটি পদ্ধতি। জাপানি উদ্ভিদবিদ এবং উদ্ভিদ বাস্তুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আকিরা মিয়াওয়াকি বনায়নের এই পদ্ধতিটি তৈরি করেছিলেন।
যার মূল উদ্দেশ্য ছিল, প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাত্র ২০-৩০ বছরের মধ্যে শতভাগ জৈব, ঘন এবং বৈচিত্র্যময় বন তৈরি করা।
এই পদ্ধতির মাধ্যমে ছোট জায়গায় নিজেদের মত কৃত্রিম বন তৈরি করা যায়। যা স্বাভাবিক বনাঞ্চলের তুলনায় ১০ গুণ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে, অনেক বেশি ঘন এবং জীববৈচিত্র্য ধারণ করতে সক্ষম।
নির্দিষ্ট জলবায়ু পরিস্থিতি বিবেচনা করে, শুধুমাত্র সেই স্থানীয় প্রজাতিগুলোই রোপণ করা হয়, যা ওই অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবেই জন্মেছিল।
এ পদ্ধতিতে লাগানো গাছ প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা বনের গাছের তুলনায় ১০ গুণ দ্রুতগতিতে বড় হয়। এছাড়া অন্য সাধারণ বন থেকে এই বন ৩০ গুণ বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে পারে, যা এই পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা বনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।
বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করে বনাঞ্চল গড়ে তোলা হয়েছে। বিশেষ করে আকিরা মিয়াওয়াকির এই ধারণা কাজে লাগিয়ে ‘মিয়াওয়াকি ফরেস্ট’ গড়ে তুলে সুফল পাচ্ছে ভারত এবং নেদারল্যান্ড।
বাংলাদেশে মীরসরাই উপজেলার সোনাপাহাড় এলাকায় ‘প্রকল্প সোনাপাহাড়’ নামে একটি প্রকল্পে প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলকভাবে এই ‘মিয়াওয়াকি ফরেস্ট’ ধারণার বাস্তবায়ন করা হয় প্রায় তিন বছর আগে।
যেখানে এখন ছোট আকারের একটি বন তৈরি হয়েছে, যা ওই এলাকার জীববৈচিত্র্য রক্ষায়ও বড় ভূমিকা রাখছে।

এই পদ্ধতিতে বন তৈরির প্রক্রিয়া
মিয়াওয়াকি পদ্ধতি মূলত প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম এই দুইয়ের মিশ্রণ। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট অঞ্চলের গাছ সেই অঞ্চলেই রোপণ করতে হবে। কেবল চারা রোপণের আগে জমি প্রস্তুতির বিশেষ ধরণ রয়েছে সেটি অনুসরণ করেই এগোতে হবে।
বাংলাদেশে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি কৃত্রিম বন তৈরি করা হয়েছে চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ের সোনাপাহাড় ফার্মহাউজে।
এই প্রজেক্টে কর্মরত শামীম শেখ বিবিসি বাংলাকে জানান, এই পদ্ধতিতে বৃক্ষরোপণ প্রচলিত পদ্ধতি থেকে সামান্য আলাদা।
শুরুতে প্রাকৃতিক উপায়ে আলাদা জায়গায় মাটি প্রস্তুত করতে হয়, যেখানে কিছু জৈব সার ব্যবহার করা হয়, যেমন- গুঁড়ি, খড় ও লতাপাতা পঁচা। এরপর এক মিটার পরিমাণ ঢালু করে মাটি বিছিয়ে দেওয়া হয় যাতে বৃষ্টির সময় পানি জমে গাছের ক্ষতি করতে না পারে।
মিয়াওয়াকি পদ্ধতিতে ভারসাম্য তৈরি করতে একসাথে কাছাকাছি বিভিন্ন ধরনের গাছের মিশ্রণ রোপণ করা হয়।
যে এলাকায় এই পদ্ধতিতে বন তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে সেই এলাকায় যেসব গাছ প্রাচীন কাল থেকেই জন্মে বা সাধারণত বেশি হয়, ওই সব গাছই ব্যবহার করা উচিত। যাতে সহায়ক বাস্তুতন্ত্রে স্থানীয় পরিবেশের সাথে গাছের খাপ খাইয়ে নেয়া সহজ হয়।
এই পদ্ধতিতে সহায়ক পরিবেশে গাছগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এছাড়া খুব কাছাকাছি রোপণ করা চারাগুলিকে যেহেতু আলোর জন্য প্রতিযোগিতা করতে হয়, যা কেবল উপর থেকেই তাদের উপর পড়ে, তাই পাশের পরিবর্তে খুব দ্রুত উপরের দিকে বাড়তে থাকে।
উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষকরা মনে করেন, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অধিক ঝুঁকিতে থাকা শহরগুলোর জন্য এই পদ্ধতি বেশ কার্যকর।
কারণ এর মাধ্যমে খুব কম সময়েই নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক একাধিক বন গড়ে তোলা সম্ভব যা ওই এলাকার আবহাওয়া ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশে এই পদ্ধতি কতটা কাজে দিবে
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সাধারণ হিসেবে একটি দেশের মোট আয়তনের ২৫ শতাংশ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন। তবে, বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ এর থেকে অনেক কম, যা দেশের মোট ভূমির প্রায় ১৫ দশমিক ৫৮ শতাংশ।
শুধু বাংলাদেশ নয় বনভূমি কম থাকার বিরূপ প্রভাব উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে সম্প্রতি বড় মাত্রায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে গত কয়েক বছর ধরেই বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে ধারাবাহিকভাবে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে জানা যায়, গত তিন দশক ধরে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা আগের তিন দশকের চেয়ে তীব্রভাবে বাড়ছে।
অর্থাৎ, ১৯৬১ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলের তাপমাত্রা তুলনামূলক কম ছিল। কিন্তু ১৯৯১ সালের পর থেকে এটি ক্রমশ বাড়ছেই।
জলবায়ু ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বাংলাদেশে সবুজায়ন বা বৃক্ষ রোপণের কথা সব সময় বলা হলেও তাতে কাজ হচ্ছে কতটা, এ নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।
এমন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য ‘মিয়াওয়াকি ফরেস্ট’ পদ্ধতি কম সময়ে ছোট ছোট বনভূমি তৈরির ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর একটি উপায় হতে পারে বলেই মনে করেন সৈয়দা সারওয়ার জাহান। তিনি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য এলাকায় বনায়ন কর্মসূচির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন ।
বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছেন, “স্বল্প জায়গা প্রয়োজন হয় বলে মিয়াওয়াকি ফরেস্ট পদ্ধতি আমরা খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারি। আমাদের দেশে জায়গার স্বল্পতা রয়েছে, খুব বেশি সারের প্রয়োজন হয়না, কেবল প্রাকৃতিক উপায়ে কিছু জৈব সার ব্যবহার করলেই হয়।”
এর মাধ্যমে কম সময়ে বনাঞ্চলের চাহিদাও যেমন মিটবে, তেমনি জীববৈচিত্র্যের স্বাভাবিক ধারাও রক্ষ করা যাবে, বলেন তিনি।
চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে গড়ে ওঠা মিয়াওয়াকি ফরেস্ট প্রকল্পের সঙ্গে শুরু থেকে যুক্ত ছিলেন প্রাকৃতিক কৃষি কেন্দ্রের উদ্যোক্তা ও পরিচালক দেলোয়ার জাহান।
তিনি বলছেন, প্রথম দুই থেকে তিন বছর পরে রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত এবং নয় বর্গমিটারের মতো ছোট জায়গায় এটি তৈরি করা যেতে পারে, তাই মিয়াওয়াকি বন দ্রুত জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করা প্রয়োজন, এমন শহরগুলোর জন্য কার্যকর সমাধান।
বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে মিয়াওয়াকি ফরেস্ট পদ্ধতিই হোক কিংবা সামাজিক বনায়ন হোক- যেকোনো ভাবেই গাছের সংখ্যা বৃদ্ধির বিকল্প নেই বলেই মনে করেন মি. জাহান।
এছাড়া জলাশয় ভরাট করার যে অশুভ প্রতিযোগিতা দেশজুড়ে শুরু হয়েছে, সেটিও বন্ধ করার কথা বলছেন তিনি।
বাংলাদেশে মিয়াওয়াকি ফরেস্ট পদ্ধতিতে ছোট ছোট বনাঞ্চল তৈরি করলে জীববৈচিত্র্যে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেই মনে করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক মো. দানেশ মিয়া।
তবে বাংলাদেশে যেভাবে জন্যসংখ্যা ও খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে, তার বিপরীতে ভূমির পরিমাণ কমে আসছে, তাতে এই ধরনের বন যুগের বিবর্তনে টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে বলেও মনে করেন তিনি।
মি. মিয়া বলছেন, “একটা জেনারেশন এই পদ্ধতিতে বনাঞ্চল তৈরি করলো নেক্সট জেনারেশন মনে করলো যে তাদের সেখানে একটা ঘরবাড়ি তৈরির প্রয়োজন আছে, তখন এটি আবারো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, যেটা অতীতেও হয়েছে।”
বিবিসি বাংলা

 Sarakhon Report
Sarakhon Report