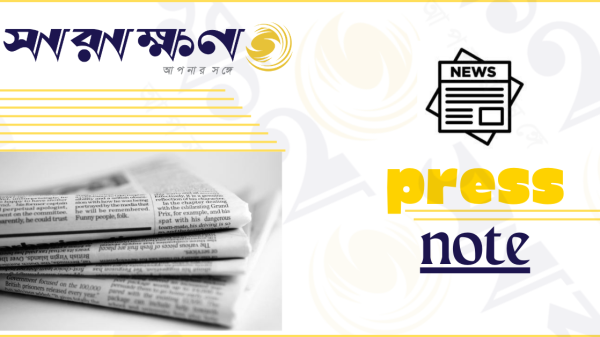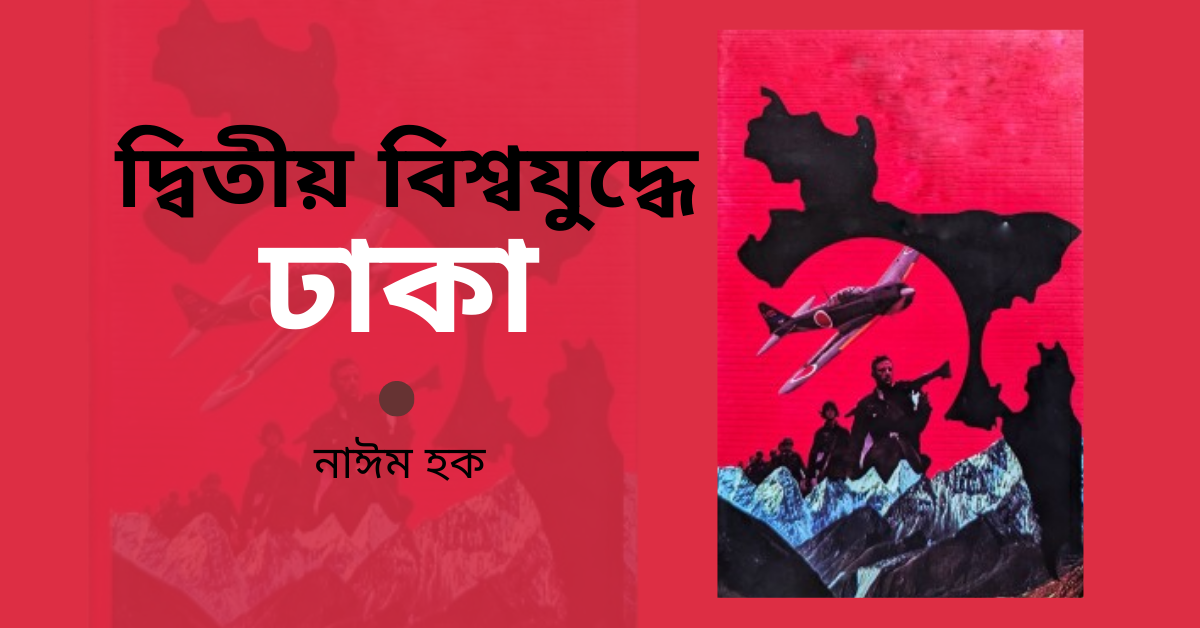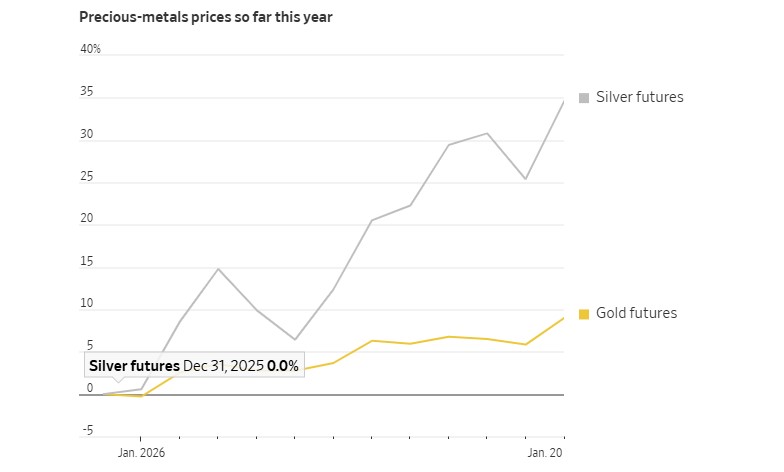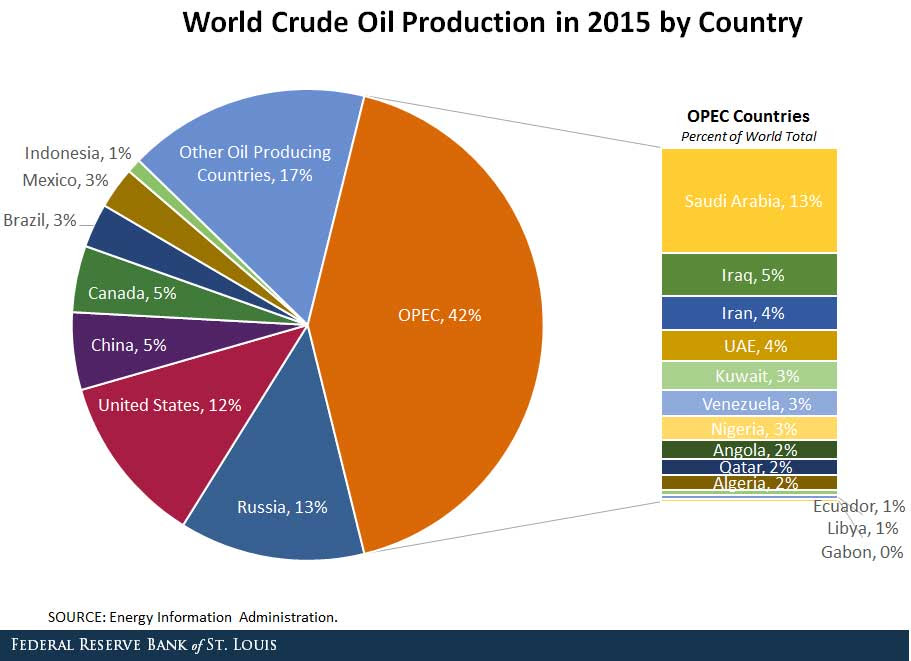১৭ নভেম্বর ব্রিটেনের দু’জন সফল জাতিগত সংখ্যালঘু রাজনীতিক—হোম সেক্রেটারি শবানা মাহমুদ এবং কনজারভেটিভ পার্টির নেতা কেমি বাডেনখ—অভিবাসন ও জাতিগত বিভাজন নিয়ে একটি বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। দু’জনের বক্তব্যেই ছিল হতাশার সুর। মাহমুদ বলেন যে অভিবাসন দেশের ভেতরে বিভাজন বাড়িয়েছে। অপরদিকে বাডেনখ সতর্ক করে দেন যে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও ঘৃণা ক্রমশ জমতে শুরু করেছে।
ব্রিটেনের আশ্রয় নীতিতে বড় পরিবর্তনের ঘোষণা
শবানা মাহমুদ আশ্রয় ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তনের প্রস্তাব দেন। তিনি যুক্তি দেন যে ব্রিটেন আশ্রয়প্রার্থীদের বিষয়ে অতিরিক্ত নরম হয়ে উঠেছে এবং সেই কারণেই রাষ্ট্র আর আর্থিকভাবে অসহায় আশ্রয়প্রার্থীদের সহায়তা দেওয়ার আইনগত বাধ্যবাধকতা রাখবে না। তিনি মানবাধিকার আইনের যেসব ধারা বহিষ্কারে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলো শিথিল করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং আরও বেশি পরিবারকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করার কথা বলেন। বর্তমানে নির্যাতন বা সহিংসতা থেকে বাঁচতে যেসব মানুষ আশ্রয় পান, তারা সাধারণত পাঁচ বছরের জন্য আশ্রয় পান এবং এরপর নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারেন। কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের মাত্র ৩০ মাসের জন্য আশ্রয় দেওয়া হবে এবং প্রতি ৩০ মাস পর নবায়ন করতে হবে। যদি তাদের নিজ দেশ নিরাপদ হয়ে ওঠে, তবে নবায়ন নাও হতে পারে এবং অনেককে নাগরিকত্বের জন্য অপেক্ষা করতে হতে পারে ২০ বছর পর্যন্ত।
অভিবাসন নিয়ে ব্রিটিশদের উদ্বেগ
ইপসোসের জরিপ অনুযায়ী অভিবাসন এখন ব্রিটেনে সবচেয়ে বড় জাতীয় ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। গত বছর মোট ১,০৮,০০০ মানুষ আশ্রয়ের আবেদন করেছে, যা এক রেকর্ড সংখ্যা। ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেন বছরে প্রায় ৪০ হাজার মানুষ, যা জনমনে আরও বেশি প্রভাব ফেলে। অথচ বাস্তবে কর্মী, ছাত্রসহ অন্য বড় গোষ্ঠীর অভিবাসীরা ব্রিটেনে প্রবেশ করে, যাদের নিয়ে আলোচনায় তুলনামূলকভাবে কম মনোযোগ দেওয়া হয়।

ডেনমার্ক: ব্রিটেনের নতুন অনুপ্রেরণা
১৭ নভেম্বর সরকারের প্রকাশিত নীতিপত্রে ডেনমার্কের নাম এসেছে সাতবার। ডেনমার্ক ২০০০ সালের পর থেকেই আশ্রয় নীতিকে কঠোর করেছে। এক দশক আগে বড় আশ্রয় আবেদন ঢলের পর তারা আশ্রয় প্রক্রিয়াকে সাময়িক করে এবং প্রয়োজনে শরণার্থীদের গয়না পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করার নীতি নেয়। এসব পদক্ষেপের ফলে আশ্রয় আবেদন দ্রুত কমে যায়। লেবার পার্টির কাছে বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, কারণ এসব কঠোর নীতি নেওয়ার পরও ডেনমার্কে কেন্দ্র-বাম দল বহু বছর ক্ষমতায় ছিল।
কঠোরতার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন
মাহমুদের পরিবর্তনগুলো বাস্তবায়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও দুটি বড় ঝুঁকি রয়েছে। প্রথমত, নীতি প্রয়োগ করলেই আবেদন কমবে—এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। দ্বিতীয়ত, ডেনমার্কের নীতি নকল করতে গিয়ে ব্রিটেন ডেনমার্কের মতো দুর্বল অভিবাসী-সমন্বয় ব্যবস্থাও নকল করে ফেলতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০২২ সালে প্রীতি প্যাটেলও অনুরূপ কঠোর নীতি ঘোষণা করেছিলেন এবং পরের বছর ঘোষণা আসে যে অনেক আবেদনকারীকে ব্রিটেনে আশ্রয়ই দেওয়া হবে না, বরং রোয়ান্ডায় পাঠানো হবে। তবুও আবেদন সংখ্যায় তেমন পরিবর্তন হয়নি। অনেকের মতে ব্রিটেনের বড় অভিবাসী সম্প্রদায় এবং ইংরেজি ভাষার আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা সরকার চাইলে পরিবর্তন করতে পারে না, যা দেশটিকে আশ্রয়প্রার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে রাখে। তাছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসার পর ব্রিটেন আর ইউরোপের মতো ফিঙ্গারপ্রিন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে আবেদনকারীদের আগের অবস্থান যাচাই করতে পারে না, ফলে অনেকের কাছে ব্রিটেন দ্বিতীয় সুযোগ হিসেবে রয়ে যায়।
ডেনমার্কের কঠোরতা সফল, সমন্বয় ব্যর্থ
ব্রিটেনে অনেকেই ডেনমার্ককে স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা ও সৌন্দর্যের দেশ হিসেবে দেখেন। কিন্তু বাস্তবে অভিবাসী সংহতকরণে ডেনমার্কের রেকর্ড দুর্বল। ব্রিটেনে স্থানীয় ও বিদেশি বংশোদ্ভূত কর্মীদের চাকরির হার প্রায় সমান এবং অনেক ক্ষেত্রে অভিবাসীরা বেশি আয় করে। কিন্তু ডেনমার্কে স্থানীয়দের চাকরির হার অভিবাসী ও অভিবাসী সন্তানদের তুলনায় অনেক বেশি। OECD–এর PISA পরীক্ষায় দেখা যায়, ডেনমার্কে অভিবাসী শিশুদের শিক্ষার ফলাফল দুর্বল, আর ব্রিটেনে তারা ভালোই করে। এমনকি গণিত ও পাঠে ব্রিটিশ অভিবাসী শিশুদের স্কোর ডেনিশ শিশুদের চেয়েও বেশি।
ইতিহাসগতভাবে ডেনমার্ক ১৯৬০-এর দশকে ‘গেস্ট ওয়ার্কার’ বা অস্থায়ী শ্রমিক নিয়ে আসে, যা অস্থায়ী থাকার ধারণা তৈরি করে। অন্যদিকে ব্রিটেন মূলত কমনওয়েলথ দেশগুলো থেকে মানুষ এনেছিল, যারা স্থায়ীভাবে নিজেকে ব্রিটিশ হিসেবে দেখত এবং তীব্র বর্ণবাদ সত্ত্বেও সেই পরিচয় ধরে রাখতে দৃঢ় ছিল।

ডেনমার্কে সংকেতের দ্বৈততা
ডেনিশ রিফিউজি কাউন্সিলের ইভা সিঙ্গার জানান যে ডেনমার্কে রাষ্ট্রের একাংশ আশ্রয়প্রার্থীদের দ্রুত ভাষা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কাজ শেখানোর চেষ্টা করে। কিন্তু জাতীয় সরকার বারবার মনে করিয়ে দেয় যে তারা এখানে সাময়িকভাবে আছে। এই দ্বৈত বার্তা অভিবাসীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তা তৈরি করে, যা তাদের সমন্বয়ের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
নাগরিকত্বের শক্তি
লুক্সেমবার্গ ইনস্টিটিউটের ক্রিস্টিনা গাথমান দেখিয়েছেন যে জার্মানিতে নাগরিকত্ব পাওয়া সহজ হওয়ার পর অভিবাসী নারীরা বেশি উপার্জন করতে শুরু করেন, দেরিতে বিয়ে করেন এবং কম সন্তান নেন। ইউরোপের শরণার্থীদের ক্ষেত্রেও একই অভিজ্ঞতা পাওয়া গেছে। কারণ নাগরিকত্ব দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত দেয়—একটি হলো অভিবাসীর কাছে যে তিনি নিরাপদ; অন্যটি হলো নিয়োগদাতার কাছে যে ওই ব্যক্তি দেশে স্থায়ীভাবে থাকবেন, ফলে তার ওপর বিনিয়োগ করা যায়।
কিন্তু মাহমুদের নীতির লক্ষ্য ঠিক এর বিপরীত। তিনি শরণার্থীদের আরও অনিরাপদ করে তুলতে চান, যেন কম মানুষ দেশে আসে। একই সঙ্গে যারা আসবে তাদের অনেককে মূলধারার সমাজের বাইরে রেখে বহুসংস্কৃতিবাদকে রক্ষা করতে চান। নীতি সফল হবে কি না, তা এখনো অনিশ্চিত। তবে এটি নিঃসন্দেহে এক অদ্ভুত ও পরীক্ষামূলক ধারণা।
ব্রিটেন ডেনমার্কের কঠোর আশ্রয় নীতি নকল করতে চাইছে, কিন্তু যদি এর সঙ্গে ডেনমার্কের দুর্বল সমন্বয় পদ্ধতিও নকল হয়ে যায়, তবে সমস্যাই বাড়বে। আশ্রয় প্রক্রিয়ায় কঠোরতা আনা তুলনামূলকভাবে সহজ, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে অভিবাসীদের সফলভাবে সমাজে সম্পৃক্ত করা অনেক বেশি কঠিন কাজ।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট