বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় আড়াইশ কিলোমিটার দূরে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার মনিরামপুর উপজেলা। ২০২৪-এ এখানে বন্যা হয়েছিলো। এবার এখন সেখানে হেমন্ত সিজনের ধান, “আমন ধান” কাটার সময় এসে গেছে। এই এলাকার প্রান্তিক চাষী মহিবুল্লাহ বললেন, এই সরকারের আমাদের কথা ভাবার সময় নেই। তারা কী কাজ করছে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ— আমরা বুঝি না। গত বছর বন্যা হয়েছিলো, সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে কিছুই করা হয়নি। এবার আগাম ধান কেটেছি, তবুও যে দামে ধান বিক্রি করতে হচ্ছে তাতে চাষের খরচ উঠবে না।অন্যদিকে সব জিনিসের দাম বেশি।
এই অবস্থা কি শুধু এই এক বছরের বেশি সময় হয়েছে না আগেও ছিলো? এমন একটি প্রশ্ন করতে সে প্রশ্নকর্তাকে উত্তর দিতে ভয় পায়। তারপরে অনেকটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চার পাশে তাকিয়ে বলে, আগে তো যাই হোক চলতে পারতাম। কাজকর্ম ছিলো। এখন তো আর চলতে পারছি না।
বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা সম্পর্কে কয়েক বছর আগেও একটা কথা ছিলো ঢাকার বাতাসে টাকা ওড়ে। গ্রামের অফ সিজনে আর দুই ঈদের আগে ঢাকার রাজপথ ভরে যেতো রিকশায়। ঈদের খরচ আর বাড়তি কিছু আয় করার জন্যে এ ছিলো গ্রামের এক শ্রেণীর মানুষের সহজ উপায়।
আবার স্থায়ী রিকশাওয়ালাও আছে। যারা দশ-পনের বছর ধরে ঢাকায় থেকে রিকশা চালিয়ে গ্রামে সংসার চালায়। ঢাকার বস্তিতেও বাসা ভাড়া নিয়ে পরিবারসহ থাকে।
ঢাকায় পনের বছর ধরে রিকশা চালাচ্ছে রংপুরের রশিদ। সে শেখ হাসিনার সরকার পতনের আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলো। আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কারণ হিসেবে তার বক্তব্য, তাকে অনেকে বলেছিলো শেখ হাসিনা ব্যাংকের টাকা সব বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। আর ভারতীয় রেলগাড়ি দেশের ভেতর দিয়ে যাবে, যা দিয়ে ভারত আমাদের সব জিনিসপত্র নিয়ে যাবে। আমাদের এখানে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে। এটা ঠেকাতে হবে।

তার কথায়, “কয়েকদিন ছাত্রদের সঙ্গে যাওয়ার পরে তো দেখলাম, শেখ হাসিনার সরকার পড়ে গেলো। এখন দেখছি ভারতের থেকে পেঁয়াজ, চাল, এমনকি কাঁচা মরিচ না আনলে আমাদের কোনো উপায় নেই। এ সপ্তাহে মাত্র ৫’শ গ্রাম পেঁয়াজ কিনেছি। কারণ, পেঁয়াজের দাম ১২০ টাকা কেজি।”
তার আয় বেড়েছে কিনা জানতে চাইলে উত্তর দেয়, “আপনারা শিক্ষিত মানুষ, আপনারা বোঝেন না আমরা কী অবস্থায় আছি। আগে মালিকের রিকশার ভাড়া, গ্যারাজের ভাড়া দিয়েও দিনে ১৫’শ টাকা থাকতো। আর এখন দিনে তিনশ, চার’শ—দুই একদিন মাত্র ৫’শ টাকা থাকে। ৬০ টাকা চাল, ১২০ টাকা পেঁয়াজ, মাছ ছুঁয়ে দেখার উপায় নেই, পোল্ট্রি মুরগিও ২’শ টাকার ওপরে কেজি। পাঁচজনের সংসার—মরা ছাড়া কি উপায় আছে?”
কোভিড-১৯ এর আগে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা ছিলো সবচেয়ে ভালো। ছোট দেশ হয়েও কোভিডের পরেও ২০২১ সালে শ্রীলংকাকে ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়ে দাতা দেশের খাতে নাম লিখিয়েছিলো বাংলাদেশ। তবে তারপরে ২০২৩-এর দিকে কোভিড-উত্তর প্রকৃত অর্থনৈতিক শক যখন প্রকাশ পায় তখন আবার আইএমএফ-এর বাজেট সাপোর্ট নিতে বাধ্য হয়।
বর্তমানে ওই বাজেট সাপোর্টের ঋণের কিস্তি বন্ধ রেখেছে আইএমএফ। তারা বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে, এই অস্থিতিশীল সরকার পরবর্তী স্থিতিশীল সরকারের সঙ্গে আলোচনার পর তারা ওই ঋণের বাকি অংশ দেবে।
কিন্তু আইএমএফ-এর ঋণ যে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন খুব দ্রুত ঘটাতে পারবে তা বলা যাচ্ছে না। কারণ, বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল পিলারগুলো ভেঙে না গেলেও আক্রান্ত হয়েছে।
যেমন বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের মূল সোর্স গার্মেন্টস শিল্প। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের হিসাব অনুযায়ী বর্তমান ইন্টারিম ব্যবস্থা দায়িত্ব নেওয়ার পর গত এক বছরে বাংলাদেশের দুটি প্রধান গার্মেন্টস শিল্প এলাকায়—সাভার ও গাজীপুরে—বন্ধ হয়েছে ৩৫৬টি কারখানা। আর এই ৩৫৬টি কারখানা বন্ধ হবার ফলে বেকার হয়েছে তাদের হিসাবে ১ লাখ ৪ হাজার শ্রমিক।
কিন্তু এখানে এই অফিসিয়াল হিসাবের বাইরেও আরেকটি হিসাব আছে। বাংলাদেশে অধিকাংশ গার্মেন্টসই কন্ট্রাক্টে একটি বড় অংশ শ্রমিককে কাজ করায়। তাহলে তাদেরকে আর সরকার নির্ধারিত ওয়েজ বোর্ডে বেতন দেওয়া লাগে না। সেই বেকারের সংখ্যার কোনো হিসাব নেই। তবে তাদের সংখ্যা কম নয়।
আবার বাংলাদেশে এই ধরনের ৩৫৬টি গার্মেন্টস কারখানার সঙ্গে প্রায় সমসংখ্যক বা সংখ্যায় আরও বেশি ছোট ছোট আনরেজিস্টার্ড গার্মেন্টস জড়িত থাকে। তারা এই সব কারখানার কাছ থেকে কন্ট্রাক্টে কাজ নেয়। তারা যেহেতু আনরেজিস্টার্ড, তারা আরও কম বেতনে শ্রমিকদের কাজ করাতে পারে। তাই বিপুল সংখ্যক মানুষ সেখানে কাজ করে। এ বাস্তবতা থেকে বলা যায়, ৩৫৬টি কারখানায় যেমন ১ লাখ চার হাজার শ্রমিক বেকার হয়েছে, এর সঙ্গে জড়িত আনরেজিস্টার্ড কন্ট্রাক্ট গার্মেন্টসগুলোতেও কমপক্ষে আরও ১ লাখ ৪ হাজার শ্রমিক বেকার হয়েছে।

এর পরে বাংলাদেশে যে সিনথেটিক জুতা ও চামড়ার জুতা রপ্তানি করে সেখানেও বহু শ্রমিক বেকার হয়েছে। শ্রমিক বেকার হয়েছে প্লাস্টিক শিল্পে, শিপ ব্রেকিং শিল্পে, সিমেন্ট শিল্পে, নির্মাণ শিল্পে, এমনকি এগ্রো-বেসড শিল্পেও। যেমন বাংলাদেশের এগ্রো-বেসড শিল্পের একটি বড় বাজার ছিল ভারতের সেভেন সিস্টার্সে। ভারতের ল্যান্ড পোর্ট বন্ধ ও কড়াকড়িসহ নানা বিধিনিষেধ আরোপ করায় বাংলাদেশ সে বাজারের বড় অংশ হারিয়েছে। আর এর বিপরীতে শ্রমিক বেকার হয়েছে। তাছাড়া মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় ক্রেতা কমে গেছে। যার ফলে বিভিন্ন শপিং মলেও শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। সারাদেশে তাদের সংখ্যাও কম নয়।
তাই বাংলাদেশে কৃষিকাজের শ্রমিক বা কৃষক থেকে শুরু করে শহরের রিকশা শ্রমিক এরা যেমন এক ধরনের ছদ্মবেকারত্বে ঢুকে গেছে, তেমনি পুরোপুরি বেকার হয়েছে গার্মেন্টস থেকে এগ্রো-বেসড শ্রমিক। গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেকার হবার কয়েকটি নমুনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।
অন্যদিকে বাংলাদেশের অন্যতম অর্থনৈতিক রিসার্চ প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস-এর গবেষণায় উঠে এসেছে গত এক বছরে ৩ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে নেমে গেছে। অন্যদিকে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে ১৩ লাখে পৌঁছেছে। বারবার সরকারি কর্ম কমিশন পরীক্ষা নিয়েও কোনো কিছু করতে পারছে না। কারণ, সরকারি চাকরির সুযোগ খুবই সীমিত।
অন্যদিকে বাংলাদেশে গত তিন দশক ধরে যে প্রাইভেট সেক্টর গড়ে উঠেছিলো—গত দশ বছরে যা অনেকটা বিকশিত হয়েছিলো—তা শুকিয়ে যাচ্ছে। ব্যাংক থেকে প্রাইভেট সেক্টরের লোন নেওয়ার হার ও ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানির হার তার বড় প্রমাণ।
গত এক বছরে প্রাইভেট সেক্টরে ঋণ কমেছে ৬.৫%। ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানি কমেছে ২৫%। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে প্রাইভেট সেক্টর আর আগের মতো জব ক্রিয়েশনের পথ সৃষ্টি করছে না।
অন্যদিকে, সোভরেন বন্ড ক্রয় কমেছে ৬০০০ কোটি টাকার। এবং ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট কমেছে ২২%। ইন্টারিম ব্যবস্থা অবশ্য এখানে ১৯% বৃদ্ধি দেখিয়েছে—যা সরকারের একটি সাজানো হিসাব। অর্থাৎ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর লাভের অংশ সরকার এবার বাংলাদেশে থেকে নিতে দেয়নি। ওটাকেই ফরেন ইনভেস্টমেন্টের হিসাবে দেখানো হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে তো কমেছে ২২%।
অন্যদিকে ব্যাংকিং খাতে সুব্যবস্থা আনার জন্যে যেভাবে পাঁচটি ব্যাংককে মার্জার করা হচ্ছে—তা ব্যাংকিং খাত নয়, শেয়ার বাজার ঘিরেও ভীতি তৈরি করছে।

ব্যাংক ব্যবসাটি খুবই সেনসিটিভ বিষয়—পৃথিবীর সবাই স্বীকার করবেন। কারণ, ব্যাংকিং ব্যবসাটাই নির্ভর করে আস্থার ওপর। সরকারকে এখানে সংস্কার বা কোনো ক্ষত কাটাতে হলে খুব কৌশলী হতে হয়। শক্তি প্রয়োগ ও প্রচার এখানে বুমেরাং হয়। প্রচার করতে গিয়ে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বলেছেন, ২৮টি ব্যাংক রুগ্ন। অথচ ২৮টির নাম বলেননি। এ অবস্থায় মানুষ প্রতিটি ব্যাংক নিয়ে সন্দেহ করছে। তাই ব্যাংকে যেমন টাকা কম যাচ্ছে তেমনি ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে নেওয়ার জন্যে গ্রাহকের মধ্যে একটা চাপা তাগিদ রয়েছে।
আবার যে পাঁচটি ব্যাংককে মার্জার করার কাজ চলছে, সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বলা হয়েছে, এই পাঁচটি ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী অর্থাৎ এই ব্যাংকগুলোর শেয়ার যারা কিনেছিলেন তাদের বিনিয়োগ এবং যারা এই ব্যাংকগুলোর স্পন্সর শেয়ার হোল্ডার তাদের বিনিয়োগ—এখন শূন্য। এটা শুধু বেআইনি নয়, সার্বিক অর্থনীতির জন্যেও ক্ষতিকর। কারণ, এখন যাদের কাছে অন্যান্য ব্যাংকের শেয়ার আছে—তারা সেগুলো যে দাম পায় সেই দামেই দ্রুত বিক্রি করে দেবে। যার ফলে শেয়ারবাজারের পতন ঠেকানোর কোনো পথ থাকবে না।
যার ফলে গত ১৩ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টা মি. ইউনূস যখন তার ভাষণে বলছিলেন দেশের অর্থনীতির সব সূচক ঊর্ধ্বমুখী—সে সময়ে দেশের শেয়ারবাজারের সূচক ছিল সর্বকালের সর্বনিম্ন, অর্থাৎ ১২২।
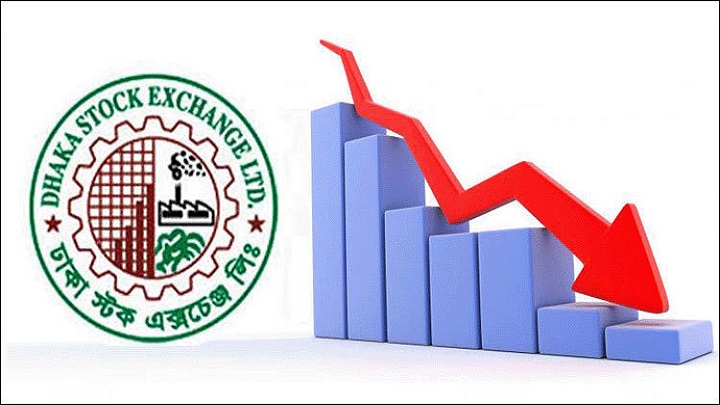
অন্যদিকে আর্টিফিশিয়ালি ডলার মার্কেট নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে নিয়মিত ডলার কিনছে। আর্টিফিশিয়ালি ডলার মার্কেট ধরে রাখলে তার ফল কী হয় সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর যাই হোক একটা প্রকৃত ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে এই ব্যবস্থা যায় না।
অন্যদিকে বাংলাদেশে এই হেমন্তে মাছ ও সবজি বেশি বাজারে আসে। তারপরেও দুটোই সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। আর এই দামের ফলে দেশের মূল্যস্ফীতি এখন কোনো কোনো হিসাব মতে ৮.৩৬, কোনো হিসাব মতে ৯-এর ওপরে।
এই মূল্যস্ফীতির ফলে দরিদ্র শ্রেণীর অবস্থা কী তার ছবি কিছুটা লেখার শুরুতেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। অন্যদিকে, সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সবচেয়ে বড় সংকট পড়েছে পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রোটিন জোগানো এবং ছোটদের শিক্ষা ও বৃদ্ধদের চিকিৎসা ব্যয় জোগানো।
মাত্র ১৮ মাস আগে যে দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথপ্রদর্শক হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ায় সবার কাছে বিস্ময় ছিলো—সেই দেশের মানুষ এখন বেঁচে থাকার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। খুব দ্রুত এ সংকট থেকে বের হয়ে আসারও কোনো পথ আছে বলে প্র্যাকটিকাল অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট কেউ মনে করেন না।
লেখক: বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক, সম্পাদক, সারাক্ষণ, The Present World.
( এই লেখাটি পাকিস্তানের The Financial Daily তে প্রকাশিত হয়। এটা তার বাংলা অনুবাদ। The Financial Daily তে প্রকাশিত ই- পেপার কপি লেখার ভেতরে দেয়া হলো।)
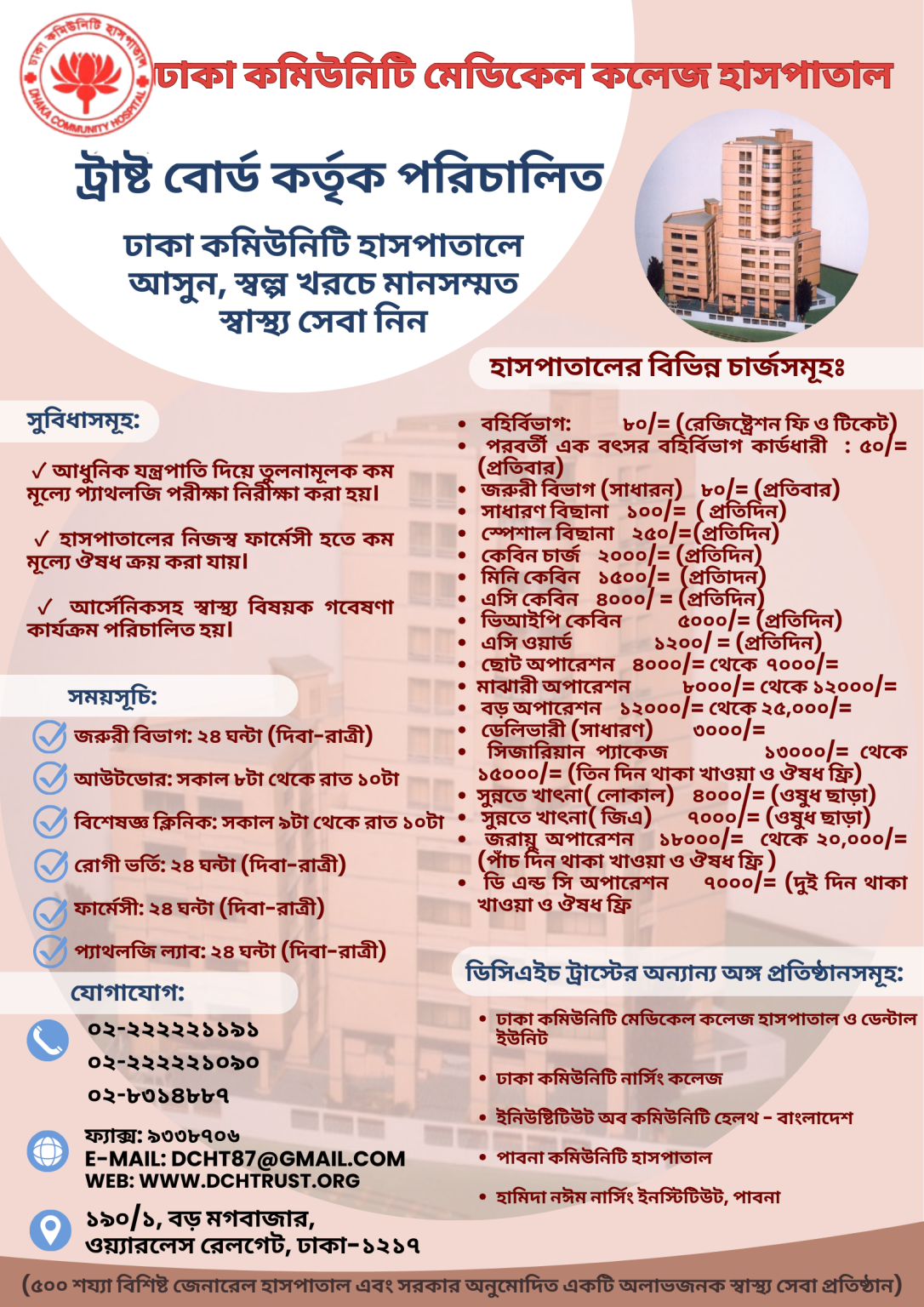

 স্বদেশ রায়
স্বদেশ রায় 



















