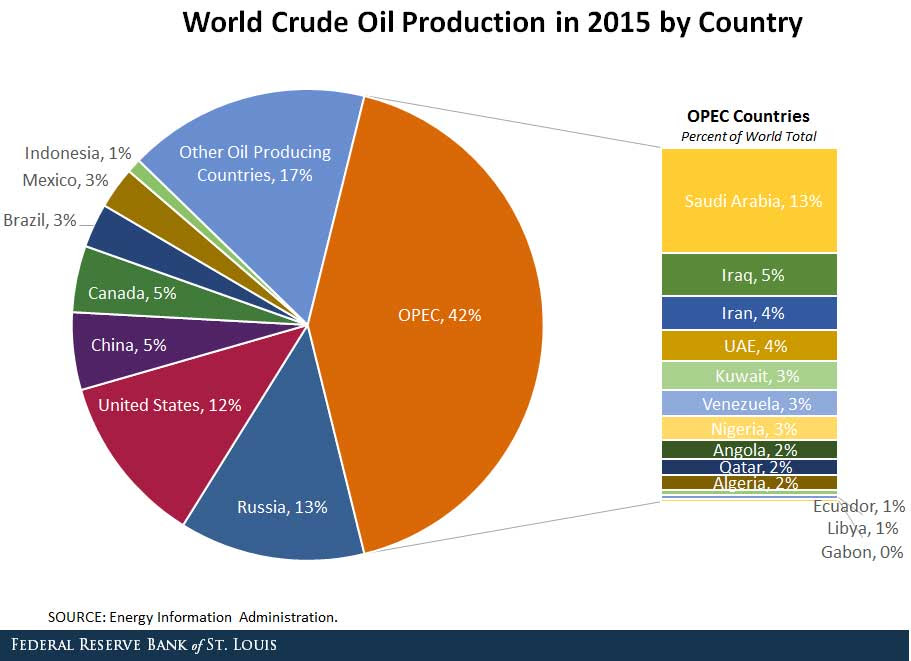অর্থনীতির নজিরবিহীন পতন
দুই বছরের গাজা যুদ্ধ ও অধিকৃত এলাকাজুড়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞার ফলে ফিলিস্তিনের অর্থনীতি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ধসের মুখে পড়েছে বলে নতুন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সংস্থা ইউনক্টাড। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কয়েক দশকে গড়ে ওঠা অর্থনৈতিক অগ্রগতি এক ধাক্কায় উধাও হয়ে গেছে; মাথাপিছু আয়ের অবস্থান ফিরে গেছে প্রায় ২০০৩ সালের স্তরে। গবেষকেরা সতর্ক করেছেন, এই ধারা চলতে থাকলে গাজা ও পশ্চিম তীরের প্রজন্মের পর প্রজন্ম দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্র্যে আটকে যাবে।
ইউনক্টাডের হিসাবে ১৯৬০ সালের পর বিশ্বে যেসব দেশ সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক পতনের মুখে পড়েছে, তাদের শীর্ষ দশটি ঘটনার ভেতরে এখন ফিলিস্তিনও জায়গা করে নিয়েছে। এ তালিকায় আছে বড় যুদ্ধবিধ্বস্ত ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে পড়া কয়েকটি দেশ। সাধারণ মানুষের জীবনে এর মানে দাঁড়িয়েছে—বেকারত্বের তীব্রতা, নিত্যপণ্যের দাম বাড়া, মৌলিক সেবা ভেঙে পড়া ও দ্রুত বাড়তে থাকা খাদ্যসংকট। স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর ভাষ্য, বহু পরিবার এখন কেবল সাহায্য সামগ্রী বা স্বজনদের পাঠানো টাকার ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে।
গাজায় যুদ্ধের সরাসরি ধাক্কাটা দেখা যাচ্ছে অবকাঠামো ধ্বংসের ভেতর দিয়ে। আবাসিক ভবন, সড়ক, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহব্যবস্থা, হাসপাতাল ও স্কুল–সবকিছুর বড় অংশই মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। এক সময়কার ছোট কারখানা ও কর্মশালা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ায় উৎপাদনক্ষমতাই হারিয়ে গেছে। প্রতিবেদনে অনুমান করা হয়েছে, পুনর্গঠনের ব্যয় কয়েক দশক ধরে বিলিয়ন ডলারের বেশি হতে পারে এবং টেকসই শান্তি না ফিরলে সেই বিনিয়োগ কখনোই পূর্ণ সুফল দেবে না।
এ পরিস্থিতির কেন্দ্রে আছে চলাচল ও বাণিজ্যে কঠোর নিয়ন্ত্রণ। দীর্ঘদিনের অবরোধ আরও কঠোর হওয়ায় গাজার ভেতরে কাঁচামাল প্রবেশ ও পণ্য রপ্তানি প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ব্যবসায়ীরা সময়মতো মাল আনতে পারছেন না, ঠিকমতো পাঠাতেও পারছেন না; নতুন বিনিয়োগে ঝুঁকি অনেক বেশি। ব্যাংকিং ও বীমা সেবার ওপরও বিধিনিষেধ থাকায় ব্যবসা পুনরুদ্ধার বা বিস্তার কঠিন হয়ে গেছে। ইউনক্টাডের ভাষায়, ‘ক্লোজার রেজিম’ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে স্বাভাবিক উদ্যোগ থেকে উচ্চ ঝুঁকির জুয়ায় পরিণত করেছে।
পশ্চিম তীরে গভীর মন্দা
গাজায় দৃশ্যমান ধ্বংসযজ্ঞের তুলনায় পশ্চিম তীর তুলনামূলকভাবে শান্ত হলেও অর্থনৈতিক মন্দা সেখানে ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে তীব্র বলে জানিয়েছে ইউনক্টাড। বসতি সম্প্রসারণ, নিরাপত্তাজনিত কারণে নতুন নতুন চেকপোস্ট ও রাস্তা বন্ধ হওয়ায় কৃষি, পর্যটন ও ছোট শিল্প সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতিদিন কর্মস্থলে যাতায়াতই অনেকের জন্য অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়েছে; অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গ্রাহক কমে যাওয়ায় বা মালামাল আনানেওয়ার ঝামেলায় বন্ধ হতে বাধ্য হয়েছে।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের আর্থিক সংকট এ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। কর রাজস্ব ও কাস্টমস আয় ইসরায়েলের মাধ্যমে আসায় রাজনৈতিক টানাপোড়েনে তা প্রায়ই আটকে থাকে বা কমিয়ে দেওয়া হয়। বহু দাতা দেশ ইতিমধ্যে ক্লান্ত; কেউ কেউ অগ্রাধিকার বদলে অন্য সংকটে বেশি অর্থ দিচ্ছে। ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে অর্থঘাটতি তীব্র হয়ে উঠেছে। ইউনক্টাডের আশঙ্কা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের এই ভাঙন দীর্ঘমেয়াদে পুনর্গঠনের সক্ষমতাকেই দুর্বল করে দিতে পারে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কেবল আন্তর্জাতিক সহায়তা বাড়ানোই যথেষ্ট নয়; চলাচল ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়া টেকসই পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। মানুষ ও পণ্যের চলাচলে বাধা কমানো, বিদ্যুৎ ও পানির মতো মৌলিক অবকাঠামো পুনরুদ্ধার, এবং অর্থনৈতিক নীতিতে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে বেশি স্বাধীনতা দেওয়ার সুপারিশ করেছে ইউনক্টাড। না হলে প্রকল্পভিত্তিক পুনর্গঠনে কিছু ভবন গড়ে উঠলেও কর্মসংস্থান ও দীর্ঘমেয়াদি আয়ের পথ খুলবে না।
আন্তর্জাতিক পরিসরে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের অর্থ কীভাবে জোগাড় হবে এবং কে তা পরিচালনা করবে। কেউ কেউ শর্তসাপেক্ষ বহু-পক্ষীয় তহবিলের কথা বলছেন; অন্যরা মানবিক জরুরি অবস্থা মাথায় রেখে দ্রুত ও কম শর্তে অর্থ দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রতিবেদনটির ভাষ্য, অর্থনৈতিক পতন যদি এভাবে চলতে থাকে, তবে অঞ্চলজুড়ে অস্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক সহিংসতা ও অনিয়মিত অভিবাসনের চাপ আরও বেড়ে যাবে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট