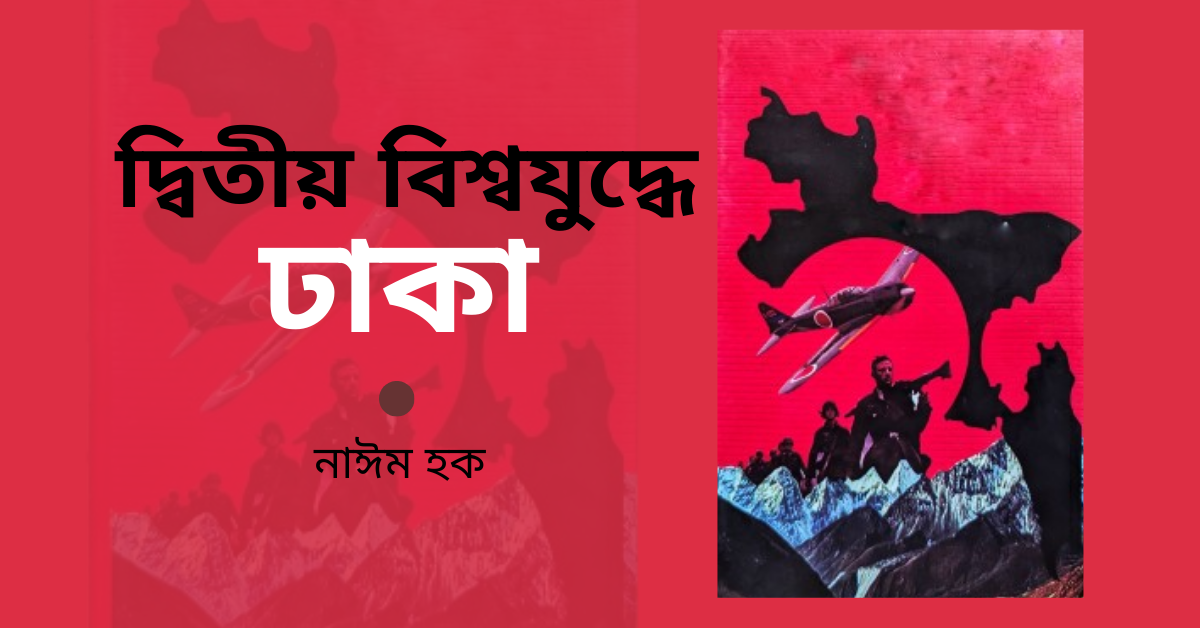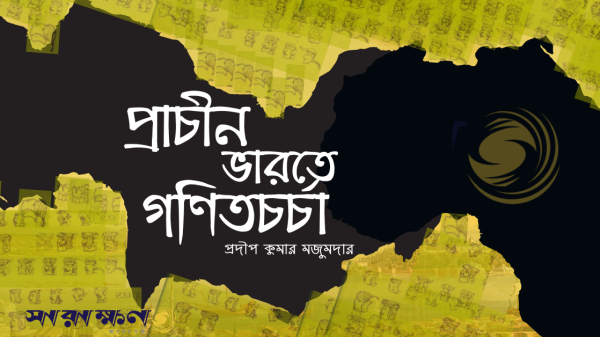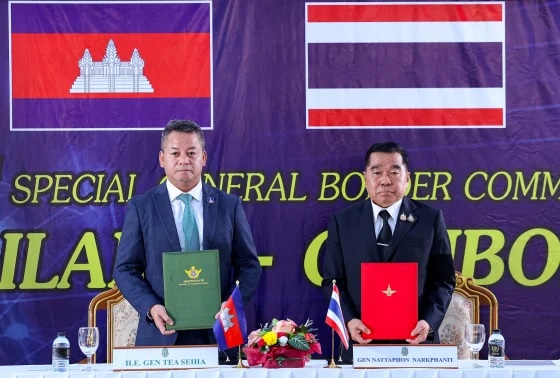কেদারীর মা
সামনেই রামেরাজের আস্তানা। তার ছেলে রাজমিস্ত্রির কাজ করিয়া বহু টাকা জমাইয়াছে। খুব ঘটা করিয়া তাহার বাড়িতে পুজা হয়। সেখান হইতে বাঁশঝাড়ে ঘেরা পথ বাহিয়া খানিক আওগাইলেই বসুদের দালান। গাভরা সোনার গয়না পরিয়া বসুবাড়ির বউরা এ-কাজে ও-কাজে যাইতেছে। বাড়ির বড় মেয়েটি ডালায় করিয়া খই মুড়ি নারকেলের লাড্ডু আনিয়া আমাদের কোঁচড়ে ঢালিয়া দিল। তার সারা গায়ে যেন সোহাগ ঝরিয়া পড়িতেছে। বসুদের বাড়ির ওধারে ঘোষেদের বাড়ি, তারপর বামুনবাড়ি পার হইলেই ছুতোর পাড়া। ঘট চাহিতে ঘটের সঙ্গে মুড়ি নারকেল খই-এর মওয়া আনিয়া দেয়। ইহার পরে আরও বড় হইলে একাই আমি হিন্দুপাড়ায় পূজা দেখিতে যাইতাম। কেদারীর
মা সঙ্গে থাকিত না বলিয়া কেহই মুড়ি-মুড়কি দিত না। কিন্তু সুন্দর সুন্দর প্রতিমাগুলি দেখিতে আমার বড়ই ভালো লাগিত। বিশেষ করিয়া সরস্বতী পূজার প্রতিমাগুলি কতই না সুন্দর বলিয়া মনে হইত। আর সেই প্রতিমার চাইতেও সুন্দর হিন্দু মেয়েগুলি নতুন শাড়ি পরিয়া যখন এ-কাজে ও-কাজে ঘুরিত আমার মনে হইত পূজার প্রতিমাগুলিই যেন জীবন পাইয়া তাহাদের আঙিনায় ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছে।
কেদারী যখন বড় হইয়া বিবাহ করিয়া সংসার পাতিল, তখন তো কেদারীর মার অভাব ছিল না কিন্তু কোনো কাজকর্মে মা তাহাকে ডাকিলে সে হাসিমুখে আসিয়া মায়ের যে-কোনো কাজই করিয়া দিয়াছে। বাড়িতে পিঠা তৈরি করিয়া পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদিগকেও ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইয়াছে। মুখে বলিয়াছে, “তোদের বাড়িতে কত খাইয়াছি, আমি আর তার কতটা পরিশোধ করিব।”
কেদারীর মা একবার খুব অসুখে পড়িল। সেই অসুখের মধ্যে বলিয়া পাঠাইল, জসীর মার হাতের রান্না একটু ডাল খাইলে আমি ভালো হইয়া উঠিব। আমি নিজে মাকে দিয়া ডাল রাঁধাইয়া কেদারীর মাকে আনিয়া দিলাম। সত্য সত্যই কেদারীর মা ভালো হইয়া উঠিল। পরবর্তীকালে বন্ধুদের সামনে আমি মাকে খেপাইতাম, “মা, তোমার হাতের ডাল খাইয়া সেবার কেদারীর মার অসুখ সারিয়া গেল, আজ তুমি ডাল পাকাইবে।”
আমার মা অনেক কিছু রান্না করিতে জানিতেন না, কিন্তু যে-কয়টি পদ তিনি রান্না করিতেন তেমন রান্না আর কোথাও খাই নাই। যখনই মায়ের হাতের রান্না খাইতে ইচ্ছা করে বোনেদের বাড়ি যাইয়া খাইয়া আসি। আমার বোনেরা মায়ের হাতের রান্নার কিছুটা উত্তরাধিকারিণী হইয়াছে। এই উত্তরাধিকার বংশানুক্রমিক কি না জানি না। আমার ভাবি প্রায় সারাজীবন মায়ের সঙ্গে কাটাইলেন কিন্তু মায়ের রান্নার উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন নাই।
কেদারীর মা মৃত্যুকালে আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিল। তখন তাহার শ্বাস উঠিয়াছে। আমার হাত দুইখানি বুকের মধ্যে লইয়া কি যেন বলিতে চেষ্টা করিল, বলিতে পারিল না। আমার চোখ দুইটা হইতে অশ্রুধারা মানিতে চাহিতেছিল না। কেদারীর মা মরিয়া যাইতেছে। তার সঙ্গে যখন যেখানে গিয়াছি, সব কথা ছবির মতো মনে আসিতেছিল। দেশের কোনোরকম রাজনৈতিক ইতিহাসেও কেহ তাহার নাম উল্লেখ করিবে না। এই স্নেহময়ী, সেবার প্রতিমা, নিজের স্বল্পপরিসর গ্রামখানিতে সেবা দিয়া আত্মত্যাগ দিয়া যে ভালোবাসার দীপটি জ্বালাইয়া দিয়া গেল, উহার উত্তরাধিকারী কি আর গ্রামে আসিবে?
তখন গ্রামও ছিল মহীয়ান। আত্মীয়-স্বজনহীনা বিধবারা নিজদিগকে তাই অসহায় মনে করিত না। গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে আত্মীয়-স্বজনের মতো লালন পালন করিত। বিধবারাও তাই সেবার প্রতিমা হইয়া তাহাদের এই দানের প্রতিদান দিয়াছে। তাহাদের গলগ্রহ হয় নাই। কেদারীর মার ছেলেও তাই গ্রামের অন্যান্য ছেলেরা যেমন মানুষ হয় তেমনিভাবে মানুষ হইয়াছে। এজন্য তাহাকে এতিমখানায় পাঠাইতে হয় নাই।
চলবে…

 Sarakhon Report
Sarakhon Report