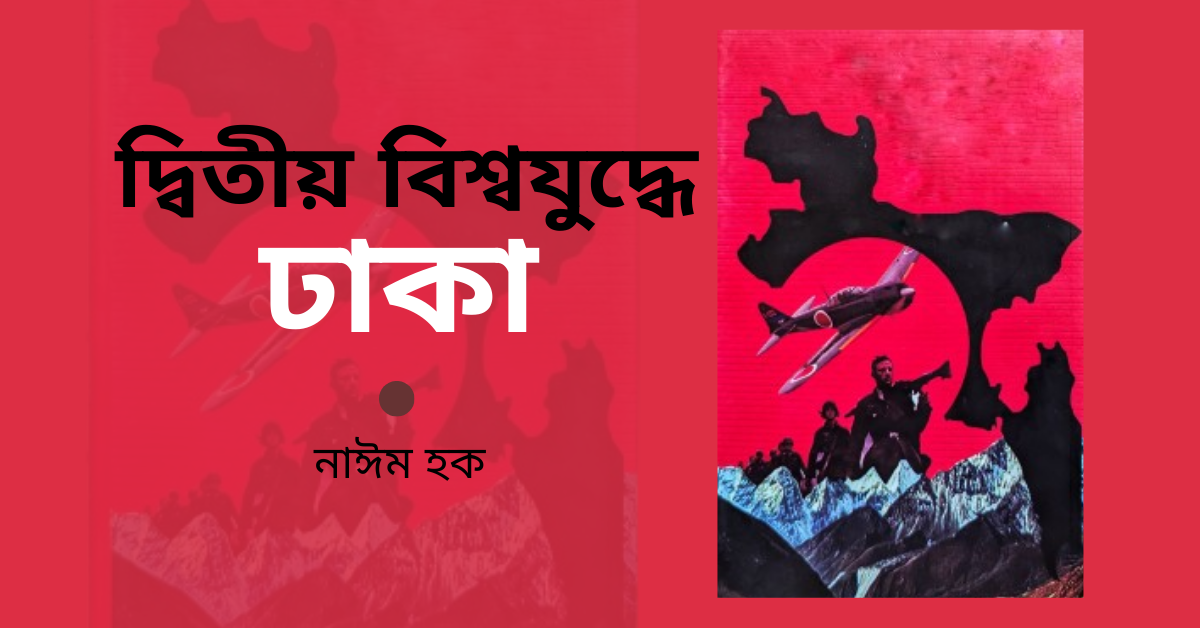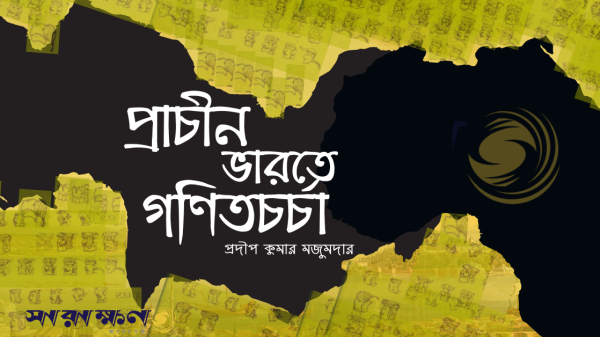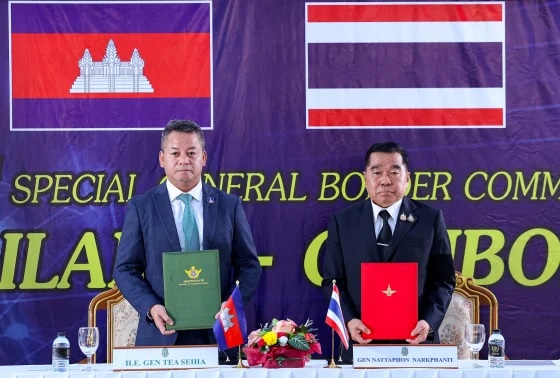মায়ের সংসার
মাত্র কয়েকখানা ছেঁড়া নেকড়া, পুরাতন কাঁথা ছাড়া প্রসূতিরা আগে কিছুই সংগ্রহ করিয়া রাখিত না। সন্তান হইলে একজন দৌড় পাড়িত, বাঁশের ঝাড় হইতে ‘নেইল’ (বাঁশের ধারালো ছাল) কাটিয়া আনিবার, অপরজন দৌড়াইয়া যাইত ও-বাড়ি সে-বাড়ি হইতে একটু মধু আনিয়া সেই মধু সদ্যোজাত শিশুর মুখে দিতে। প্রসূতি যদি বেদনায় অজ্ঞান হইয়া পড়িত তখন তাহার মাথায় তেলপানি দেওয়া হইত। সেই তৈল যদি বাড়িতে না থাকিত অপর বাড়ি হইতে তৈলের বাটি লইয়া তৈল আনিবার জন্য কোনো লোকের দৌড়াইতে হইত। আনাড়ি দাইয়ের অপরিষ্কার হাতে নাড়ি কাটাইতে কত শিশু ধনুষ্টঙ্কার হইয়া মারা যাইত। লোকে বলিত, শিশুকে পেঁচোয় পাইয়াছে। এজন্য ওঝা ও ফকির বৈষ্টমেরা সুর করিয়া মন্ত্র পড়িয়া সরলপ্রাণ গ্রামবাসীদের নিকট হইতে বেশ কিছু আদায় করিয়া লইত। আমার ছোট ছোট দুইটি ভাই আঁতুড়ঘরেই মারা যায়। একটি ভাইকে কাফনে সাজাইয়া যখন কবর দিতে লইয়া যায় মা তখন কাঁদিয়া আমার চাচিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন, “দেখ বু! আমার বাছা সাজিয়াগুজিয়া বিবাহ করিতে চলিয়াছে।” সেই কথাটি আজও আমার মনে আছে।
আমার মায়ের সংসার ছিল একার। ছয়দিন আঁতুড়ঘরে থাকিয়া সাত দিনের দিন গোসল করিয়া মা বাহির হইয়া আসিতেন। তখন হইতে আমাদিগকে রান্নাবান্না করিয়া খাওয়াইতেন। আমার এক দূর-সম্পর্কের চাচি ছিলেন। তিনি সন্তান প্রসবের পরদিন হইতেই সংসারের কাজকর্ম করিতেন। সাতদিন পরে ঢেঁকিঘরে যাইয়া ধান ভানিতেন। তাঁর একটি সন্তানও নষ্ট হয় নাই।
হিন্দুপাড়ায় পোয়াতিদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। তাহারা উঠানের মধ্যে একটি কুঁড়েঘর তুলিয়া দিত। সেখানে এক মাসের জন্য সদ্যোজাত শিশু ও পোয়াতিকে কাটাইতে হইত। বৃষ্টি-বাদলে উঠানের পানি গড়াইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিত। সেই কুঁড়েঘর পোক্ত না বলিয়া অনেক সময় ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া যাইত। তখন অসহায়া মা ও শিশু নিউমোনিয়া হইয়া মারা যাইত। এক মাস এইভাবে সেই কুঁড়েঘরে থাকিয়া মা বাহির হইয়া আসিত। নবাগত শিশুর জন্মের জন্য সেই ঘর অশুচি হইয়াছে বলিয়া গৃহবাসীরা তাহা ভাঙিয়া নদীর তীরে লইয়া গিয়া পোড়াইয়া আসিত। তারপর স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া ঘরে ফিরিত। আজও গ্রাম্য হিন্দুসমাজ হইতে এই পদ্ধতিটি উঠিয়া যায় নাই।
আমাদের মুসলমান পাড়ায় কিন্তু সবচাইতে ভালো ঘরখানিই পোয়াতি মায়েদের জন্য রাখা হইত। এখনও তাহাই হয়। শিশুর জন্মের ছয় দিন পরে ‘ছয় হাটুরে’ হয়। এইদিন আঁতুড়ঘর লেপিয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার করা হয়। সামান্য ঝাল মিশাইয়া গুড় দিয়া সেমাই পাক করিয়া ও মুরগি রান্না করিয়া পোয়াতিকে খাইতে দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের লইয়া একটি ছোটখাটো ভোজ হয়। যাহারা গরিব মানুষ তাহারা অভ্যাগত প্রতিবেশীদের পান তামাক সাজিয়া দিয়া হাসিয়া গাহিয়া আঁতুড়ঘরখানিকে আনন্দমুখর করিয়া যায়। এই ধরনের একটি গান নিম্নে দেওয়া হইল,-
জন্মিল জন্মিল গোপাল আমির আলির ঘরের, গোপাল জন্মিল কার ঘরে।
চাচির কোলে যায়া গোপাল জামা জুতা চাহেরে গোপাল জন্মিল কার ঘরে।
খালার কোলে যায়া গোপাল মোহন বাঁশি চাহেরে গোপাল জন্মিল কার ঘরে।
বাপের কোলে যায়া গোপাল মাথার টুপি চাহেরে গোপাল জন্মিল কার ঘরে।
বোনের কোলে যায়া গোপাল রাঙা সুতা চাহেরে গোপাল জন্মিল কার ঘরে।
নবজাতক শিশুকে অবলম্বন করিয়া এই গানটিতে একটি গৃহের আনন্দ-উৎসবের কি মধুর ছবিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে! বাবা, মা, চাচা, চাচি, খালা, বোন এবং অপরাপর আত্মীয়স্বজনেরা প্রত্যেকে গানের এক-একটি চরিত্র হইয়া সেই আনন্দ-উৎসবটিকে আরও জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই গানটি হয়তো প্রথমে কোনো হিন্দুবাড়িতে গীত হইয়াছিল। কারণ গোপালের জন্ম হিন্দুবাড়িতেই হওয়া সম্ভবপর। প্রথমে কোনো মুসলমানি বধূ হয়তো, গানটি সেখান হইতে শিখিয়া আসিয়া আমির আলির নবজাতকের জন্ম-উৎসবে ইহাকে সামান্য পরিবর্তন করিয়া গাহিয়াছিল। সেই হইতে এই গান মুসলমান সমাজে চালু হইয়াছে। এরূপ আদান-প্রদানের ছাপ আমাদের পল্লীসঙ্গীতগুলিতে বহু আছে। গানগুলি বহু রীতিনীতিসম্পন্ন দুই ধর্মের লোকদের মধ্যে একটি সুন্দর মিলনসেতু রচনা করিয়া দেয়।
আমার পিতা এদেশে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিভূ হাজী শরিয়তুল্লার জামাতের প্রতিনিধি ছিলেন। সেইজন্য আমাদের বাড়ির আঁতুড়ঘরে কোনোরকমের গান হইবার জো ছিল না।
চলবে…

 Sarakhon Report
Sarakhon Report