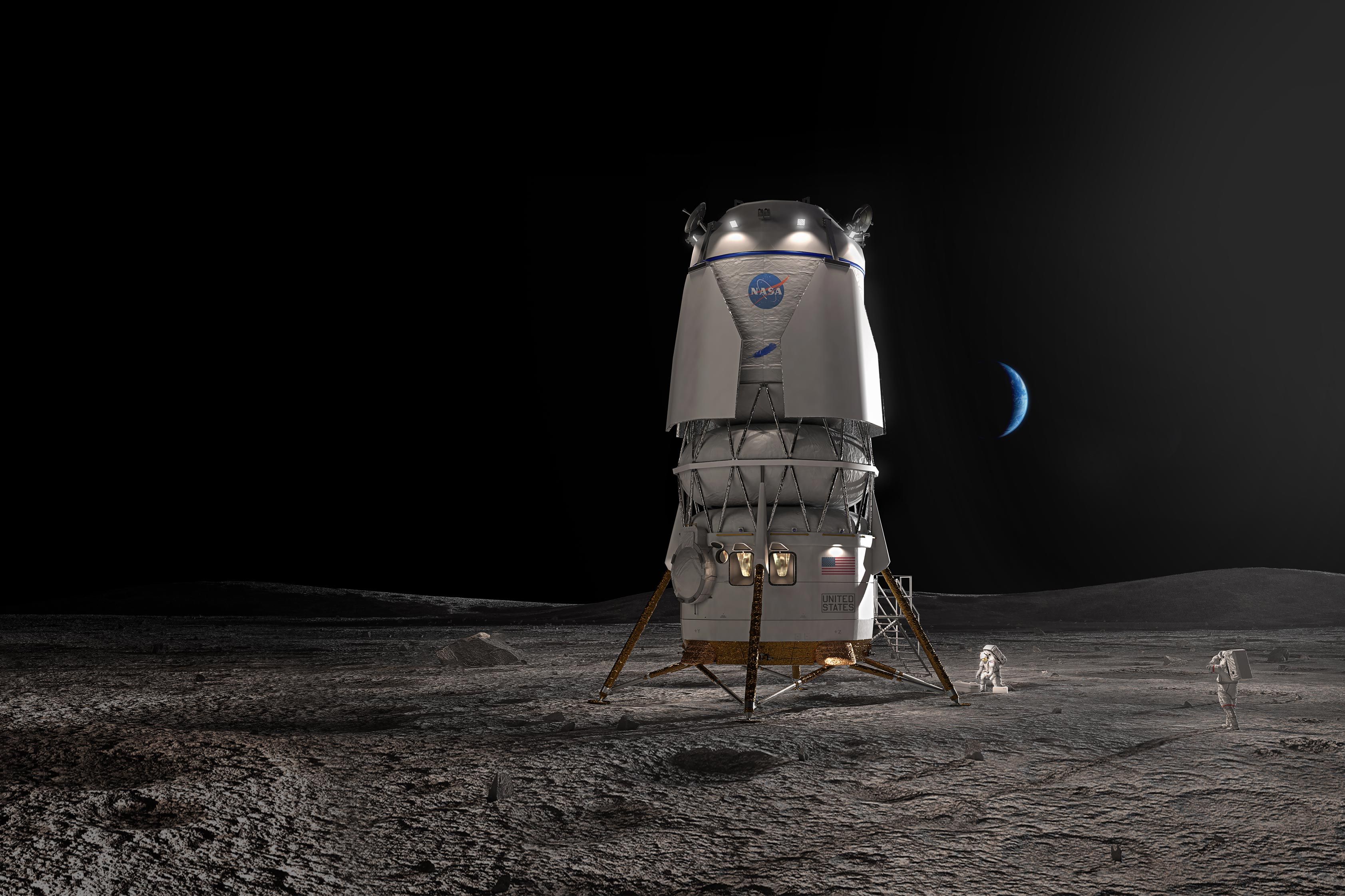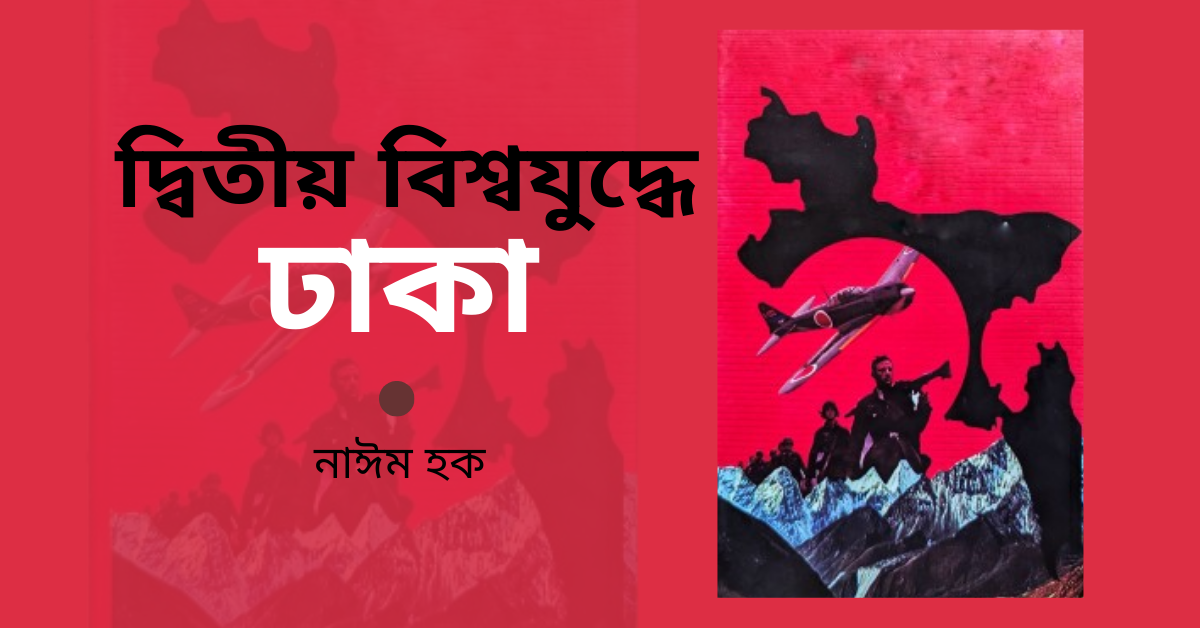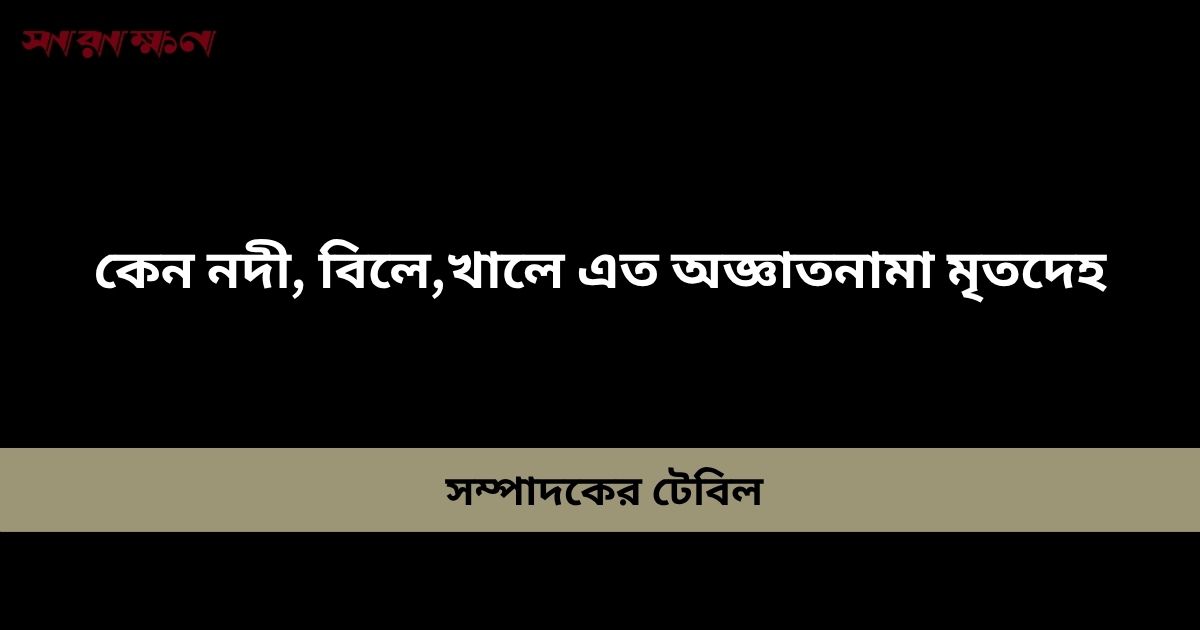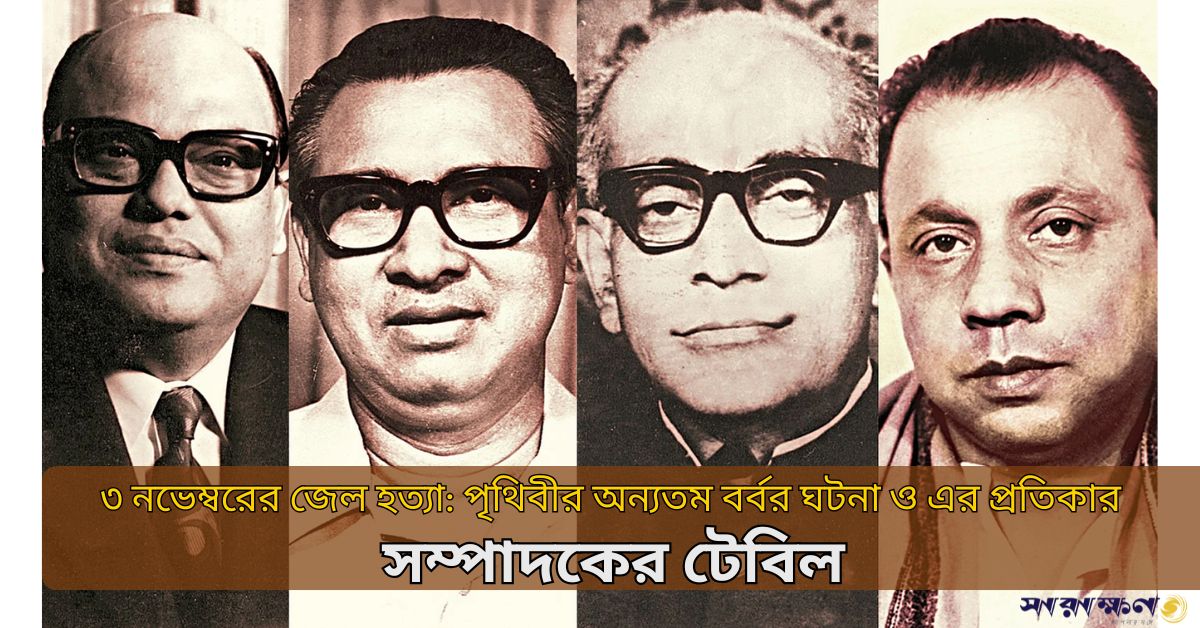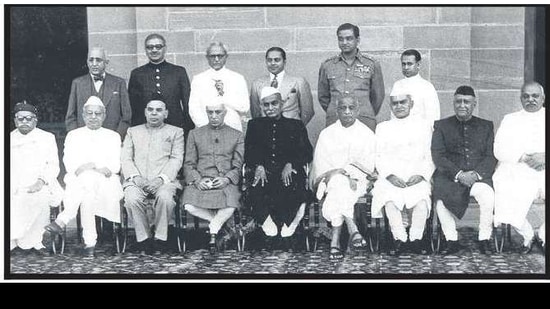প্রসেনজিৎ চৌধুরী
একটি বই যা ১৯৪৭ সালের পরে ভারতীয় ভাষায় সৃষ্ট সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে এবং এর ব্যপ্তি এতটাই বিস্তৃত যে এটি সালমান রুশদির পুরোনো দাবিকে খণ্ডন করে। রুশদি বলেছিলেন, ওই সময়কালে ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের গদ্যচর্চা ভারতের ১৬টি “সরকারি ভাষার” সাহিত্যের তুলনায় শক্তিশালী। এম কে রঘবেন্দ্র সম্পাদিত এই বইটি একটি বহুভাষিক সংকলন হওয়ার পরিবর্তে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে।
“আধুনিক ভারতীয় ভাষা সাহিত্যের রাজনীতি” ১৯৪৭ সালের পর ভারতীয় ভাষা সাহিত্যের উদ্বেগ এবং মনোভাবগুলোর প্রথম বিস্তৃত রাজনৈতিক পর্যালোচনা। এর পরিধি কাশ্মীরি এবং মণিপুরির মতো জাতীয় সংস্কৃতির প্রান্তবর্তী ভাষা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা এবং নারীদের সাহিত্যকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এটি বিশেষ ভাষাগুলোর প্রচারে বৈষম্য দূর করার জন্যও দৃঢ় দাবি তোলে, কারণ ভারতীয় সাহিত্য বহু ভাষায় সমৃদ্ধ।
রঘবেন্দ্র লিখেছেন, “ইংরেজি ভাষার অনুবাদই বিভিন্ন ভাষার ভারতীয় সাহিত্যকে অন্য লেখকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সর্বোত্তম উপায় হতে পারে। তবে মোট সাহিত্যের খুব সামান্য অংশই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।”
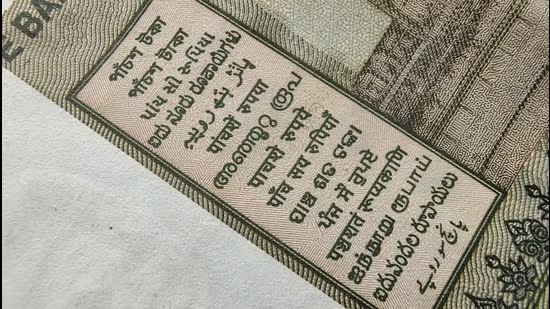
রুশদির যুক্তি এখন অনেকটা পুরোনো বিতর্ক। তিনি যে ভারতীয় ইংরেজি লেখকরা — রুশদির সংকলনে জওহরলাল নেহরু থেকে কিরণ দেশাই পর্যন্ত ছিলেন — ভাষা লেখকদের চেয়ে ভালো ছিলেন বলে দাবি করেছিলেন, তা কেবল বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছিল। এই গ্রন্থের সম্পাদক বিভিন্ন ভারতীয় লেখকদের পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।
প্রথম অধ্যায়, “জাতি এবং এর জাতিসত্তা”-তে, গিরিশ কারনাডের তিনটি ঐতিহাসিক নাটক (১৯৬৪-২০১৯), কুররাতুলাইন হায়দারের “রিভার অব ফায়ার” (১৯৫৯) এবং মোহন রাকেশের ছোটগল্প এবং একটি নাটক (১৯৬১-১৯৭৩) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়, “আধুনিকতা এবং এর প্রভাব”-এ উর আনন্তমূর্তির “সংশ্কারা” (১৯৬৫), ওভি বিজয়নের “দ্য লেজেন্ডস অফ খাসাক” (১৯৬৮) এবং ভিলাস সরংয়ের “ফেয়ার ট্রি অফ দ্য ভয়েড” (১৯৭৪-১৯৯০) আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়, “নারী এবং তাদের অবস্থান”-এ অমৃতা প্রীতমের “পিঞ্জর” (১৯৫০) এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের “দ্য আণ্ট হু উডন’ট ডাই” (২০১৭) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। “জাতিভেদ এবং তার অভিজ্ঞতা” অধ্যায়ে বামার “করুক্কু” (১৯৯২) এবং শরনকুমার লিম্বালের “দ্য দলিত ব্রাহ্মিন অ্যান্ড আদার স্টোরিজ” (১৯৮৪) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়, “মানবতাবাদ এবং লেখকের ভাবনা”-তে জয়ন্ত কৈকিনির ছোটগল্পগুলো (১৯৮৬-২০০৬) আলোচিত হয়েছে।
এই বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস রঘবেন্দ্রর আলোচনার ব্যাপ্তি এবং এর বর্তমান সংযোগ সম্পর্কে পাঠকদের ধারণা দেয়। গিরিশ কারনাড যখন মাত্র ২৬ বছর বয়সে “তুঘলক” রচনা করেন, তখন তিনি দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের বিষয়ে লিখেছিলেন, যিনি ১৩২৫ থেকে ১৩৫১ সাল পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। এটি নেহরুবাদের যুগের জন্য একটি রূপকও ছিল, যা স্বপ্ন দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং হতাশায় শেষ হয়েছিল। অবশ্যই, এই রাজনৈতিক রূপকটি বর্তমান সময়ের জন্যও প্রযোজ্য।

রঘবেন্দ্র যুক্তি দিয়েছেন যে, ভাষাগত বিভাজনের সত্ত্বেও, বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের ভারতীয় ভাষার উপন্যাসগুলো পরস্পরকে শক্তিশালী করে। একসঙ্গে, তারা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতির কল্পনা করে এবং স্থানীয় ভাষাগুলো ভারতীয় পরিচয় ছাড়া অন্য কোনো পরিচয়কে আকৃষ্ট করে না।
এটি একটি জটিল জাতির একটি বহুস্তরীয় চিত্র উপস্থাপন করে, যেখানে বাস্তবতা প্রায়ই পরস্পরের সাথে বিরোধপূর্ণ। যেমন, মহাশ্বেতা দেবীর “ছোট্টি মুন্ডা অ্যান্ড হিজ অ্যারো” (১৯৮০)-এ ১৯০০ সালকে প্রধান চরিত্রের জন্মবছর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি সেই বছর, যখন আদিবাসী নেতা বীরসা মুন্ডা, মাত্র ২৫ বছর বয়সে, কারাগারে মারা যান। বীরসা মুন্ডার স্বাধীনতা আন্দোলনে অন্তর্ভুক্তি আদিবাসী বাস্তবতাকে জাতীয় ইতিহাস দ্বারা “অধিকার” হিসেবে দেখা যেতে পারে। একইভাবে, এম কে বিনোদিনী দেবীর “দ্য প্রিন্সেস অ্যান্ড দ্য পলিটিক্যাল এজেন্ট” (১৯৭৬)-এ প্রিন্স কয়রেং-এর মৃত্যু মণিপুরি ইতিহাসকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দ্বারা “অধিকার” হিসেবে দেখা যেতে পারে।
“আধুনিক ভারতীয় ভাষা সাহিত্যের রাজনীতি” বইটিতে বিশদ টীকা রয়েছে। কখনও কখনও এর উচ্চতর গাম্ভীর্য পাঠের আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। তবে এই ভলিউমটি যা উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে তা সফলভাবে অর্জন করেছে: “পাঠকদের ভাল সাহিত্য সম্পর্কে জাগ্রত করা যা প্রায়ই উপেক্ষিত হয়।”

 Sarakhon Report
Sarakhon Report