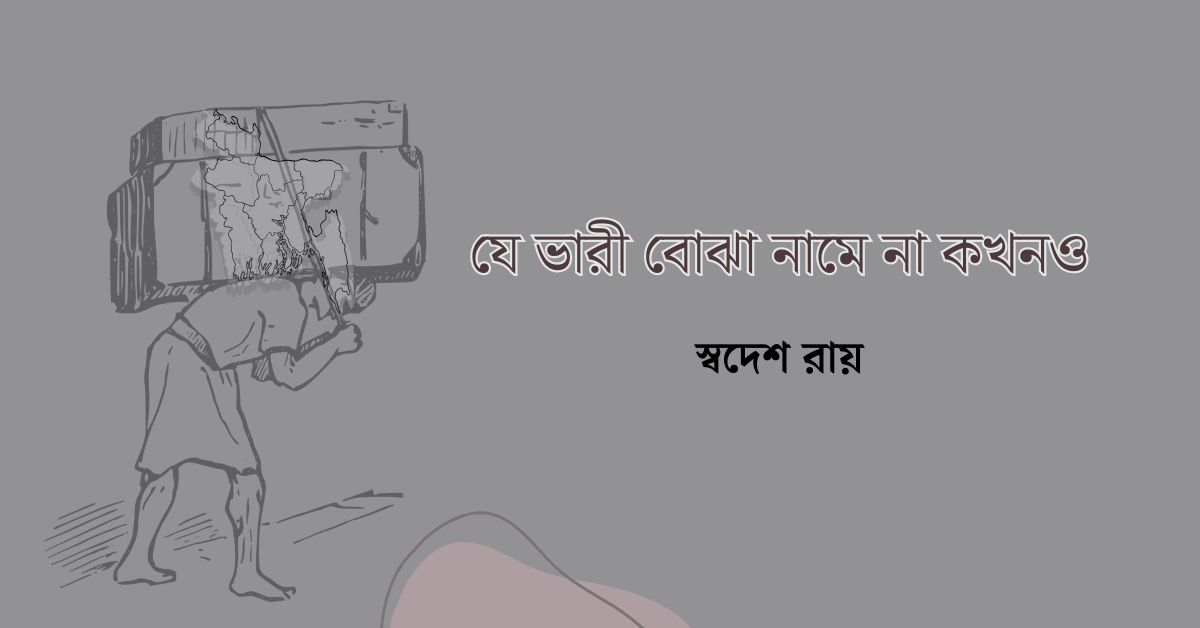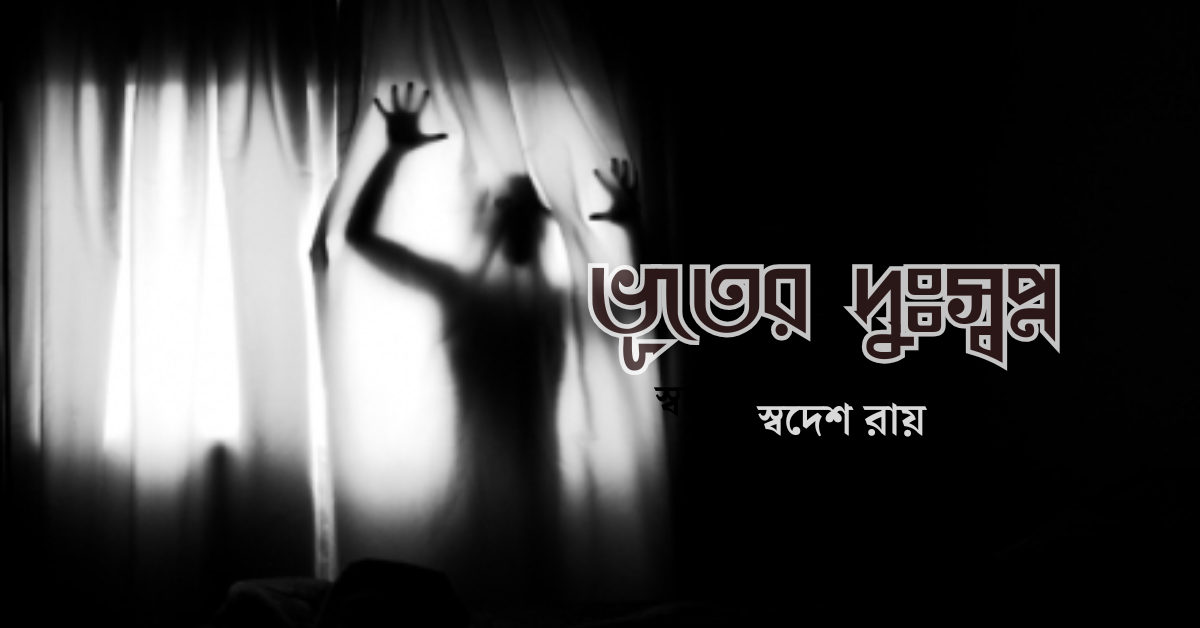মাও জেদং ও তাঁর অনুসারীরা আদর্শগত বিশ্বাস থেকে চীনা রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সমাজকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে চেয়েছিলেন। যেখানে ফরিদ ইলন মাস্কের ডিওজ প্রকল্পে মাওবাদী ভাঙচুরের ছাপ দেখছেন—যা আংশিকভাবে সিলিকন ভ্যালির স্বল্প-সরকার ও ইউটোপীয় রাজনৈতিক চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে—সেখানে নিউ ইয়র্কারের একটি প্রবন্ধে কাইল চাইকা অন্য একটি (এবং একই সঙ্গে অস্বস্তিকর) তুলনা টেনেছেন: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব জাপানের সাথে।
চাইকা লিখেছেন, যখন দ্বিতীয় ট্রাম্প প্রশাসনের সূচনায় (জানুয়ারিতে) যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো ট্রাম্পকে সমর্থন জানায়, তখনই ইতিহাসবিদ জেনিস মিমুরা এক ভয়াবহ পূর্বাভাস দেখেছিলেন: শিল্প ও সরকারি ক্ষমতার একটি নতুন, আগ্রাসী মিলন, যেখানে রাজ্য উদ্দীপনামূলক শিল্পনীতি গ্রহণ করবে এবং উদারনৈতিক রীতিনীতিকে উপেক্ষা করবে। তাঁর মতে, এই দ্বিতীয় ট্রাম্প প্রশাসনে সিলিকন ভ্যালির একটি দল এমনভাবে রাজনীতিতে নিজেদের ঢুকিয়েছে, যা মিমুরার গবেষণার প্রধান বিষয়—জাপানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা এলিট আমলাদের—স্মরণ করিয়ে দেয়। “এরা প্রযুক্তিবিষয়ক মানসিকতা ও পটভূমিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ, অনেকেই প্রকৌশলী, যাদের এখন সরকারের মধ্যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে,” মিমুরা জানিয়েছেন। তাঁর বই “প্ল্যানিং ফর এম্পায়ার” (২০১১)-এ তিনি একে বলেছেন “টেকনো-ফ্যাসিবাদ”—প্রযুক্তিনি

পুতিন কি যুক্তিসঙ্গত অভিনেতা?
রাশিয়া ২০১৪ সালে একতরফাভাবে ইউক্রেনের ভূমি দখল করে এবং ২০২২ সালে পূর্ণমাত্রায় আক্রমণ শুরু করে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা প্রশ্ন তুলেছেন, ঠাণ্ডা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ন্যাটো কি খুব বেশি উল্লাস করেছিল বা রাশিয়ার আশপাশে খুব আগ্রাসীভাবে বিস্তৃতি ঘটিয়েছিল কি না। এমআইটি-র জার্নাল ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটির বর্তমান সংখ্যায় ব্যারি আর. পোসেনের লেখা এই ভারসাম্য-রাজনীতির বিশ্লেষণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, পুতিনের ইউক্রেন আক্রমণকে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ হিসেবে ধরা যেতে পারে, যা মস্কোকে একটি অশুভ ফলাফল থেকে আগেভাগে রক্ষা করার চেষ্টা।
পোসেন লিখেছেন, “অসংখ্য প্রমাণ দেখায় যে পুতিন ও তাঁর উপদেষ্টারা প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের যুক্তিতে কাজ করেছেন। তারা দেখেছেন যে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত হচ্ছে, এবং এই পরিবর্তন রাশিয়ার স্বার্থের জন্য গুরুতরভাবে ক্ষতিকর হবে। সুতরাং, যারা এই ভারসাম্য বদলে দিতে চেয়েছে, তারা অন্তত আংশিকভাবে এই যুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে দায়ী। যদি তারা জানত যে রাশিয়া এটিকে হুমকি হিসেবে দেখছে, তাহলে এ বিষয়ে তাদের দায়িত্ব আরও বেশি। এর মধ্যে ইউক্রেনের নিজস্ব নেতারাও আছেন, তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের নীতিনির্ধারকেরা। ইউক্রেনের মানুষ ন্যাটোতে যোগ দিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাওয়ায় তাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিম ইউরোপের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য যে ইউক্রেনকে ন্যাটোতে আনতেই হবে, এমন কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কেউ কেউ এমনকি বলেছিলেন যে ইউক্রেনের সদস্যপদ তাদের জন্য বরং সমস্যা হবে। তবুও অনেক মার্কিন ও ইউরোপীয় নেতা ইউক্রেনকে এ লক্ষ্য অর্জনে উৎসাহ দিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন। যদি এই সমর্থন সত্যিই রাশিয়ার প্রতিরোধমূলক হামলার প্রধান চালিকা হয়ে থাকে, তাহলে নৈতিকভাবে তাদের উচিত ইউক্রেনকে আত্মরক্ষায় সহায়তা করা। তবে এখানেই দায় শেষ হওয়া উচিত নয়। তাদের উচিত এই বিধ্বংসী যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং রাশিয়ার সঙ্গে একটি স্থিতিশীল যুদ্ধ-পরবর্তী নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করা, যাতে আরেকটি যুদ্ধ এড়ানো যায়।”

দ্য রেনেগেইড অর্ডার
ফরেন অ্যাফেয়ার্স-এর একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে, ইতিহাসবিদ ও উইলসন সেন্টারের কেনান ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কিমেজ যুক্তি দিয়েছেন যে, ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি নতুন জাতীয়তাবাদী বিশ্বব্যবস্থা অথবা প্রকৃতকর্তৃপক্ষ এক নতুন বিশৃঙ্খলা—প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছেন, যেখানে “নিজস্ব স্বার্থকেন্দ্রিক” জাতীয় এজেন্ডার নানা মোজাইকের পরিবর্তে ১৯৪৫ পরবর্তী সময়ের উদারতাবাদী ব্যবস্থা বহুলাংশে নড়বড়ে হয়ে গেছে। কিমেজের মতে, ট্রাম্পকে পুতিন, চীনের সভাপতি শি জিনপিং, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে—তাঁরা সবাই প্রতিষ্ঠান বা প্রাতিষ্ঠানিকতার তোয়াক্কা না করে কেবল নিজের দেশের “মহানত্ব” বৃদ্ধিতেই মনোযোগী।
কিমেজের সঙ্গে একমত হয়েছেন ইতিহাসবিদ ও জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাল ব্র্যান্ডস, যিনি অন্য একটি ফরেন অ্যাফেয়ার্স প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে বর্তমান অস্থিতিশীল এবং বিশৃঙ্খল বিশ্ব, কিন্তু এ সময়টাও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একেবারে খারাপ নাও হতে পারে। ওয়াশিংটনের হাতে বিশাল ক্ষমতা রয়েছে।
তবু, ব্র্যান্ডস বলছেন, সমস্যা হলো, এ ধরনের বিশ্বপরিস্থিতি সামাল দিতে ট্রাম্পকে প্রায়ই তাৎক্ষণিকভাবে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এর ঝুঁকি হলো, আমেরিকা এক “দুষ্কৃতিকারী” শক্তিতে পরিণত হতে পারে।

ব্র্যান্ডস লিখেছেন, “ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে, যুক্তরাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবেশের বাস্তবতায় বিশৃঙ্খলভাবে নিজেদের অবস্থানকে মানিয়ে নেওয়া শুরু করেছিল। দ্বিতীয় মেয়াদে, এটি এমন একটি পররাষ্ট্রনীতিকে নির্দেশ করতে পারে যা—শত্রু ও মিত্র উভয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করে—গুরুত্বপূর্ণ লড়াইগুলোয় মুক্ত বিশ্বের প্রতিরক্ষা জোরদার করবে। … সমস্যা হলো, এর জন্য ট্রাম্পকে সব সময় তার সর্বোত্তম ভূকৌশলগত বোধ অনুসরণ করতে হবে, অথচ তিনি প্রলুব্ধ হবেন তার সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিগুলোকে কাজে লাগাতে। যদি তিনি সেই ধ্বংসাত্মক পথে যান, তবে যুক্তরাষ্ট্র আগের চেয়ে বৈশ্বিক পরিসরে কম সম্পৃক্ত থাকবে, কিন্তু আরও আগ্রাসী, একতরফাভাবে শক্তি প্রয়োগকারী, এবং উদারনৈতিক মূল্যবোধ-বিরোধী হয়ে উঠবে। সেটি হবে এমন এক দুষ্কৃতিকারী পরাশক্তি, যে বিশ্বে বিশৃঙ্খলা উসকে দেবে এবং শত্রুদের সাহায্য করবে যুক্তরাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতে। ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সি ওয়াশিংটনকে তার বৈশ্বিক স্বার্থের দৃঢ়—যদিও আগের মতো বিস্তৃত নয়—প্রতিরক্ষার দিকে ঠেলে দেওয়ার একটি সুযোগ তৈরি করে। কিন্তু একই সঙ্গে এটি একটি ভয়াবহ আশঙ্কাও জাগায়: ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে না নিয়ে গিয়ে এমন এক বিপজ্জনক পথে নিয়ে যাবেন, যা তাঁর পূর্বসূরিদের গড়ে তোলা বিশ্বব্যবস্থার জন্য আরও সাংঘাতিক।”

 Sarakhon Report
Sarakhon Report