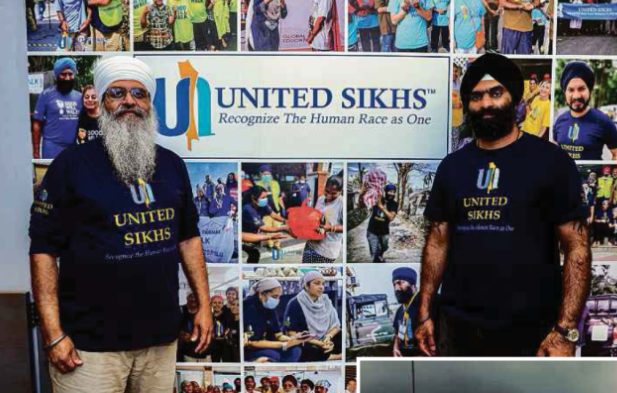মধুমতীর পরিচয় ও উৎস
বাংলার নদ-নদীর ইতিহাসে মধুমতী এক অনন্য নাম। এটি পদ্মা নদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। পদ্মার হরিদাসপুর পয়েন্ট থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণে বয়ে গিয়ে ফরিদপুর, বাগেরহাট, নড়াইল, গোপালগঞ্জ হয়ে পিরোজপুরের বলেশ্বর নদীতে মিলিত হয়। নদীর দৈর্ঘ্য আনুমানিক ১৯৮ কিলোমিটার। দুই শতকেরও বেশি সময় ধরে এই নদী দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার কৃষি, বাণিজ্য, যোগাযোগ, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে।
ব্রিটিশ আমলে নদীর গুরুত্ব
১৮ শতকের শেষ ভাগ থেকে ব্রিটিশ শাসকেরা নদীপথকে বাণিজ্যের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করত। কলকাতার সঙ্গে ফরিদপুর, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার সংযোগ স্থাপনে মধুমতী ছিল একটি প্রধান নৌপথ। ইংরেজরা নীল, পাট, চাল-ডাল, মাছ, গুড়সহ নানারকম কৃষি পণ্য এই নদীপথে কলকাতায় রপ্তানি করত। বিশেষ করে নীল চাষের সময় নীলের পাট মধুমতী হয়ে কলকাতায় পাঠানো হতো। কলকাতার বন্দর ও বাংলাদেশের ভেতরের ছোট ছোট ঘাটগুলো এই নদীর মাধ্যমে যুক্ত ছিল।

পাকিস্তান আমলে নদীর বাণিজ্যিক ব্যবহার
পাকিস্তান শাসনামলে মধুমতী নদীর গুরুত্ব কমেনি, বরং কিছু ক্ষেত্রে বেড়েছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নদীপথ ছিল সস্তা ও সহজলভ্য। ফরিদপুর, খুলনা ও মোংলা বন্দরের সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরীণ অঞ্চলের সংযোগে মধুমতী ব্যবহৃত হতো। কৃষি উৎপন্ন ধান, পাট, মাছ, মাটির হাঁড়ি-পাতিল, কাঠের আসবাবপত্র নদীপথে স্থানান্তরিত হতো। ভারতীয় সীমান্তের কাছে ছোট নদীবন্দর ও ঘাট থেকে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি হতো।
স্বাধীন বাংলাদেশের সময়ে নদীর যোগাযোগ ব্যবস্থা
স্বাধীনতার পরও মধুমতী নদী দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অভ্যন্তরীণ নৌযান চলাচলের অন্যতম রুট। ফরিদপুর থেকে শুরু করে মোংলা বন্দরের পণ্য গোপালগঞ্জ, নড়াইল, বাগেরহাট অঞ্চলে নদীপথে পরিবাহিত হয়। স্থানীয় কৃষকরা ধান, সবজি, মাছ, গাছের চারা, নারকেল, সুপারি, কাঠসহ নানারকম পণ্য নদীপথে বাজারে নিয়ে আসে। নদী-ভিত্তিক ফেরি, ইঞ্জিনচালিত নৌকা, পণ্যবাহী ট্রলার চলাচল করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নদীখননের অভাবে অনেক স্থানে নাব্যতা কমলেও, এখনও বহু অঞ্চলে এটি জীবনের সঙ্গী।

দুই তীরের জনপদ ও সভ্যতা
মধুমতীর দুই তীরে গড়ে উঠেছে শত শত গ্রাম, হাট-বাজার, বন্দরের ঘাট। ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, নড়াইল ও বাগেরহাট জেলার বহু গ্রাম নদীর তীরে অবস্থিত। নদীর দুই পাড়ে কৃষিনির্ভর জনপদ গড়ে উঠেছে। উর্বর পলিমাটি কৃষিকে সমৃদ্ধ করেছে। ধান, পাট, কলা, শাকসবজি, নারকেল, সুপারি চাষের জন্য উপযুক্ত অঞ্চল। নদী-ভিত্তিক মৎস্যজীবী সম্প্রদায় রয়েছে। নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে নৌকা তৈরির কারখানা, মাছের আড়ত। অনেক গ্রামেই নদী বাঁচিয়ে বংশপরম্পরায় নৌকা চালানো, মাছ ধরা, নদী পারাপার পেশা হয়েছে।
মধুমতীর জলজ সম্পদ ও মাছ
মধুমতী নদী দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার একটি বড় মিঠা পানির মাছের উৎস। রুই, কাতলা, ইলিশ, পাবদা, টেংরা, শোল, গজার, বাইনসহ নানা প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। ফরিদপুরের অংশ থেকে শুরু করে নিচের জেলাগুলোয় মৎস্যচাষ ও প্রাকৃতিক মাছ ধরা গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্ষাকালে নদী ফুলে ওঠে এবং মাছের প্রজনন বাড়ে। নদীর সাথে সংযুক্ত খাল-বিল ও পুকুরের মাছের বংশবিস্তারে মধুমতীর অবদানও উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃতি, গান ও সাহিত্য
মধুমতী নদী বাঙালি লোকসংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। নদীকে কেন্দ্র করে বহু পালা, গান, কবিতা রচিত হয়েছে। ফরিদপুরসহ নদীর তীরবর্তী জেলার বাউল, ভাটিয়ালী, জারি-সরিতে নদীর বেদনা, প্রেম, বিরহের কথা বলা হয়েছে। অনেক বাউল কবি নদীর ধারে বসে গান লিখেছেন। নদীর ওপর ভর করে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা, গ্রামীণ মেলা, উৎসব হয়েছে।
বাংলা সাহিত্যে নদীর প্রসঙ্গ এলে পদ্মা-যমুনার সঙ্গে মধুমতীর নামও উঠে আসে। স্থানীয় কবি-গীতিকাররা মধুমতীর পাড়ে জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রকৃতির রূপ, প্রেম-বিরহের কথা লিখেছেন। লোককথা, উপাখ্যানেও মধুমতীর কথা আছে।
ভবিষ্যৎ ভাবনা ও নদীর রক্ষণাবেক্ষণ
দুই শতকের ইতিহাসে মধুমতী বহু পরিবর্তনের সাক্ষী। তবে নদীর নাব্যতা অনেক জায়গায় কমে এসেছে, ভরাট হয়েছে খাল এবং চর জেগেছে। বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ, অপরিকল্পিত নৌযান চলাচল, দখল ও দূষণ নদীর জন্য হুমকি। নদীর রক্ষা, নাব্যতা ফিরিয়ে আনা, পরিকল্পিত নদী ব্যবস্থাপনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অপরিহার্য।
মধুমতী শুধু একটি নদী নয়, এটি এ অঞ্চলের জীবনের প্রতিচ্ছবি। দুই শতক ধরে এটি মানুষের রুটি-রুজি, বাণিজ্য, সংস্কৃতি, প্রেম-বিরহ, আশা-নিরাশার সাক্ষী হয়ে আছে। এই নদীকে রক্ষা করা মানেই এ অঞ্চলের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখা।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট