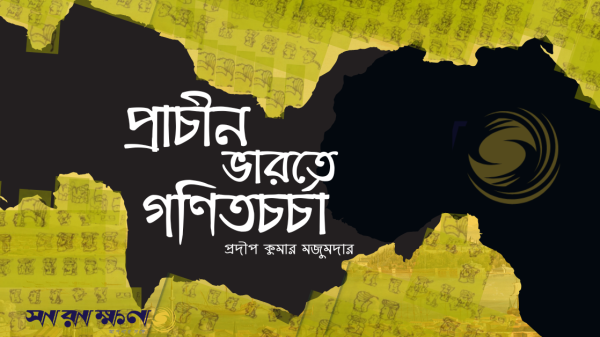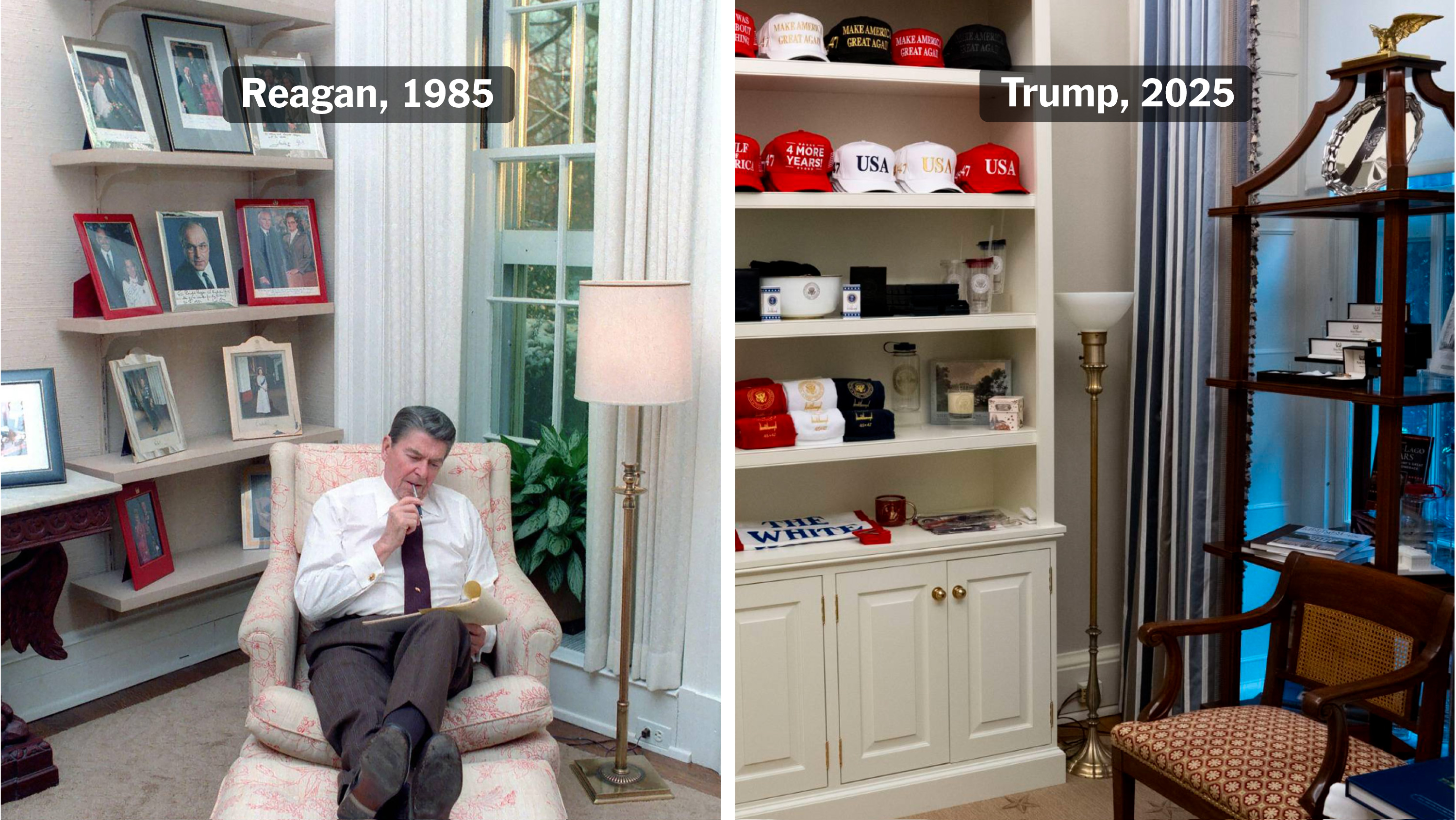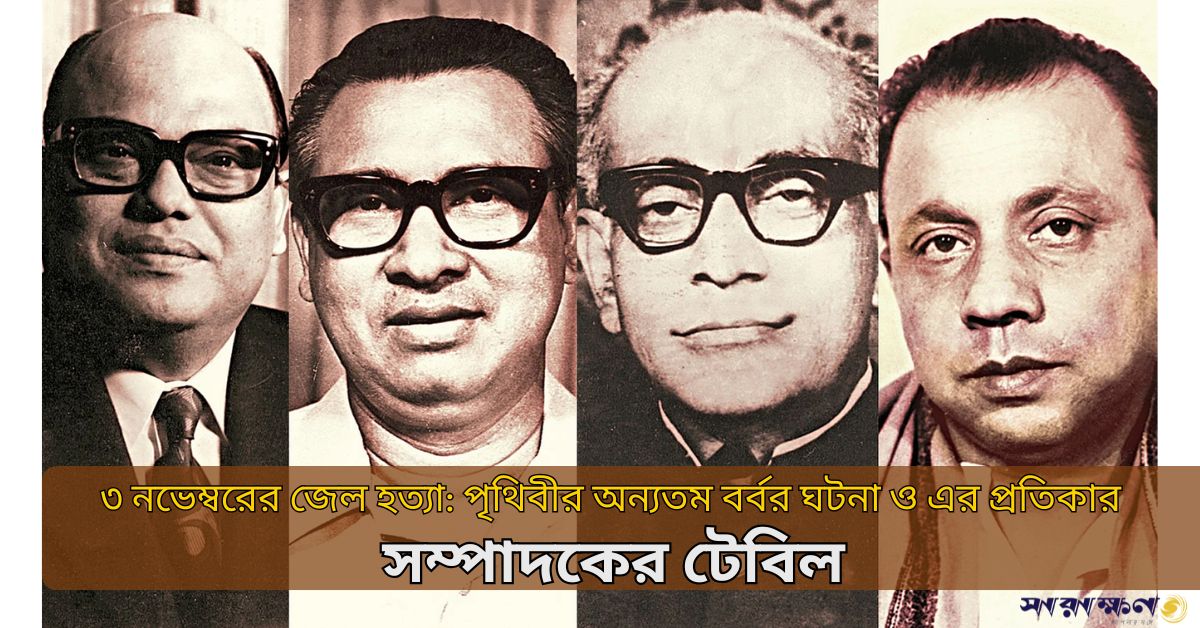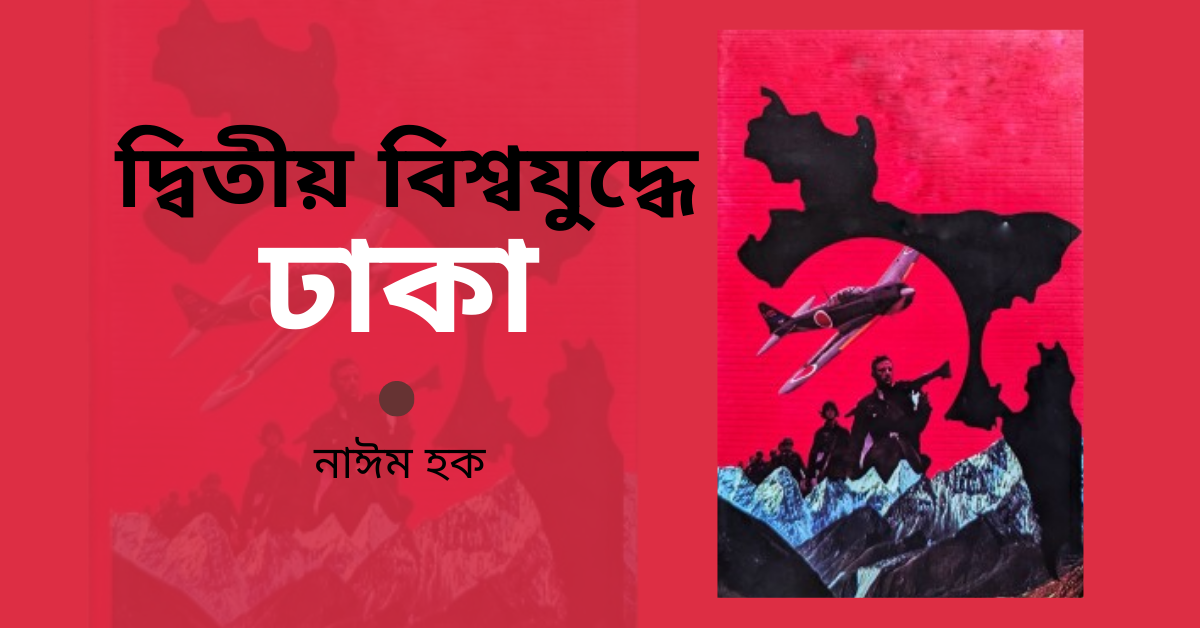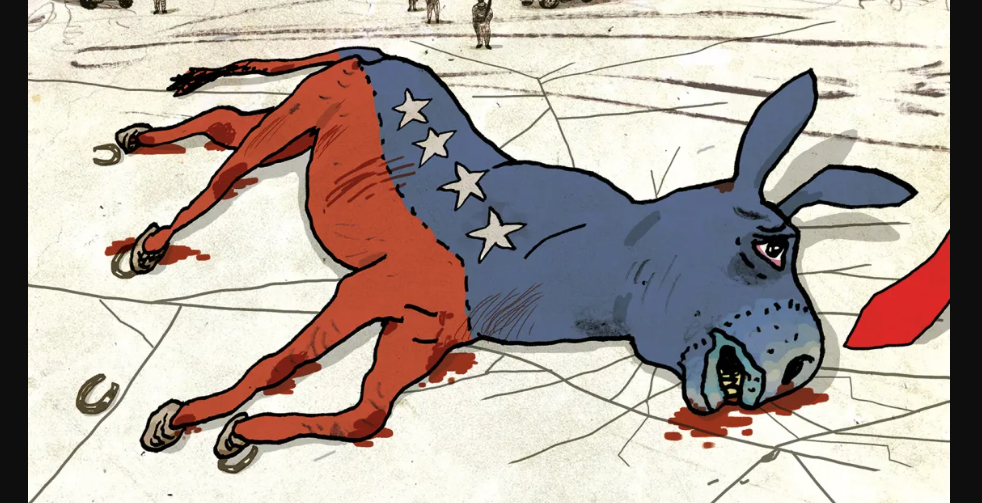সমকালের একটি শিরোনাম “এবার জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পথ খুঁজছে কমিশন”
বিএনপি মতামত দিলেও জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫-এর খসড়ায় মতামত দেয়নি জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, ইসলামী আন্দোলনসহ অন্তত ১৩টি দল। সনদের আইনি ভিত্তি চাওয়া এ দলগুলোর দাবি– নির্বাচনের আগেই সাংবিধানিক সংস্কার হতে হবে, ভোট হবে সনদের অধীনে। এই বাস্তবতায় জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পথ খুঁজছে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।
গতকাল রোববার সংসদ ভবনে কমিশনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আরও আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেন কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার। আলী রীয়াজ সমকালকে বলেন, কমিশনের বৈঠকের বিষয়ে সরকারপ্রধানকে অবহিত করা হয়েছে।
কমিশনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল, ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে সনদ স্বাক্ষরের কাজ শেষ করা। পরে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় ৫ আগস্ট। কিন্তু এখনও খসড়া চূড়ান্ত না হওয়ায় কমিশনের মেয়াদের মধ্যে সনদ হবে কিনা– এমন অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ১৫ আগস্ট কমিশনের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হবে।
মনির হায়দার সমকালকে বলেন, সব দলের মতামত পাওয়ার পর সনদের খসড়া করা হবে। এরপর বাস্তবায়নে পথ নিয়ে আলোচনা হবে। তারপর সনদ চূড়ান্ত হবে। আশা করা যাচ্ছে, কমিশনের মেয়াদের মধ্যে এসব কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।
জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ সমকালকে বলেছেন, সনদে মতামত দিতে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কাজ করছেন তারা। এর জন্য আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। সনদ কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়– এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত কমিশনকে জানাবে জামায়াত। তিনি বলেন, সনদ নির্বাচনের আগে বাস্তবায়ন হতে হবে। পরবর্তী সংসদ সনদ অনুযায়ী সংবিধান সংস্কারকে অনুমোদন করবে। এর জন্য কী কী কাজ করতে হবে তা জামায়াতের মতামতে থাকবে। সনদের চূড়ান্ত খসড়ায় যদি বাস্তবায়নের পথ না থাকে তবে সই করা হবে না।
গত শনিবার এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম দাবি করেন, জুলাই সনদের অধীনে নির্বাচনে হতে হবে। একই অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে সংলাপে দলের প্রতিনিধিত্ব করা এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন সমকালকে বলেছেন, সংস্কার বাস্তবায়নে কমিশনের প্রস্তাব ছিল গণভোট, গণপরিষদ, পরবর্তী সংসদসহ ছয়টি উপায়।
আজকের পত্রিকার একটি শিরোনাম “বুড়ো ইঞ্জিনে বারবার থমকে যাচ্ছে ট্রেন”
বাংলাদেশ রেলওয়ের ৯০ শতাংশ ইঞ্জিনেরই (লোকোমোটিভ) মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। ৩০ থেকে ৬০ বছরের পুরোনো এসব ইঞ্জিন যাত্রাপথে বিকল হয়ে দুর্ভোগে ফেলছে যাত্রীদের। শুধু পণ্যবাহী, লোকাল বা মেইল নয়; কোনো কোনো আন্তনগর ট্রেনও চলছে কার্যকাল পেরিয়ে যাওয়া ইঞ্জিনে। ফলে এসব ট্রেনও চলার পথে থমকে যাওয়ায় একই রকম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। ট্রেন বিলম্বিত হচ্ছে, যাত্রা বাতিলের ঘটনাও ঘটছে।
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বলছে, যাত্রীসেবা উন্নত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও ‘বুড়ো’ ইঞ্জিনে সাফল্য আসছে না।
জানতে চাইলে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক (ডিজি) মো. আফজাল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, রেলওয়ের ইঞ্জিনগুলো ৩০ থেকে ৬০ বছরের পুরোনো হওয়ায় যত্রতত্র বিকল হচ্ছে। এতে যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়ছেন। দেশের ৯০ শতাংশ ইঞ্জিন মেয়াদোত্তীর্ণ। ইঞ্জিনের অভাবে প্রতিদিন রেলের যাত্রীসেবা ব্যাহত হচ্ছে।
রেল সূত্র জানায়, গত ১৪ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ১৫ দিনে ৩৭টি ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১৮টি আন্তনগর ট্রেনের, ১৫টি মেইল ট্রেনের ও ৪টি পণ্যবাহী ট্রেনের ইঞ্জিন। সারা দেশে প্রতিদিন রেলসেবা দিতে ২০৫টি ইঞ্জিন দরকার। এগুলোর মধ্যে ১০৫টি মিটারগেজ এবং ১০০টি ব্রডগেজ। তবে সংকট থাকায় দেওয়া যায় ১৭০টি ইঞ্জিন।
রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের দৈনিক ইঞ্জিনের (লোকোমোটিভ) চাহিদা ১১৬টি, পাওয়া যায় ৭০-৭৫টি। তবে কানেক্টিং ইঞ্জিনসহ স্বল্প দূরত্বের পথের ফিরতি ইঞ্জিনের মাধ্যমে কোনোরকমে সেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চলছে। সাম্প্রতিক সময়ে রেলের মিটারগেজ ইঞ্জিনগুলোর বিকল হওয়ার হার অস্বাভাবিক বেড়েছে। এতে ট্রেন পরিচালনা মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে।
রেলওয়ের সূত্র জানায়, ২০২৪ সালের জুলাইয়ের তুলনায় ডিসেম্বরে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের যাত্রাপথে ইঞ্জিন বিকলের সংখ্যা তিন গুণের বেশি। জুলাইয়ে সব মিলিয়ে ১২টি ইঞ্জিন বিকল হলেও ডিসেম্বরে হয়েছে ৩৮টি। এর মধ্যে আন্তনগর ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল ১৬টি।
মানবজমিনের একটি শিরোনাম “গতি ফেরেনি রাজধানীর থানাগুলোতে”
গত বছরের জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের সময় ছাত্র-জনতার ওপর বেপরোয়া গুলি করে গণহত্যা চালিয়েছিল পুলিশসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। অভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদী সরকারের পতনের দিন মানুষের ক্ষোভের কেন্দ্র ছিল অনেক থানা। মানুষ থানায় আগুন দেয় এবং অস্ত্র লুট করে। থানাগুলোতে অবস্থান করা পুলিশ সদস্যদের অনেক স্থান থেকে উদ্ধার করতে হয় অন্য বাহিনীকে। অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর থানাগুলো সংস্কার, পুলিশকে জনবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার নানা উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু অভ্যুত্থানের এক বছরের মাথায়ও গতি ফিরেনি পুলিশের কাজে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের দমনপীড়নের ট্রমা থেকে বের হতে পারছেন না অনেক পুলিশ সদস্য। কেউ আবার বিচারের কাঠগড়ায়। গণ-অভ্যুত্থানের বছরপূর্তির সময়ে রাজধানীর বিভিন্ন থানা ঘুরে দেখা গেছে ভাঙচুর বা অগ্নিসংযোগের চিহ্ন মুছে আগের চেহারায় ফিরেছে থানাগুলো। কিন্তু অধিকাংশ জনবল ঢাকার বাইরে থেকে আসা। দায়িত্বপ্রাপ্তরাও অনেকে ঢাকার বাইরে থেকে এসেছেন।
গত বছরের ৫ই আগস্ট ও পরদিন ৬ই আগস্ট দেশের প্রায় ৪ শতাধিক থানায় হামলা ও ভাঙচুর করা হয়। সেদিনের আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঢাকা মেট্রোপলিটনের অন্তত ২১টি থানা। টেবিল-চেয়ার, আসবাবপত্র, কম্পিউটার, জব্দকৃত আলামতসহ আগুনে পুরোপুরি ধ্বংস হয় মিরপুর, মোহাম্মদপুর, আদাবর, যাত্রাবাড়ীসহ ডিএমপি’র ১৪টি থানা ভবন। পুড়ে যায় হাজার হাজার মামলার নথি। শুধু মিরপুর, মোহাম্মদপুর, বাড্ডা, আদাবর, পল্টন ও ওয়ারী এই ৬ থানায় আগুনে প্রায় ১ হাজার ২২৬টি মামলার নথিপত্র পুড়ে যায়। বাকি যাত্রাবাড়ী, শ্যামপুর, ভাটারা, শেরেবাংলা নগর, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, খিলগাঁও ও খিলক্ষেত থানায় যে কতো নথিপত্র আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে তার কোনো হদিসই পাওয়া যায়নি। জনরোষে সেদিন অস্ত্র-গোলাবারুদ এমনকী গায়ের পোশাক খুলে থানা থেকে পালাতে বাধ্য হন পুলিশ সদস্যরা। আত্মগোপনে চলে যান প্রশাসনের সকলে। দেশ জুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ে। ডাকাত আতঙ্কে মহল্লায় মহল্লায় রাত জেগে পাহারার ব্যবস্থা করে খোদ সাধারণ বাসিন্দারাই। সরকার গঠনের পর পুলিশ প্রধান, ডিএমপি কমিশনারসহ নিয়োগ দেয়া হয় পুলিশ কর্মকর্তাদের। নানা চড়ায়-উতরায়ের পর নাগরিকদের সঙ্গে মিটিং, ক্যাম্পিংসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যদিয়ে পোড়া থানায় আসতে থাকে পুলিশ সদস্যরা। তবে তখনো নিজেদের পুলিশ সদস্য পরিচয় দিতেন না কেউই। প্রাণভয়ে পুলিশি পোশাক কেউ গায়ে জড়ায়নি তখন। সেনা সদস্যদের নিরাপত্তায় থানার বাইরে ব্যাঞ্চে বসে ডিউটি করে নীরবে বাসায় ফিরে গিয়েছেন। অনেক ডিউটি শেষে ব্যাগে করে পোশাক বহন করতেন। থানা সংস্কারের পরে আগস্টের মাঝামাঝি থেকে ধীরে ধীরে কার্যক্রম শুরু হয় সকল থানার। ঘটনার এক বছরের মাথায় দেশের সকল থানায় আবারো স্বাভাবিকভাবে পুলিশি কার্যক্রম চলছে।
তবে মো. ইয়াসিন আহমেদ নামে এক ব্যবসায়ী বলেন, পুলিশ যে কতো ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল তা গত ১৭ বছরে এদেশের মানুষ দেখেছে। কিন্তু পুলিশ যখন থানায় ছিল না তখন আমরা পুলিশের গুরুত্ব বুঝেছি। সমাজের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের ভূমিকা অপরিসীম। তিনি বলেন, থানা পুড়িয়ে দেয়ার পর বিভিন্ন প্রচেষ্টার পর পুলিশ সদস্য থানায় ফিরে স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে তাদের মধ্যে আগের সেই অবস্থা চোখে পড়ছে না। আগে রাত ২/৩টার সময় বাসা থেকে বের হতে ভয় লাগতো না। কিন্তু এখন রাত ১১টা বাজলেই ঢাকা শহরে রাস্তায় বের হতে চিন্তা হয়। ছিনতাই-চুরি আগের থেকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মোড়ে মোড়ে চাঁদাবাজি চলছে। দিনের আলোতে সকলের সামনে রাস্তার ওপর মানুষকে পাথর দিয়ে পিটিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করা হচ্ছে। পুলিশ আসামি ধরছে কিন্তু ঘটনা ঘটনার পর। তিনি বলেন, পুলিশ যদি পূর্ণ গতি নিয়ে কাজ করতো তাহলে এসব নির্মমতা করা তো দূরের কথা কেউ এসব করার চিন্তাও করতে সাহস পেতো না।
বণিকবার্তার একটি শিরোনাম “মূলধনি যন্ত্রের ঋণপত্র খোলা কমায় ডলারের চাহিদা কম”
গত তিন অর্থবছরজুড়ে ডলারের তীব্র সংকটে ছিল বাংলাদেশ। এ কারণে ব্যবসায়ীরা চাহিদা অনুযায়ী ঋণপত্র (এলসি) খুলতে পারেননি। সংকট কাটিয়ে এ মুহূর্তে চাহিদার চেয়েও দেশে ডলারের জোগান বেশি। কিন্তু বাড়তি এ জোগান অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। আমদানিনির্ভর বাংলাদেশে এলসি খোলার প্রবণতা ধারাবাহিকভাবে নিম্নমুখী।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, সদ্য শেষ হওয়া ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে আমদানির এলসি খোলা বেড়েছে ১ শতাংশেরও কম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬ হাজার ৮৮৯ কোটি ডলার বা ৬৮ দশমিক ৮৯ বিলিয়ন ডলারের এলসি খোলা হয়েছিল। আর গত অর্থবছরে এলসি খেলা হয়েছে ৬৯ দশমিক শূন্য ১ বিলিয়ন ডলারের। অর্থাৎ অর্থনীতির প্রয়োজন, আকার ও জনসংখ্যা বাড়লেও আমদানি প্রায় একই অবস্থায় থেকে গেছে।
অর্থনীতির স্বাভাবিক চাহিদা মেটাতে প্রতি মাসে বাংলাদেশকে ৫ থেকে ৬ বিলিয়ন ডলারে পণ্য আমদানি করতে হয়। গত অর্থবছরের শুরুতে আমদানির যে পরিস্থিতি ছিল, সেটির ধারাবাহিকতা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যায়নি। অর্থবছরের শেষ মাস তথা জুনে এলসি খোলার পরিমাণ মাত্র ৪ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে, যা সাড়ে চার বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুনেও ৫ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলারের এলসি খোলা হয়েছিল। সে হিসাবে আগের অর্থবছরের তুলনায়ও জুনে ২৪ দশমিক ৪২ শতাংশ কম এলসি খোলা হয়েছে।
অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংক নির্বাহীরা বলছেন, আমদানি কমে যাওয়ার পেছনে বিনিয়োগ খরা, অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও ভোগ ব্যয় কমে যাওয়ার প্রভাব রয়েছে। দেশের বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি মাত্র ৬ দশমিক ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে। নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে না ওঠায় মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানিও আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে। অর্থনীতিকে প্রাণচঞ্চল করতে হলে আমদানি বাড়াতে হবে বলে মনে করছেন তারা।

 সারাক্ষণ ডেস্ক
সারাক্ষণ ডেস্ক