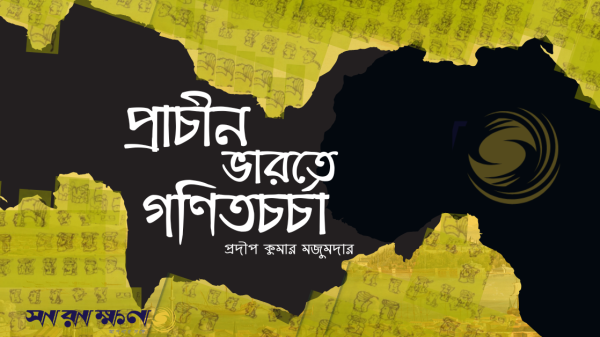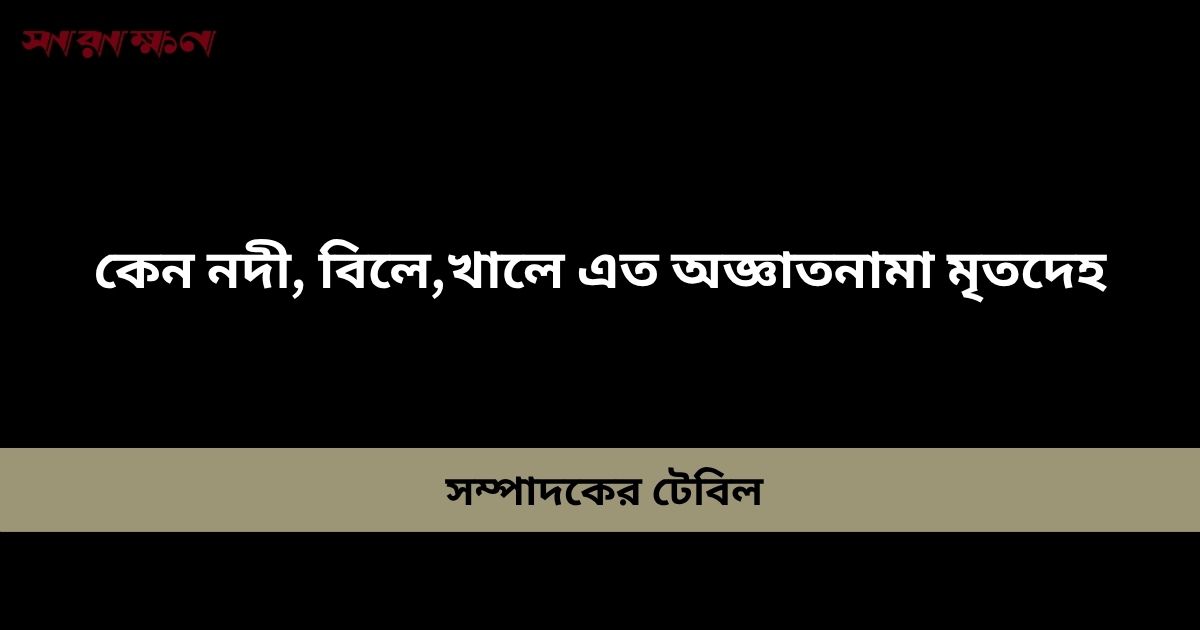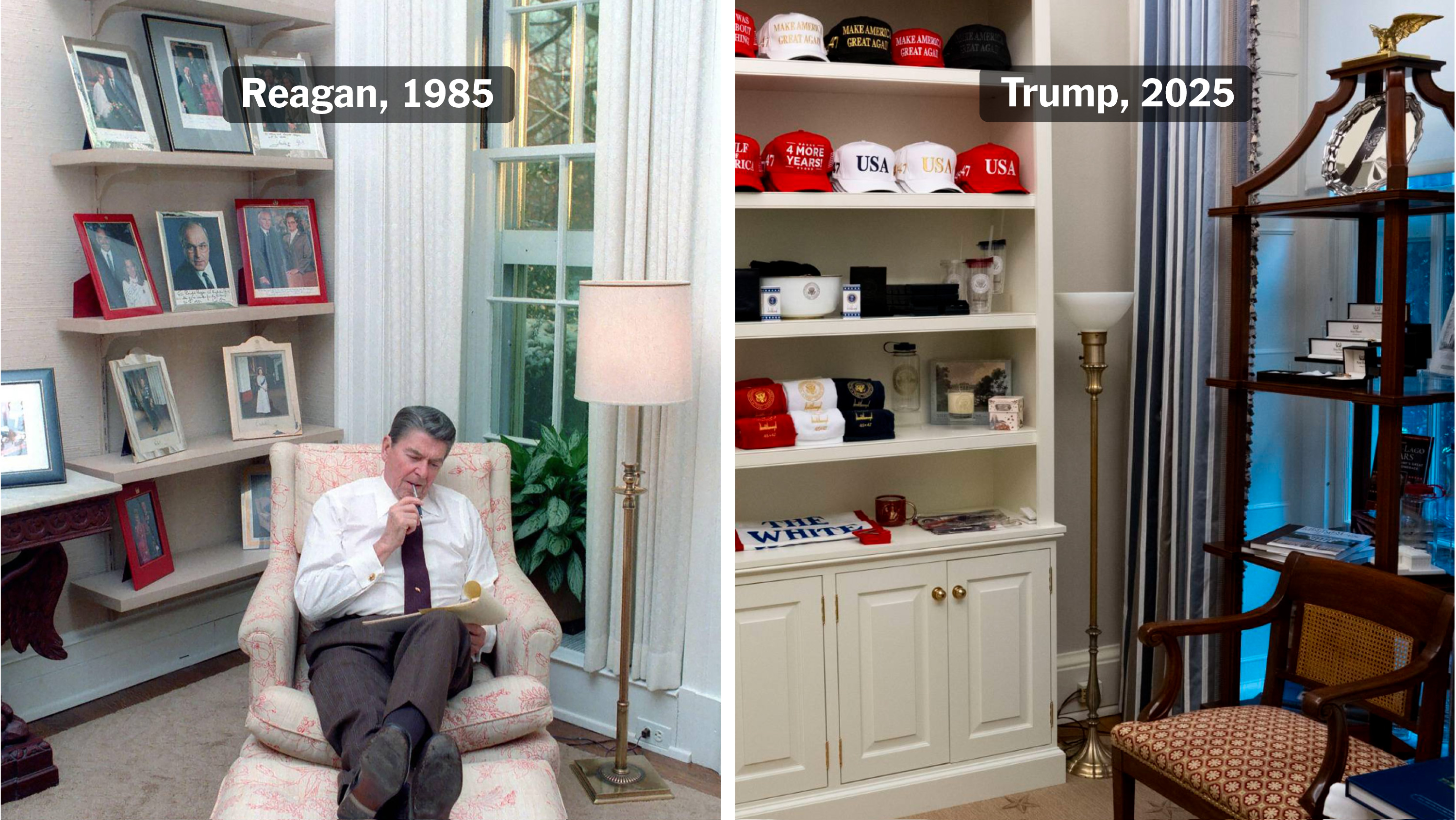বেতনা নদীর উৎস ও প্রবাহপথ
বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী বেতনা। এর উৎপত্তি যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে। প্রাচীনকাল থেকেই এই নদী জনপদের জীবন, ব্যবসা ও পরিবেশের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। যশোর থেকে নদীটি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং শেষে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়।
এই নদী যাত্রাপথে বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন নামে পরিচিত হয়। যশোরের অংশে নদীটি ‘বেতনা’ নামে পরিচিত হলেও সাতক্ষীরায় পৌঁছালে একে স্থানীয়ভাবে ‘শাকবাড়িয়া’ নামে ডাকা হয়। খুলনার অংশে এটি ‘কয়রা’ বা ‘ধানসাগর’ নামে পরিচিত হয়ে থাকে। শেষদিকে সুন্দরবন অতিক্রম করে এটি ‘রায়মঙ্গল’ নামে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশে যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্যে বেতনা নদীর ভূমিকা
বেতনা নদী এক সময় দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণরেখা ছিল। যশোর, সাতক্ষীরা, কলারোয়া, তালা, পাইকগাছা, কয়রা—এইসব অঞ্চল থেকে কৃষিজ পণ্য, কাঠ, মাছ ও লবণ জলপথে কলকাতা পর্যন্ত রপ্তানি করা হতো। এই নদীপথ ব্যবহার করে নৌকা, পালতোলা বড় বড় কার্গো চলাচল করত। বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলে ও দেশভাগের পূর্বে এই নদীপথে কলকাতার বাজারে পণ্য পৌঁছে দিত স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। কলকাতা বন্দরের সঙ্গে সংযোগ থাকায় এই নদীর মাধ্যমে গ্রামীণ বাংলার ব্যবসা শহরমুখী হতো।
দুই তীরের বনভূমি: ২০০ বছর আগের চিত্র
দুই শতাব্দী আগে বেতনা নদীর দুই পাড় ছিল ঘন বনভূমিতে আচ্ছাদিত। যশোর থেকে শুরু করে সুন্দরবনের মুখ পর্যন্ত এই নদীপথে ছিল নানা প্রজাতির বৃক্ষরাজির সমাহার।
উত্তরাংশে (যশোর-সাতক্ষীরা):
এই অঞ্চলে দুই পাড়ে ছিল শাল, গজারী, হিজল, করচ, বট, পাকুড়, হরীতকী, আমলকী প্রভৃতি গাছের আধিক্য। বনের মাঝে মাঝে ছিল বাঁশঝাড়, ঝাউবন ও কেওড়া গাছ।

দক্ষিণাংশ (সুন্দরবনের অংশ):
খুলনার অংশে প্রবেশ করলে নদীর দুই তীরে ছিল ম্যানগ্রোভ বন—বিশেষ করে গরান, গেওয়া, সুন্দরী, পশুর, কাঁকর ইত্যাদি প্রজাতির গাছ। এই সব গাছ নদীর লবণাক্ত পানিতে টিকে থাকতে পারত।
বন্যপ্রাণী ও মাছের আধিক্য
বেতনা নদী ও তার বনাঞ্চলে ছিল সমৃদ্ধ বন্যপ্রাণের বসবাস। ১০০ থেকে ২০০ বছর আগে এখানে দেখা যেত:
- স্তন্যপায়ী প্রাণী:চিতা বিড়াল, মেছোবাঘ, বানর, বনরুই, খাটাশ, শেয়াল, বন্য শুয়োর
- জলজ প্রাণী:ডলফিন, শুশুক, গাঙ্গেয় কুমির (Gharial), এবং নোনাজলের কুমির (Crocodile)
- পাখি:সারস, মাছরাঙা, বক, পানকৌড়ি, বালিহাঁস
মাছের আধিক্য:
বেতনার জলে প্রচুর প্রজাতির মাছ পাওয়া যেত। এর মধ্যে অন্যতম ছিল:
- ইলিশ (যদিও মূলত লবণাক্ত জলে),
- বাইন,বোয়াল, পুঁটি, টেংরা, চিংড়ি, কৈ, মাগুর, শিং
- মিঠাপানির ৪০টির বেশি প্রজাতি এখানে পাওয়া যেত

কুমির ও হাঙরের উপস্থিতি
বিশেষ করে খুলনার দক্ষিণাংশ থেকে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে বেতনা নদীতে একসময় নোনাজলের কুমিরের আধিক্য ছিল। সেইসঙ্গে, বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি এলাকায় ছোট প্রজাতির হাঙরও দেখা যেত, যারা জোয়ার-ভাটার সময় বেতনায় উঠে আসত। ১০০ বছর আগেও কয়রা ও ধানসাগরের মধ্যবর্তী নদীপথে এইসব প্রাণীর আধিপত্য ছিল।
ধ্বংসের শুরু ও বর্তমান পরিস্থিতি
বেতনা নদীর বন, জীববৈচিত্র্য ও পানিপ্রবাহে ধ্বংসের সূচনা শুরু হয় ১৯২০-এর দশকে। এর কারণ ছিল:
- বৃক্ষনিধন ও বনভূমির দখল
- নদী ভরাট ও বাঁধ নির্মাণ
- চিংড়ি ঘেরের বিস্তার
- রাসায়নিক চাষাবাদ
- নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও খননের অভাব
১৯৪৭-এর দেশভাগের পর কলকাতার সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নদীর গুরুত্ব কমতে থাকে। স্থানীয়ভাবে ঘের ও কৃষিকাজে অতিরিক্ত ব্যবহার এবং অপরিকল্পিত বাঁধ ও স্লুইসগেট নির্মাণে নদীর স্বাভাবিক জোয়ার-ভাটা ও পানি চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। এতে নদীর গভীরতা কমে এবং নাব্যতা হারায়।
আজকের বেতনা: কী কাজে আসে?
বর্তমানে বেতনা নদীর বিভিন্ন অংশে পানি স্বল্পতা রয়েছে। অনেক জায়গায় নদী নালায় পরিণত হয়েছে, অন্যত্র আবার চিংড়ি ঘেরের জলাধার।
তবে এখনও কিছু এলাকায় এই নদী ব্যবহার করা হয়:
- চাষাবাদের সেচ কাজে
- মাছ চাষে (চিংড়ি,তেলাপিয়া, রুই, কাতলা)
- স্থানীয় যোগাযোগে ছোট নৌকাযোগে
তবে জোয়ার-ভাটা দুর্বল হয়ে পড়ায় কৃষি উৎপাদনে পানি সংকট দেখা দিচ্ছে। লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে অনেক জমিতে আর ধান চাষ সম্ভব নয়।
বাঁচাতে হবে বেতনাকে
বেতনা নদী কেবল একটি জলপ্রবাহ নয়—এটি এক সময়কার সমৃদ্ধ বন, জীববৈচিত্র্য, ব্যবসা এবং ঐতিহ্যের প্রতীক ছিল। এখন তার অস্তিত্ব সংকটে। বেতনাকে যদি পুনরুজ্জীবিত করা না যায়, তবে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশের নদীভিত্তিক কৃষি, মৎস্য ও জীববৈচিত্র্য চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে। জরুরি ভিত্তিতে নদী পুনঃখনন, স্লুইসগেট সংস্কার, বন রোপণ এবং পানি প্রবাহের স্বাভাবিকতা নিশ্চিত করতে হবে।

 সারাক্ষণ ডেস্ক
সারাক্ষণ ডেস্ক