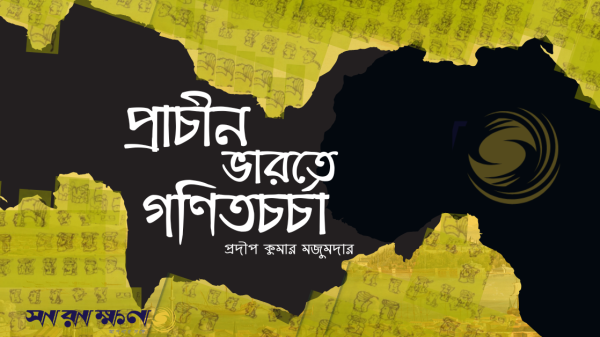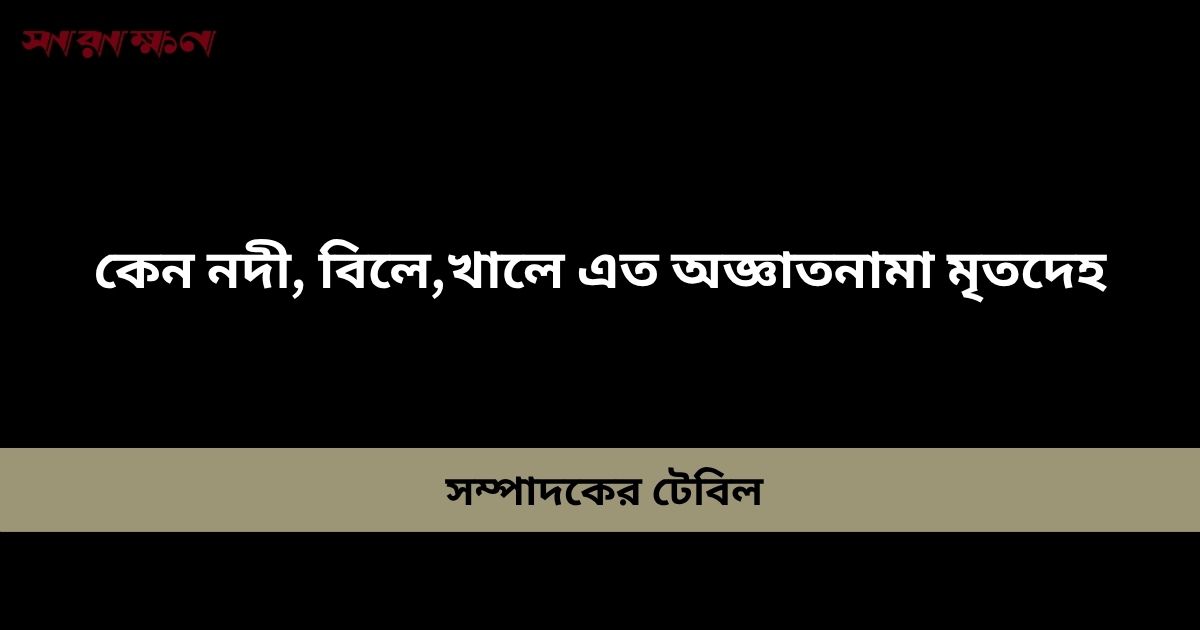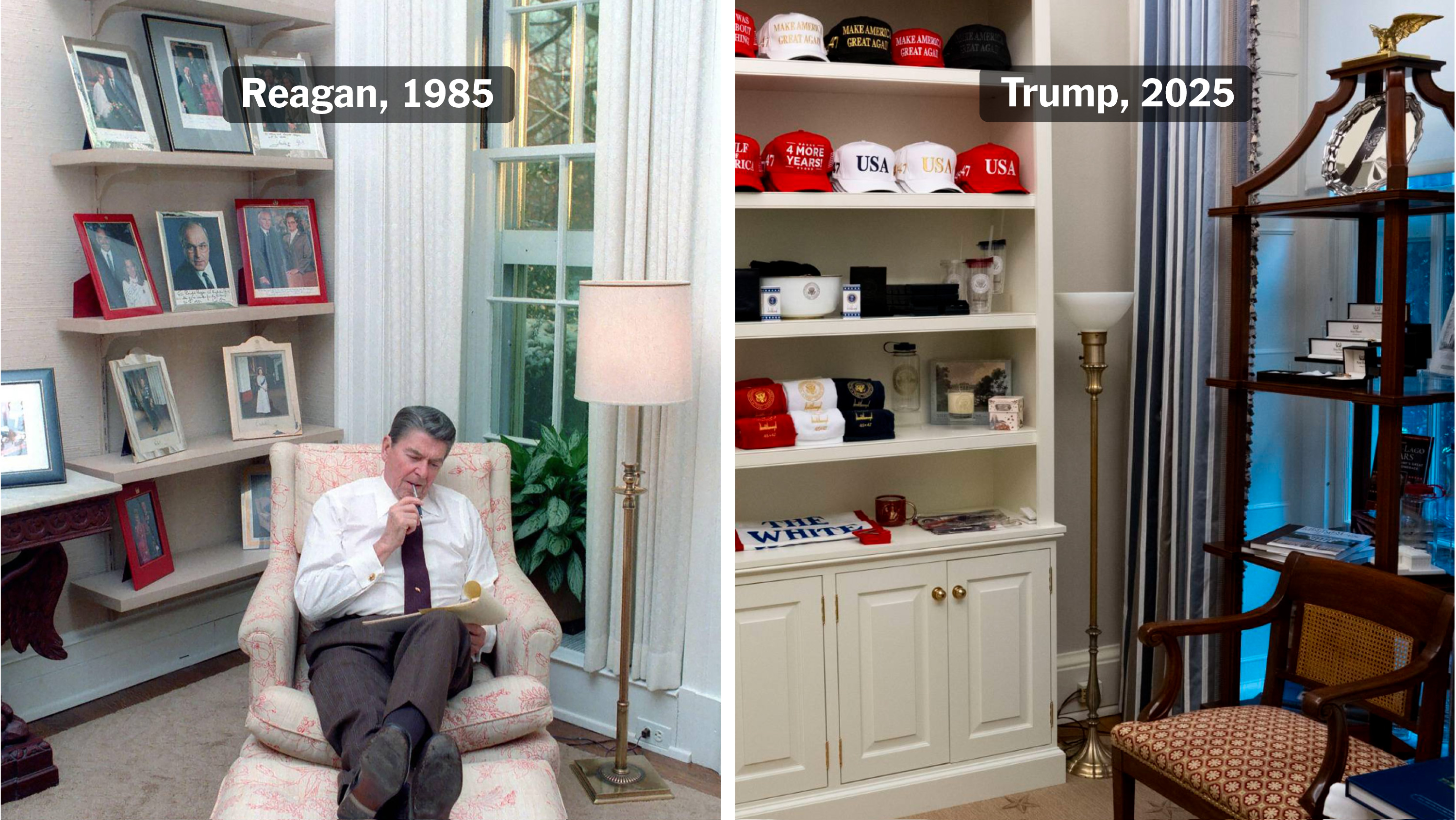নীতির পেছনের যুক্তি ও বাস্তবতা
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার (যেমন খুলনা, বরিশাল, যশোর, বাগেরহাট, পিরোজপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, বরগুনা ইত্যাদি) বাসগুলো আর ঢাকার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। এসব বাসকে নগরের বাইরে নির্ধারিত টার্মিনালে থামতে হবে এবং সেখান থেকে যাত্রীদের অন্য বাহনে শহরে ঢুকতে হবে।
এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য শহরের যানজট কমানো এবং ‘বাস রুট রেশনালাইজেশন’ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে সাধারণ ও দরিদ্র যাত্রীরা, যাদের হাতে সময় ও অর্থের ঘাটতি।
এক যাত্রায় দুই ভাড়া: আর্থিক চাপে দরিদ্র যাত্রীরা
সাধারণ মানুষ আগে একবার বাসে উঠেই রাজধানীর গন্তব্যে পৌঁছে যেতেন। এখন নতুন নিয়মে তাদের একবার বাসে, তারপর রিকশা, সিএনজি কিংবা নগর পরিবহন ধরে শহরে ঢুকতে হবে।
এতে যাতায়াতে খরচ বেড়ে যাবে দ্বিগুণ। শ্রমজীবী, দিনমজুর, পোশাককর্মী কিংবা রোগী যারা নিয়মিত ঢাকায় যাতায়াত করেন, তারা পড়বেন গভীর আর্থিক চাপের মুখে। প্রান্তিক পরিবারগুলো একবার ঢাকায় আসতে যেভাবে সংগ্রাম করে, এখন সেটাই হবে আরও কঠিন।
শারীরিক কষ্ট ও নিরাপত্তাহীনতা: যাত্রা হবে দুর্বিষহ
ঢাকার বাইরে নির্ধারিত বাস টার্মিনালগুলো এখনো পুরোপুরি প্রস্তুত নয়। সেখানে নেই পর্যাপ্ত ছায়া, বিশ্রামাগার, নিরাপদ সড়কপথ কিংবা সঠিক গণপরিবহন সংযোগ।

নারীরা, বয়স্করা, শিশু ও শারীরিকভাবে অক্ষম যাত্রীরা অতিরিক্ত হাঁটা ও অপেক্ষায় বিপদে পড়বেন। রাতে কিংবা বৃষ্টির দিনে নিরাপত্তাহীনতা আরও বাড়বে। হকার, ছিনতাইকারী ও দালালদের দৌরাত্ম্য টার্মিনাল এলাকায় যাত্রীদের জন্য হবে বড় ঝুঁকি।
সময়ের অপচয়: ভোগান্তির এক নতুন মাত্রা
একটি বাসে চেপে ঢাকায় পৌঁছানোর যে সুবিধা ছিল, তা এখন হারিয়ে যাবে। গন্তব্যে পৌঁছাতে লাগবে ২-৩ গুণ বেশি সময়।
সকালবেলা অফিসগামী কিংবা রোগী বহনকারী যাত্রীরা অফিস টাইম বা চিকিৎসার সময় মিস করবেন। ঢাকা শহরের যেকোনো বড় মেট্রো রেল স্টেশন বা হাসপাতাল পৌঁছাতে ৩-৪টি বাহন বদলাতে হতে পারে।
স্বাস্থ্য ও জীবনের ঝুঁকি: শ্রমিকদের কষ্ট আরও বাড়বে
বহু শ্রমজীবী মানুষ প্রতিদিন ঢাকা শহরে প্রবেশ করেন কাজের জন্য। নতুন নিয়মে তারা যদি প্রতিদিন ৫-৭ কিলোমিটার হাঁটতে বাধ্য হন, তা হলে তাদের শারীরিক সক্ষমতা দ্রুত কমে যাবে।
অতিরিক্ত ঘাম, হিটস্ট্রোক কিংবা হাঁটতে গিয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়বে। রোগীরা সময়মতো হাসপাতাল পৌঁছাতে না পারায় জীবনের ঝুঁকি তৈরি হবে।
একতা ও সমতার প্রশ্নে নীতি বিভাজনমূলক
এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে গ্রামাঞ্চল বা মফস্বল থেকে আসা দরিদ্র জনগণ। তারা আগে যেভাবে শহরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এখন তাতে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হচ্ছে।
নারীরা ও শিক্ষার্থীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, কারণ তারা দীর্ঘ যাত্রায় নিরাপত্তা ও খরচের কারণে পিছিয়ে পড়বেন। প্রান্তিক জেলা ও ঢাকার মাঝে যে সেতুবন্ধন ছিল, সেটি এখন ভেঙে পড়ার পথে।

অপরিকল্পিত বাস্তবায়ন: পরিকাঠামোর অভাব
বাস প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা চালু হলেও এখনো অনেক বাস টার্মিনাল, যেমন কাঞ্চনপুর, হেমায়েতপুর, গাবতলী বাইপাস প্রভৃতি পুরোপুরি প্রস্তুত নয়।
এসব স্থানে নেই মানবিক অবকাঠামো। কোথাও পর্যাপ্ত গণশৌচাগার নেই, কোথাও বিশ্রামের জায়গা নেই। কোনো জায়গায় কোনো সরকারি তথ্যকেন্দ্র বা ডিজিটাল রুট নির্দেশিকা নেই।
সম্ভাব্য সুবিধা, কিন্তু দরকার মানবিক ভারসাম্য
এটা ঠিক যে এই নীতির মাধ্যমে ঢাকার ট্রাফিক কিছুটা কমতে পারে, এবং ঢাকা নগর পরিবহন প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজ হতে পারে।
কিন্তু এ ধরনের প্রকল্পের মূল লক্ষ্য যদি হয় “মানুষের ভোগান্তি কমানো”, তবে তা সঠিক ও পরিকল্পিত বাস্তবায়ন ছাড়া অসম্ভব।
জনবান্ধব নীতির প্রয়োজন
এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আগে দরকার ছিল সাশ্রয়ী ও নিরাপদ শাটল বাস চালু পার্শ্ববর্তী টার্মিনাল থেকে শহরের মূল স্থানে। টার্মিনালগুলোতে বিশ্রাম, ছায়া, তথ্য, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। রিকশা, সিএনজি ও নগর বাসের ভাড়া নিয়ন্ত্রণে আনাও ছিল প্রয়োজনীয়।
দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন চলাচল যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, সেটাই রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব হওয়া উচিত।
এই প্রতিবেদনের মূল বার্তা: একটি ভালো উদ্যোগ তখনই সুফল বয়ে আনে, যখন তা জনমানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়। না হলে তা পরিণত হয় আরেকটি ‘সুন্দর কিন্তু নিঃসহায়’ সিদ্ধান্তে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট