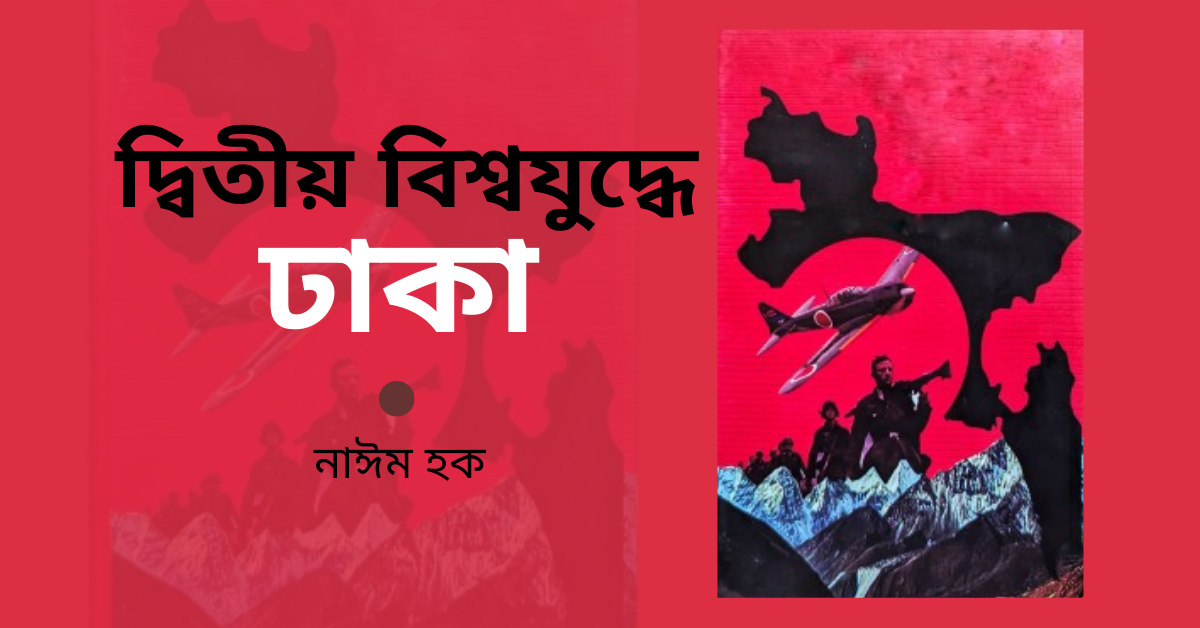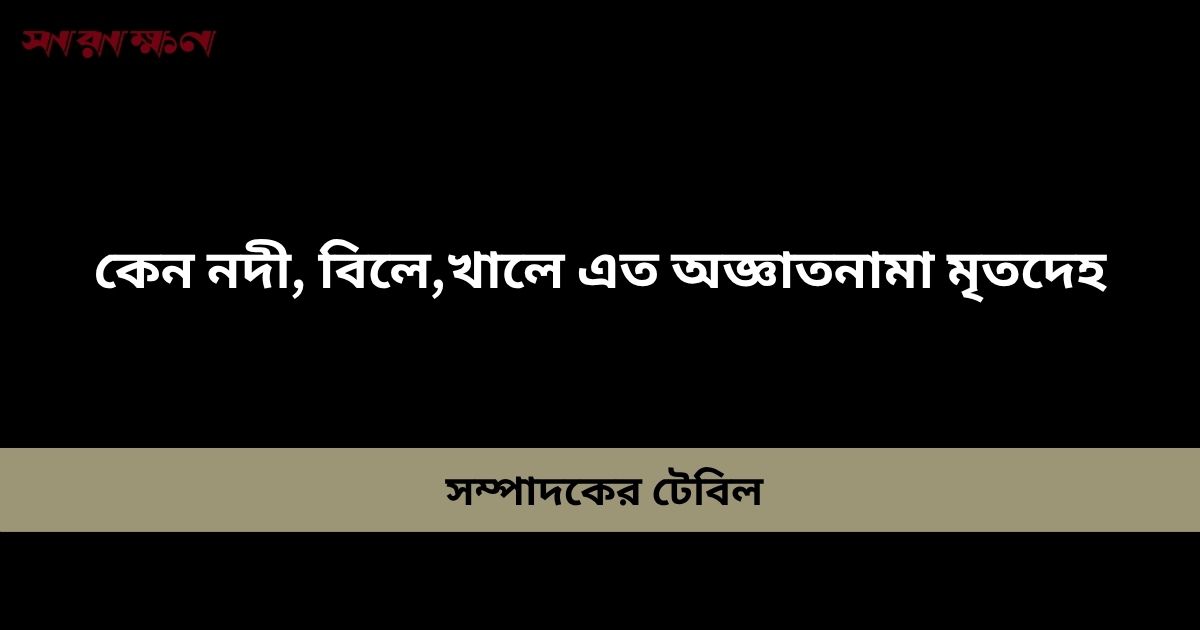বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। দেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলে, ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর জেলার বুক চিরে বয়ে চলেছে এক প্রাচীন নদী—ঝিনাই। একসময় এ নদী ছিল জীবনের প্রতীক, শস্যক্ষেতের প্রাণ, মানুষের আস্থার ঠিকানা। আজ নদীটি দখল, ভরাট, পলি জমা আর অবহেলায় মৃত্যুপথযাত্রী। শেরপুরবাসীর ইতিহাস, সংস্কৃতি আর জীবনধারার সঙ্গে যে নদী এত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে, তার অস্তিত্ব সংকট এখন গোটা অঞ্চলের জন্যই এক সতর্ক সংকেত।
নদীর ভৌগোলিক বিস্তৃতি
ঝিনাই নদীর উৎপত্তি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র থেকে। শেরপুর জেলার শ্রীবরদী ও নালিতাবাড়ী অঞ্চলে এর ধারা শুরু হয়ে জামালপুর হয়ে টাঙ্গাইলের দিকে চলে যায়। মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩৩ কিলোমিটার, প্রস্থ গড়ে ৭০–৮০ মিটার। দক্ষিণে গিয়ে নদীটি বংশী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বৃহত্তর ধারা তৈরি করে।
এ নদীর প্রবাহ সর্পিলাকার। বর্ষায় নদী হতো প্রমত্তা, শুকনো মৌসুমে আবার শান্ত। একদিকে কৃষি জমিকে সেচ দিত, অন্যদিকে বাণিজ্যিক নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত হতো।
নামকরণের ইতিহাস
“ঝিনাই”—নামটির সঙ্গে আছে এক বিশেষ কাহিনি। স্থানীয়রা বলেন, একসময় নদীর তলদেশে অসংখ্য ঝিনুক বা শামুক পাওয়া যেত। ঝিনুকের আধার বলেই এ নদীর নাম হয়েছে ঝিনাই। আরেকটি ব্যাখ্যায় বলা হয়, “ঝিনাই” শব্দের অর্থ হলো সর্পিল, ঘোরানো; নদীর গতিপথ সর্পিল হওয়ায় এ নামের উৎপত্তি।
যে কারণেই নামকরণ হোক, শেরপুরবাসীর কাছে ঝিনাই কেবল একটি জলধারা নয়, বরং জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব
ঝিনাই নদী শত শত বছর ধরে শেরপুর অঞ্চলের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির চালিকাশক্তি। কৃষিজমির সেচ, মাছ ধরা, নৌকায় পণ্য পরিবহন—সবকিছুই এ নদীকে ঘিরে আবর্তিত হতো।
এক পুরনো প্রবাদ আছে:
“ঝিনাই নদীর শীর্ণ কায়া শীর্ণ, তবু দুই তীরে নেই গঞ্জ গায়ের অভাব।”
অর্থাৎ নদী যত সরুই হোক, তার তীরে মানুষের বসতি, গঞ্জ-বাজার ও কোলাহল কখনো কমেনি।
ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসনামলে শেরপুরে পাট ও ধানের ব্যবসা জমজমাট ছিল। নৌকায় করে এসব পণ্য ঝিনাই নদী দিয়ে ঢাকাসহ দেশের নানা প্রান্তে যেত। স্থানীয় আখের গুড় ও ধান-চাল এই নদীপথে বাণিজ্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল।
মানুষের জীবন ও নদীর সম্পর্ক
শেরপুরের মানুষ ঝিনাইকে বলত “মায়ের নদী”। কারণ, এ নদী থেকে তারা পেত সেচের পানি, মাছ, পানীয় জল, এমনকি জীবিকার উপায়ও।
- কৃষকের জীবন:কৃষকেরা বলত—“ঝিনাই থাকলে ফসল হয়, ঝিনাই না থাকলে খরা।” নদীর পানি সেচে ধান, পাট, গম, ভুট্টার চাষ হতো।
- জেলেদের জীবন:নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত—রুই, কাতলা, বোয়াল, শোল, টেংরা, আইড় ইত্যাদি। জেলেরা জাল ফেলে জীবিকা নির্বাহ করত।
- শিশুদের জীবন:গ্রীষ্মে শিশুরা সাঁতার কাটত, শীতে নদীর কুয়াশা ভেদ করে খেলাধুলা করত। নদীর বুকে নৌকা বাইচ ছিল স্থানীয় উৎসবের অন্যতম বিনোদন।
একজন স্থানীয় প্রবীণ কৃষক বলেন,
“আমি ছোটবেলায় ঝিনাইয়ে সাঁতার কেটেছি, মাছ ধরেছি। এ নদী ছাড়া আমাদের জীবন কল্পনাও করা যেত না।”

অর্থনৈতিক গুরুত্ব
ঝিনাই নদী ছিল শেরপুরের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু।
- নদীপথে পাট,ধান, আখ, তেলবীজ পরিবহন হতো।
- নদীর পাড়ে গড়ে উঠত হাটবাজার।
- নৌকা ছিল যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম।
১৯৫০–৬০ দশকেও ঝিনাই নদীপথ ছিল ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র। নৌকায় করে ব্যবসায়ীরা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত পণ্য নিয়ে যেতেন। এভাবেই শেরপুরের কৃষিজ পণ্য সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ত।
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্য
ঝিনাই নদী ছিল প্রকৃতির এক অনন্য সৌন্দর্যের প্রতীক।
- শীতকালেনদীর জলে ভাসত কুয়াশার আস্তরণ, যা এক স্বপ্নিল দৃশ্য তৈরি করত।
- বর্ষায়নদী হতো প্রমত্তা, গর্জন করে ভাসিয়ে নিয়ে যেত আশেপাশের জমি।
- গ্রীষ্মেনদী শান্ত হয়ে যেত, শিশুরা খেলায় মেতে উঠত।
নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছিল নানা বৃক্ষরাজি—বট, অশ্বত্থ, কদম, তাল। নদীতে নানা প্রজাতির মাছ ছাড়াও ছিল কচ্ছপ, শামুক ও ঝিনুক। পাখিদের কলকাকলি নদীর পরিবেশকে করে তুলত প্রাণবন্ত।
বর্তমান সংকট
আজ ঝিনাই নদী আর আগের মতো নেই।
দখল: নদীর দুই তীর দখল করে গড়ে উঠেছে বসতি, দোকানপাট।
ভরাট: নদীর বুক ভরাট করে বানানো হয়েছে চাষের জমি।
পলি জমা: বছরে বছরে পলি জমে নদীর গভীরতা কমে গেছে।
পানি প্রবাহ কমে যাওয়া: পুরাতন ব্রহ্মপুত্র থেকে সংযোগ দুর্বল হয়ে যাওয়ায় নদী এখন শুষ্ক মৌসুমে প্রায় শুকিয়ে যায়।
একজন প্রবীণ বলেন,
“আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আর ঝিনাই নদীও যেন আমার মতো বুড়িয়ে গেছে। আগের সেই স্রোত, সেই মাছ, সেই জীবন আর নেই।”

ভাঙন ও প্রাকৃতিক বিপদ
বর্ষায় নদী আবার ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।
- হঠাৎ পানি বেড়ে আশেপাশের গ্রাম ভেঙে যায়।
- টাঙ্গাইল ও জামালপুর এলাকায় প্রতি বছর শত শত ঘরবাড়ি নদীগর্ভে হারিয়ে যায়।
- কৃষিজমি বিলীন হয়ে যায় নদীতে।
অতএব, নদী আজ আশীর্বাদ যেমন, তেমনি অভিশাপও বটে।
প্রশাসনিক ব্যর্থতা
ঝিনাই নদী রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড বহুবার পরিকল্পনা নিয়েছে।
- জরিপ করা হয়েছে,কিন্তু খনন হয়নি।
- দখল উচ্ছেদের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে,কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি।
- নদী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ এলেও তা টেকসই ব্যবহারে রূপ নেয়নি।
স্থানীয়দের অভিযোগ—“প্রতিবার নির্বাচন এলে নদী খননের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু ভোট শেষ হলে আর কোনো উদ্যোগ থাকে না।”
পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা
ঝিনাই নদীকে পুনর্জীবিত করার জন্য যা প্রয়োজন—
- খনন:নদীর গভীরতা ফিরিয়ে আনা।
- দখল উচ্ছেদ:নদীর জমি থেকে অবৈধ স্থাপনা সরানো।
- সংযোগ পুনঃস্থাপন:ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে প্রবাহ স্বাভাবিক করা।
- সামাজিক উদ্যোগ:স্থানীয় জনগণকে নদী রক্ষায় সম্পৃক্ত করা।
যদি এসব উদ্যোগ বাস্তবায়ন হয়—
- কৃষকরা আবার সেচের পানি পাবেন।
- জেলেরা মাছ ধরতে পারবেন।
- স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হবে।
- এমনকি পর্যটনের নতুন সম্ভাবনাও তৈরি হবে।

সাহিত্য, লোকসংস্কৃতি ও ঝিনাই
ঝিনাই নদী স্থান পেয়েছে লোকসংগীত, পালাগান ও কবিতায়। শেরপুর অঞ্চলের গানগুলোতে বারবার উচ্চারিত হয় এই নদীর নাম। এক গ্রামীণ গানে বলা হয়েছে—
“ঝিনাইয়ের জলে ভেসে যায়,
আমার শৈশবের খেলা।
সেই নদীর তীরে দাঁড়িয়ে,
আজও মনে পড়ে বেলা।”
এই গান নদীর সঙ্গে মানুষের আবেগ ও নস্টালজিয়ার প্রতিফলন।
ঝিনাই নদী শুধু একটি প্রাকৃতিক জলধারা নয়—এটি শেরপুরের ইতিহাস, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও মানুষের জীবনের প্রতীক। আজ তা মৃত্যুপথযাত্রী হলেও সঠিক উদ্যোগ নিলে আবারও প্রাণ ফিরে পেতে পারে।
ঝিনাইকে বাঁচানো মানে শেরপুরকে বাঁচানো। নদী পুনর্জীবিত হলে কৃষক, জেলে, ব্যবসায়ী—সবাই উপকৃত হবেন। সবচেয়ে বড় কথা, প্রজন্মের পর প্রজন্মের ঐতিহ্য রক্ষা পাবে।
নদী বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও। ঝিনাই বাঁচলে শেরপুরের আশা আবার ফিরবে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট