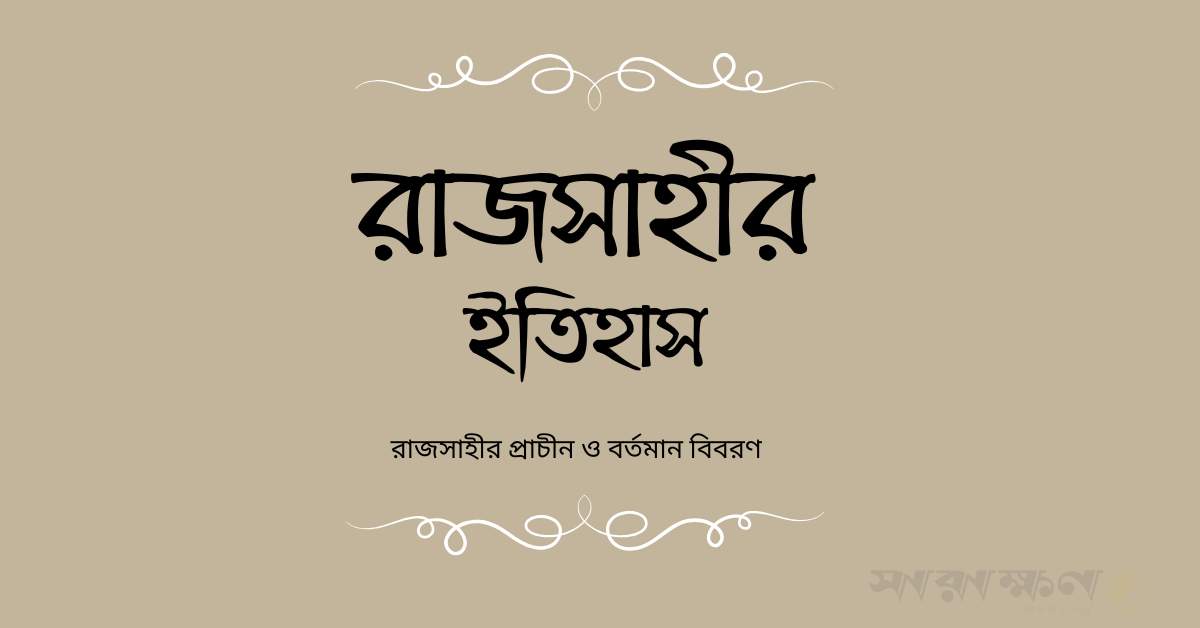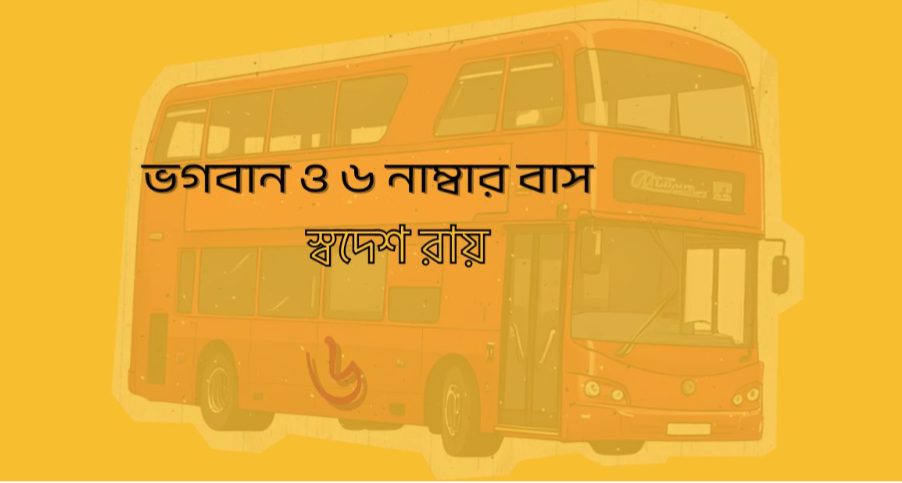৫ঃকায়স্থ কি শূদ্র?-অগ্নিপুরাণ মতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদপদ্ম হইতে শূদ্রমণি উৎপন্ন হয়। শূদ্র ব্রাহ্মণের সেবা করিবে। শূদ্রমণির পুত্র হীম, হীমের পুত্র প্রদীপ, এবং প্রদীপের পুত্র কায়স্থ। এই পুরাণমতে শূদ্রমণি হইতে কায়স্থের উৎপত্তি হইল। এই কায়স্থমণির তিন বিখ্যাত পুত্র-চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রগুপ্ত স্বর্গে গমন করিয়া যমের সভায় লেখক হইয়া আছেন। বিচিত্র নাগলোকে গমন করেন। চিত্রসেন পৃথিবীতে বংশবিস্তার করেন। চিত্রসেনের দুইপক্ষ-এক পক্ষ হইতে করণ ও অনুকরণ এবং অপর পক্ষ হইতে ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ, দত্ত, করণ ও মৃত্যুঞ্জয় এই ৭ জন পুত্র জন্মিল। আবার করণ হইতে ঘোষ, সিংহ, মিত্র, দাস, দত্ত এই পাঁচজন পুত্র এবং অনুকরণ হইতে দেব, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ, নন্দী, চাকী এই নয়জন পুত্র জন্মে। এই বংশ হইতে ৭২ ঘর কায়স্থ উৎপন্ন হয়।১০ কিন্তু অন্যান্য পুরাণ মতে চিত্রগুপ্ত দেবই চতুর্দশ যম বলিয়া প্রসিদ্ধ। যমতর্পণের মন্ত্রে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে পিতামহ ব্রহ্মা আপন শরীর হইতে যম, ধর্মরাজ, বৈবস্বত, চিত্রগুপ্ত প্রভৃতিকে উৎপন্ন করেন।১২ তপন (তৃপ্ প্রীতি করা অনট্) পিতৃপুরুষদিগের প্রীতির নিমিত্ত জল দান করাকে বুঝায়। এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল জাতিই তর্পণ করিয়া থাকে। উচ্চজাতি অধস্তন জাতির প্রীতির জন্য স্বপিতৃ লোকের পূর্বে অপর বর্ণকে জল দান করিতে কোন মতে পারে না। অতএব চিত্রগুপ্ত শ্রেষ্ঠ এবং মাননীয়। “এই চিত্রগুপ্তের পুত্র চৈত্ররথ দেব। ইনি চিত্রকূট পর্বতের রাজা ছিলেন। গৌতম ঋষি ইহার উপনয়ন সংস্কার করিয়াছেন।”১২ মহারাষ্ট্র প্রদেশীয় চিত্রগুপ্ত বংশজ কায়স্থগণের ৪১টি উপাধি আছে, তন্মধ্যে গড়করী, রণদিবে, বিবাদে ও চৌবল উপাধি দেখা যায়। “গড়করী” শব্দে দুর্গরক্ষক, “রণ-দিবে” শব্দে রণবিজয়ী; “বিবাদে” শব্দে রাজদূত, “চৌবল” শব্দে চারি প্রকার সৈন্যের নায়ক বুঝায়। “কায়স্থ বংশাবলীর” সংগৃহীতা বলেন-পরাশরীয় কুলার্ণবে কায়স্থ শব্দের বুৎপত্তি এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, ক-শব্দে প্রজাপতি, আয় শব্দে বাহু, স্থ-শব্দে স্থিত, অর্থাৎ ব্রহ্মার বাহুতে স্থিত থাকিয়া উদ্ভূত। এই হেতু কায়স্থ বলিয়া কীর্তিত। যথা:-
কঃপ্রজাপতি ব্যাখ্যাত আয়ো বাহুস্তথৈব চ।
তত্রস্থস্তং সমুদ্ভূতঃ কায়স্থ ইতি কীর্তিতঃ।
বাহুজাত ক্ষত্রিয় সমাজ হইতেই চিত্রগুপ্ত নামে একজন লেখাপড়ার আবিষ্কার করিয়া, কায়স্থ আখ্যায় স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। সুতরাং কবি কল্পনার দ্বারা ঐরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে। কায়স্থ শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা “কায়েস্থিত”।
ভরতের দেশ বলিয়া আমাদের বাসস্থানকে “ভারতবর্ষ” বলে। এক সময়ে এদেশ কেবল জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কোন কোন স্থানে দুই এক ঘর ভীল, খন্দ, সাঁওতালদের মত অসভ্য জাতীয় লোক বাস করিত। অতি পূর্বকালে এশিয়ার মধ্যদেশে “আর্য” নামে একজাতি বাস করিতেন। তাহারা সময়ে সময়ে দলে দলে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে বাস করেন। তাহাদের এক দল ইউরোপে প্রবেশ করেন, একদল পারস্য দেশও ছাড়িয়া আইসেন এবং তৃতীয় দল সিন্ধু নদী পার হইয়া পাঞ্জাবে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহারাই সরস্বতী ও দূষদ্বতী নদীর নিকটবর্তী ব্রহ্মবর্ত নামক জনপদে বাস করিতে লাগিলেন। ইহারাই ভারতবর্ষের আর্থ জাতি। ইহারাই আমাদের পূর্বপুরুষ। ইংরেজ, ফরাসি, জর্মান প্রভৃতি ইউরোপীয় লোকেরা এবং আরবি ও পারসি প্রভৃতি এশিয়া-দেশবাসীরাও আর্য বংশসম্ভূত। অতএব, বর্তমান ইংরেজ, ফরাসি, মুসলমান, পারসি, হিন্দু সকলেই এক জাতি ছিল। এই ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা স্বীকার করিলে সকলেই বলিতে পারে যে আর্যদিগের মধ্যে প্রথমে জাতিভেদ ছিল না। এই আর্যজাতিরা গুজরাট হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত তাহাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়া, সেই দেশকে আর্যবর্ত নাম দিলেন। এই বঙ্গবাসীরাও আর্য সন্তান। আর্যজাতিরা স্বভাবত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু তাহারা এদেশে আসিয়াবধি আদিমবাসীদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া, নিজে সকল সময় যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম সম্পন্ন করিতে পারিবেন না, এই বিবেচনায় তাহারা পুরোহিত নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ কার্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তজ্জন্য আর্যেরা নিজ বাসস্থান ছাড়িয়া দূরদেশে অনেক সময় থাকিতে লাগিলেন। দৈবকার্য ও পরিবারের ভরণপোষণ জন্যও কৃষিকার্য আবশ্যক হইয়া উঠিল। আর্যজাতির কৃষি প্রিয় কার্য ছিল। যাহারা যুদ্ধে পটু নহে, তাহারাই বাটিতে থাকিয়া কৃষি ও বাণিজ্য এবং যাগ-যজ্ঞাদি নির্বাহ করিতেন। এই সময় সমাজের এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে একজাতি থাকিলে কাজকর্মের সুবিধা হয় না। অতএব কালক্রমে আর্যজাতির মধ্যে যাহারা পুরোহিত অর্থাৎ বেদজ্ঞ জ্ঞানী এবং যাগযজ্ঞের ভার গ্রহণ করিলেন, তাহারা ব্রাহ্মণ; যাহারা যুদ্ধ করিয়া শত্রু হইতে দেশরক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিলেন, তাহারা ক্ষত্রিয় এবং যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার ভার গ্রহণ করিলেন, তাহার বৈশ্য বা বণিক নাম প্রাপ্ত হইলেন। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যে সকলকে বন্দি করিয়া আনিতে লাগিলেন, তাহারা কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র’ নাম প্রাপ্ত হইল। প্রভুর সেবা করা এবং কৃষি দ্বারা তাহাকে প্রতিপালন করা শূদ্রের কর্তব্যকর্ম নির্ধারিত হইল। এখন বলা যাইতে পারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আর্যবংশ সম্ভূত, শূদ্র বা দাস আর্যবংশ-সম্ভূত নহে। এই ত জাতিভেদের সৃষ্টি হইল। এইরূপে জাতিভেদের সৃষ্টির পর হইতে ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ বিদ্যায় এত পটু হইলেন যে সমুদয় রাজ্য তাহাদের করতলস্থ। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধে অনভ্যাসবশত তাদৃশ যুদ্ধ-নিপুণ ছিলেন না আবার ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং অস্ত্রধারণ না করিয়া ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তখন ক্ষত্রিয়েরা প্রবল এবং ব্রাহ্মণেরা হীনবল হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে সংগ্রাম করিতে লাগিল। ভুজবলে ক্ষত্রিয়েরা এবং তপোবলে ও ব্রাহ্মণ্য বলে ব্রাহ্মণেরা তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। আবার ‘এই সময়ে পরশুরাম ক্ষত্রিয়বংশও প্রায় ধ্বংস করেন, এবং তৎপরে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া ক্ষত্রিয় বংশ বিস্তার করেন। পরশুরাম ক্ষত্রিয় রাজা চন্দ্রসেনকে নিহত করিয়া ক্ষত্রিয় জাতিকে যেরূপ দুর্দশায় পাতিত করেন, তাহা নিম্নোদ্ধত শ্লোকে প্রতিপন্ন হইবে।
তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্যে। ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ।।
তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে।
ততো দালভ্যঃ প্রতুবাচ দদামি তব বাঞ্চিতং।।
স্কন্দ পুরাণ।
রাজা চন্দ্রসেন নিহত হইলে পর, তাহার গর্ভবর্তী পত্নী মহর্ষি দালভ্যের শরণাপন্ন হইলেন। পরশুরাম জানিতে পারিয়া, ঋষির নিকট হইতে রাজমহিষীকে প্রার্থনা করেন। ঋষি বলিলেন, শাস্ত্রে ইহা লিখিত আছে যে স্ত্রী ও বালক অবধ্য। অতএব স্ত্রীলোককে ক্ষমা করা উচিত। পরশুরাম ক্ষমা করিলেন এবং বলিলেন যে রাজমহিষীর গর্ভজাত সন্তান “কায়স্থ” নামে পরিচিত এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইবে। এই সময় হইতে চন্দ্রসেনের পুত্র “কায়স্থ” নামে খ্যাত এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম বর্জিত হইলেন। মহর্ষি দালভ্য কায়স্থকে ক্ষত্রিয় ধর্ম হইতে বর্জন করিয়া চিত্রগুপ্তের ধর্ম প্রদান করেন। এই ঘটনার পর হইতে চন্দ্রসেন বংশ ও চিত্রগুপ্ত বংশ এক হইয়া গিয়াছে। “মহর্ষি দালভ্যের অনুগ্রহে কায়স্থগণ ধার্মিক, সত্যবাদী, সদাচার পরায়ণ হইয়াছেন”।” এই বিপ্লব সময়ে সকল জাতির বিশেষত ক্ষত্রিয় জাতির আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ক্রিয়াকলাপ, নাম উপাধি ও সামাজিক নিয়মাদির ব্যতিক্রম ঘটিল। অতএব এই সময় হইতে অনেক ক্ষত্রিয় পরশুরামের ভয়ে বা ব্রাহ্মণের উৎপীড়নে শূদ্রের মত আচার গ্রহণ করিলেন। তপোবলে ব্রাহ্মণেরা তেজস্বী হইলে, তাহারা ক্ষত্রিয়দের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। তখন ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রাহ্মণের উপদেশ ভিন্ন কোন কার্য নির্বাহ করিতেন না। অতি প্রাচীন কালে জাতিভেদ সৃষ্টি হওয়ার পরেও, বেদানুযায়ী সকল কার্য নির্বাহ হইত। পুরাণ শাস্ত্র প্রণয়নের পর হইতেই বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ অনেক শিথিলভাব অবলম্বন করিল এবং হিন্দু শান্ত ক্রমে জটিল রূপ ধারণ করিল। যখন ব্রাহ্মণের প্রাধান্যই বেশি, এবং ক্ষত্রিয়ের কোন প্রাধান্যই নাই, তখন ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের অনুগত এবং দাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবার ব্যবস্থানুযায়ী জাতিভেদ একবারে দৃঢ়ীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহার অনেক পরে সেন বংশীয় রাজাদের সময়ে বরেন্দ্রভূমিতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত হয়। নবগুণ বিশিষ্ট হইলেই কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, কি বৈদ্য কুলীন হইল। এস্থলে জাতিভেদে নবগুণের তারতম্য হইল না। এই নয়টা গুণ মধ্যে একটি গুণ আবৃত্তি। আবৃত্তি শব্দে বেদপাঠ বুঝাইত। শূদ্রের যে কেবল বেদপাঠের অধিকার নাই এমন নহে। বেদ পাঠ শুনিবারও অধিকার নাই। এমতাবস্থায় কায়স্থ ক্ষত্রিয় না হইলে কি প্রকারে নবগুণের অন্তর্গত পর্যন্তও কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সম্মানিত হইতেন। আবৃত্তি (বেদপাঠ) কায়স্থের কুলীনদের পক্ষেও সম্ভব হইল? সেনবংশীয় রাজাদের সময় পর্যন্তও কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সম্মানিত হইতেন।
উপরে যাহা যাহা ব্যক্ত করিয়াছি তাহার বলে, আমরা বলিতে পারি যে আদিতে কায়স্থ ত্রিবর্ণের সেবক ছিল না। “বাহেরাশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা কায়স্থা জগতীতলে। চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমন্ডলে।” এই প্রাচীন ঋষি-বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারা যায় যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্ত বংশোন্তব। “কায়স্থ শব্দ জাতি বাচক নহে, উহা লিপি-ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়দিগের উপাধি মাত্র। কালক্রমে ঐ উপাধিই জাতিগত হইয়া কায়স্থগণ এক স্বতন্ত্র জাতিতে পরিগণিত হইয়াছেন। এইরূপে চিত্রগুপ্ত বংশজ কায়স্থ শ্রেণি গঠনের পর পরশুরামের বিপ্লব সময়ে চন্দ্রসেন রাজর্ষির সন্তানও কায়স্থ আখ্যা গ্রহণ করিয়া চিত্রগুপ্ত বংশধরদিগের শ্রেণিভুক্ত হইয়াছেন।”১” আরও প্রতীতি হয় যে, এককালে কায়স্থ ঋষির শিষ্য হইয়া উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যুদ্ধকার্যে নিবিষ্ট হইয়াছিলেন, লিপিকর ছিলেন এবং জ্যোতির্বিৎ ও রাজকর্মচারী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আদিশূরের সময় পঞ্চ কায়স্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে আইসেন। এ সময়ও কায়স্থ-কুলদীপিকার “এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোহস্মি তবালয়ে” বচনে কায়স্থ রক্ষক বলিয়া কথিত। এই কায়স্থগণ সম্বন্ধে দেবীবর নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, “আর কয়েকজন ব্যক্তির ব্রাহ্মণের চিহ্ন ছিল না, তাহারা অসি কবচ ধনুর্ধারী হইয়া অশ্বারোহণে বীরবেশে আগমন করাতে রাজার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। তজ্জন্য তিনি একি একি বলিয়া ভয়ে অন্তঃপুরে পলায়ন করিলেন। “১” দেবীবরের মতে কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণ রক্ষক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেছে। রঘুনন্দনের প্রাদুর্ভাবে বঙ্গীয় কায়স্থগণের সম্মান খর্ব হইলেও, “ব্রাহ্মণকুলের চূড়ামণি নবদ্বীপাধিপতি সর্বশাস্ত্র বিশারদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়বাহাদুর তাহার অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী যজ্ঞ সময়ে সভামণ্ডপে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয়ের আসন প্রদান করিয়াছিলেন।” “কায়স্থ ব্রাহ্মণের দাস।” যে প্রভুর সেবা করে, যে প্রভুকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করে, যে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করে, সেই তাহার দাস। ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থের যে দাসত্বসম্বন্ধ, সে আর্থিক সম্বন্ধ নহে; সে পরমার্থিক সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর অর্থদ্বারা সৃষ্টি হইবার নহে। কায়স্থ ব্রাহ্মণের সেবা করিবে বলিয়া শিষ্য, শত্রুহস্ত হইতে যাগযজ্ঞাদি রক্ষা করিবে বলিয়া মোক্ষ্যাভিলাষী হইয়া থাকে। মনু বলিয়াছেন, “বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ।” এবাক্য কায়স্থের শিরোধার্য। যে ব্রাহ্মণের শরণাগত হইলে পরব্রহ্ম ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তিপথে দণ্ডায়মান হওয়া যায়, সেই ব্রাহ্মণের দাস হওয়া কায়স্থের গৌরবের কথা। কোন বৈদিক ক্রিয়া কলাপের সময় কায়স্থ নিজ নামের পরে দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, সে বেতনভোগী চাকরের চিহ্ন নহে; সে ব্রাহ্মণের ও দেবতার প্রতি ভক্তির চিহ্ন। যে ব্রাহ্মণের প্রতি সগর, যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতি ক্ষত্রিয় মহাত্মাগণ বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহার ধর্মোপদেশ গ্রহণে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার করা চিত্রগুপ্ত বংশোদ্ভব কায়স্থের প্রার্থনীয় এবং প্রশংসনীয়। এখন বঙ্গদেশে সে ব্রাহ্মণও নাই। সে কায়স্থও নাই, সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। সুতরাং কলির ব্রাহ্মণ সমাজেই কায়স্থগণ শুদ্র বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। এই কলির কায়স্থ তমোগুণবিশিষ্ট শূদ্রবৎ; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কায়স্থ যে শূদ্র নহে, তাহা হারিতবচনে প্রমাণিত হইবে।
‘গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন ধাতুত্বণং ন দর্ভঃ পশবোনগাবঃ।
প্রজাপতেঃ কায়সমুত্তবাচ্চ কায়স্থ বর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ।।
হারিত বচনং।
গঙ্গা জল নহে; কনক ধাতু নহে; কুশ তৃণ নহে। গো সকল পশু নহে। এবং প্রজাপতির কায় হইতে সমুদ্ভুতহেতু কায়স্থ শূদ্র নহে।
মহারাজ আদিশূরের পুত্রেষ্টি যাগ সম্পন্ন জন্য যে পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাগাণ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আইসেন, তাহাদের রক্ষক” হইয়া গৌতম গোত্রীয় দশরথ বসু, সৌকালীন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, কাশ্যপ গোত্রীয় দাশরথি গুহ, বিশ্বামিত্র গোত্রীয় কালিদাস মিত্র এবং মৌদগল্য গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত, এই পঞ্চ কায়স্থ তাহাদের সহিত আগমন করেন। যাগ সমাপন’ হইবার পর যেমন ব্রাহ্মণেরা স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তেমনই পঞ্চ কায়স্থও তাহাদের সহিত স্বদেশে ফিরিয়া যান। কিন্তু স্বদেশীয় কান্যকুব্জজ সমাজে অপরিগৃহীত হওয়ায়, সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ পুনরায় বঙ্গদেশে আগমন করেন। দ্বিতীয়বার আসিবার সময়ে তাহাদের সঙ্গে নাগ ও নাথ উপাধিধারী আর দুইজন কায়স্থ আইসেন। এই ৭ জন কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আগমনের পূর্বে গৌড়দেশে কতকগুলি কায়স্থ ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গৌড় দেশীয় কায়স্থ মধ্যে বসু উপাধির কায়স্থ ছিল না। কান্যকুব্জাগত কায়স্থের গৌড় দেশীয় কায়স্থের সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এই দুই প্রকারের কায়স্থ ৯৯ উপাধিধারী ছিল। এই সমুদয় কায়স্থগণকে বল্লালসেন চারি ভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগ বঙ্গে, দ্বিতীয় ভাগ দক্ষিণ রাঢ়ে, তৃতীয় ভাগ উত্তর রাঢ়ে এবং চতুর্থ ভাগ গৌড় দেশের বরেন্দ্র ভূমিতে বাস করেন। সেই সময় হইতে কেবল কান্যকুব্জাগত কায়স্থদিগের বংশধরগণের মধ্যে কেহ বঙ্গে, কেহ দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করেন। কিন্তু গৌড়দেশীয় কায়স্থ ঐ চারি খণ্ডে বাস করিয়া বঙ্গজ, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, উত্তর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই চারি শ্রেণিতে বিভক্ত হন। ইহাদের কুলের নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট