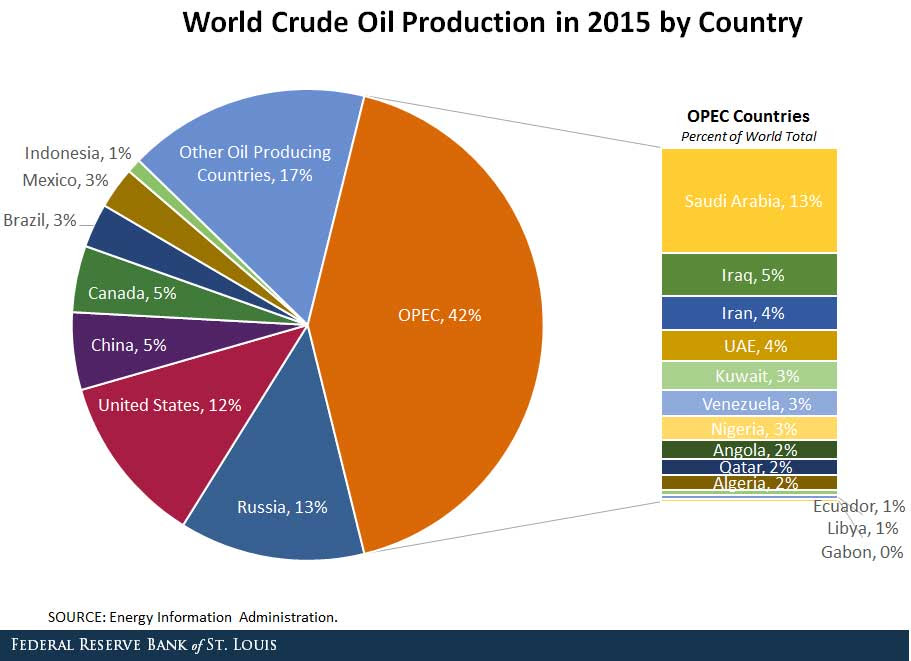বাংলাদেশে শিল্পায়নের নেপথ্যে শ্রমিক ইউনিয়ন নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। তৈরি পোশাক থেকে চামড়া, জাহাজভাঙা থেকে খাদ্যপ্রক্রিয়াজাত—প্রায় সব খাতেই শ্রমিকদের সংগঠন আছে; কোথাও তারা অধিকার রক্ষার ঢাল, কোথাও বা উৎপাদনের স্রোতে কাঁটা। প্রশ্নটা তাই একরৈখিক নয়: শ্রমিক ইউনিয়ন কতটা প্রয়োজনীয়, আবার কোথায় কোথায় তা হোঁচট খাওয়ায়?
কেন এখন এই আলোচনাটি জরুরি
রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতিতে স্থিতিশীল উৎপাদন ও বিনিয়োগ নিশ্চিত করা আজ প্রধান চ্যালেঞ্জ। বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের ঝুঁকি, অর্ডারের ওঠানামা, এবং নৈতিক উৎপাদনের দাবির মধ্যে বাংলাদেশের কারখানাগুলোতে নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি ও সামাজিক সংলাপ—এই তিনটি বিষয়কে সামনে এনে দিয়েছে। ফলে ইউনিয়নের উপস্থিতি ও তাদের কার্যকর ভূমিকা শুধু নীতিগত প্রশ্ন নয়; সরাসরি প্রতিযোগিতার সক্ষমতার সঙ্গেও জড়িত।

ইউনিয়ন: অধিকার রক্ষার কাঠামো
শ্রমিক ইউনিয়নের প্রথম কাজই হলো একটি সংগঠিত কণ্ঠস্বর তৈরি করা—যাতে মজুরি, কর্মঘণ্টা, ছুটি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, নিরাপত্তা সরঞ্জাম বা অভিযোগ নিষ্পত্তির মতো মৌলিক বিষয়গুলো আলোচনার টেবিলে আসে। সু-সংগঠিত ইউনিয়ন থাকলে মালিক পক্ষের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক, সমঝোতা স্মারক, এমনকি যৌথ উৎপাদনশীলতা পরিকল্পনা করা সহজ হয়। অভিজ্ঞতা বলছে, যেখানে অভিযোগ শোনার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা (grievance mechanism) চালু, সেখানে কর্মী বদলির হার কমে এবং কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বাড়ে—যা শেষ পর্যন্ত মুনাফাতেই প্রতিফলিত হয়।
আন্তর্জাতিক বাজারে ভাবমূর্তি ও সুবিধা
ইউরোপ-আমেরিকার বহু ব্র্যান্ড এখন ‘দায়িত্বশীল ক্রয়নীতি’ অনুসরণ করে। তারা সরবরাহকারীদের কাছে কেবল সময়মতো সরবরাহ নয়, বরং স্বাধীন ইউনিয়ন, সমঝোতা চুক্তি, এবং কারখানার সামাজিক নিরীক্ষার প্রমাণও চায়। ফলে কার্যকর ইউনিয়ন একদিকে শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করে, অন্যদিকে বাংলাদেশকে ‘দায়িত্বশীল উৎপাদনকারী দেশ’ হিসেবে উপস্থাপনে সহায়ক হয়—যা শুল্ক-সুবিধা, দীর্ঘমেয়াদি ক্রেতা সম্পর্ক ও বাজার বৈচিত্র্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।
কোথায় তৈরি হয় জটিলতা

তবে বাস্তবের চিত্র একরঙা নয়। অনেক ক্ষেত্রে ইউনিয়নের সঙ্গে রাজনীতির ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়; সংগঠনের এজেন্ডা তখন শ্রমিক কল্যাণ থেকে সরে দলীয় লক্ষ্য পূরণে ব্যবহৃত হয়। ফলশ্রুতিতে অহেতুক কর্মবিরতি, একতরফা কর্মসূচি বা উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি—যা উৎপাদন ব্যাহত করে এবং বিদেশি ক্রেতাদের আস্থা নষ্ট করে। এছাড়া আলোচনার দক্ষতা, শ্রম আইন বোঝাপড়া কিংবা তথ্যভিত্তিক দাবি উপস্থাপনের সক্ষমতার ঘাটতি থাকলে ন্যায্য দাবিও কাঙ্ক্ষিত ফল পায় না।
মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের গিঁট
কারখানা পরিচালনায় অনেক উদ্যোক্তা এখনো ইউনিয়নকে ‘বিরোধী পক্ষ’ হিসেবে দেখেন; আবার শ্রমিকদের একাংশ মালিক পক্ষকে ‘শুধুই মুনাফাখোর’ হিসেবে বিবেচনা করেন। এই পারস্পরিক অবিশ্বাস ভাঙা না গেলে ক্ষতি হয় দুই পক্ষেরই। বাজার হারালে অর্ডার যায় প্রতিবেশী দেশে; আর উৎপাদন কমলে চাকরি অনিশ্চিত হয় শ্রমিকের। তাই বিরোধ নয়, স্বচ্ছতা ও পূর্বানুমতিতে (predictability) ভরসা ফেরানোই কৌশল।
নীতি, দক্ষতা ও শাসনব্যবস্থার প্রশ্ন
ইউনিয়নকে কার্যকর করতে তিন স্তরে পরিবর্তন দরকার—
১) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: ইউনিয়ন নেতাদের জন্য শ্রম আইন, আলোচনার কৌশল, তথ্য বিশ্লেষণ, আর্থিক জবাবদিহি—এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ।
২) কারখানা স্তরের সংলাপ: যৌথ পরামর্শ কমিটি, নিয়মিত সভা, অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা, ও লিখিত সমঝোতা—এসবকে বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়ায় আনা।
৩) স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা: রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নেতৃত্ব নির্বাচন, সদস্য রেজিস্ট্রি, অডিটেড তহবিল, এবং সদস্যদের কাছে বার্ষিক কার্যপ্রতিবেদন প্রকাশ।

‘সংঘাত’ নয়, ‘সমঝোতা’কে নীতিতে তোলা
শিল্প খাতে বিরোধ অনিবার্য; তবে বিরোধ মানেই কাজ বন্ধ নয়। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, ‘ইন্টারেস্ট-বেইজড বার্গেইনিং’—অর্থাৎ উভয় পক্ষের অন্তর্নিহিত স্বার্থ চিহ্নিত করে সমাধান—দীর্ঘমেয়াদে বেশি কার্যকর। যেমন, উৎপাদনশীলতা বাড়লে প্রণোদনা; নিরাপত্তা মান বজায় রাখলে বোনাস; স্বাস্থ্যবিমা থাকলে অনুপস্থিতি কমে—এমন ‘উইন-উইন’ কাঠামো গড়া সম্ভব।
ন্যূনতম সাধারণ কর্মপরিকল্পনা (একটি প্রস্তাব)
- • রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমানো: ইউনিয়ন নেতৃত্ব নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত ও দলীয় প্রভাবমুক্ত নির্দেশিকা।
- • দক্ষতা উন্নয়ন: ত্রিপক্ষীয় (সরকার-মালিক-শ্রমিক) ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেশন।
- • তথ্যভিত্তিক সংলাপ: মজুরি, কর্মঘণ্টা, উৎপাদন, অনুপস্থিতি, দুর্ঘটনা—এসব ডেটা উভয় পক্ষের জন্য উন্মুক্ত রেখে আলোচনার মানোন্নয়ন।
- • দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি: কারখানা পর্যায়ে সময়বদ্ধ সালিশ ব্যবস্থা; ব্যর্থ হলে শিল্পাঞ্চলভিত্তিক মধ্যস্থতা সেল।
- • আন্তর্জাতিক মান ও নিরীক্ষা: সামাজিক নিরীক্ষার সুপারিশ বাস্তবায়নে যৌথ রোডম্যাপ এবং ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা।

সামনে যে ভাবনা
বাংলাদেশের শিল্পায়ন আজ কেবল কারখানা বাড়ানো নয়; সামাজিক ন্যায্যতা, কর্মস্থলের নিরাপত্তা এবং প্রতিযোগিতার সক্ষমতা—সব কিছুর সমন্বয়। সেই সমন্বয়ের কেন্দ্রে শ্রমিক ইউনিয়ন থাকতে পারে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে, যদি তারা শ্রমিককেন্দ্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসনের পথে হাঁটে। অন্যদিকে দলীয় রাজনীতির যন্ত্রে পরিণত হলে একই ইউনিয়ন শিল্পোন্নয়নের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।
অবশেষে প্রশ্নটা ‘ইউনিয়ন ভালো না খারাপ’—এভাবে দেখার নয়। বরং দেখা দরকার, কীভাবে ইউনিয়ন পরিচালিত হচ্ছে, কোন প্রক্রিয়ায় সংলাপ চলছে, এবং কতটা তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমানো, নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মালিক-শ্রমিক-সরকারের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য সহযোগিতা—এই তিন শর্ত পূরণ হলে শ্রমিক ইউনিয়নই হবে টেকসই শিল্পায়নের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। অন্যথা, সম্ভাবনার বাংলাদেশ অর্ডার হারাবে, কর্মসংস্থান অনিশ্চিত হবে, আর উন্নয়নের গতি থমকে যেতে পারে।
নীতিনির্ধারক, উদ্যোক্তা ও শ্রমিক—তিন পক্ষেরই এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়: সংঘাতের পথে এগোব, নাকি সমঝোতার টেবিলে বসে টেকসই শিল্পায়নের নতুন গল্প লিখব?

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট