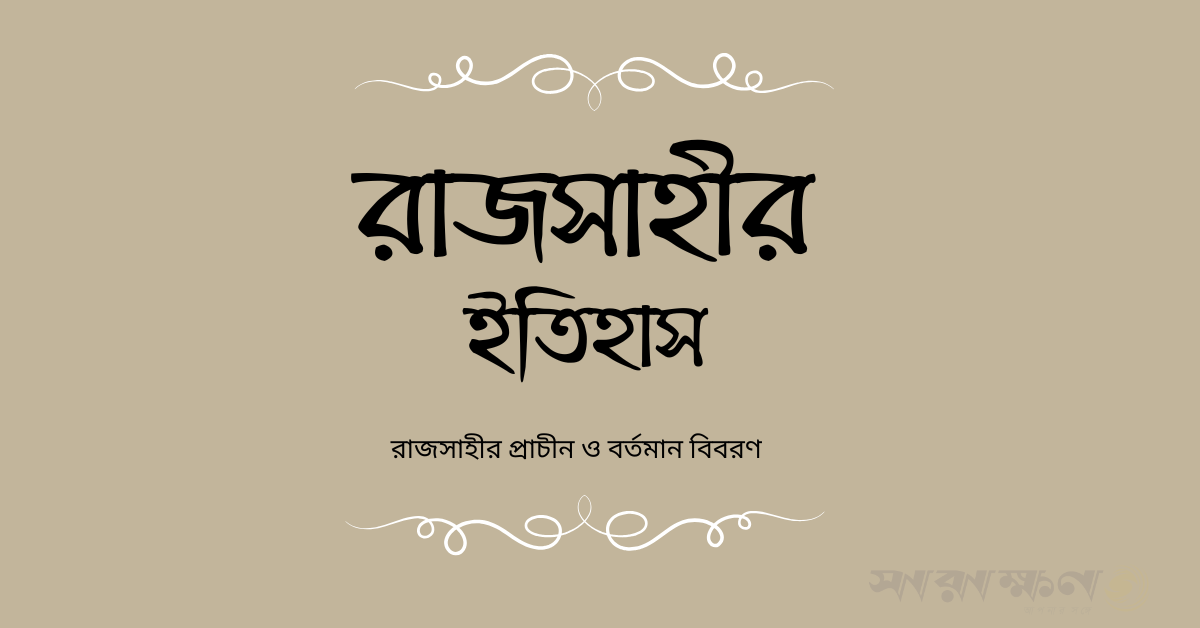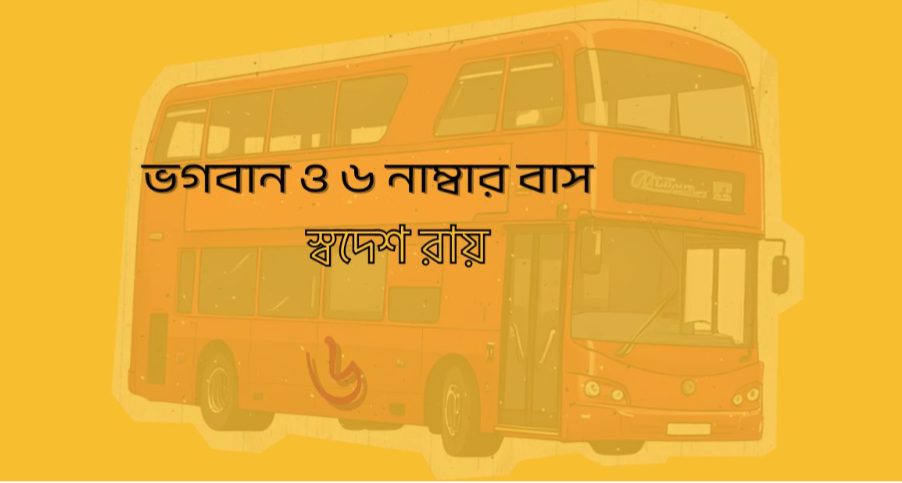স্বাধীন পাঠানদিগের সময়ে বঙ্গদেশে রঘুনন্দন, কুল্লুকভট্ট, চৈতন্যদেব প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু মোঘল সম্রাটের অধীনে বাংলার সুবাদারদের সময়ে ঐরূপ প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই বঙ্গেশ্বরদের সময়ে মুকুন্দরাম, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির জন্ম হইলেও, তাহারা রঘুনন্দন, কুল্লুকভট্ট, চৈতন্যদেব প্রভৃতির সমকক্ষ হইতে পারে না। মোঘল রাজত্ব সময়ে প্রজাগণের শিক্ষার কোনও সুবন্দোবস্ত ছিল না। সে সময়ে সংস্কৃত ভাষার যে উন্নতি দেখা যায়, তাহা হিন্দু জমিদারগণের টোল, চতুষ্পাঠীতে ভূমি ও অর্থদানের ফল। এ সময় যবন রাজার শিক্ষা বিস্তারের যত্ন ছিল না। আবার মোঘল সম্রাট বঙ্গদেশ হইতে বহুদুরে বাস করেন এবং সুবাদারগণই বঙ্গদেশের হর্তাকর্তা বিধাতা। সুবাদারগণের অধীনে জমিদারগণের ক্ষমতাও প্রচুর। বঙ্গের সুবাদার ও জমিদারগণ নিজ নিজ রাজ্য শাসনে ব্যস্ত। প্রজার শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত নহে। এইরূপ অবস্থায় মুসলমান রাজত্বের শেষ সময় এবং ইংরাজ অধিকারের কেবল প্রারম্ভে রাজ্য শাসনের সুবন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত জমিদারগণের ও মহাজনগণের অত্যাচার বৃদ্ধি হইল, চুরি ডাকাইতি বেশি হইতে লাগিল; স্থানে স্থানে দস্যু দলের সৃষ্টি হইতে লাগল; আবার নবাগত পুলিশের দারগা, জমাদার, বরকন্দাজগণের অত্যাচারে প্রজাগণ অস্থির হইয়া পড়িল। চোর ডাকাইতের অত্যাচারও বরং ভাল; কিন্তু আবার দারগা, জমাদার ও বরকন্দাজগণকে উৎকোচ দেওয়া নিঃস্ব প্রজার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। সাধারণ অশিক্ষিত প্রজাগণ আরো বেশি অস্থির হইল। জমিদারগণের অত্যাচারে, মহাজনের পীড়নে, পুলিশের শাসনে প্রজাগণ ভীত হইতেছিল কেন? সুবাদারের অশ্বারোহী, জমিদারের সিপাহি, পুলিশের লাল পাগড়ি ও চাপরাশ দেখিয়াই সে সময় প্রজাগণ ঘরে লুকাইতে লাগিল কেন? এ সময় সাধারণ প্রজাগণের এত আতঙ্ক হইয়াছিল কেন? সর্বসাধারণ প্রজাগণের মূর্খতা এবং অনভিজ্ঞতাই ইহার প্রধান কারণ। প্রজাগণকে শিক্ষিত করিলে, তাহারা সমুদয় বুঝিতে পারিবে এবং অন্যায় অত্যাচারের দায় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইবার সাহসী হইবে। ইংরেজ গবর্ণমেন্টের রাজত্বের প্রারন্তেই এই কথার আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রজার অভিযোগ সমূহ তৎকালিক ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির কর্ণগোচর হইল। কি উপায়ে সাধারণ প্রজাকে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহার যুক্তি হইতে লাগিল ।
রাজসাহীর ইতিহাস (পর্ব -২৯)
-
 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট - ০৪:৩৯:১০ অপরাহ্ন, বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
- 141
আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে প্রাকৃত ভাষা বাংলা ভাষার জননী। সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশে প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। ক্রমে পরিবর্তনে বর্তমান বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয় এবং ভাষার সঙ্গে সঙ্গে দেবনাগর অক্ষর হইতে বাংলা অক্ষরের উৎপত্তি হয়। বঙ্গভাষার আদি গ্রন্থকার কে তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাদের গ্রন্থাবলী বঙ্গভাষার আদিগ্রন্থ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন লাউসেনের মনসার গানই আদিগ্রন্থ। ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যদেবের জন্ম হয় এবং ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাহার অন্তর্ধান হয়। তাহার সময় হইতেই বঙ্গভাষার অনেক পরিবর্তন হয়। কিন্তু সেকালে এই বঙ্গভাষার উন্নতিস্রোত রাজসাহীতে প্রবাহিত হয় নাই। চৈতন্যদেব গৌড়ে গমনকালে রাজসাহীস্থ এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র স্পর্শ করেন। রাজসাহীতে তান্ত্রিক মতেরই প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সুতরাং চৈতন্যের প্রেম উঠল জ্বলদাক্ষরে প্রকাশ করিবার জন্য রাজসাহীর ব্রাহ্মণ মধ্যে তাহার কোন শিষ্যের নাম পাওয়া যায় না। তাহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণ বঙ্গভাষার বিস্তর উন্নতিসাধন করিয়া যান। গোবিন্দ দাস, জীব গোস্বামী, রূপসনাতন প্রভৃতির লেখনীতেই বঙ্গভাষা উন্নতশালিনী হয়। এই শিষ্য সম্প্রদায় মধ্যে “চৈতন্যদেবের ৮২ বৎসর পরে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বুধরী গ্রামে বৈদ্য জাতীয় পরমানন্দ গুপ্তের ঔরসে এক গোবিন্দদাস জন্মগ্রহণ করেন। “১১ ইহার প্রণীত গ্রন্থের নাম পদমালা। ইহার পদাবলী বাংলা ও হিন্দীভাষায় মিশ্রিত। এই গোবিন্দদাসের পর রাজসাহীতে কোন প্রসিদ্ধ বঙ্গকবির পরিচয় পাওয়া যায় না। একখণ্ড “উৎসাহে” রাজসাহীর প্রাচীন গ্রাম্য কবিতার নিদর্শন পাওয়া যায়। ঐ বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। “জয়গোবিন্দ গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ি নাটোরের নিকটবর্তী বাজুরভাগ গ্রামে ছিল। হাস্যরসের কবিতায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এদেশে তাহার রচিত অনেক কবিতা মুখে মুখে প্রচলিত আছে। তাহার যে সকল কবিতা আমি সংগ্রহ করিয়াছি তন্মধ্য হইতে হারু নাপিতের কবিতা পাঠাইলাম। অনুমান ৩০ বৎসর হইল ইহার প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। রাজসাহীর অন্তর্গত উপৈলসর গ্রামে গোস্বামী মহাশয় তাহার ভগিনীর বাড়িতে গিয়াছিলেন। হারু নাপিত তাহাকে যে রূপ ক্ষৌরি করে তাহাতে তিনি নরসুন্দরাজকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।”
“উপৈলসরের নরসুন্দর নামটি তার হারু। পাশম্পার্শের যত নাপিত সকল হতে মারু।। লোক মুখেতে নাম রটিল শব্দ গেল দূরে। নিত্য রুধির ভোজন করে হারুনাপিতের ক্ষুরে।। ক্ষুর হয়েছে কালের খাঁড়া সর্বলোকের হস্তা। নরুণ নিলে জ্ঞান যেন ভালুকের হাতে খস্তা।।”
বিস্তার হইবে বিধায় কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল। ইহাতে প্রাচীন গ্রাম্যকবিতা এবং সেকালের গ্রাম্যভাষার পরিচয় পাওয়া যাইবে।এই ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগে “রাজসাহী নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকার সম্পাদক থাকিয়া রচনা-শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। তৎপ্রণীত সভ্যতার ইতিহাস একখানি প্রশংসার্হ গ্রন্থ। “১২ “জ্ঞানাঙ্কুর” বঙ্গদর্শনের ন্যায় প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা ছিল। এই পত্রদ্বারা বঙ্গভাষার বিস্তর উপকার সংসাধিত হইয়াছে। এই জ্ঞানাঙ্কুরে নূতন নূতন বিষয় লিখিত হইত এবং অনেক অজ্ঞাত ও অশ্রুতপূর্ব তত্ত্বের আবিষ্কার ও আলোচনা হইত। কিন্তু এইরূপ উন্নতশালী পত্রিকার অকাল মৃত্যুতে রাজসাহীর নিতান্ত দুর্ভাগ্য। রামপুরবোয়ালিয়া হইতে ২/৩ বৎসর হইল “উৎসাহ” নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রিকায় নূতন বিষয় অতি সুন্দর ভাষায় লিখিত হইতেছে। “উৎসাহ” অতি প্রশংসনীয় পত্রিকা। বোয়ালিয়াতে “হিন্দু-রঞ্জিকা” নামে এক প্রাচীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। এস্থলে বলিহারের রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি রাজা এবং স্কুল বা কলেজে রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইয়া নিজ অধ্যবসায়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। “সুখভ্রম”, “সীতাচরিত”, “এখন আসি” ও “স্বভাব নীতি” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম দুইখানি পদ্যে এবং শেষ দুইখানি গদ্যে রচিত। তাহার কবিতা লিখিবার শক্তি যে একেবারে ছিল না তাহা আমরা বলিতে পারি না। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের নিকট শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি মহাশয়ের জন্মস্থান। ইনি একজন সুলেখক। ইহার প্রণীত গ্রন্থগুলিও প্রশংসনীয়।
রাজসাহীতে চিকিৎসা বিদ্যালয়েরও অভাব ছিল না। বৈদ্য জাতিরা সংস্কৃত ভাষায় এই বিদ্যাশিক্ষা করিত। বৈদ্য বেলঘরিয়া, হাজরা-নাটোর, হরিদা-খলসী ও থাঐপাড়া গ্রামের চিকিৎসা বিদ্যালয়ই প্রসিদ্ধ। আডাম সাহেব বলেন সে সময়ে ২৯৭ জন ধাত্রী ছিল। “তাহারা অনভিজ্ঞ ছিল না।”১৩
ইংরাজ রাজত্বের অব্যবহিত পূর্বে রাজসাহীতে উচ্চজাতীয়দের সংস্কৃত ও বাংলা এবং কোন কোন স্থলে পারস্যভাষা শিক্ষা ভিন্ন সাধারণ প্রজাগণের কোন প্রকার বিদ্যাশিক্ষার সুবন্দোবস্ত ছিল না। নিম্ন শ্রেণি হিন্দুদের মধ্যে পাটওয়ারী, তহশিলদার বা আমিনের কার্য জন্য কোন কোন ব্যক্তি শিক্ষিত হইত এবং এই শ্রেণির লোকেরাই প্রায় পাঠাশালার কার্য নির্বাহ করিত। উচ্চজাতীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে এরূপ শিক্ষার প্রচার একবারে যে ছিল না তাহাও বলা যায় না।
জনপ্রিয় সংবাদ

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট