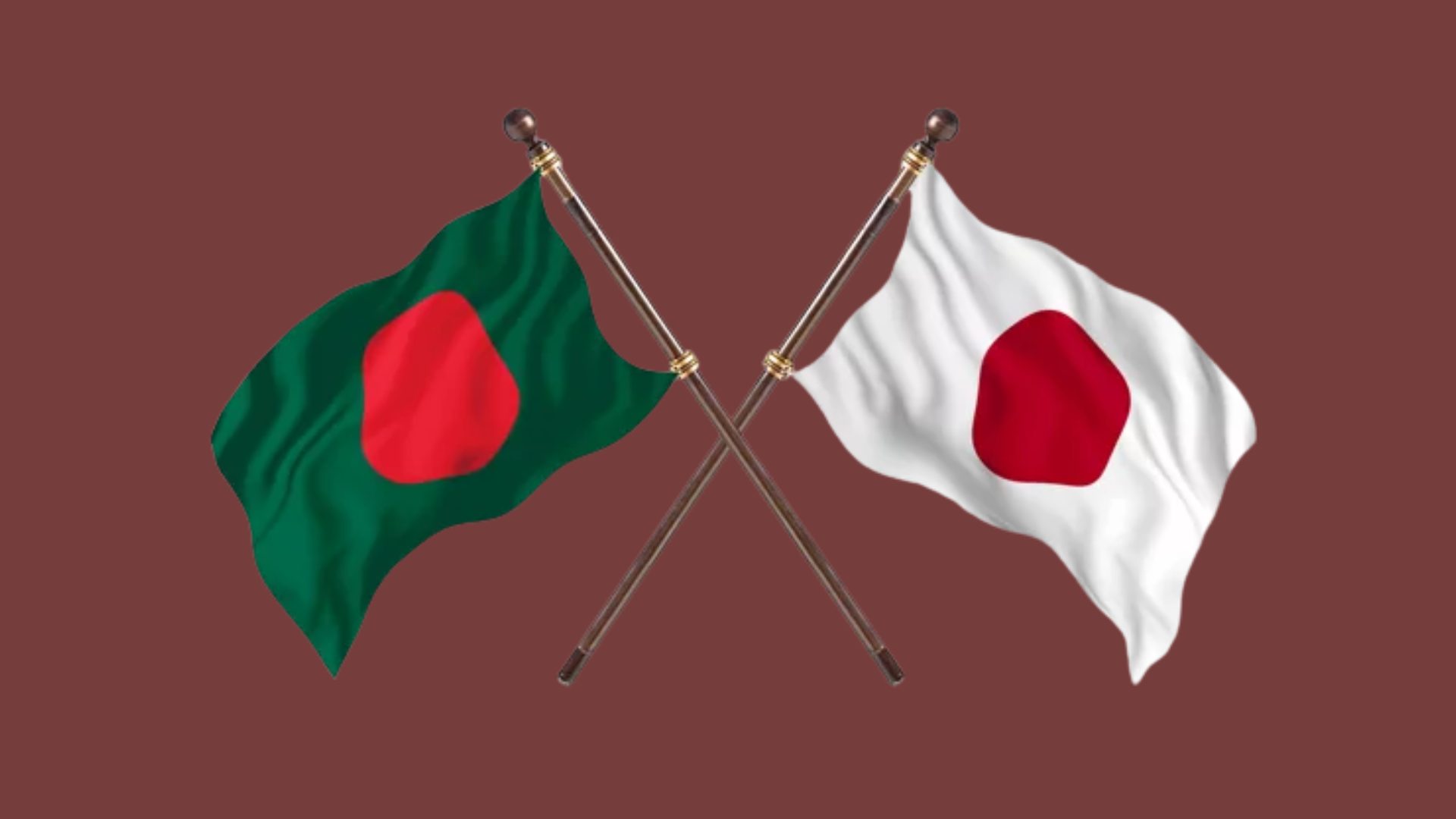রাফাহর এক বাড়ির সামনে ইসরায়েলি বিমান হামলার পর এক ফিলিস্তিনি বাবা ও তাঁর ছেলেরা—এমন ছবির অন্তরাল থেকেই এই লেখা। ‘কে বলবে আমার কাহিনি: গাজার এক ডায়েরি’ বই থেকে নেওয়া একটি অংশ—ত্রিশোর্ধ্ব এক গাজাবাসীর লেখা, যিনি ঘরছাড়া হয়ে নির্বাসনে বাস করছেন। দরজাহীন এক চাবি, রুটিহীন এক বেকারি, স্মৃতিতে পরিণত এক নগর। মিশরে আশ্রয় নেওয়া এই মানুষটি উচ্ছেদ, পরিচয় ও বেঁচে থাকার এক অনাড়ম্বর দিনলিপি তুলে ধরেছেন। হারিয়ে যাওয়া নিত্যজীবনের প্রতিধ্বনি—তাজা ফালাফেলের গন্ধ, সাগরতীরের ক্যাফের গুঞ্জন, শিশুদের খেলাধুলার শব্দ—এর ভেতর দিয়ে তিনি আমাদের সাক্ষ্য দিতে ডাকছেন গাজার ধ্বংসস্তূপের, আর সেইসব মানুষের স্থৈর্যের, যারা আজও বুকের ভেতর গল্পগুলো বহন করে চলেছেন।
আমি কোনোদিন ‘ফেরার চাবি’র ধারণাটা বুঝিনি—সেই মরচেধরা তামার চাবি। ১৯৪৮ সালে যারা ঘরছাড়া হয়েছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে সে চাবি গেছে তাঁদের সন্তানদের হাতে, সেখান থেকে নাতিনাতনিদের হাতে—এভাবেই প্রজন্মান্তরে। কয়েক বছর আগে মারা যাওয়া আমার এক বন্ধুর নানি—যিনি নাজারেথে (আরবিতে আল নাসরা) জন্মেছিলেন, বড় হয়েছেন, সংসার পেতেছিলেন—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশে শায়িত হওয়ার, শেষবার নিজের বাড়ি দেখার আকাঙ্ক্ষা পুষে রেখেছিলেন। স্বপ্নটা আর পূরণ হয়নি। শেষ বয়সে তাঁর চলাফেরা ছিল কষ্টসাধ্য, তবু নাতিনাতনিদের জন্য রান্না করার প্রাণপাত চেষ্টা করতেন—তখনও তারা ত্রিশ পেরিয়েছে। আমি যেতাম, তিনি চেয়ারে বসে থাকতেন, আর অন্তরের গভীরে খোদাই হয়ে থাকা জায়গাগুলোর গল্প শোনাতেন। তাঁর চোখে ঝিলিক দেখতাম—নিজের রান্নাঘর, পিকনিক, হারিয়ে আসা সেইসব জায়গার কথা বলতে বলতে।
আমারও সেই অনুভূতি বুঝতে সময় লেগেছে—পঁয়ত্রিশ বছরেরও বেশি। যখন আমাকেই ঘর ছাড়তে হলো—আমার বাড়ি, আমার রাস্তা, আমার শহর, আমার দেশ। গাজার দক্ষিণে অসহনীয়, যন্ত্রণাময় কয়েক মাসের উদ্বাস্তুজীবন শেষে আমি মিশরে পৌঁছালাম। শরীরটা এসেছে, কিন্তু মন-প্রাণ পড়ে রয়েছে ওখানে। ভাড়া বাসায় প্রতি রাতেই আলমারিতে হাত বাড়াই—কাপড়-চাদরের ফাঁকে লুকানো পেন্সিলবক্সটা বার করি, খুলে দেখি আমার বাড়ির চাবি। জানি—তার আর কোনো কাজ নেই; ভয়াবহ বোমায় দরজাগুলো চূর্ণ হয়ে গেছে। তবু প্রতিবার চাবিটা দেখলেই মনে করাই—আশা আছে। কোনো একদিন আমি ফিরব—আমার ফ্ল্যাটে, আমার রাস্তায়, আমার আপনজনদের কাছে, আমার গাজায়।

আমি ছোটবেলা থেকেই জানার আগ্রহী ছিলাম। যত জেনেছি, ততই কখনো না জানলেই বোধহয় ভালো হতো—এমন মনে হয়েছে। এই বছর আমাকে শিখিয়েছে—‘পরিচয়’ বলতে কেবল গুণ, বিশ্বাস, আচরণ আর চেহারার সমষ্টি বোঝায় না। আমার ফ্ল্যাটের সেই চাবিটাই এখন আমার পরিচয়ের অংশ। গাজায় প্রতিদিন যেসব পথ ধরে কাজে যেতাম, বন্ধুর কাছে যেতাম—সেসব পথও আমার সত্তার অংশ হয়ে গেছে। গন্ধগুলো, দৃশ্যগুলো, শব্দগুলো—সবই আমার অবিচ্ছেদ্য অংশ।
গাজা সিটিতে আল নাসের আর ওয়াহদা সড়কের মোড়ে গেলে পরিবারের বেকারির রুটি-তন্দুরির সুগন্ধে থমকে দাঁড়াতে হতো। ১৯৮৪ সালে, চল্লিশ বছর আগে, ছোট্ট দোকান হিসেবে শুরু—মালিক তাঁর সন্তানদের সঙ্গে রুটি বানাতেন, নিজস্ব গাড়িতে সরবরাহ করতেন। পরে বড় হলো—ক্রোসাঁ, মিষ্টি, কুকি—সব যোগ হলো।
ডায়েট চলার সময় সেই দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়া ছিল নিদারুণ যন্ত্রণা। বন্ধুরা ওই দোকানটিকেই আড্ডার জায়গা বানিয়েছিলাম—কোথাও যাওয়ার আগে খাবার দিয়ে শুরু—পৃথিবীর সেরা শুরু! এক বন্ধু তাদের ডোনাটে প্রেমে পড়ল; আমার প্রিয় ছিল সিম্পল পাউরুটি। সামান্য জাতার আর অলিভ তেল—ব্যস, পৃথিবীর সেরা স্যান্ডউইচ। পরে শুনলাম—উৎপাদন লাইন আর সোলার প্যানেল—সব বোমায় গুঁড়ো হয়ে গেছে। বেকারি বন্ধ। তাদের ফেসবুক পেজে শেষ পোস্ট ৬ অক্টোবর ২০২৩—গ্রাহকদের প্রতি শুভ শুক্রবারের প্রার্থনা।
বেকারির পাশেই আবু তলাল ফালাফেল—ছোট দোকান, বড় ইতিহাস। তাজা গরম ফালাফেলের জন্য লম্বা লাইন। আমার মতে সেরা ফালাফেল আবু তলাল—যদিও গাজাবাসীর চিরন্তন বিতর্ক—আবু তলাল, নাকি আল সউসি? আল রিমাল সড়কে ১৯৭৫ সালে শুরু হয়েছিল আল সউসি—বছরের পর বছর ‘ডাউনটাউন গাজা’ হয়ে ওঠা সেই এলাকাতেই। সেই ছোট্ট দোকানই থেকে গেছে—শত শত মানুষ সকালের নাশতা বা দিনের শেষে স্যান্ডউইচ নিতে লাইনে দাঁড়াত।

যুদ্ধের মাঝেও শুনলাম—আল সউসি দক্ষিণে ছোট্ট এক মোড়ে আবার ফালাফেল বিক্রি শুরু করেছে—ফাটা কাগজে নাম লেখা টাঙিয়ে। আমি গেলাম—যাদের হাতে টাকা আছে, যারা কিনতে পারছে—তাদের মুখে একরকম আনন্দ দেখলাম। দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকেও আমি কিনলাম না—ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতে পারে ভেবে নয়; কাঠের চুলায় ধীরে তেল গরম হচ্ছে বলে নয়; বরং জায়গাটা আর আগের জায়গা নয়—মানুষগুলোও নয়, গন্ধ নয়, অনুভবও নয়।
আমি সৌভাগ্যবান—গাজা ছাড়তে পেরেছি, মিশরে আসতে পেরেছি। আজও বুঝি না—কেন আমার জীবনটা ওখানে আটকে থাকা শিশু-মহিলা-পুরুষদের জীবনের চেয়ে মূল্যবান হলো। আমার পাওনা—ছাড়ার, বাঁচার, বেঁচে থাকার। কিন্তু আমি কি সত্যিই বেঁচে আছি? মিশর সুন্দর, কিন্তু গাজাবাসীর ভেতর ক্ষত—ত্রাস, অনিশ্চয়তা। লক্ষ মানুষের ভিড়ে—মিশরীয় বা অন্য দেশের—আমি সহজেই একজন গাজাবাসীকে চিনে ফেলি। চেহারা বা উচ্চারণে নয়—আত্মার গায়ে খোদাই হওয়া যন্ত্রণায়। যেন আমাদের শক্তিগুলো একে অন্যকে টেনে নেয়। সেই বিমর্ষ, বিহ্বল, শোকাভিভূত দৃষ্টি—ভুল হয় না কখনো। আরেকজন গাজাবাসী—সব হারিয়ে মাথা তুলে থাকার চেষ্টা, বাঁচার চেষ্টা, আদৌ পারবে কি না—জানা নেই।
আমি খুব কম বেরোই। পারি না। স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করা এক পৃথিবীতে নিজেকে ভাবতেই পারি না—কর্মস্থলে যাওয়া মানুষ, বই হাতে শিশু, চারদিকে খাবার। হে ঈশ্বর! সর্বত্র খাবার! এই পৃথিবীতে সবার জন্য যথেষ্ট খাবার আছে—তবু গাজাবাসীরা অনাহারে।
মিশরে এসে প্রথম দিকে পাগলের মতো খাবার অর্ডার করতাম—ক্ষুধা না থাকলেও খেতাম। তারপর উল্টোটা—খাওয়া বন্ধ। আমার এক বান্ধবী মা-কে নিয়ে মিশরে এসেছেন—গাজায় রয়ে গেছে পরিবার-পরিজন। বললেন, ভীষণ অপরাধবোধ হয়—ওরা যা খায়, সেও তাই খায়। গাজায় যদি একটা বীনসের ক্যান জোটে, সে-ও মিশরে বীনসের ক্যান কিনে খায়; যদি আধখানা রুটি ভাগ পড়ে, সেও আধখানা রুটি খায়। ‘ওরা না খেলে, আমি খাই কীভাবে? আমি মায়ের জন্য রান্না করি—তিনি অসুস্থ—কিন্তু হাত দিই না। ওরা খেলে, আমি খাই। না খেলে, আমিও না।’

আরেক বন্ধু আমাকে কয়েক বছর আগের এক ছবির কথা মনে করিয়ে দিল—তার কাছে আমার পাঠানো—কুনাফার তিন থালা। শীতে আমি তিন থালা কুনাফা খেয়ে দিতাম—চিনি-উল্লাসে। সে বলল—সাকাল্লাহ বা আবু আল সা’উদ—গাজার বিখ্যাত মিষ্টির দোকান—ওখানে গিয়ে মিষ্টি খাওয়ার স্বপ্ন দেখে। আমি তাকে কাজেম আইসক্রিমের লেবু স্লাশের ছবি পাঠালাম। বললাম—একদিন আবার একসঙ্গে মিষ্টি খাবো।
যে সমাবেশটা মোটেই মিস করি না—বিদায়-আসর। মিশরে এসে যারা কোনো না কোনোভাবে ভিসা জোগাড় করতে পেরেছে—তাদের বেশিরভাগই দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
‘কিছুই তো আর বাকি নেই। আমি চাইলে হয়তো থাকতাম, কিন্তু আমি চাই না আমার সন্তানরা আমাদের মতো দুঃস্বপ্ন দেখুক। আমরা চেষ্টা করেছি—তুমি জানো। তুমি তো আমার দেখা সবচেয়ে ইতিবাচক মানুষ। দেখো তোমাকে—তোমার প্রাণশক্তি হারিয়ে গেছে, বাঁচার ভালোবাসা হারিয়ে গেছে। আমি সন্তানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার ঝুঁকি নিতে পারি না। তাদের জীবন চিরদিনের জন্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে—আর না।’—দশ ও আট বছরের দুই সন্তানের মা-বন্ধুর কথাগুলো। তিনি বাচ্চাদের নিয়ে গাজা থেকে মিশর—কিন্তু স্বামী পারেননি। মিশরে থাকার সময়ই স্বামী তাঁর বাবাকে হারান—কবর দিতে পারেননি। যুদ্ধের শুরুতে তিনি অস্ট্রেলিয়ার ভিসা পান। মাসের পর মাস দোদুল্যমান থাকার পর কঠিন সিদ্ধান্ত—দুই সন্তানকে নিয়ে চলে গেলেন—পেছন ফিরে না তাকিয়েই।
প্রতিটি বিদায়ের শেষে আমি বন্ধুকে জড়িয়ে ধরতাম, কাঁদতাম, আর বারবার বলতাম—‘যুদ্ধটা ধিক, যে আমাদের ছেড়ে দিয়েছে আলাদা করে।’ শেষ বিদায়টা ছিল এক বন্ধুর ভাড়া বাসায়। সে স্পেনে চলে গেছে—স্ত্রী আর কন্যার জন্য ভালো জীবন খুঁজতে। সবাই চলে গেলে আমি থেকে গেলাম। আমরা কথা বললাম—এই পৃথিবী কত নির্মম, কেমন করে দূর থেকে আমাদের যন্ত্রণা দেখেও কিছুই করে না। ‘বাবার দুইটা স্বপ্ন ছিল—একটা বাড়ি বানাবেন, আর ছয় সন্তানকে তাদের পরিবারসহ কাছাকাছি দেখবেন—বার্ধক্যে তাঁদের হাসিখুশি মুখ দেখবেন।’—সে বলল। বাবা স্কুলে পড়াতেন, প্রাইভেট টিউশন করতেন—অমানুষিক পরিশ্রম—সন্তানদের ভালো জীবন দিতে। ‘ক্লাসের ফাঁকে বাবা কাঠের চেয়ারে হেলান দিয়ে পিঠের অসহনীয় ব্যথার ওষুধ খেতেন—আমার বুক ফেটে যেত।’ আজ তাদের বাড়ি নেই; ভাইবোনেরা সারা বিশ্বে ছিটকে। তার মনে হয়—ওরা বুদ্ধিমান ছিল—আগেভাগে বুঝেছিল গাজা গাজাবাসীদের জন্য নয়। সে থাকতে চেয়েছিল—থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিল—শেষ পর্যন্ত বুঝল—এখানেও থাকা যায় না। ‘বাড়ি নেই; বাবা-মা আর ভাইবোন কেউ একসঙ্গে নেই। বাবার স্বপ্ন শেষ।’
আমি নিশ্চিত নই—‘বেঁচে গেছি’ বলা ঠিক কি না। আমি বাঁচিনি। শরীর—কিছুটা—গাজা থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় আমি ভালো আছি, স্বাভাবিক আছি, আগের মানুষটা আছি (তারপরও, এই লেখা লেখার সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চলছেই)। আতঙ্ক-আক্রমণ এখন গাজাবাসীর নিত্যসঙ্গী। একবার খুব ব্যস্ত সড়কের ধারেই আতঙ্কে আমার পা ভেঙে পড়ল—দু’পাশ দিয়ে হাজার গাড়ি ছুটছে—আমি ফুটপাথে লুটিয়ে কেঁদেছিলাম আধঘণ্টা।

ভয়ানক হলো—ঘুমের ভেতরেও আতঙ্ক-আক্রমণ হয়। একদিন চোখ মেলা মাত্র মনে পড়ল কী হয়েছে আমাদের, কত বাধা সামনে, ভবিষ্যতে কী অপেক্ষা করছে—অসহ্য এক ঝাঁপটায়।
আমরা কি কোনোদিন গাজায় ফিরব—সব হারিয়ে?
আমরা কি সারাজীবন মিশরেই পড়ে থাকব—গাজা তো পাশেই?
আমাদের কি তৃতীয় দেশে ঠেলে দেওয়া হবে?
শূন্য থেকে শুরু করতে হবে?
ধীরে ধীরে জীবনভর সঞ্চয় ফুরিয়ে যাচ্ছে—টাকা শেষ হলে কী হবে?
জানি—আমার কিছু বন্ধু পরিবারসহ মারা গেছে—হে ঈশ্বর, তারা সত্যিই নেই। আর কখনো দেখব না। আমি নিজেকে প্রতারিত করি—ভাবি, যুদ্ধ থামলে—থামলে যদি—দেখা হবে। কিন্তু তারা তো মৃত। আমি কি কোনোদিন বাবা-মায়ের কবর দেখতে পারব? কবরগুলো কি অক্ষত আছে? বোমায় উড়ে গেছে কি?
বিছানা থেকে উঠে আতঙ্কে কাঁপছিলাম। এক বন্ধুকে ফোন করলাম—সে বলল—আবার আতঙ্ক-আক্রমণ হচ্ছে। আমরা কথা বললাম এক ঘণ্টা। সত্যি বলতে—আমিই কথা বললাম; সে থেরাপিস্টের মতো শান্ত রাখল।
সামান্য জিনিসও ট্রিগার হয়। এক বন্ধু দীর্ঘদিন পর ছুটি জুটিয়ে দুই দেশ ঘুরে আমার কাছে এলো—হাতে কয়েকটা উপহার। পৌঁছে সে চমকে দিতে চাইল—তার এক বন্ধুকে দিয়ে আমাকে নিচে ডাকাল। নেমে দেখি—দুটো গাছ—একটা বড়, একটা ছোট। আমরা জড়িয়ে ধরলাম, কথা বললাম—কিন্তু আমার মাথা গাছেই আটকে—আমি কি ওদের দেখভাল করতে পারব? এক বছরের বেশি সময় ধরে নিজের দেখভাল করাই দুঃসাধ্য—বেঁচে থাকা কঠিন। কিছুদিন তো বিছানা ছাড়াই সম্ভব নয়—খাওয়া-দাওয়া—এখন কি আরেকটা জীবন্ত জিনিসের দায়? পরদিন ঘুম থেকে উঠেই ছুটে বারান্দায় গেলাম—গাছ দুটো কেমন আছে। পানি দেওয়া—বড় বোঝা। যদি ভুলে যাই—এই ভাবনাই দুশ্চিন্তা।
বন্ধুর সঙ্গে গাড়িতে চেপে এক ঘণ্টার দূরত্বের এক রেস্তোরাঁয় যাচ্ছিলাম—সে নিশ্চিত ছিল, জায়গাটা আমার ভালো লাগবে। হঠাৎ আমি কেঁদে ফেললাম—সেও কাঁদল। মিনতি করল—কী হয়েছে বলি। ‘চেনা মানুষ মারা যায়—বারবার। প্রতিদিন নতুন স্বপ্ন নিভে যায়। আমার প্রাণ শুকিয়ে গেছে। আমরা শেষ। আর পারছি না। আমি ভীষণ ক্লান্ত, অসহায়, দুর্বল।’ আমি বললাম—আমি আর বাঁচি না; শরীর চলছে, ভেতরটা মৃত। বাইরে যেতে চাই না, নতুন মানুষ চিনতে চাই না, খাচ্ছি না, রেস্তোরাঁয়ও যেতে চাই না। সে চালককে থামাতে বলল। আমরা নেমে নাইলের পাড়ে মাটিতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বললাম।

নাইল সুন্দর—তবু আমার মনে পড়ে গাজার সাগর। মাহমুদ দারবিশ একটি কবিতায় লিখেছিলেন—
গাজা সবচেয়ে সুন্দর শহর নয়।
এর তীর আরব শহরগুলোর তীরের চেয়ে নীলতর নয়।
এর কমলালেবু ভূমধ্যসাগরের সবচেয়ে সুন্দর নয়।
গাজা সবচেয়ে ধনী শহর নয়।
তার তীর নিঃসন্দেহে সবচেয়ে নীল নয়—কিন্তু ওটাই আমার তীর। সমুদ্রতটের বালু জানে—বন্ধুদের সঙ্গে কত হাঁটাহাঁটি, কত গভীর আলাপ—হাসি-কান্না মেশানো। সাগরের ধারে একটা ক্যাফে ছিল—মাঝে মাঝে আমরা জমতাম। দুপুর আনতাম, খেলা খেলতাম, ছবি তুলতাম। একবার রমজানে ঠিক করলাম—সেই ক্যাফেতেই ইফতার। খাবার অর্ডার দিলাম—মাগরিবের এক ঘণ্টা আগে সবাই জড়ো। কিন্তু খাবার এল দেরিতে—আর অর্ডারের অর্ধেক নেই। মনে আছে—খ্রিস্টান বন্ধুরা গাড়ি নিয়ে ছুটল—খালি হাতে ফিরবে না কথা দিয়ে। আমরা উপোস—তবু যাদের খাবার এসে গেছে—কেউ মুখে দিচ্ছি না, যতক্ষণ না সবাই পায়। চল্লিশ মিনিট পর তারা ফিরে এল—বিজয়ীর হাসি—হাতে উঁচু করে দেখাল খাবার। আমরা তাদের নায়কের মতো অভিনন্দন জানালাম!
হ্যাঁ, গাজা সবচেয়ে সুন্দর শহর নয়—তবু এ শহরেই অনেকে প্রথম ভালোবাসার কথা বলেছে; শিশুদের ঘুড়ি উড়েছে; মানুষ ব্যবসা শুরু করেছে, সাফল্য দেখেছে। গাজার বুকে অসংখ্য স্তরে চাপা পড়ে আছে লক্ষ-লক্ষ গল্প—সবাই বলার যোগ্য।
আমি যে গাজাকে চিনি—সেখানে মসজিদ আর গির্জা পাশাপাশি। গাজার প্রাচীনতম সেন্ট পারফিরিয়ুস গির্জা—এক দেয়াল ভাগ করে আছে মসজিদের সঙ্গে। বড় ক্রুশটা মসজিদের মিনারের সমান্তরালে। আমি যে গাজাকে চিনি—সেখানে বহু মুসলমান বড়দিনে ওয়াইএমসিএ-তে গাছ আলোর উৎসব দেখে আনন্দ করে। আমি যে গাজাকে চিনি—সেখানে খ্রিস্টানরা পুরো রমজানজুড়ে উপবাস করেছে মুসলিম বন্ধুদের সংহতিতে—একসঙ্গে ইফতার করেছে। যুদ্ধের ভয়াল দিনে গির্জা আশ্রয় দিয়েছে—খ্রিস্টান-মুসলমান নির্বিশেষে—বাড়িছাড়া মানুষদের। দুর্ভাগ্য—সেন্ট পারফিরিয়ুস গির্জা বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; গাজার প্রাচীনতম আল উমারি মসজিদ—পঞ্চম শতকে নির্মিত—সেটিও ধ্বংস হয়েছে।
বন্ধুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সে বলল—তার বাড়ির ক্রিসমাস ট্রিটাকে বড্ড মিস করে। আমিও বললাম—আমার ট্রির কথা। আমরা দু’জনেই মুসলমান—তবু ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি—ট্রি ছিল ঘরের প্রাণ। দু’দিন পর গুগল ফটোস আমাকে পুরোনো একটা সেলফি দেখাল—ট্রির পাশে দাঁড়িয়ে। আমি পাঠালাম ওকে।
গুগল ফটোস একরকম ইতিহাসের খাতা। আমার এক বন্ধু আগে বিরক্ত হতো—আমি এত ছবি তুলি বলে। এখন, আমাদের বন্ধুমহল ছিটকে পড়েছে—কেউ গাজায় আটক, কেউ মিশরে, বাকিরা নানা দেশে—সে কৃতজ্ঞ—‘তুমিই তো এই ছবিগুলো পাঠিয়েছিলে—এগুলো আমাদের ভালো দিনের স্মারক। কখনো ভাবিনি—একসঙ্গে বসার সুযোগই আর হবে না।’
একজন পরিচিত—যিনি গাজাতেই আছেন—বললেন, আজ যদি সড়ক দিয়ে হাঁটো—বা যা সড়ক পড়ে আছে—দেখবে নাম-পরিচয়হীন লাশ—পুরুষ, নারী, শিশু—বোমা থেকে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে যারা মারা গেছে। তিনি ভিডিও পাঠিয়েছেন—যেসব জায়গায় আমি জীবনের বেশিরভাগটা কাটিয়েছি—চেনার উপায় নেই—তিনি না বললে বোঝাই যেত না। তিনি বলেন—গাজা আর আগের মতো হবে না। আমি মনে মনে বলি—আমরাও না।

যুদ্ধ আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে কদর্য মুখটা দেখিয়েছে—তবু দেখিয়েছে সত্যিকার মমতা। অন্ধকারতম সময়ে কেউ কেউ মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে, খাইয়েছে, কাঁধ দিয়েছে। তাদের মধ্যে আহমদের পরিবার—দীর্ঘদিন আমার আর আমার বোনকে আশ্রয় দিয়েছে। হাতে টান—সম্পদ সামান্য—তবু বুকে জড়িয়ে নিয়েছে। তারা আমাদের আগে আমাদের মুখে তুলে দিয়েছে খাবার। আহমদের মা—এই ডায়েরিতে ‘দাদি’ নামে আছেন—নিঃস্বার্থতা, দয়া, উদারতার জীবন্ত উদাহরণ। এই পরিবার আমাদের জন্য স্রষ্টার পাঠানো উপহার।
যুদ্ধের শুরুতে তারা ছিল অচেনা—ভাবছিলাম, দু-একদিন থাকব। আর যেদিন বিদায় নিলাম—তারা আমাদের পরিবারের মানুষ—চিরদিনের জন্য হৃদয়ে জায়গা পেল। দক্ষিণ থেকে খবর পাই—খাবার নেই, টাকা নেই, কিছু নেই। তবু যখন আহমদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলি—ওরা হাসিমুখে বলে—ভালো আছি, সব আছে। উল্টো আমাদের জন্য চিন্তা করে। যুদ্ধের নখ যত গভীরে গেঁথে যায়—ততই তারা আরও বেশি ভালোবাসা বিলায়। তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করি—এই দুঃস্বপ্নটা শেষ হোক।
গাজার যুদ্ধ তেতো ছাড়া কিছু নয়—তবু যারা সঙ্গে ছিল—তাদের জন্যই কিছুটা সহনীয় হয়েছে। সবার আগে আমার বোন—মিশরে পৌঁছে আমি তাকে জড়িয়ে বললাম—তুমি না থাকলে আমি টিকে উঠতাম না। আমরা দল বেঁধে ছিলাম—একসঙ্গে ভেবেছি, একসঙ্গে লড়েছি—অকল্পনীয় দৈনন্দিন সংগ্রামের মুখোমুখি হয়েছি। কাছাকাছি এলাকায় ছিটকে পড়া বন্ধুদের নিয়েও তাই—একসঙ্গে জোগাড় করেছি বাঁচার সামগ্রী; কথা, হাসি, তাস—যন্ত্রণার ভেতর একটু নিশ্বাস। আর আমার থেরাপিস্ট—তিনি ফিলিস্তিনি নন—প্রায় প্রতিদিন ইমেল করেছেন—আশাবাক্য পাঠিয়েছেন—বলেছেন, তুমি বাঁচবে। আমি বেশিরভাগ সময় এক লাইনে জবাব দিয়েছি—‘এখনও বেঁচে আছি।’ আর আমার অ-গাজাবাসী বন্ধুরা—দিন-রাত খোঁজ নিয়েছে। বহুবার মৃত্যু খুব কাছে ছিল—তখন আমি তাদের বলেছি—আমি যদি না থাকি—আমার পক্ষ থেকে একটা সৎকর্ম করে দিও। সবাই একটাই কথা বলেছে—‘তুমি বাঁচবে।’
এখন নিজেকে জিজ্ঞেস করি—আমি কেন এখনও লিখছি? লিখছি, কারণ এই ডায়েরি—আমার ফ্ল্যাটের চাবি আর গাজার বন্ধুদের সঙ্গে তোলা ছবির মতোই—একটা প্রতীক আর একরকম নিশ্চিতকরণ। ভালোবাসার প্রতীক, টিকে থাকার প্রতীক, বাঁচার আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আমরা কোথায় যে পৌঁছাই না কেন—যত দুঃখ-যন্ত্রণা যাই পেরিয়ে আসি—গাজায় ফেরার স্বপ্ন কখনো থামবে না। গাজা আমাদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী থাকবে।
অনুগ্রহ করে গাজাবাসীদের জন্য ইতিবাচক চিন্তা আর প্রার্থনায় রাখবেন।
জিওগ্রাফিক্যাল কন্ট্রিবিউটর

 Sarakhon Report
Sarakhon Report