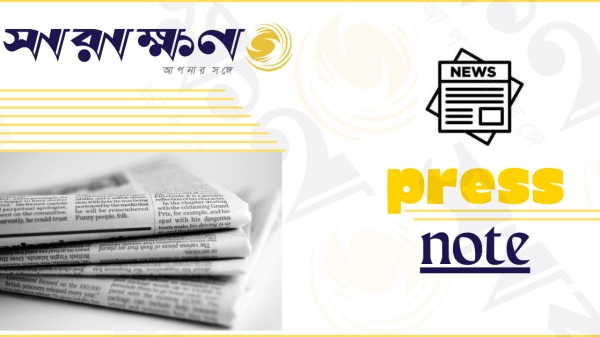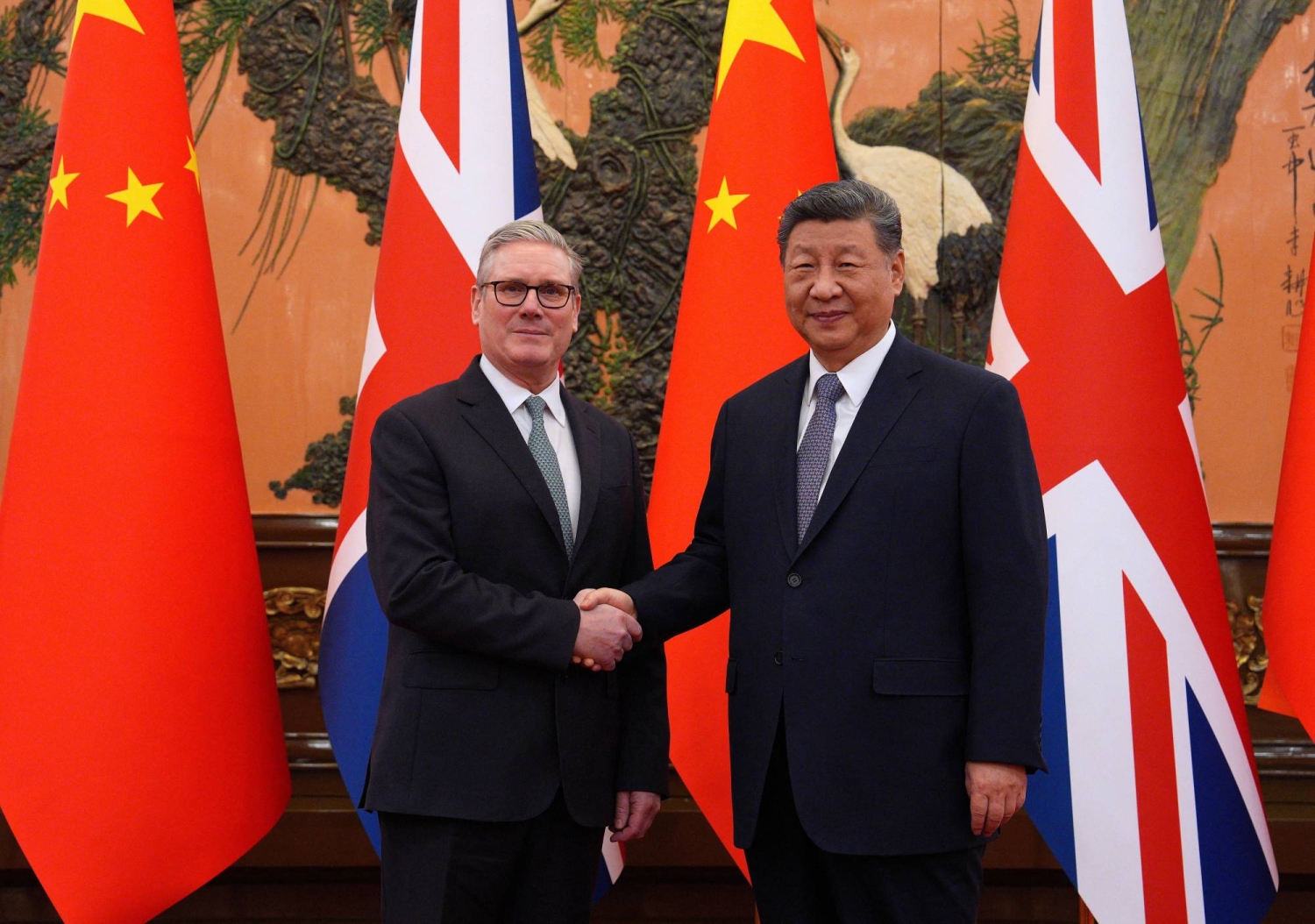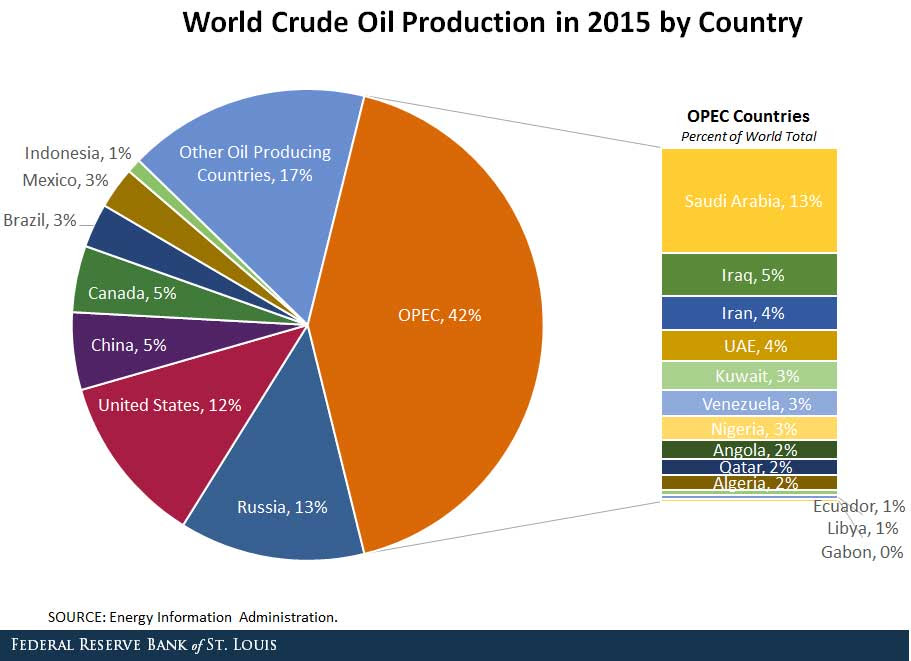আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের অর্থনীতি গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।
অন্তর্বর্তীকালীন ইউনূস সরকার স্থিতিশীলতা আনতে ব্যর্থ হওয়ায় বিনিয়োগে আস্থা ভেঙে পড়েছে,
ব্যাংক খাতে ঋণপ্রবাহে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ মন্দা।
দেশি–বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ‘অপেক্ষা ও পর্যবেক্ষণ’ নীতিতে চলে গেছেন—
ফলে বেসরকারি খাতের প্রবৃদ্ধি ২২ বছরের মধ্যে নেমে এসেছে সর্বনিম্ন পর্যায়ে।
অর্থনীতিতে হিমশীতল প্রবাহ
বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য বলছে—২০২৫ সালের আগস্ট শেষে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে ৬ দশমিক ৩৫ শতাংশে, যা ২০০৩ সালের পর সর্বনিম্ন।
আগস্টের আগের তিন মাসেও এই হার ক্রমান্বয়ে নিচে নেমেছে: জুনে ৬.৪৫%, জুলাইয়ে ৬.৫২%, আগস্টে ৬.৩৫%।
এটি শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়—এটি পুরো অর্থনীতির ভিত কাঁপিয়ে দেওয়া এক সতর্ক সংকেত।
রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিনিয়োগে আস্থাহীনতা, ব্যাংকের ঋণসংকট ও সরকারের দুর্বল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা—সব মিলিয়ে বেসরকারি খাতে অর্থপ্রবাহ কার্যত থমকে গেছে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট: পরিবর্তনের পর স্থবিরতা
গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকেই দেশের অর্থনীতিতে অচলাবস্থা বিরাজ করছে।
অন্তর্বর্তীকালীন ইউনূস সরকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা—দু’দিকেই ব্যর্থ হয়েছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।
রাজধানী থেকে জেলা শহর পর্যন্ত “জুলাই আন্দোলনের ছাত্রনেতা” ও “সরকারপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের” একাংশ এখন চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব ও ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়েছে।
ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করছেন, “আমরা শুধু চাপের মধ্যে নই, ভুয়া মামলাতেও জড়ানো হচ্ছে।”
ফলে নতুন বিনিয়োগের আগ্রহ বিলুপ্ত, বিদ্যমান কারখানাও টিকে থাকতে হিমশিম খাচ্ছে।
ব্যাংক খাতে সঙ্কট: ঋণপ্রবাহে ঠান্ডা হাওয়া
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ব্যাংক নতুন ঋণ দেওয়া বন্ধ রেখেছে।
অন্য ব্যাংকগুলোও ঋণ না দিয়ে নিরাপদ সরকারি বিল ও বন্ডে অর্থ বিনিয়োগ করছে।
এর পেছনে তিনটি বড় কারণ রয়েছে—
প্রয়োজনীয় পুঁজির ঘাটতি: ব্যাংকগুলোতে তারল্য সংকট তৈরি হয়েছে।
অসাধু ঋণ (NPL): বড় অঙ্কের খেলাপি ঋণ বেড়েছে, পুনরুদ্ধারে ব্যর্থতা বাড়ছে।
সুদহার বৃদ্ধি: নীতি সুদহার বৃদ্ধির ফলে ঋণ নেওয়ার খরচ বেড়ে গেছে ১৪–১৫% পর্যন্ত।
এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক মূলত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগী, ফলে বাজারে টাকার প্রবাহ আরও কমে গেছে।

ব্যবসায়ীদের আস্থা ভেঙে পড়েছে
ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি তাসকীন আহমেদ বলেন,
“বিনিয়োগের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন আস্থা। বর্তমানে অনিশ্চয়তার মধ্যে কেউ নতুন প্রকল্পে যেতে চাইছেন না। নির্বাচনী সময় পর্যন্ত এই অনিশ্চয়তা কাটবে না।”
রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর ব্যবসায়ীরা দ্বিধায় পড়েছেন—কার প্রভাব কাজ করছে, কার কারণে বাজার স্থবির—তা কেউ জানেন না।
অনেক প্রভাবশালী উদ্যোক্তা, যাঁরা আগের সরকারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের ব্যবসা বন্ধ বা সীমিত হয়ে গেছে।
ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর দাবি, “নিরপেক্ষ অর্থনৈতিক প্রশাসন না ফিরলে বিনিয়োগে আস্থা ফিরবে না।”
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে কিছু উদ্যোগ নিলেও তা কার্যকর হয়নি।
রাজস্ব ঘাটতি বেড়েছে, বাজেট বাস্তবায়নে দুর্বলতা রয়ে গেছে, আর সরকারি ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ প্রায় নেই।
অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন,
“ইউনূস সরকারের আর্থিক দল কৌশলগতভাবে দুর্বল; রাজস্ব বাড়াতে না পেরে ব্যাংক খাত থেকে সরকারি ঋণ বাড়িয়েছে।”
এতে ব্যাংকগুলোর হাতে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় বেসরকারি খাতে ঋণ সরবরাহ আরও কমে গেছে।
সরকারি বন্ড ও ট্রেজারি বিল কেনার নিরাপদ পথই এখন ব্যাংকগুলোর মূল লক্ষ্য।
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ‘অপেক্ষা ও পর্যবেক্ষণ’
AIIB, ADB ও বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণ বলছে—বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের সংকোচন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও নীতিনির্ধারণে অস্পষ্টতার কারণে তীব্র হয়েছে।
বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এখন “Wait and See Policy” অনুসরণ করছে।
এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরকারের মৌলবাদপন্থী শক্তির প্রতি নরম অবস্থান, যা আন্তর্জাতিক আস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন,
“যদি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা দ্রুত না ফেরে, তাহলে ২০২৬ সালে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) আরও ৩০–৪০% পর্যন্ত কমতে পারে।”

মুদ্রানীতি ও সুদহার: বিনিয়োগে বাধা
মূল্যস্ফীতি ৯%-এর ওপরে থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের লাগাম টেনেছে।
এই নীতিতে নতুন উদ্যোক্তারা ঋণ নিতে ভয় পাচ্ছেন।
ব্যাংকের গড় সুদহার এখন ১৪–১৫%, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।
উচ্চ সুদে ঋণ নেওয়ার ফলে মুনাফা কমে যাচ্ছে, অনেক কারখানা উৎপাদন বন্ধ করে দিচ্ছে।
এখন প্রায় ১,৩০০ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ঋণ পুনঃতফসিলের আবেদন করেছে—এর মধ্যে বিএনপি ও অন্যান্য রাজনৈতিকভাবে সম্পর্কিত ব্যবসায়ীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।
কর্মসংস্থান ও বাজারে প্রতিক্রিয়া
ঋণপ্রবাহ কমে যাওয়ায় শিল্পখাতে কর্মসংস্থান প্রায় স্থবির।
রপ্তানি খাতের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা নতুন আদেশ নিচ্ছেন না, ভোগ্যপণ্যের বাজারেও ক্রেতাদের খরচ কমে গেছে।
ব্যবসায়ীরা বলছেন, “গ্রাহক ও বাজার—দু’দিকেই টান পড়েছে।”
বেকারত্ব বাড়ছে, খুচরা বাজারে ক্রয়ক্ষমতা কমছে—এমন পরিস্থিতিতে সামষ্টিক অর্থনীতি আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে।
আন্তর্জাতিক গবেষণা: আর্থিক স্থিতিশীলতা দুর্বল হচ্ছে
সম্প্রতি একাডেমিক গবেষণা (Arxiv, জুলাই ২০২৫) বলছে—বাংলাদেশের ব্যাংক ও মাইক্রোফাইন্যান্স সিস্টেমের “aggregate financial stability” সূচক ২০২৩–২৫ সময়কালে ক্রমাগত নিম্নমুখী।
Basel III নিয়ম মেনে চলার খরচ বেড়ে যাওয়ায় ব্যাংকগুলোর জন্য ঋণ দেওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ছে।
অন্যদিকে, দুর্নীতিপ্রবণ ঋণব্যবস্থা ও দায়মুক্ত নীতির কারণে ব্যাংক সেক্টর সংস্কারে বাস্তব অগ্রগতি হয়নি।

ভবিষ্যৎ ঝুঁকি
- ঋণপ্রবাহ সংকোচন শিল্প ও বাণিজ্য খাতকে স্থবির করবে।
•বেকারত্ব বৃদ্ধি সামষ্টিক প্রবৃদ্ধিকে ধীর করবে।
• আন্তর্জাতিক আস্থাহীনতা নতুন বিনিয়োগে প্রতিবন্ধক হবে।
• রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দীর্ঘস্থায়ী হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর চাপ বাড়বে।
বাংলাদেশের অর্থনীতি একসময় দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুতবর্ধনশীল ছিল।
আজ সেই অর্থনীতি রাজনৈতিক অস্থিরতা, নীতিগত বিভ্রান্তি ও ব্যাংকিং দুর্বলতায় জর্জরিত।
বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহ থেমে যাওয়ায় বিনিয়োগের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হতে বসেছে।
যদি শাসন, স্বচ্ছতা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দ্রুত পরিবর্তন না আসে,
তবে ২০২৬ সাল নাগাদ বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৪%-এর নিচে নেমে যেতে পারে—
যা ইতিমধ্যে ২০২৪ সালের আগস্টে ৬.৭% থেকে নেমে এসেছে ৩.৯%-এ—
এমন আশঙ্কাই করছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো।
#বেসরকারিখাত #ঋণপ্রবৃদ্ধি #ইউনূসসরকার #অর্থনীতি #রাজনৈতিকঅস্থিরতা #ব্যবসা #বাংলাদেশব্যাংক #InvestRiskReport #সারাক্ষণরিপোর্ট

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট