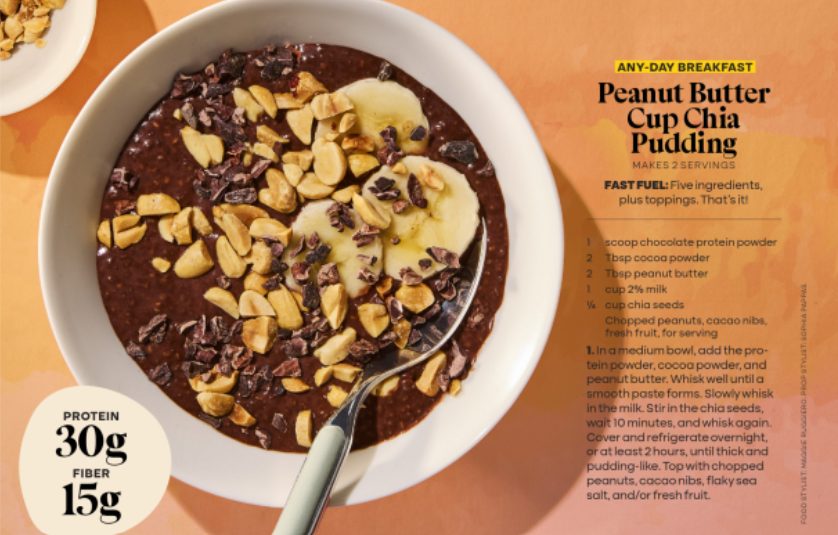জি–৭ বলছে, তারা রাশিয়ার তেল রপ্তানির ওপর “সর্বোচ্চ চাপ” সৃষ্টি করতে চায়। ধনী শিল্পোন্নত দেশগুলো যদি এতে সত্যিই অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে, তারা মস্কোর বিদেশে অপরিশোধিত তেল বিক্রি থেকে অর্জিত আয় বছরে সর্বোচ্চ ৮০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে। এতে ক্রেমলিনের দুর্বল অর্থনীতি বড় ধাক্কা খাবে এবং এমনকি প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থামাতে বাধ্যও করতে পারে।
বুধবার ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভা উপলক্ষে জি–৭–এর অর্থমন্ত্রীদের বৈঠক হওয়ার কথা। পুতিনের যুদ্ধ-তহবিল খালি করতে তাদের হাতে ইতিমধ্যে কয়েকটি প্রস্তাব রয়েছে—যেমন রাশিয়া থেকে তেল কেনা দেশগুলোর ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ, যেমনটি যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে লক্ষ্য করে করেছে।
তবে জি–৭ একটি মূল কৌশলগত দিক এড়িয়ে যাচ্ছে। অন্য উৎপাদকরা ঘাটতি পোষাতে না পারলে রাশিয়ার তেল রপ্তানি চেপে ধরা উল্টো ফল দেবে। সরবরাহ কমলে বৈশ্বিক অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়বে, পশ্চিমা অর্থনীতিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দাম বাড়ায় রাশিয়ার আয়ও খুব একটা কমবে না, কারণ বেশি দাম কম উৎপাদনের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারে।

এর চেয়ে ভালো পরিকল্পনা হলো—অন্য উৎপাদকদের, বিশেষ করে উপসাগরীয় দেশগুলোকে, বেশি তেল তুলতে রাজি করানো। একই সঙ্গে জি–৭–কে মস্কোর বড় ক্রেতাদের—বিশেষত ভারতকে—রাশিয়া থেকে কম এবং সৌদি আরবের মতো সরবরাহকারীদের কাছ থেকে বেশি তেল কিনতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
এই দ্বিমুখী পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে হলে ‘লাঠির’ পাশাপাশি ‘গাজর’ও দেখাতে হবে—সব পক্ষের জন্য লাভের সুযোগ তৈরি করতে হবে। একটি বড় পদক্ষেপ হতে পারে রাশিয়ান তেলের ওপর জি–৭ আরোপিত মূল্যসীমা (প্রাইস ক্যাপ) আরও কমিয়ে দেওয়া। এমনভাবে চুক্তি সাজানো গেলে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) অতিরিক্ত কয়েক বিলিয়ন ডলার মুনাফা এবং ভারতের জন্য বড় অঙ্কের সাশ্রয় তৈরি হবে। কীভাবে তা সম্ভব, নিচে ব্যাখ্যা করা হলো।
উপসাগরীয় চুক্তি
প্রথমেই রিয়াদ ও আবুধাবিকে দেখাতে হবে—অতিরিক্ত তেল তুললে তাদের আয় আরও বাড়তে পারে। উভয় দেশেরই অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা আছে: আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার হিসাবে সৌদি আরব প্রতিদিন আরও ২.৪৩ মিলিয়ন ব্যারেল (এমবিডি) এবং ইউএই ০.৮৫ এমবিডি পর্যন্ত বাড়াতে পারে।
উপসাগরীয় রাজতন্ত্রগুলো উৎপাদন বাড়াতে চায়। তাদের উৎপাদন খরচ কম এবং মজুত তেল এত বেশি যে বিশ্ব পরিচ্ছন্ন জ্বালানির দিকে সরে গেলেও বহু দশক টিকে থাকবে। একই সময়ে রিয়াদের ব্যয়বহুল অ–তেল প্রকল্পগুলো বাজেটকে ঘাটতিতে ঠেলে দিয়েছে। ফলে চাহিদা যতদিন আছে, বাজার-শেয়ার দখল করাই তাদের জন্য যৌক্তিক। এজন্যই সৌদি আরব অনেক দিন ধরে ওপেক+ কার্টেলকে উৎপাদন-কোটা বাড়াতে চাপ দিচ্ছে।

সমস্যা হলো, সরবরাহ বড় আকারে বাড়ালে তেলের দামে চাপ পড়তে পারে। তখন বাড়তি ভলিউম থেকেও আয় কমে যেতে পারে। তাই জি–৭–কে তাদের বোঝাতে হবে—দাম ভেঙে পড়বে না। এর উপায় হলো: সৌদি আরব ও ইউএই যতটা অতিরিক্ত তেল বাজারে দেবে, ততটা পরিমাণ রাশিয়ান তেল বিশ্ববাজার থেকে সরিয়ে দেওয়া।
ধরা যাক, রিয়াদ ও আবুধাবি তাদের অতিরিক্ত সক্ষমতার ৭০% ছাড়ল—সৌদির ১.৭ এমবিডি এবং ইউএই–এর ০.৬ এমবিডি, মোট ২.৩ এমবিডি। ব্রেন্ট তেলের বর্তমান ব্যারেলপ্রতি ৬৫ ডলারের দরে সৌদি আরব বছরে প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার এবং আবুধাবি প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত রাজস্ব পাবে। নিম্ন উৎপাদন-খরচের কারণে এর সিংহভাগই হবে মুনাফা।
ভারত–তুরস্ক চুক্তি
তবে ‘উপসাগরীয় চুক্তি’ তখনই কাজ করবে, যখন এর সঙ্গে ‘ভারত–তুরস্ক চুক্তি’ মিলবে। চীন রাশিয়ান তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা; বেইজিং–মস্কোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিবেচনায় সেখানে হস্তক্ষেপের চেষ্টা জি–৭–এর জন্য বাস্তবসম্মত নয়।
বরং নয়াদিল্লি ও আঙ্কারার দিকে নজর দেওয়া বেশি সম্ভাবনাময়। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ভারত রাশিয়া থেকে দৈনিক প্রায় ১.৯ এমবিডি অপরিশোধিত তেল ও তেলজাত পণ্য আমদানি করেছে, আর তুরস্ক করেছে ০.৯ এমবিডি—ইউক্রেনের কেএসই ইনস্টিটিউটের হিসাবে। এই দেশগুলোকে দেখাতে হবে—মস্কো থেকে কম এবং উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে বেশি কিনলে তাদের আর্থিক লাভ হবে; আর সেটি নিশ্চিত করার উপায় হলো রাশিয়ান তেলে আরও বড় ডিসকাউন্ট আদায় করা।
জি–৭–এর বর্তমান মূল্যসীমা ব্যারেলপ্রতি ৬০ ডলার। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্য নিজেদের সীমা ৪৭.৬০ ডলারে নামালেও তেমন প্রভাব পড়েনি, কারণ রাশিয়া ‘শ্যাডো ফ্লিট’ ব্যবহার করে সীমা এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এ ধরনের ট্যাঙ্কারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপে অনেক বেশি সক্ষম। তারা যদি সীমা আরও কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তা কার্যকরভাবে চাপ তৈরি করবে। জি–৭ রাশিয়ান তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৪০ ডলার পর্যন্ত নামিয়েও আনতে পারে।
ভারত বর্তমানে শিপিং খরচসহ রাশিয়ান তেলে সর্বোচ্চ ব্যারেলপ্রতি প্রায় ২.৫০ ডলার পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাচ্ছে—বার্ষিক সাশ্রয় দাঁড়ায় প্রায় ১.৭ বিলিয়ন ডলার। এখন কল্পনা করা যাক, ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি ৭৫% কমাল, কিন্তু কম মূল্যসীমার কারণে ব্যারেলপ্রতি ২০ ডলারের ডিসকাউন্ট পেল—তাহলে তার বার্ষিক সাশ্রয় দ্বিগুণ হয়ে প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন ডলারে যেতে পারে। তুরস্কও একইভাবে উপকৃত হবে।
এতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য-টানাপোড়েনও প্রশমিত হবে, যা বছরে প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানিতে প্রভাব ফেলছে। নয়াদিল্লি রাশিয়া থেকে কেনা কমালে ওয়াশিংটন সম্ভবত ৫০% শাস্তিমূলক শুল্ক কমাতে রাজি হবে।
একই সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়া থেকে যে অবশিষ্ট ০.২ এমবিডি তেল এখনো আমদানি করে, সেটিও থামাতে হবে। এটিকে ভারতের ও তুরস্কের ৭৫% কাটছাঁটের সঙ্গে যোগ করলে রাশিয়ার রপ্তানি ২.৩ এমবিডি কমে যাবে—যা উপসাগরীয় দেশগুলোর বাড়তি সরবরাহের সাথে ঠিক সমান।

এমন জটিল এক সমঝোতা বাস্তবায়ন সহজ নয়। উপসাগরীয় দেশগুলো, ভারত ও তুরস্ককে রাশিয়ার সঙ্গে কঠিন কথোপকথনের মুখোমুখি হতে হবে। নয়াদিল্লিকেও অনেকটা ওয়াশিংটনের চাওয়া মেনে চলতে হবে। তবে বড় আর্থিক প্রণোদনা পেয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া আর হুমকির কাছে নতি স্বীকার করার মধ্যে বড় পার্থক্য আছে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এটিকে নিজের কূটনৈতিক বিজয় হিসেবেও তুলে ধরতে পারেন।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এই চুক্তি রাশিয়ার জন্য খুবই ক্ষতিকর হবে। আগস্টে দেশটি গড়ে দৈনিক ৭.৩ এমবিডি তেল রপ্তানি করেছে, ব্যারেলপ্রতি গড় দাম ছিল প্রায় ৫৬ ডলার। যদি সেটি কমে দৈনিক ৫ এমবিডিতে নেমে আসে এবং দাম নেমে যায় ৪০ ডলারে, তবে তাদের রপ্তানি আয় প্রায় অর্ধেকে নেমে আসবে। বছরে ক্ষতির অঙ্ক দাঁড়াতে পারে প্রায় ৭৬ বিলিয়ন ডলারে।
এ ধরনের একটি চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছেও আকর্ষণীয় হতে পারে। তিনি বহু–বিলিয়ন ডলারের ‘ডিল’ পছন্দ করেন। রাশিয়ার তেল–আয়ে চাপ সৃষ্টি করা এমন একটি বড়সড় ফলাফলই এনে দেবে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট