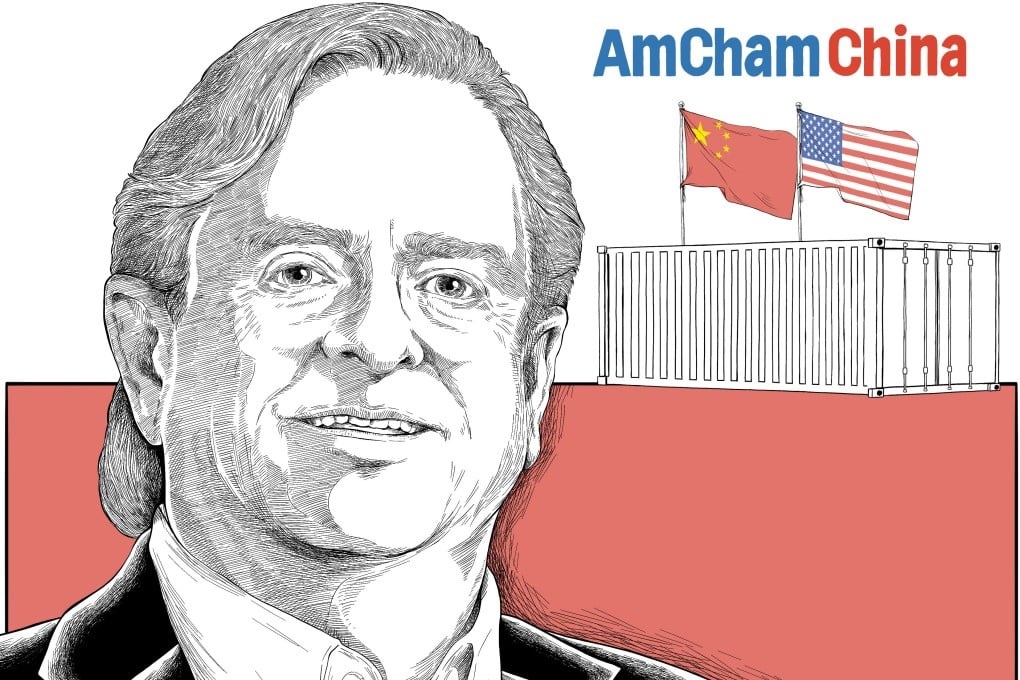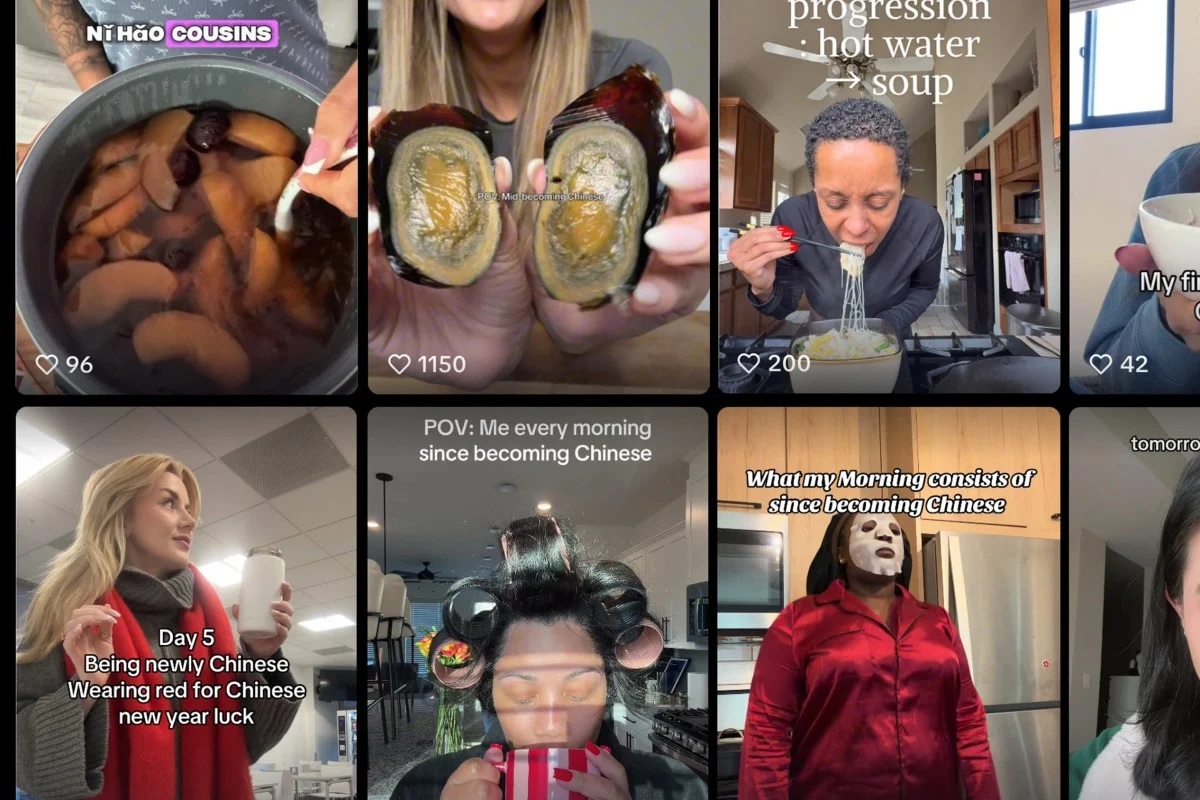নতুন রূপে পুরোনো আতঙ্ক
মেরি শেলির কল্পনায় জন্ম নেওয়া ‘ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন’-এর দানব আজও জীবন্ত। কিশোরী লেখিকার সৃষ্টি সেই চরিত্রের জলভরা চোখ, হলদে ত্বক ও কালো ঠোঁট যেমন মানবদেহের সীমা ছুঁয়েছিল; তেমনি নৈতিকতা ও বিজ্ঞানের সংমিশ্রণেও প্রশ্ন তুলেছিল। গিলারমো দেল তোরোর নতুন চলচ্চিত্র সেই পুরোনো মিথকেই ফিরিয়ে এনেছে সমসাময়িক রূপে—যেখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সংঘাত আবারও নতুনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
১৯ শতকের আবহে নতুন ভিজ্যুয়াল বিস্ময়
চলচ্চিত্রের পটভূমি উনিশ শতকের মাঝামাঝি, যখন ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন (অস্কার আইজাক) নিজের ভয়ানক ইতিহাস বর্ণনা করছেন এক ড্যানিশ সমুদ্র ক্যাপ্টেনকে। গথিক টাওয়ারে তার সৃষ্টি প্রক্রিয়া ভয়ানকভাবে বাস্তব—চোখ, হাড়ের করাত ও ছেঁড়া চামড়ার দৃশ্যে ক্যামেরা থেমে থাকে কিছুটা বিকৃত মুগ্ধতায়।

দেল তোরোর এই ফ্রেম যেন সিনেমার ইতিহাসের নানা টুকরো থেকে তৈরি—‘ব্যাক টু দ্য ফিউচার’-এর বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ, ‘স্নো হোয়াইট’-এর মতো ইঁদুরের সঙ্গী দানব, আবার র্যাম্বোসুলভ ক্রোধে নেকড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। ১৯১০ সালের থমাস এডিসনের প্রথম নির্বাক সংস্করণের প্রতিফলনও এখানে দেখা যায়—একই আয়নায় ডাক্তার ও দানবের উপস্থিতিতে।
মৃত্যু–অর্থনীতির অন্তরালে
দেল তোরো কেবল পুনর্জীবনের গল্পই বলেননি, বরং প্রশ্ন তুলেছেন—এই পরীক্ষাগুলোর অর্থ ও দেহাংশ কোথা থেকে আসে? ছবিতে দেখা যায়, এক অস্ত্র ব্যবসায়ী অর্থ জোগায় এই ভয়ানক গবেষণার জন্য; মৃতদেহ আসে যুদ্ধক্ষেত্র ও ফাঁসির মঞ্চ থেকে। ফলে সিনেমাটি কেবল গথিক কল্পনা নয়, আধুনিক যুগের ‘মৃত্যু–অর্থনীতির’ প্রতীক হয়ে ওঠে।
মানবিক মুখ ও ইনস্টাগ্রামযুগের দানব
এই দানব শেলির মূল উপন্যাসের মতো ভয়ানক নয়। সেখানে সে ভাই, প্রিয়তমা ও বন্ধুকে হত্যা করেছিল; এখানে রক্ত ঝরে কেবল গৌণ চরিত্রদের শরীরে। দেল তোরোর দানব (জ্যাকব এলোরদি অভিনীত) বরং আকর্ষণীয় ও মানবিক—পেশিবহুল, কোমল মুখাবয়বের এক ইনস্টাগ্রামযুগের সৃষ্টি।

সবচেয়ে বড় থিম হয়ে ওঠে ‘পিতৃত্ব’। মূল গ্রন্থে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের পিতা স্নেহশীল হলেও এখানে তিনি ঠাণ্ডা, দূরবর্তী ও কঠোর। স্রষ্টা নিজেও প্রথমে মুগ্ধ হলেও পরে ক্লান্তি ও বিষণ্নতায় হয়ে ওঠেন নির্মম—এক ‘ডেডবিট ড্যাড’, যিনি নিজের সন্তানের সঙ্গেও সহমর্মিতা হারান। দর্শকের মনে প্রশ্ন জাগে—এই দানবের প্রয়োজন একজন থেরাপিস্টের, নাকি এক মানবিক পিতা?
মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই ও প্রযুক্তির প্রতিচ্ছবি
মূল বইয়ে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের লক্ষ্য ছিল জীবনের রহস্য উদ্ঘাটন—‘অমরত্বের এলিক্সির’ আবিষ্কার। দেল তোরোর সংস্করণে সেই লক্ষ্য এক ধাপ এগিয়ে যায়—এখানে তিনি চান মৃত্যু জয় করতে। ফলে তার চরিত্র যেন আজকের যুগের বিলিয়নিয়ার ও বিজ্ঞানীদের মতো, যারা প্রযুক্তির মাধ্যমে অমরত্ব খুঁজছেন।
এইভাবে চলচ্চিত্রটি হয়ে ওঠে সময়ের আয়না—যেখানে মানবদেহের পরীক্ষাগার এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ল্যাবে রূপান্তরিত। জীবনের সৃষ্টি আর কোষ বা টিস্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সিলিকন চিপ ও অ্যালগরিদমেও প্রবাহিত।
ভবিষ্যতের ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন: মাংস নয়, মেশিন
দেল তোরোর সংস্করণ প্রমাণ করে, ‘ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন’ কাহিনি এখনো শেষ হয়নি। আগামী বছরই মুক্তি পাচ্ছে ‘দ্য ব্রাইড!’, যেখানে ম্যাগি গিলেনহাল গল্পটিকে নিয়ে যাচ্ছেন ১৯৩০-এর দশকের শিকাগোতে।

কিন্তু ভবিষ্যতের এক সংস্করণে হয়তো দানব আর মানুষ দুজনেই হবে কৃত্রিম—রক্তমাংস নয়, চিপ ও কোডে গঠিত AI-সত্তা। তখন হয়তো মেরি শেলির শতাব্দীপ্রাচীন প্রশ্ন আবারও ফিরে আসবে—মানবতা ঠিক কোথায় শেষ হয়, আর সৃষ্টির দায় কোথা থেকে শুরু?
# ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, #গিলারমো_দেল_#তোরো, #সিনেমা_#রিভিউ, নৈতিকতা_ও_প্রযুক্তি, #কৃত্রিম_বুদ্ধিমত্তা, #মেরি_শেলি, #সারাক্ষণ_রিপোর্ট

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট