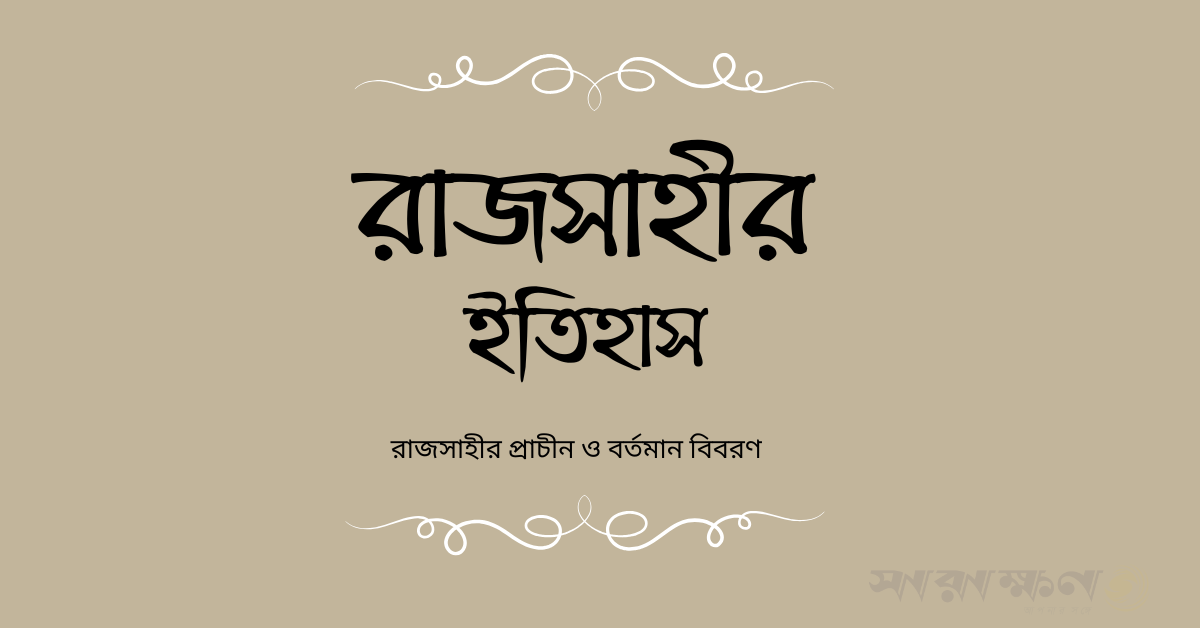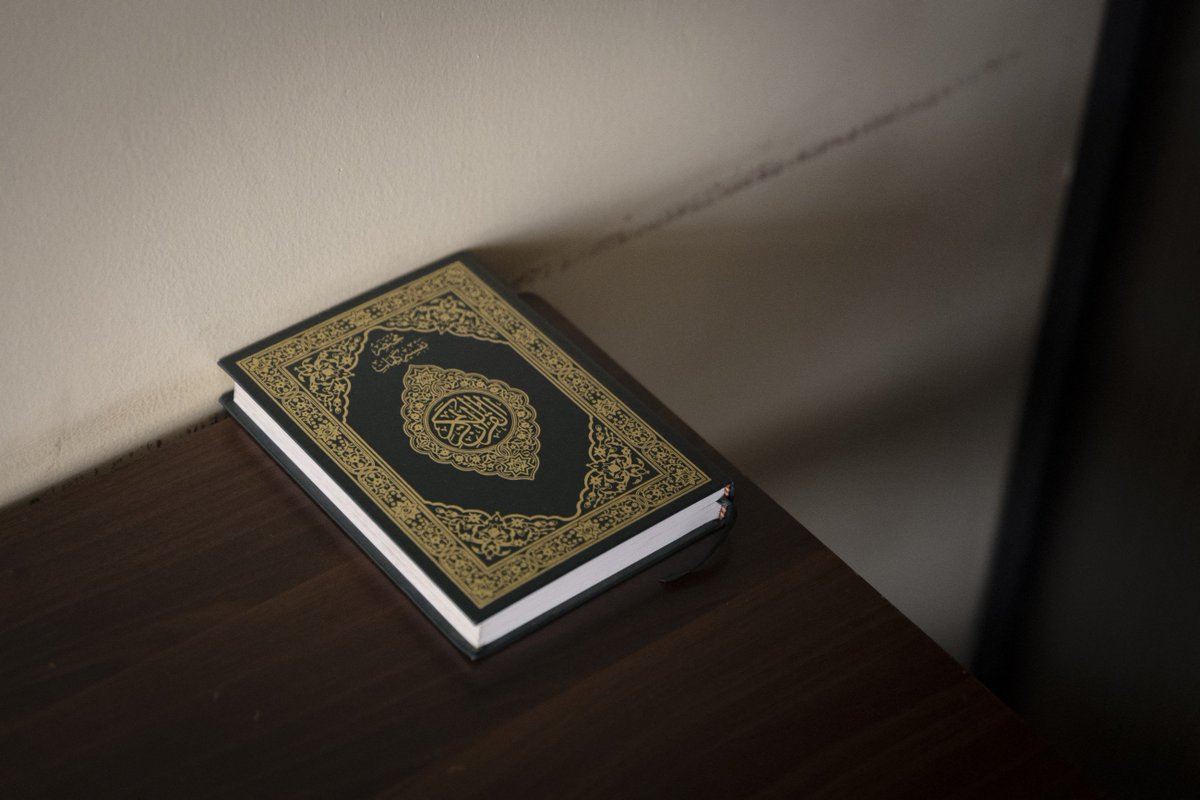রঘুনন্দনের সময় জমিদারি এসময় জমিদারি তিন শ্রেণিতে বিভক্ত যথা: (১) জঙ্গলবুড়ি,
(২) ইস্তীকালী, (৩) আহকামী।
(১) জঙ্গলবুড়ি পতিত অনাবাদী ভূমি। জমিদার পরিশ্রম দ্বারা জমি হাসিল করিয়া নিষ্কর বা সামান্য করে বন্দোবস্ত করিয়া লয়।
(২) ইস্তীকালী-ফশলী উত্তর জমি। নিযুক্ত জমিদার রাজস্ব বাকি ফেলে বা অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু বা উত্তরাধিকারী বিহীন বা রাজ বিদ্রোহী হইলে অন্য জমিদার সম্রাট নিকট ঐ ভূসম্পত্তি সনন্দ করিয়া লয়।
(৩) আহকামী-জমিদারের বিনা দোষে এবং নবাবের কর্মচারীদের চাতুরি ও কৌশলে নবাবের বা সম্রাটের আদেশে যে জমিদারি হইতে জমিদার রাজ্যচুত হয় তাহা নবাবের কর্মচারী নিজ নামে বা আত্মীয়ের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লয়।
রঘুনন্দন যে সকল জমিদারি তাহার ভ্রাতা বা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লয় তাহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত জমিদারি।
রামজীবনের সামাজিক পদ গৌরব-সামান্য অবস্থা হইতে রাজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া এবং বৃহৎ রাজ্যের অধিপতি হইয়াও রামজীবন সামাজিক পদ গৌরবকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। বৈষয়িক পদ গৌরব অপেক্ষা সামাজিক পদ গৌরবও কম নহে। সুতরাং রামজীবন সামাজিক পদ গৌরব বৃদ্ধির জন্য বিশেষ যত্নবান হইলেন।
কুল্লুকভট্টের সময় কাশ্যপ গোত্রীয় ভাদুড়ি বংশে তর্কশাস্ত্রে বিশারদ বৃহস্পতি আচার্যের ঔরসে উদয়নাচার্য নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরেন্দ্র ভূমিতে একটি নূতন সমাজ সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার দুই স্ত্রী। তাহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে ছয় পুত্র এবং মধু মৈত্রের দুই পুত্রের সহিত তিনি মিলিত হইয়া এক নূতন দল গঠিত করিলেন। কিন্তু বিচারে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত হইয়া এক নূতন দল “কাপ”১২ নামে প্রসিদ্ধ হইল। কাপের সঙ্গে কন্যা আদান প্রদানে কুলীনের কুলচ্যুত হইতে লাগিল। এমন কি কাপের সঙ্গে আহারে, শয়নে ও উপবেশনেও কুলীনের কুল নষ্ট হইতে লাগিল। সুতরাং কাপের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সমাজের এই অবস্থা দেখিয়া তাহিরপুরের বিখ্যাত শ্রোত্রীয় রাজা কংসনারায়ণ মধ্যস্থ হইলেন এবং কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রচলিত করিয়া দিলেন। এই নূতন নিয়মে শ্রোত্রীয় বরে কন্যা দান করিলে কাপ পোত্রীয় হইবে এবং সোস্ত্রীয় হওয়ার পর কুলীন পরে কন্যা দান করিলে সেই ব্যক্তি সিদ্ধ শ্রোত্রীয় হইবে। ইহাও নিয়ম হইল যে কুশবারি সংযুক্ত না হইলে কাপের স্পর্শে পুর্ণীদের কুলপাত হইবে না। এ নিয়মে কুলীন ও কাপ উত্তয়েরই সুবিধা হইল। ইহা পূর্বে উল্লেন করা গিয়াছে যে নাটোর বংশের আদি পুরুষ কামদের জীবর মৈত্রের বংশধর এবং সেই আবির নৈর নিয়মানুসারে জীবর মৈত্রের বংশধর কাপ হইয়াও পরে শ্রোত্রীয় বরে কন্যা দানে শ্রোত্রীয় ঘন। এইক্ষণ রামজীবন ও রঘুনন্দন সিদ্ধ শ্রোত্রীয় হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজা কংসনারায়ণ কুলীনের আশ্রয়দাতা ছিলেন। সুতরাং বারেন্দ্র সমাজে পদগৌরব তাহার সামনে কেহই ছিল না। তাহার বংশধরগণেরও সেই পদগৌরব ছিল। রামজীবন ও রঘুনন্দনের সময় রাজা কংসনারায়ণের প্রপৌত্র রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ তাহিরপুরে রাজত্ব করিতেন। সেই লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার সহিত রামজীবনের পুত্র কালিকাপ্রসাদ বা “কালুকোত্তরের” বিবাহ জনা রঘুনন্দন ও রামজীবন প্রস্তাব করিলেন। ভবিষ্যতে “কালুকোঙর” রাজসাহীর মহারাজা হইবেন, তখন কন্যাদানে লক্ষ্মীনারায়ণ সম্মতি প্রদান করিলেন। অতি সমারোহে এই বিবাহ সম্পন্ন হইল। এই বিবাহে নাটোর বংশের সামাজিক পদগৌরব বৃদ্ধি হইল।
রামজীবন ও দয়ারাম নাটোরে, রঘুনন্দন মুরশিদাবাদে রামজীবন নাটোরের রাজবাটিতে বাস করিতেন এবং রাজকার্য সম্পন্ন জন্য দিঘাপতিয়া রাজবংশের আদিপুরুষ অসাধারণ বুদ্ধিমান দয়ারাম রায় তাহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন যে ‘রঘুনন্দন নাটোর রাজ্য সৃষ্টি করেন এবং দয়ারাম রাজ্য দৃঢ়ীভূত করেন। রঘুনন্দন নাটোর রাজ্যের ক্লাইন এবং দয়ারাম হেস্টিংস ছিলেন। “১৩ আমরা বলি রামজীবন ধনরক্ষক বা কুবের। যদিচ রঘুনন্দন মুরশিদাবাদে থাকিয়া মুরশিদকুলি খাঁর প্রসাদাৎ নাটোর রাজ্যের ভীত্তি স্থাপন করেন, তথাপি রামজীবন ও দয়ারামের বুদ্ধি কৌশলের সাহায্যে তাহা রক্ষা করিয়া উন্নতি সাধন করেন। নাটোর রাজ্যের মূল রঘুনন্দন তাহার আর ভুল নাই। রামজীবনের বাস-স্থান নাটোর এবং রঘুনন্দনের বাসস্থান গঙ্গাতীরে বড়নগর বা বীরনগর ছিল।
রামজীবন ও রঘুনন্দন-রামজীবন ও রঘুনন্দন দুই ভ্রাতা। রামজীবন জ্যেষ্ঠ ও রঘুনন্দন মধ্যম। রামজীবন ও রঘুনন্দনের ভ্রাতৃপ্রেম অকৃত্রিম। রঘুনন্দনের জ্যেষ্ঠ-প্রাতার প্রতি ভক্তি আদর্শনীয়। রামজীবনের রঘুনন্দনের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম প্রশংসনীয়। রঘুনন্দন আইনজ্ঞ এবং রাজস্ব সচিব ছিলেন। রামজীবন জমিদারি কার্যে দক্ষ ছিলেন। রঘুনন্দনের বৃদ্ধি কৌশল ও প্রতিভা অসাধারণ এবং রামজীবনের সাহস ও কার্যকুশলতা অসীম। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যথার্থই বলিয়াছিলেন যে “রামজীবনের বীরত্ব, সাহস, ধর্মশীলতা এবং রঘুনন্দনের বৃদ্ধি, কৌশল, প্রতিভা এবং ভ্রাতৃপ্রেম একত্রিত হওয়াই নাটোর রাজবংশের বিস্তীর্ণ রাজ্যলাভের মূল কারণ।” দয়ারামের পরামর্শে রামজীবন বিস্তীর্ণ রাজ্যের তিনটি প্রধান রাজধানী, (১) নাটোর, (২) বড়নগর, (৩) সেরপুর স্থাপন করিয়া জমিদারি কার্য-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। রামজীবনের সংস্কৃত শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ ছিল। ১৪
রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম-ইহারা তিন ভ্রাতা এবং তিনজনই একান্নভুক্ত। বাংলা ১১৩১ সালে (১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে) রঘুনন্দনের মৃত্যু হয়। সেই সময় রামজীবনের একমাত্র পুর কালিকাপ্রসাদ (কালুকোঙর) পরলোক গমন করেন। ইহার কিছুদিন পরে রঘুনন্দনের একমাত্র শিশু পুত্রেরও মৃত্যু হয়। রঘুনন্দনের উত্তরাধিকারী রহিল না এবং রামজীবনের একমাত্র পূত্র কালিকাপ্রসাদেরও মৃত্যু হইল। কেবল বিষ্ণুরামের দেবীপ্রসাদ নামে এক পুত্র রহিল। কেহ দত্তক পুত্র রাখিবার জন্য রামজীবনকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন এবং কেহ বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদকেই রাজ্যদান করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। অবশেষে দত্তক পুত্র রাখিলেন।
এই দত্তক পুত্র নাটোর রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা রামকান্ত নামে প্রসিদ্ধ। বর্তমান রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পরগণা চৌগ্রাম ও বর্তমান রপুর জেলার অন্তর্গত পরগণা ইস্লমাবাদ পুরস্কার স্বরূপ রামজীবন রসিককে দিলেন। রসিকের পুত্র কৃষ্ণকান্ত চৌগ্রামে রাজবাটি নির্মাণ কারেন। ইহারই প্রপৌত্র রাজা রমণীকান্ত রায় বিএ, শান্ত, ধীর, মিতব্যয়ী ও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত। এই দত্তক পুত্র রাখার পর হইতে দেবীপ্রসাদ রাজ্য প্রার্থনা করেন। দত্তক পুত্রকে রাজ্যের ৪০ আনা অংশ দিতে রামজীবন স্বীকার করেন। কিন্তু দেবীপ্রসাদ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় সমগ্র রাজ্য দত্তক পুত্র রামকান্তের প্রতি অর্পিত হইল।
স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামজীবন পরলোক গমন করেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় রাজা রামজীবনের মৃত্যুর তারিখ ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে নির্দেশ করেন। সে সময় রামকান্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক। রাজা রামজীবনের মৃত্যু সময়, তাহার রাজ্যের ভার তাহার প্রিয় বন্ধু ও উপদেষ্টা দয়ারামের হস্তে সমর্পিত হইল। রামকান্তের অপ্রাপ্ত বয়ক্রমকালে অর্থাৎ ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দয়ারাম এরূপ সুকৌশলে রাজ্য রক্ষা করেন যে দেবীপ্রসাদ নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন দিয়াও কোন ফল পাইল না। রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারাম রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দিঘাপতিয়ার রাজবাটি নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন বটে; কিন্তু তিনি রামকান্তের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত রহিলেন।
দয়ারাম রায়- নাটোর রাজ্যের সহিত দয়ারামের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে তাহাকে নাটোর রাজবংশের ইতিহাস হইতে পৃথক করা নিতান্ত কঠিন। নাটোর রাজবংশের ইতিহাস লিখিতে গেলে দয়ারামের প্রতিভা ও বুদ্ধি কৌশলের বিষয় না বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। নাটোর রাজবংশের ইতিহাসে যেখানে উল্লেখ না করিলে নয় সেই স্থানেই কেবল তাহার নাম উল্লেখ করা যাইবে। কিন্তু দিঘাপতিয়া রাজবংশের ইতিবৃত্ত লিখিবার সময় দয়ারামের ইতিহাস বিস্তৃত রূপে লিখিত হইবে।
রাজা রামকান্তের রাজ্যভার গ্রহণ- ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে হইতে রামকান্ত স্বাধীনভাবে রাজ্য
শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন যে “পিতার রাজ্য অধিকার সময় রামকান্তের বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর ছিল। তিনি একটি ধার্মিক মনুষ্য ছিলেন। দেবতাদের পূজা ও ধর্মকার্যে তিনি দিনপাত করিতেন। কিন্তু সাংসারিক কার্য নির্বাহ করিতে তিনি জানিতেন না। “১৫
রামকান্তের সময় রাজ্যলাভ- রাজা রামজীবনের মৃত্যুর পর দেবীপ্রসাদ রাজ্য প্রাপ্তি জন্য
নবাব দরবারে বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। সে সময় সুজা খাঁ মুরশিদাবাদে নবাব। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে নবাব জমিদারি স্বরূপপুর এবং পাতিলাদহ রামকান্তকে অর্পণ করেন।১৬ ইহাও দয়ারামের কৌশল। এখন দেবীপ্রসাদ বুঝিতে পারিলেন যে দয়ারামের কৌশলে নবাব সুজাখাঁর নিকট কোন ফল হইবে না। সেই সময় পাতিলাদহ পরগণায় ৭০০০ টাকার বেশি আদায় হইত না, কিন্তু ঐ জমিদারি মহামান্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের হস্তে আসিলে, উহার আদায় বার্ষিক তিন লক্ষ টাকারও বেশি হয়।

 Sarakhon Report
Sarakhon Report