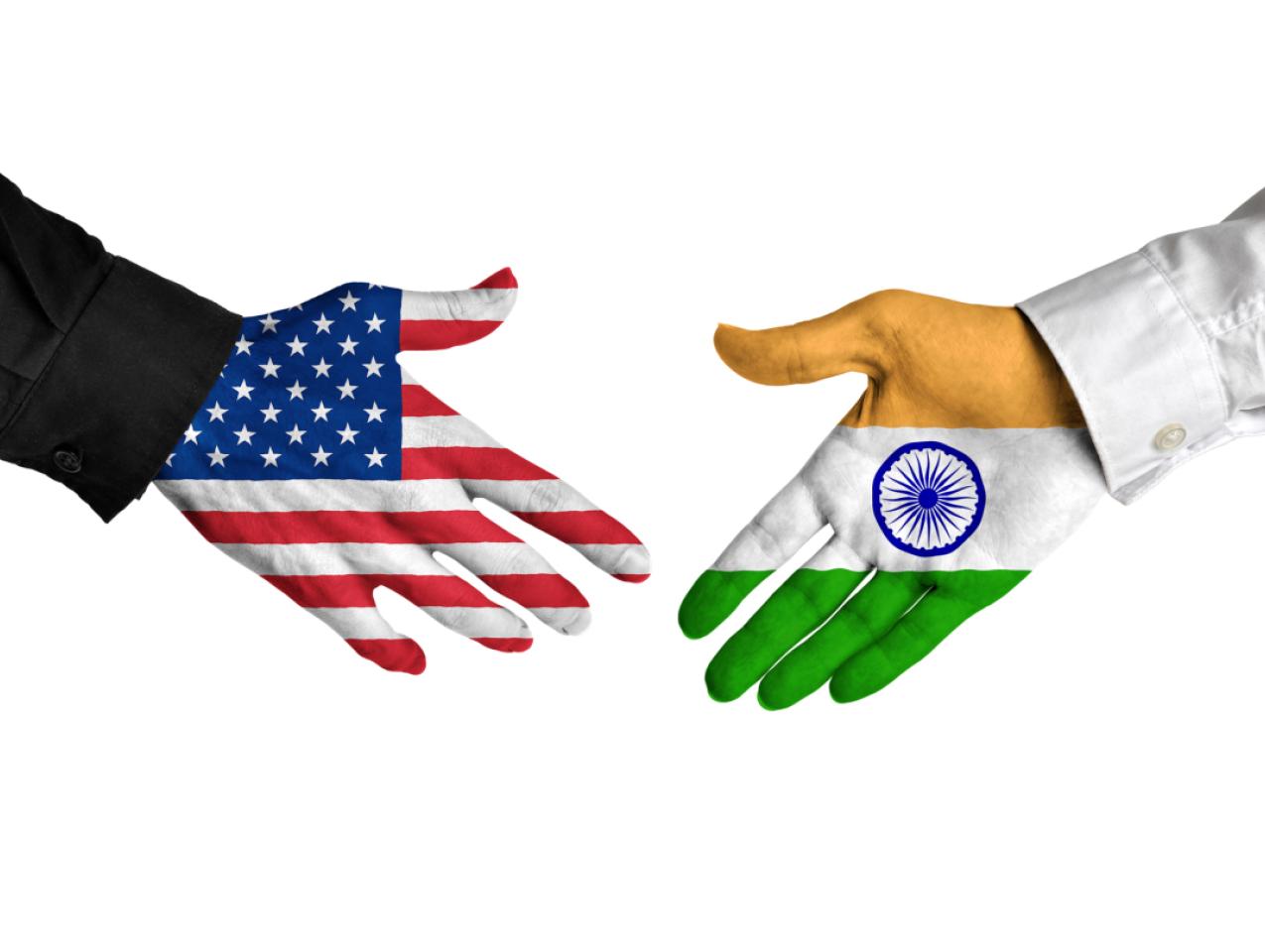ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের জন্য বছরটি শুরু হয়েছিল আশাব্যঞ্জকভাবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওয়াশিংটন সফর দুই দেশের অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করার অভিপ্রায়কে দৃঢ় করেছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদেই দুই নেতার ব্যক্তিগত সম্পর্ক গভীর হয়েছিল, যা ফলাফলনির্ভর কূটনৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনা জাগিয়েছিল। ২০২৫ সালের শুরুতে ওয়াশিংটনে দ্বিদলীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে ভারতকে ইন্দো-প্যাসিফিক ভারসাম্যের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে দেখা হচ্ছিল।
কিন্তু বছরের শেষ নাগাদ সেই আশাবাদ অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। বহু প্রতীক্ষিত বাণিজ্য চুক্তি এখনও সম্পন্ন হয়নি, সর্বোচ্চ পর্যায়ের সংলাপ ধীর হয়েছে, আর দুই দেশের বক্তব্য আরও কঠোর হয়েছে। এখনও সম্পর্ক সংকটে পড়েনি, কিন্তু পথনির্দেশ অনিশ্চিত। এ বছর দেখিয়েছে, ব্যক্তিনির্ভর কূটনীতিকে টেকসই রাখতে হলে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রয়োজন।
বছরের শুরুতে ট্রাম্প প্রশাসনের বাণিজ্য ঘাটতির ওপর নতুন গুরুত্ব আরোপের প্রেক্ষিতে ভারত বাস্তববাদী কৌশল নেয়। ফেব্রুয়ারিতে মোদি-ট্রাম্প বৈঠকে “মিশন ৫০০” নামে একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়, যার লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে দুই দেশের বাণিজ্যকে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা। কিন্তু এপ্রিলেই যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় রপ্তানিতে ২৬ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করলে অগ্রগতি থেমে যায়। আলোচনায় ভারতীয় সংরক্ষণবাদ এবং ওয়াশিংটনের বাজার-প্রবেশ অগ্রাধিকার—এই কাঠামোগত দূরত্ব চুক্তি সম্পন্ন হতে দেয়নি।
এর মাঝে ভূ-রাজনীতি এসে বাণিজ্য উত্তেজনা আরও বাড়ায়। মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত যুদ্ধবিরতিতে গড়ালে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতাকে কৃতিত্ব দেয়, কিন্তু ভারত তা অস্বীকার করে। এরপর ট্রাম্প দাবি করেন, ওয়াশিংটনের কঠোর অবস্থান ও সম্ভাব্য বাণিজ্য শাস্তির হুমকি যুদ্ধ থামাতে ভূমিকা রেখেছে।
ভারতের জন্য এটি বিদেশি হস্তক্ষেপের সংবেদনশীলতা আবার সামনে এনে দেয় এবং ভিন্নমতের বর্ণনা কীভাবে আস্থার সংকট তৈরি করে, তা স্পষ্ট করে। যদিও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও আশ্বস্ত করেছেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে সমন্বয় ভারতের স্বার্থের ক্ষতি করবে না, তবু ইসলামাবাদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ঝোঁক দিল্লিতে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
আগস্টে যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় রপ্তানিতে আরও ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে বলে যে সস্তায় রাশিয়ান তেল কেনা মস্কোর যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পরোক্ষভাবে সহায়তা করছে। ভারত এটিকে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে দেখলেও প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেয়নি এবং তেল আমদানি কমায়নি।
ঘরোয়া রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে ভারতের জন্য প্রকাশ্যে পিছু হটা কঠিন ছিল। কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের নীতি বজায় রাখায় নীতিগত পরিবর্তনের সুযোগও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে ট্রাম্প প্রশাসন এইচ–ওয়ান–বি (H-1B) ভিসার ফি বৃদ্ধি ঘোষণা করলে, যা মূলত ভারতীয় পেশাজীবীদের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করে—দুই দেশের আস্থার সংকট আরও গভীর হয়।
এ বছর কোয়াডের (যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া) পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের দুই দফা বৈঠক হলেও, বছরের শেষে নয়াদিল্লিতে শীর্ষ সম্মেলন হবে কি না তা অনিশ্চিত। ইউক্রেন ও গাজার যুদ্ধ শেষ করার ওপর ট্রাম্প প্রশাসনের মনোযোগ বাড়ায় ইন্দো-প্যাসিফিক অগ্রাধিকার তালিকার নিচে নেমে গেছে। ভারতের কাছে এটি আরেকটি স্মারক—আমেরিকার মনোযোগ গভীর হলেও সীমাহীন নয়।
অন্যদিকে ওয়াশিংটন যখন অর্থনৈতিক অবস্থান কঠোর করছে, তখন ভারত কৌশলগত ভারসাম্যের জায়গা ধরে রাখার চেষ্টা করছে। আগস্টে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর দুজনেই মস্কো যান। জয়শঙ্কর ভারত-রাশিয়া সম্পর্ককে “সবচেয়ে স্থিতিশীল প্রধান অংশীদারিত্ব” হিসেবে বর্ণনা করেন। পরবর্তীতে মোদির সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন সম্মেলনে অংশগ্রহণ, যা ছিল সাত বছরে তাঁর প্রথম চীন সফর—এটি কোনো সমীকরণ বদলের ইঙ্গিত নয়, বরং ভারসাম্য রক্ষার প্রচেষ্টা।
ভারত আঞ্চলিক উত্তেজনা কমাতে, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগত অনিশ্চয়তার মাঝে কৌশলগত নমনীয়তা বজায় রাখতে চাইছে। ওয়াশিংটন এ প্রবণতাকে উদ্বেগের চোখে দেখলেও ভারতের কাছে এটি বাস্তববাদী কূটনীতি। চীন ভারতের বৃহত্তম প্রতিবেশী এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার। সীমান্ত ও বাণিজ্য সম্পর্ক স্থিতিশীল করা—যদিও সতর্কতার সঙ্গে—ভারতের জন্য অর্থবোধক।
শরতে বাণিজ্য আলোচনা পুনরায় শুরু হলেও নেতৃত্ব পর্যায়ে সংলাপ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। মালয়েশিয়ায় আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনকে সম্ভাব্য সুযোগ মনে হলেও মোদি ভার্চুয়ালি অংশ নেওয়ায় আশা কমে যায়। জয়শঙ্কর ও রুবিওর বৈঠকেও অগ্রগতি সীমিত ছিল।
রাশিয়ার বড় তেল কোম্পানির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নিষেধাজ্ঞা ভারতের তেল আমদানির কাঠামোকে জটিল করে তুলেছে। ভারতের রাশিয়া থেকে অধিকাংশ সরবরাহ নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আসে। তাই আমদানি ধরে রাখতে হলে মধ্যস্থতাকারী বা বিকল্প ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হতে পারে—যা ওয়াশিংটনের সঙ্গে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করতে পারে।
আরও গঠনমূলক পথ হতে পারে দুই দেশের মধ্যে জ্বালানি ও নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক সংলাপ তৈরি করা। যুক্তরাষ্ট্র-ভারত জ্বালানি বাণিজ্য বাড়লে এ খাতের উত্তেজনা একটি যৌথ কৌশলগত স্বার্থে রূপ নিতে পারে।
চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও অংশীদারিত্বের ভিত্তি টিকে আছে। প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বেড়েছে এবং কোয়াড এখনো জোগান শৃঙ্খল, অবকাঠামো এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজে কার্যকর সহযোগিতার প্ল্যাটফর্ম। রুবিওর মতো নেতারা, যাঁরা কোয়াডের এজেন্ডায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন, দেখাচ্ছেন যে ওয়াশিংটনে এখনও প্রতিষ্ঠানগত সক্ষমতা আছে যা এই সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে পারে।
ওয়াশিংটন বা নয়াদিল্লি—কেউই কৌশলগত আত্মতুষ্টির সুযোগ নিতে পারে না। চীনের প্রভাব বাড়ছে, রাশিয়া নতুন বাজার খুঁজছে, আর ইন্দো-প্যাসিফিকে ভারসাম্য নির্ভর করছে প্রধান গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সমন্বয়ের ওপর। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত একসঙ্গে কাজ করলে এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা বাড়ে; বিচ্ছিন্ন হলে অনিশ্চয়তা বাড়ে।
ভারতের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগত উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বোঝা এবং সে অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নেওয়া জরুরি। ট্রাম্প প্রশাসনের পদ্ধতি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ধৈর্যের বদলে তাৎক্ষণিক সুবিধা, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বার্তা এবং বাণিজ্যিক প্রতিদানে বেশি গুরুত্ব দেয়।
এ প্রেক্ষাপটে দৃশ্যমান মূল্য ও নমনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্য ও জ্বালানি এই দুই ক্ষেত্রেই তা পরীক্ষা করা সম্ভব। নির্দিষ্ট কিছু নন-ট্যারিফ বাধা শিথিল করে এবং জ্বালানি আমদানি বৈচিত্র্য আনার মাধ্যমে ভারত নমনীয়তার বার্তা দিতে পারে এবং নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে তার ভাবমূর্তি জোরদার করতে পারে—বিশেষ করে যখন যুক্তরাষ্ট্র-চীন উত্তেজনা তুলনামূলকভাবে কমছে।
এই বছরের অস্থিরতা ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের গত দশকের অগ্রগতিকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এখন মূল কাজ হলো দ্বিপাক্ষিক মতবিরোধ ব্যবস্থাপনা থেকে কৌশল ব্যবস্থাপনায় এগিয়ে যাওয়া—এবং সেইসঙ্গে এ সম্পর্ককে এশিয়ার পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে পুনরায় স্থাপন করা।

 ফারওয়া আমার
ফারওয়া আমার