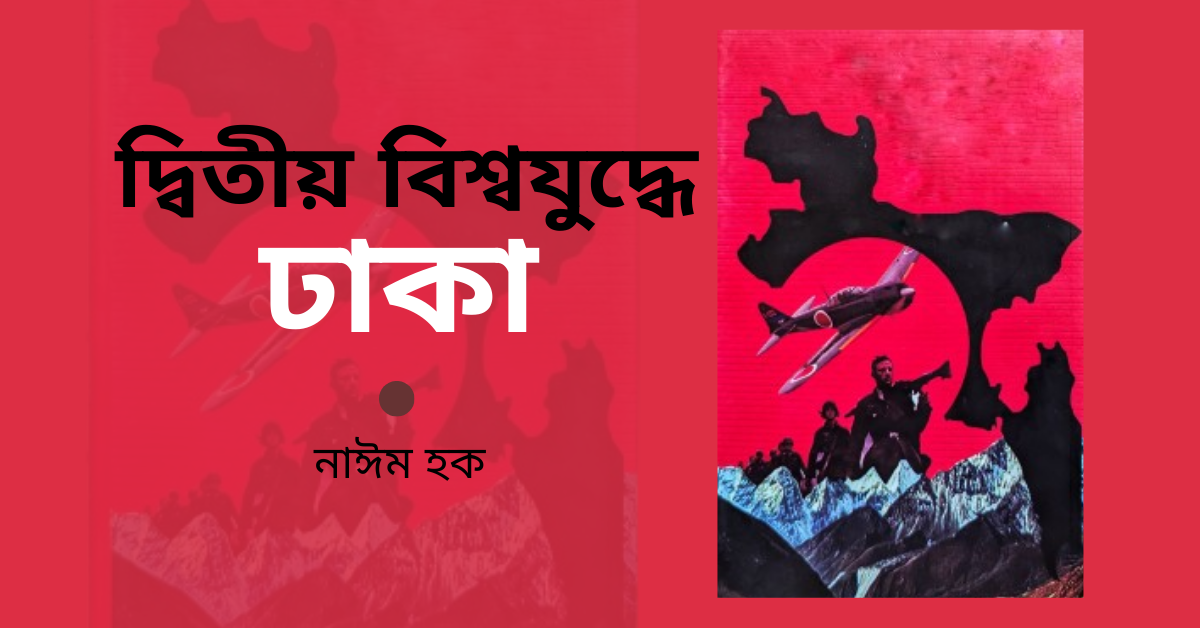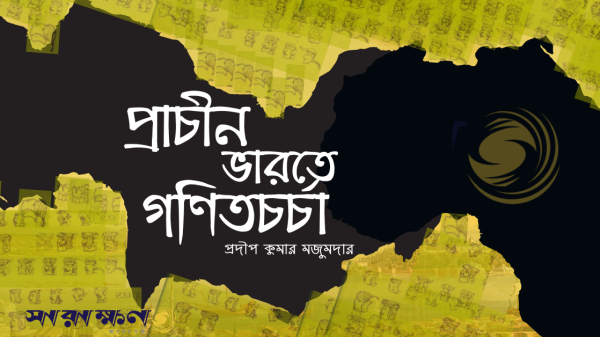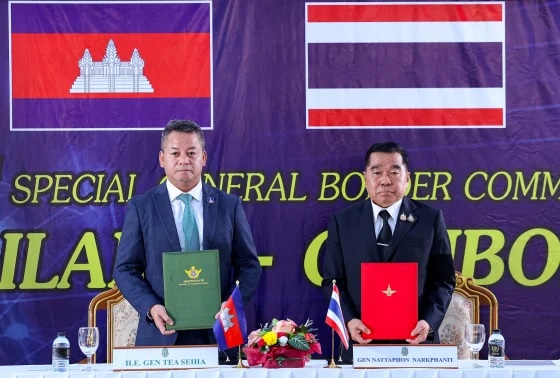রাঙাছুটুর বাপের বাড়ি
খাইয়া দাইয়া মাথায় তেল সিন্দুর লইয়া (আগেকার দিনে মুসলমান বধুরা মাথায় সিন্দুর দিত-ইদানীং সিন্দুরের প্রচলন কমিয়া গিয়াছে) মা পাড়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। আমি মায়ের আঁচল ধরিয়া। প্রথমেই ফেলিদের বাড়ি। ফেলির মা এক গোছা পান বেতের ঝাঁপিতে সাজাইয়া কাঁচা সুপারি কাটিয়া মায়ের সামনে আনিয়া দেয়। “এর সবগুলি খাইয়া তবে আমার বাড়ি হইতে উঠিতে পারিবে। কতদিন পরে আসিলে মেয়ে।”
সে-বাড়ি হইতে হালট পার হইলেই মিঞাজানের বাড়ি। ফেলি মার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। মিঞাজানের ঘরের কি সুন্দর দুখানা চালা। প্রত্যেকটা রুয়ার মধ্যে রাঙ দিয়া চিত্র করা। আঁটনে ছাঁটনে প্রজাপতির বাঁধন, শুকতারা বাঁধন। কালো বার্নিশ দিয়াছে ফুস্যির আর আঁটনের গায়ে, তাহার উপরে চাঁছা বেতের বাঁধনগুলি ঝকমক করে-ঘরের কপাটের দুই পাল্লার উপর কতই না সুন্দর কারুকার্য। মাটির মেঝে। বুড়ো মিঞাজান আর তার বউ লেপিয়া পুঁছিয়া তক তক করিয়া রাখিয়াছে। সিঁদুর পড়িলেও তোলা যায়। ঘরের মধ্যে সিকার উপরে দুলিতেছে কতরকমের হাঁড়িকুড়ি। এতসব থাকিতেও মিঞাজানের কিছুই নাই। একটি বেটা পুত্র নাই। ক্ষেতখামারে ধান গড়াগড়ি যায়। দুইজনে কত আর খাইবে।
মিঞাজান বিড়াল পোষে। প্রায় ৫০/৬০টা বিড়াল। রাঁধিয়া বাড়িয়া বুড়োবুড়ি খায় আর বিড়ালগুলিকে খাওয়ায়। মিঞাজানের বাড়িতে গেলে আমার আর উঠিতে ইচ্ছা করে না। বিড়ালগুলির মধ্যে নিজেই একটি বিড়াল হইয়া উঠি। সে-বাড়ি হইতে পথ বাঁকিয়া গিয়াছে মোকিমের বাড়ি। মোকিমের বউ সাজিভরা পান, সাজিভরা সুপারি মেলিয়া ধরে বারান্দায় মাদুরের উপর। মা আর কয়টা পান খান। মায়ের দুই মুঠি পানে ভরা। আঁচলে পান-সুপারি বাঁধা। রাঙাছুটু আজ দেশে আসিয়াছে। বউঝিরা তোরা আয়-ও-বাড়ির বউ, সে-বাড়ির বউ, এই তো সেদিন বিবাহ হইয়াছে, তারা আসিয়া মাকে সালাম করে। মা তাদের খোঁপা খুলিয়া নতুন করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া দেন। আদর করিয়া কাছে ডাকেন। বিদায়ের সময় বউরা বলে, “রাঙা-বুবু। আবার আসিবেন।”
এ-বাড়ি ও-বাড়ি হইতে কত মেয়ে মায়ের সঙ্গী হইয়াছে। মোকিমের বাড়ি ছাড়াইয়া সামনের হালট দিয়া আগাইয়া যাও। ওই তো তেঁতুলতলা-তারপরে বাঁশঝাড় পরাইয়া গেলেই বরোজদের পাড়া। সাত-আট ঘর বরোজ একসঙ্গে বাস করে। বড় বড় খড়ের আটচালা ঘর। উঁচু উঁচু দাওয়া সেখানে। বারান্দার উপরে ঘষামাজা পিতলের কলসিগুলি ঝকমক করিতেছে। তারও চাইতে ঝকমক করিতেছে বরোজদের বউগুলি। গায়ে যেন পিতলগোলা মাখাইয়া লইয়াছে। মাকে আদর করিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের মাঝখানে বসায়। বাড়ির গিন্নি আসিয়া এক ডালা পান দিয়া যায়। “সবগুলি না খাইয়া যাইতে পারিবে না, রাঙাছুটু। আমার বেলা, সেই তো সেদিন গেল শ্বশুরবাড়ি। থাকিলে তোমাকে দেখিয়া কত খুশি হইত।” মা গল্প করেন বরোজ-বউদের সঙ্গে। আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাদের পানের বরজগুলি দেখি।
যে-পান মা খায়, বাজান খায়, হাট হইতে বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া খায়, সেই পান একটা একটা করিয়া কঞ্চি বাহিয়া উপরে উঠিয়াছে। চারিধারে পাটখড়ির বেড়া-মাথার উপরেও সরু পাটখড়ির চিকন আচ্ছাদন। সূর্যের আলো যেন সবটা আসিয়া পানে পড়িতে না পারে। পানের কচি পাতায় সূর্যের আলো সবটা পড়িলে পান খাইতে ঝাল হইবে। কত সাবধানে পানের বরজ লালন-পালন করিতে হয়। মাঝে মাঝে পানের পাতায় খৈল-ভিজানো পানি ছিটাইয়া দিতে হয়। তাও পরিমাণমতো। বেশি দিলে পান পুরু হইয়া যাইবে। এতসব কিছু কেরামতি জানে বরোজরা। নিজের হাতে কোনো কাজ করে না। মুসলমান ক্ষেতি মেহনতি লোক লাগাইয়া কাজ করায়। তারা এমন বোকা।
চলবে…

 Sarakhon Report
Sarakhon Report