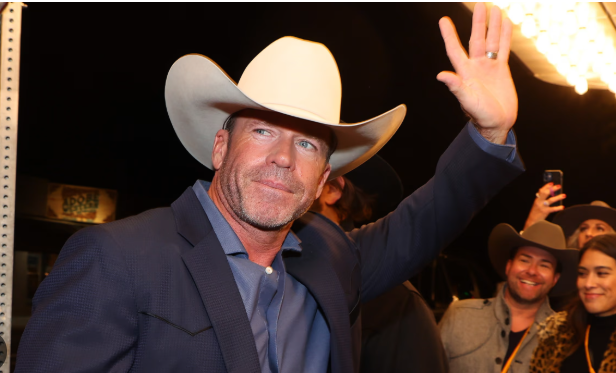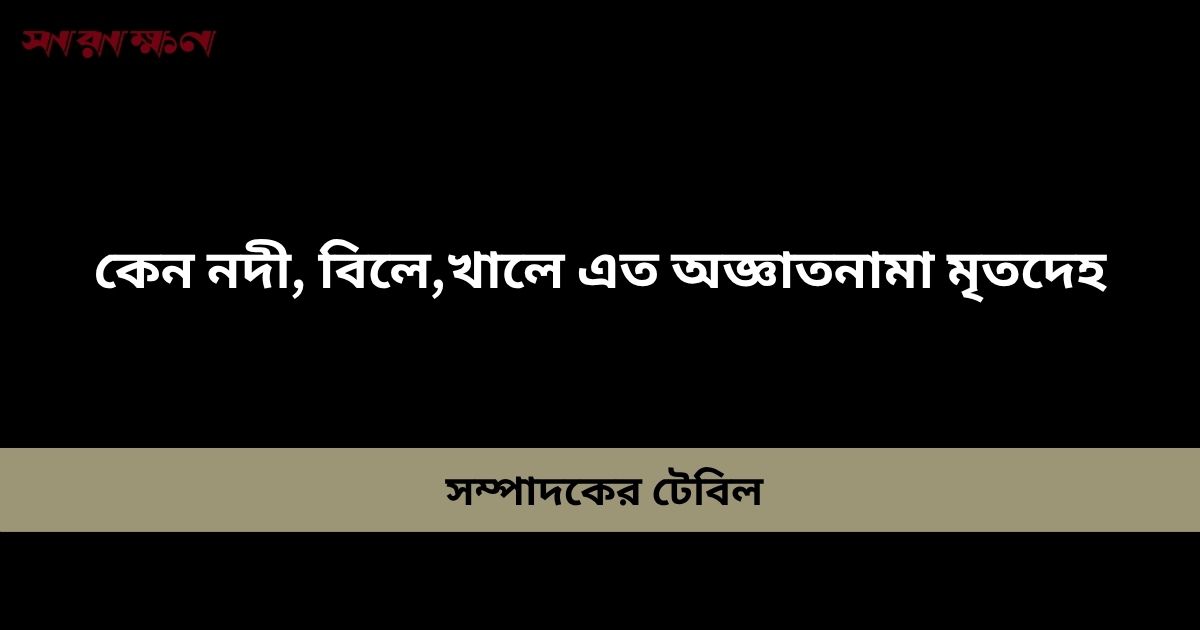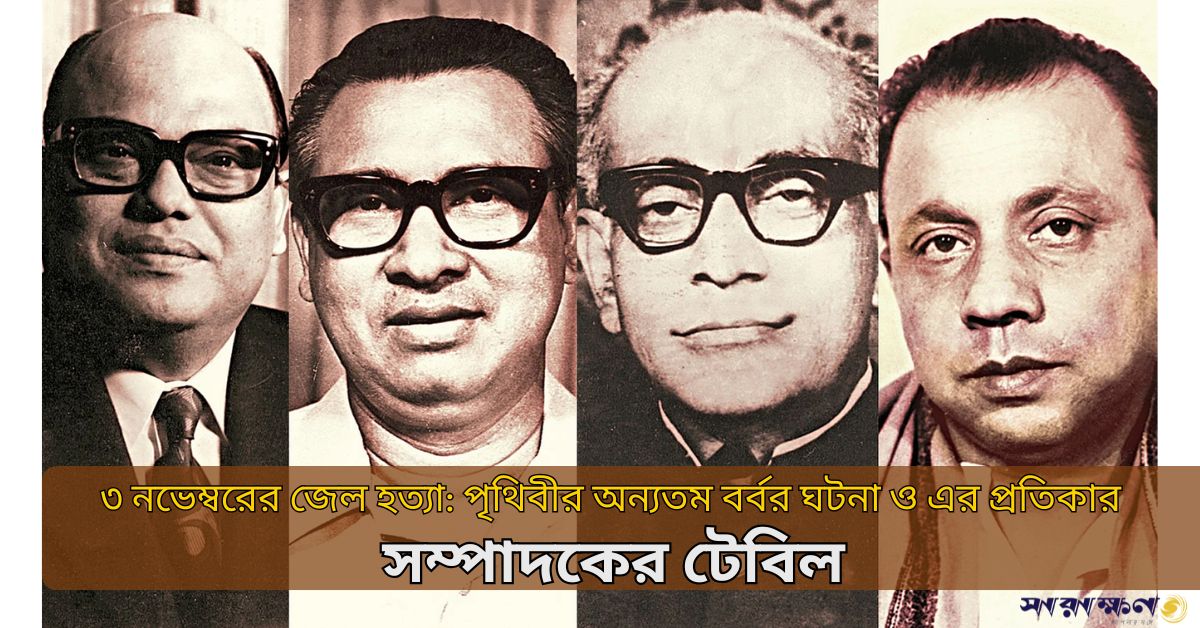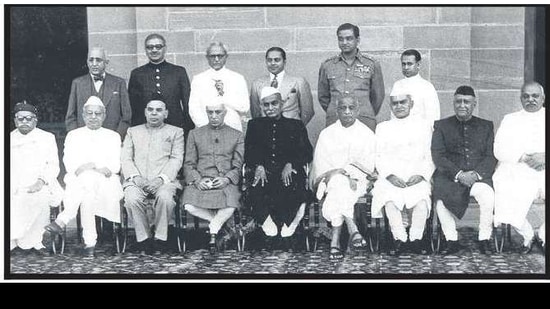ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার ঘোষণা দিয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্র গাজা উপত্যকা “দখল” করে সেটিকে নতুন একটি “রিভিয়েরা” হিসেবে পুনর্গঠন করবে। এই ঘোষণায় বিস্ময় ও ক্ষোভ—দুটোই দেখা গেছে বিভিন্ন মহলে।
ট্রাম্পের নিজস্ব কিছু সহযোগী পর্যন্ত পরে এই পরিকল্পনার কিছু অংশ “নরম” করার চেষ্টা করেছেন বা পেছনে সরে গেছেন। সিএনএন-এর কেভিন লিপটাক লিখেছেন, “হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বুধবার বারবার বলছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের ‘অস্থায়ীভাবে’ সরিয়ে নেওয়ার কথা বলছিলেন—যা একদিন আগের ঘোষণার সঙ্গে স্পষ্টতই সাংঘর্ষিক, কারণ ট্রাম্প আগে বলেছিলেন ‘স্থায়ীভাবে’ তাদের অন্য কোথাও পূর্ণবাসনের কথা।” অন্যদিকে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্কো রুবিও গাজায় ধ্বংসাবশেষ ও অবিস্ফোরিত বোমা সরিয়ে পুনর্গঠনের ওপর জোর দিয়েছেন, আর মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক দূত স্টিভ উইটকফ reportedly রিপাবলিকান সিনেটরদের ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছেন যে এই প্রকল্পে মার্কিন সেনা মোতায়েন করতে ট্রাম্প আগ্রহী নন, বলে টাইমস অফ ইসরায়েলের জেকব ম্যাগিড জানাচ্ছেন।
মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী শক্তিগুলো ট্রাম্পের এই প্রস্তাবে তেমন সাড়া দেয়নি। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের ররি জোন্স ও ওমর আবদেল-ব্যাকি জানিয়েছেন, সৌদি আরব বুধবার বলেছে যে ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার যে কোনো প্রচেষ্টাকে তারা প্রত্যাখ্যান করছে এবং একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের প্রতি তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে। তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ট্রাম্পের ধারণাকে “হাস্যকর” বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং গাজার জনগণকে “সমীকরণ থেকে বাদ দেওয়া” বা তাদের উচ্ছেদের যেকোনো প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছেন। মিসর, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার এবং ফিলিস্তিনি নেতারা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের স্থানান্তরের পরিকল্পনায় স্পষ্টতই না করেছেন।

তাহলে ট্রাম্পের এই ঘোষণা কি আদৌ গুরুত্ব দিয়ে নেওয়া উচিত?
নিউইয়র্ক টাইমস-এর জেরুজালেম ব্যুরো চিফ প্যাট্রিক কিংসলির বিশ্লেষণ বলছে, পরিকল্পনাটি এতটাই অবাস্তব যে অনেকে মনে করছেন এটিকে আক্ষরিক অর্থে নেওয়ার দরকার নেই। তিনি লেখেন, “শুধু যে এটি অবাস্তব তাই নয়, বরং ট্রাম্প অন্য ক্ষেত্রেও অতীতে বড় বড় হুমকি দিলেও পরে তা বাস্তবায়িত করেননি। সুতরাং অনেকে ধারণা করছেন গাজায় তাঁর এই উদ্যোগ আসলে আরব নেতাদের ও হামাসকে চাপের মুখে ফেলার একটি আলোচনা কৌশল।”
মধ্যপ্রাচ্য-বিশেষজ্ঞ পিটার বাইনার্ট (সাম্প্রতিক সময়ে ফরিদ জাকারিয়ার জিপিএস অনুষ্ঠানের অতিথি) তার নিউজলেটার ‘দ্য বাইনার্ট নোটবুক’-এ প্রকাশিত এক ভিডিওতে বলেছেন, ট্রাম্পের গাজা সংক্রান্ত ঘোষণাটি তাঁর গ্রীনল্যান্ড বা পানামা খাল দখলের ঘোষণার মতোই বোঝা উচিত। বাইনার্ট বলছেন, “গাজাকে বুঝতে হলে আপনাকে গ্রীনল্যান্ডকে বুঝতে হবে। ট্রাম্প মূলত পুরোনো আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী দর্শনের এতটাই বড় সমর্থক যে তিনি সেটিকে নতুন করে ফিরিয়ে আনতে চান তার নগ্নতম রূপে। শুধুই পরোক্ষভাবে নয়, তিনি সরাসরি অন্য দেশের ভূখণ্ড ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণে নিতে আগ্রহী। ঠিক যেভাবে তিনি পানামা ও কানাডা, এমনকি গ্রীনল্যান্ড নিয়েও কথা বলেছেন।”
আমেরিকার সামরিক বাহিনী:
নিয়োগে সংকট
‘দ্য নিউ ইয়র্কার’-এর ডেক্সটার ফিলকিন্স যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে বড় ধরনের নিয়োগ সংকট নিয়ে লিখেছেন। এটি সাম্প্রতিক দশকগুলোর ভেতর সবচেয়ে গুরুতর পরিস্থিতি। তিনি জানান, “ড্রাফট ব্যবস্থা (জোরপূর্বক সেনাভর্তির পদ্ধতি) বিলুপ্ত হওয়ার পর গত পঞ্চাশ বছরে এত বড় নিয়োগ ঘাটতি দেখা যায়নি। ২০২২ এবং ২০২৩ সালে, আর্মি তাদের লক্ষ্য থেকে প্রায় ২৫ শতাংশ পেছনে ছিল। নেভির অবস্থাও সুবিধার নয়। আর্মি রিজার্ভ ২০১৬ সালের পর থেকে নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারেনি। সামরিক নিয়োগকর্মীরা এমন এক জনগোষ্ঠীর মুখোমুখি হচ্ছেন যারা শুধু অনাগ্রহীই নয়, অনেকেই অযোগ্য। পেন্টাগনের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১৭ থেকে ২৪ বছর বয়সী আমেরিকানদের তিন-চতুর্থাংশের বেশি সেনাবাহিনীতে যোগদানের অযোগ্য—অতিরিক্ত ওজন, বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া, শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যগত জটিলতা অথবা অপরাধমূলক রেকর্ডের কারণে।”

এই পরিস্থিতি বড় প্রশ্ন তোলে। ফিলকিন্সের সঙ্গে কথা বলা এক বিশেষজ্ঞ জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ছোট হয়ে গেলেও বিশ্বজুড়ে আমেরিকার নিরাপত্তা-দায়বদ্ধতা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। চীন এখন স্পষ্টতই উঠে আসছে, তাই তাইওয়ান কেন্দ্রিক কোনো পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হলে এর ব্যাপক মূল্য দিতে হতে পারে। ট্রাম্প এই সংকটের জন্য “ডিইআই” (বৈচিত্র্য, সাম্য ও অন্তর্ভুক্তি) বিষয়ক নীতিমালাকে দায়ী করেছেন। ফিলকিন্স দেখিয়েছেন, কিছু প্রবীণ সামরিক কর্মকর্তা এসব নীতিমালার কার্যকারিতা নিয়ে সন্দিহান। কিন্তু “রাজনৈতিক বিতর্ক চলতেই থাকবে,” লিখছেন ফিলকিন্স, “এদিকে সামরিক নেতৃত্বের সামনে বড় চিন্তা হলো: প্রয়োজনের সময় যদি যথেষ্ট মানুষ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতেই না চায় বা যোগ দেওয়ার উপযুক্ত না থাকে, তাহলে কীভাবে কোনো দেশ আত্মরক্ষা করবে?”
‘সিরিয়ার নতুন শাসকদের সঙ্গে কীভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত’
সিরিয়ায় এখন হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) ক্ষমতায়, যারা সাবেক স্বৈরশাসক বাশার আল-আসাদের শাসন উৎখাতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু সংগঠনটি আসলে কারা? তাদের নেতা ও সিরিয়ার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট আহমাদ আল-শারা (আগে যিনি আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি নামে পরিচিত ছিলেন) আসলে কী চান?
কেউ ভালো করে জানে না, দ্য ইকোনমিস্ট-এর এক সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে যে শরা কখনো সামরিক পোশাকে হাজির হচ্ছেন, আবার কখনো স্যুট পরে আসছেন। তিনি গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আবার বলেছেন নতুন প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করতে তিন-চার বছর লেগে যেতে পারে। আর “তিনি যখন গণতন্ত্রের কথা বলেন, অনেকেই সন্দেহ করেন যে তিনি হয়তো সুন্নি আরব সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনকেই বুঝিয়ে থাকতে পারেন। (‘আমাদের অঞ্চলে গণতন্ত্রের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে,’ তিনি এমনটাই বলেছেন)” এখনো দেশটিতে নানা প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী সক্রিয়।সিরিয়ান বিদ্রোহীদের ওপর হওয়া এক গবেষণায় দেখা গেছে কীভাবে বিদেশি দেশগুলো এই অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে, তা তুলে ধরেছেন ফরেন অ্যাফেয়ার্স-এ লেখা এক নিবন্ধে নাফিস হামিদ, নিলস মালক, ব্রডেরিক ম্যাকডোনাল্ড এবং রহাফ আলদাউলি। তাদের গবেষণায় দেখা গেছে, আসাদকে উৎখাত করাই ছিল প্রায় সব সিরিয়ান বিদ্রোহীর কাছে এক পবিত্র লক্ষ্য। “আসাদকে হটানোর চূড়ান্ত লক্ষ্যে অনেক যোদ্ধাই নানা গোষ্ঠীর মধ্যে ঘুরেছেন, যেটিকে তারা মনে করেছেন শাসকবিরোধী সংগ্রামে সবচেয়ে কার্যকর।” এমনকি তারা ইসলামপন্থি ও ধর্মনিরপেক্ষ সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যেও অদলবদল করে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

সিরিয়ার সাবেক বিদ্রোহীদের এই মানসিকতা বুঝতে পারা বিদেশি শক্তিগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে এখন যখন দেশটি নতুন করে পুনর্গঠিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সরকারগুলো সাধারণত অর্থনৈতিক সহায়তাকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে—যেমন নিষেধাজ্ঞা আরোপ বা সহায়তার শর্ত আরোপ। কিন্তু যাদের কোনো একটি মূল্যবোধ বা লক্ষ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এভাবে “ক্রয়” বা “দমন” করতে চাওয়া বিপরীত ফল দিতে পারে।
ফরেন অ্যাফেয়ার্স-এর ওই লেখায় বলা হয়েছে, “বাইরের সরকারগুলোকে খেয়াল রাখতে হবে, সিরিয়ান নেতাদের ‘বিকিয়ে গেছেন’ এমনটা যাতে না মনে হয়। যে নেতারা বিদেশি সুযোগ-সুবিধা নেন, তারা দেশের ভেতরে প্রভাব হারাতে পারেন। … যদি বিদেশি সরকারগুলো সিরিয়ার বিদ্রোহীদের প্রভাবিত করতে চায়, তাহলে অর্থনৈতিক প্রলোভনের পরিবর্তে বরং প্রতীকী কিন্তু অর্থবহ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা ভালো, যেমন দামেস্কে দূতাবাস খুলে দেওয়া, আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধি দল পাঠানো বা গোপনে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় করা। যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই এইচটিএস-এর কাছে আইসিসের পরিকল্পিত একটি হামলার ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করেছে এবং আহমাদ আল-শরার (আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি)-এর মাথার দাম ১০ মিলিয়ন ডলারের যে ঘোষণা ছিল, তাও বাতিল করেছে। যখন কারো কাছে কোনো ব্যাপারটি পবিত্র লক্ষ্যের মতো, সেখানে এমন প্রতীকী কিন্তু বাস্তব পদক্ষেপ নিলে তারা সহিংসতা পরিহার করতে আরও আগ্রহী হয় এবং আপসের ব্যাপারে নমনীয় হতে শুরু করে—এমনটাই উঠে আসে ২০০৭ সালে ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের ওপর পরিচালিত জেরেমি গিনগেস, স্কট অ্যাটরান, ডগলাস মেডিন ও খালিল শিকাকির গবেষণায়।”

 Sarakhon Report
Sarakhon Report