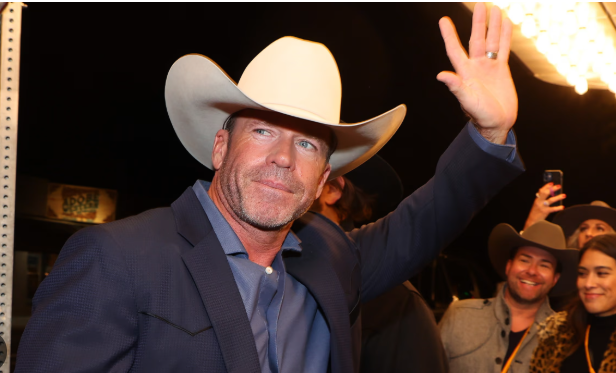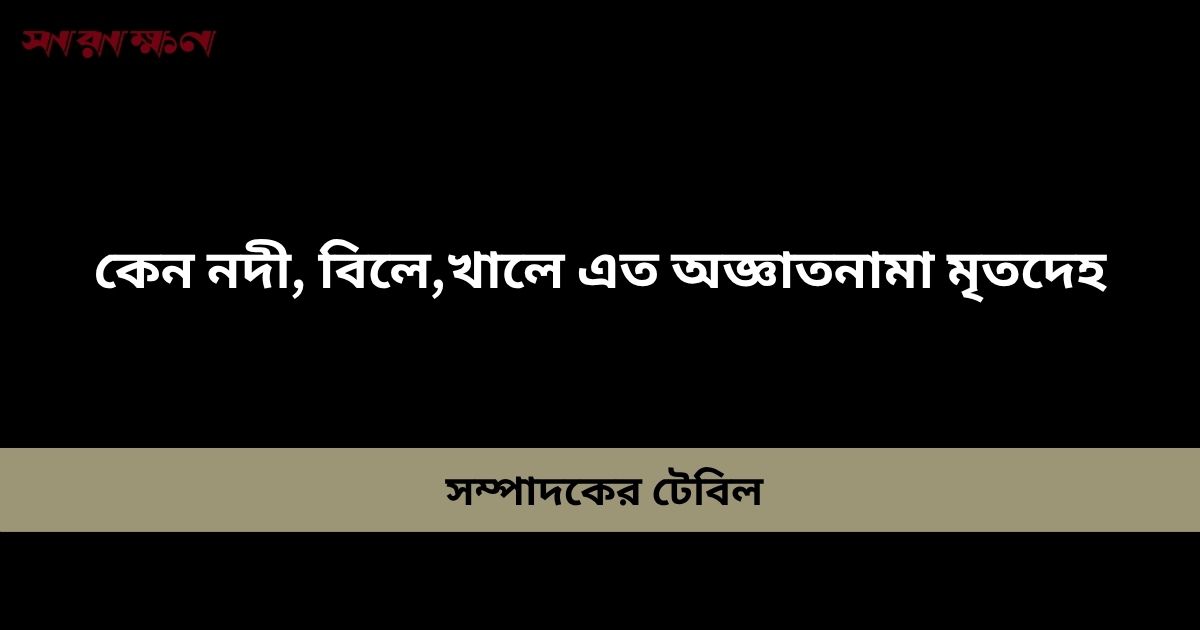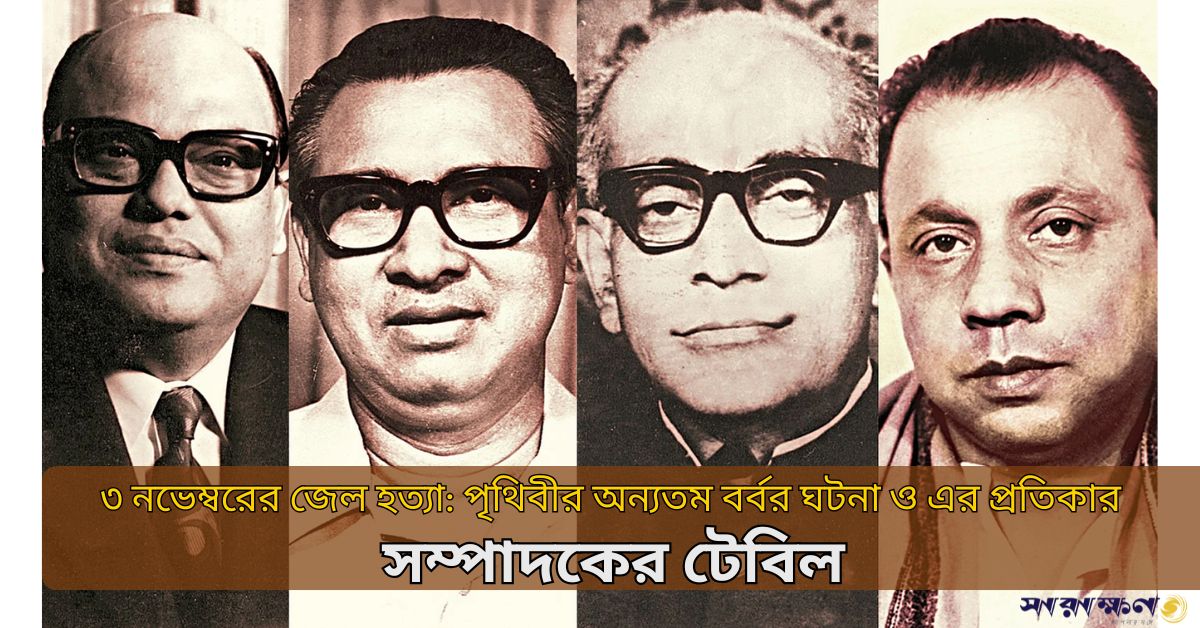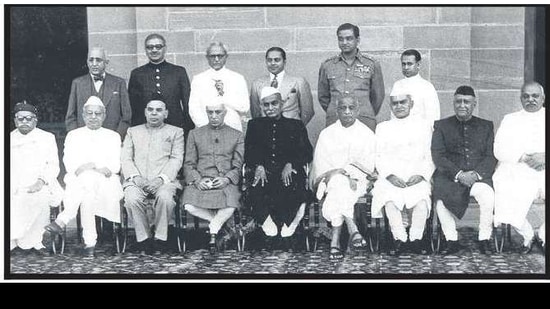অনেক পর্যবেক্ষকের কাছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা সংক্রান্ত পরিকল্পনাটি আদতে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে।
মঙ্গলবার ট্রাম্প ঘোষণা করেন যে যুক্তরাষ্ট্র গাজা নিয়ন্ত্রণে নেবে এবং সেখানে পুনর্গঠন কার্যক্রম চালাবে। আরব দেশগুলো দ্রুতই এই ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি ট্রাম্পের নিজের কয়েকজন উপদেষ্টাও পরবর্তীতে এই ঘোষণার ধারে-কাছের সম্ভাব্য পরিকল্পনার কথা নরম সুরে উল্লেখ করতে দেখা গেছে।
এর পেছনে মূল কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো, ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুতি নিয়ে যে দীর্ঘমেয়াদি সংকট চলছে, সেটি ইসরায়েল-ফিলিস্তিনি দ্বন্দ্বের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। অথচ ট্রাম্প বলেছিলেন, গাজার বাসিন্দাদের নিকটবর্তী আরব দেশে পাঠানোর কথা, যে দেশগুলো আগে থেকেই এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছে। তাছাড়া, আরও একটি বিষয় হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যে আরেকটি সামরিক উপস্থিতি বা দখলদারিত্ব মার্কিন ভোটারদের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়া কঠিন।
ট্রাম্প এই ধারণা কতখানি গভীরভাবে ভেবেছিলেন বা এটি কার্যকর করার রূপরেখা নিয়ে আগে থেকেই কোনো প্রস্তুতি ছিল কি না, তা অনিশ্চিত।
এর আগেও জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে, এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প একই ধরনের ধারণা তুলে ধরেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, “আমরা পুরোটা সাফ করে ফেলি (অর্থাৎ গাজা) এবং আরব দেশগুলোর সঙ্গে মিলিত হয়ে সেখানে আবাসন গড়ে তুলি।” মঙ্গলবারের ঘোষণার পর হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট জানিয়েছেন, ট্রাম্প বেশ কিছুদিন ধরেই বিষয়টি নিয়ে ভাবছিলেন এবং অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, আনুষ্ঠানিক কোনো লিখিত পরিকল্পনা ছিল না; ট্রাম্প একপ্রকার হঠাৎ করেই এটি ঘোষণা করেন।
দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ চারজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রের বরাতে জানানো হয়েছে যে, মার্কিন সরকারের ভিতরে এই প্রস্তাব নিয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা পেন্টাগনের সঙ্গে কোনো বৈঠক হয়নি—যা এত বড় মাপের কোনো পররাষ্ট্রনীতির পরিকল্পনার আগে সাধারণত হয়ে থাকে। কোনো ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়নি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সৈন্য বা ব্যয়ের কোনো হিসাব দেয়া হয়নি, কিভাবে এটি বাস্তবায়ন হবে সে সম্পর্কেও কোনো রূপরেখা ছিল না। বলতে গেলে, এটি প্রেসিডেন্টের মাথায় থাকা একটা ভাবনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।
অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, ট্রাম্পের এই ঘোষণার একটি ইতিবাচক দিক হতে পারে—দীর্ঘদিন ধরে ব্যর্থ হয়ে আসা ধারণাগুলোকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নতুন ও অপ্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি আনার চেষ্টা। মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার সমাধানে নতুন চিন্তা-ভাবনা প্রয়োজন। কিন্তু দ্য ইকোনমিস্ট সতর্ক করে বলছে, এই ধারণাটি এতটাই অবাস্তব ও নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ যে, এটি যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ট্রাম্প অনেক সময় যা বলেন, তা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় না—এমন বার্তা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের কথার ওজন কমে যাবে।
ওই পত্রিকাটি লিখেছে, “মধ্যপ্রাচ্যে সত্যিই নতুন চিন্তা দরকার। কিন্তু ট্রাম্প এমন একটি প্রস্তাব দিয়ে বসলেন যা অদূরদর্শী, অনৈতিক ও পুরোপুরি অপরিপক্ব। এর ফলে তিনি আমেরিকার বিশ্বাসযোগ্যতাকে দুর্বল করে দিচ্ছেন, এবং এই অঞ্চলে অস্থিরতা তৈরির পাশাপাশি জঙ্গিগোষ্ঠীকে শক্তিশালী হতে সহায়তা করতে পারেন। হামাস এখন বলতে পারবে, ‘আমেরিকা গাজার মানুষের বিষয়ে গুরুত্ব দেয় না।’ অন্যদিকে ইসরায়েলের চরম ডানপন্থীরা গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের বের করে দিয়ে সেখানে বসতি স্থাপনের পরিকল্পনায় আরও অনুপ্রাণিত হতে পারে। ট্রাম্প যে মিত্রদের সহযোগিতা প্রয়োজন, তাদের সঙ্গেও বিরোধ বেড়ে যাচ্ছে। তিনি সৌদি আরবকে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে চাপ দেওয়ার জন্য এই হুমকি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে এর ফলে সৌদিরা আরও পিছিয়ে যেতে বাধ্য হবে।”

চীন কীভাবে ট্রাম্পের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে
ট্রাম্প অনেকদিন ধরেই চীনের ওপর উচ্চ শুল্কারোপের কথা বলে আসছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১০% শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিলেও, তিনি এর আগে কানাডা ও মেক্সিকোর ক্ষেত্রে যা হুমকি দিয়েছিলেন, সেটির তুলনায় কিছুটা নরম ছিল এটি। তা সত্ত্বেও ওয়াশিংটনে অবস্থিত বৈদেশিক-বিষয়ক গবেষণা সংস্থা স্টিমসন সেন্টারের চীনা বিষয়ক কর্মসূচির পরিচালক ইউন সান ফরেন অ্যাফেয়ার্সে লিখেছেন যে চীন বরাবরই আশঙ্কা করছিল ট্রাম্প আরও আক্রমণাত্মক হবে, এবং সেই আশঙ্কা সত্যি হয়েছে।
তবে সান বলছেন, চীনেরও প্রস্তুত পরিকল্পনা আছে। তিনি লেখেন, “ট্রাম্পের মেয়াদ পার করার জন্য বেইজিং যে পথনকশা সাজিয়েছে, তার অন্যতম প্রধান দিক হলো দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক মেরামত করা এবং গ্লোবাল সাউথ বা দক্ষিণের দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা। ট্রাম্প হয়তো স্বল্পমেয়াদে কিছু সাফল্য পেতে পারেন, কিন্তু বেইজিং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করছে। চীনা নেতারা মনে করেন, চীনের ঐতিহাসিক উত্থান অবশ্যম্ভাবী এবং যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে একদিন তারা পরাশক্তির আসনে বসবে। তাদের ধারণা, ট্রাম্পের বর্তমান নীতি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার ক্ষয় ঘটাচ্ছে এবং বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কমাচ্ছে। তাই সুযোগ আসামাত্র চীন এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে।”
চীন বৃহত্তর বাণিজ্যযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত
(উপরের আলোচনার সূত্রে বোঝা যায় যে চীন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বৃহত্তর বাণিজ্যযুদ্ধের সম্ভাবনাকেও আমলে নিচ্ছে এবং সে অনুযায়ী অবস্থান শক্ত করছে।)

সার্বিয়ায় ছাত্রবিক্ষোভ
নভেম্বর মাসে সার্বিয়ার নোভি সাদ শহরের একটি ট্রেনস্টেশনের ছাদ ধসে পড়ে। শহরটি রাজধানী বেলগ্রেড থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বে। এই দুর্ঘটনায় হতাহতদের স্মরণে প্রথমে অনেকেই শান্তিপূর্ণভাবে জড়ো হয়েছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের ক্ষোভ বেড়ে যায়। কারণ, অনেকের মতে, রাষ্ট্রপতি আলেকসান্ডার ভুচিচের সরকার গত ১২ বছর ধরে দেশ শাসন করলেও অবকাঠামোর দুর্নীতি, অনিয়ম ও দুর্বল ব্যবস্থাপনার ফলেই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।
সিএনএন-এ ক্রিশ্চিয়ান এডওয়ার্ডস লিখেছেন, “শুরুতে হতাহতদের প্রতি শোক প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু ভেঙে পড়া এই ট্রেনস্টেশনের ছাদ এখন অনেক সার্বের কাছে দুর্নীতি ও অবহেলার প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রতিদিনই প্রায় বিক্ষোভ হচ্ছে, আর প্রতিবাদের মাত্রা বাড়ছে, এতে ছাত্রদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষও যুক্ত হচ্ছেন। দেশের প্রায় প্রতিটি প্রান্তে এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। … ছাত্ররা সরকারের কাছে পুনর্নির্মাণকাজ সংক্রান্ত সব নথি প্রকাশের দাবি জানাচ্ছে। এত বড় ও দীর্ঘস্থায়ী বিক্ষোভের মুখে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, এটি কি ভুচিচের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষমতার পতন ডেকে আনবে?”
সার্বিয়ার সরকারকে ডানপন্থী ও জনবিক্ষোভে-সমর্থিত বলে মনে করা হয়, এবং তারা বড় বড় বিশ্বশক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করেছে। ইউরোপীয় কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে এঞ্জেলুশে মোরিনা ও অ্যাঞ্জেলিকা ভাসকোত্তো লিখেছেন, “গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এই অস্থিরতার কারণে বসন্তকালে আগাম সংসদ নির্বাচন হতে পারে। কিন্তু জনগণের ক্রোধ এবং ভুচিচের সরকারে অস্থিরতা ছাড়াও তার আরও সমস্যা আছে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি পশ্চিমা বিশ্ব এবং রাশিয়ার মধ্যে সমানতালে সম্পর্ক বজায় রাখার যে ‘নিজস্বভাবে বাছাই করা কূটনীতি’ অনুসরণ করে আসছিলেন, সেটি এখন চাপে পড়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও রাশিয়া দু’পক্ষই বেলগ্রেডকে নিজেদের পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান নিতে চাপ দিচ্ছে। এখন ভুচিচ দেখছেন, তার অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোর প্রতি বাইরের সহানুভূতি তেমন নেই এবং এক্ষেত্রে তার কূটনৈতিক গতিশীলতাও খুব কম।”

 Sarakhon Report
Sarakhon Report