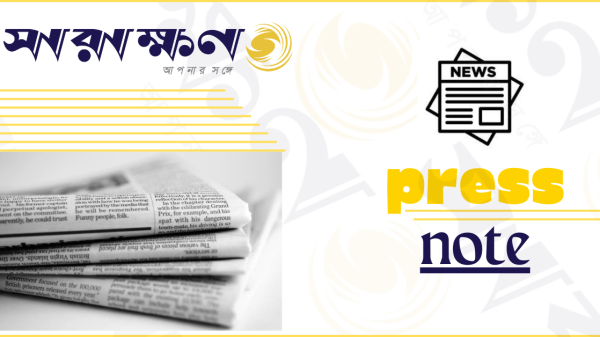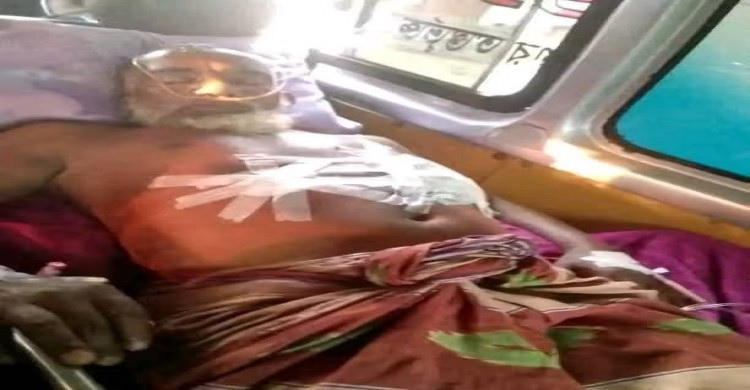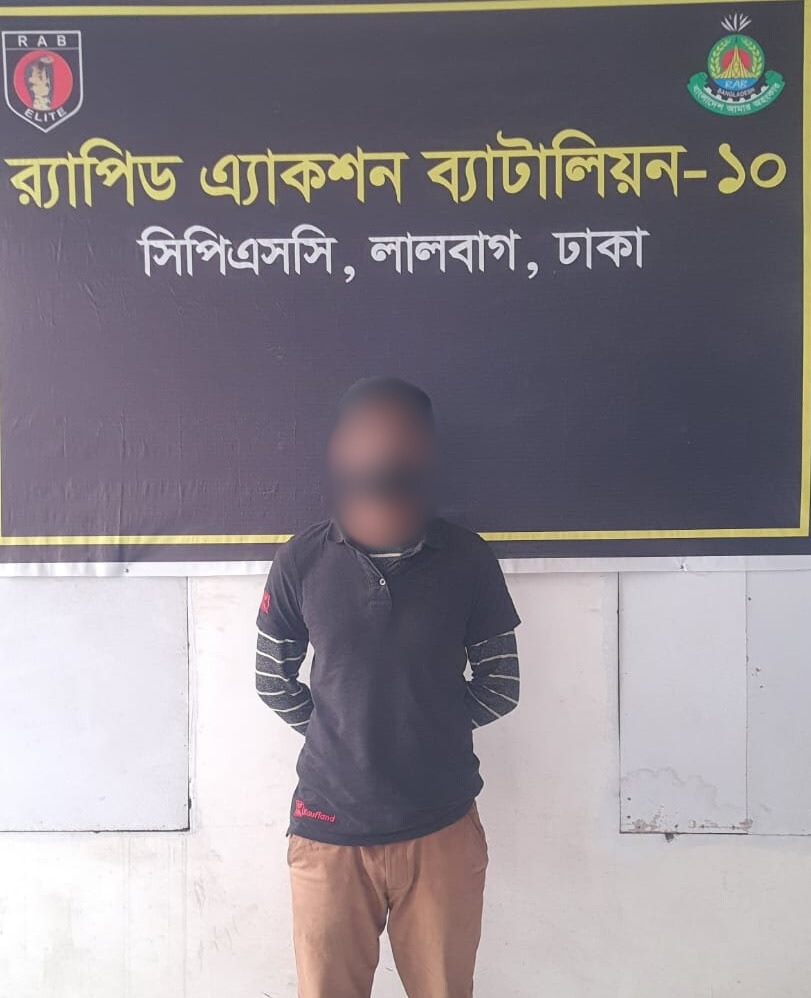সারাক্ষণ ডেস্ক
প্রথম আলোর একটি শিরোনাম “সরকারি ব্যাংকের পরিচালকদের জবাবদিহির আওতায় আনা হচ্ছে”
রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিয়োগের নীতিমালা আবার পরিবর্তন করা হচ্ছে। বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালকেরা যথেষ্ট জবাবদিহির মধ্যে নেই বলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে আপত্তি জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। সেই আপত্তি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ আমলে নিয়েছে। সে অনুযায়ী তারা পরিচালকদের অধিকতর জবাবদিহির আওতায় আনতে নিয়োগ নীতিমালা সংশোধন করতে যাচ্ছে।
২০২৪ সালের ৯ এপ্রিল রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিয়োগের বিদ্যমান নীতিমালা প্রণয়নের জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এক সপ্তাহের মাথায় ১৬ এপ্রিল এর ওপর কিছু পর্যবেক্ষণ দেয় বিশ্বব্যাংক। এরপর বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে এসে নতুন করে তা নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়।
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেকের সভাপতিত্বে গত ৬ জানুয়ারি ঢাকায় সচিবালয়ে একটি বৈঠক হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সে বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয় যে বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ ও বিশ্বব্যাংককে নিয়ে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে এ–সংক্রান্ত খসড়া দাঁড় করাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। আর জুনের মধ্যে তা অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির কাছে।
জানতে চাইলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি। আশা করি পরিচালকদের অধিকতর জবাবদিহির মধ্যে আনার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেই তাঁদের নিয়োগের নীতিমালা চূড়ান্ত করা হবে।’
জানা গেছে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এখন পর্যন্ত যতটুকু খসড়া দাঁড় করিয়েছে তাতে ঋণখেলাপি ও করখেলাপি হলে এবং ১০ বছরের প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনা বা পেশাগত অভিজ্ঞতা না থাকলে কেউই ব্যাংকের পর্ষদ সদস্য হতে পারবেন না। ফৌজদারি অপরাধ বা জাল-জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অন্য কোনো অবৈধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বা আছেন, এমন কেউ পর্ষদ সদস্য হতে পারবেন না। দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলায় আদালতের রায়ে বিরূপ পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য থাকলে এবং আর্থিক খাত-সংশ্লিষ্ট কোনো সংস্থার বিধিমালা, প্রবিধান বা নিয়মাচার লঙ্ঘন করে দণ্ডিত হলেও পর্ষদ সদস্য হওয়া যাবে না। একটি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক থাকাবস্থায় কেউ অন্য কোনো ব্যাংকের পরিচালক হতে পারবেন না।
দৈনিক ইত্তেফাকের একটি শিরোনাম”ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে নির্বাচন দিতে চায় সরকার”
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে দায়িত্ব নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। গত ১৬ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস জাতীয় নির্বাচনের একটি সম্ভাব্য সময়ের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অল্প সংস্কার করে নির্বাচন চাইলে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে, আর আরেকটু বেশি সংস্কার করে নির্বাচন চাইলে ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে নির্বাচন করা সম্ভব।
এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান রয়টার্সকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ১৮ মাসের মধ্যে যাতে নির্বাচন হতে পারে, সে জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলো সম্পন্ন করতে এই সরকারকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি নভেম্বর–ডিসেম্বের (২০২৫) মধ্যেই নির্বাচনের কথা বলেছিলেন।
এদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন এক পত্রিকার সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আমি যদি খুব ভুল না করে থাকি তাহলে অক্টোবরের দিকে তফসিল ঘোষণা, ডিসেম্বরে নির্বাচন এবং জানুয়ারির মধ্যে নতুন সরকার গঠন হতে পারে- এমন সংকেত পাচ্ছি।’
রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, সংস্কারে জোর দিলেও বিভিন্ন খাতে, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বেশ কিছু বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটেছে। মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা, দুশ্চিন্তা রয়েছে। এমতাবস্থায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি নির্বাচিত সরকার না এলে পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নিতে পারে, এমন আশঙ্কার কথাও আলোচনা হচ্ছে।
বণিকবার্তার একটি শিরোনাম “স্বাধীনতার পর কোনো সরকারই ভূমি সংস্কারে হাত দেয়নি”
মেক্সিকোয় বিপ্লবের (১৯১০-১৯২০) পর দেশটিতে ব্যাপক মাত্রায় ভূমি সংস্কার করা হয়। দেশটির ওই বিপ্লব ও পাল্টা বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল কৃষকদের ভূমি অধিকারের দাবি আদায়। দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে এ ভূমির অধিকার নিশ্চিত করেন সেখানকার বিপ্লবীরা।
বলশেকিভ বিপ্লবের পর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯১৭ সালেই বড় ধরনের ভূমি সংস্কারে হাত দেয়া হয়। এতে বৃহৎ ভূমি মালিকদের থেকে জমি উদ্ধার করে তা স্থানীয় কৃষক ও কমিউনের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। এতে কৃষি উৎপাদনে নয়া জাগরণ সৃষ্টি হয়। এ ভূমি বণ্টনকে রাশিয়াসহ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক সংস্কার হিসেবে দেখা হয়। এ সংস্কার রুশ সমাজের ক্ষমতার কেন্দ্রেও ভারসাম্য নিয়ে আসে। সামাজিক এলিটদের সঙ্গে উৎপাদন শৃঙ্খলে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে যুক্ত হন ভূমিহীন কৃষকরা। ইতিহাস অনুযায়ী, রাশিয়া ও মেক্সিকোয় বিপ্লব দানা বাঁধার বড় অংশজুড়ে ছিল কৃষকের ভূমি মালিকানার দাবি, যা পরবর্তী সময়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছাড়িয়ে পড়ে।
একইভাবে চীনেও কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর ১৯৪৯-৫০ সালে ব্যাপকভিত্তিক ভূমি সংস্কার করা হয়। জমিদারদের কাছ থেকে ভূমির মালিকানা বুঝিয়ে দেয়া হয় প্রান্তিক চাষীদের, যা দেশটির গ্রামীণ কৃষি ও অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কমিউনভিত্তিক কৃষির অভিজ্ঞতা দেখার জন্য সে সময় চীনে ভিড় বাড়তে থাকে।
একই সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই বড় ধরনের ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয় দক্ষিণ কোরিয়ায়ও। এক্ষেত্রে কৃষিকাজে কোনো ধরনের ভূমিকা রাখা ভূস্বামীদের কাছ থেকে জমির মালিকানা নিয়ে তা বিতরণ করা হয় প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে। এর মধ্য দিয়ে দেশটিতে কার্যকরভাবেই আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূমি মালিকানা ব্যবস্থার বিলোপ ঘটে। একই সঙ্গে গ্রামীণ এলাকাগুলোয় বৈষম্য কমে গড়ে ওঠে সমতাভিত্তিক সামাজিক কাঠামো। বাড়ে কৃষির উৎপাদনশীলতা, যা দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল।
একইভাবে ভূমির সংস্কার করা হয়েছিল জাপান, তাইওয়ানসহ আরো বেশকিছু দেশে। নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় শুরু হয় ভূমি সংস্কার কর্মসূচি ‘নিউ ওয়েভ’। এর মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়েতে ভূমি সংস্কার করা হয়। এক সময় ফিলিপাইন ও হন্ডুরাসেও প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভূমির সংস্কার।
ঔপনিবেশিক আমল থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভূমির অধিকার নিয়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রকট হতে থাকে। গত শতকে ভূমির অধিকার নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিপ্লব ও ক্ষমতার পালাবদলও হয়েছে। একই সঙ্গে ভূমি সংস্কারের বিষয়টি হয়ে উঠেছে যেকোনো দেশের রূপান্তরের পথে মৌলিক সংস্কারের অংশ।
কিন্তু বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের পর গত ছয় মাসেরও বেশি সময় ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্যে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। সরকার ১১টি কমিশন গঠন করলেও প্রান্তিক কৃষকের ভূমি মালিকানা নিয়ে কোনো বক্তব্য নেই। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত গত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় কোনো সরকারই ভূমির সংস্কারে হাত দেয়নি। কিছু আইন প্রণয়ন হলেও ভূমি মালিকানার কাঠামোয় কোনো কার্যকর পরিবর্তন আনা হয়নি।
দেশের গ্রামীণ কৃষিতে ভূমি বণ্টনে রয়ে গেছে বড় ধরনের বৈষম্য। এখনো দেশের গ্রামীণ কৃষি খাতে নিয়োজিত বেশির ভাগ পরিবারই ভূমিহীন। আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইএফপিআরআই) তথ্য অনুযায়ী, দেশে ৫৬ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের কোনো জমি নেই। যদিও গ্রামাঞ্চলে মোট কৃষিজমির ৬৬ শতাংশই এখন আয়-ব্যয়ের দিক থেকে শীর্ষ ১৫ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের দখলে।
বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের ভূমি সংস্কার নিয়ে কাজ শুরু করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদ ও গবেষকরাও। সরকারের অর্থনীতিবিষয়ক টাস্কফোর্সের প্রধান ও বিআইডিএসের সাবেক মহাপরিচালক ড. কেএএস মুরশিদ বণিক বার্তাকে বলেন, ‘এখানে ভূমি নিয়ে বহুকাল কোনো আলাপ নেই, গবেষণাও নেই। এখন ভূমি ব্যবস্থাপনা অনেক বেশি অন্যায্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষকের হাতে খুব বেশি জমি নেই। খাদ্যনিরাপত্তা নিয়ে আলোচনায় প্রযুক্তি ও উন্নত যন্ত্রায়নের কথা বললেও ভূমির কথা নেই। কত দ্রুত আমাদের ভূমির ব্যবহার বদলে যাচ্ছে, সেটিও বোঝা যাচ্ছে না। এটা জানা দরকার। এখন গবেষকদের মধ্যেও কৃষি নিয়ে আগ্রহ কম। যদিও জিডিপির ২৩ শতাংশে অবদান রাখছে গ্রামীণ অর্থনীতি।’
দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৫ শতাংশের বেশি নিয়োজিত রয়েছে কৃষি খাতে। কৃষিকাজে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৩ কোটি ২০ লাখ মানুষ। তবে কৃষিতে নিয়োজিত যেসব কৃষকের জমি নেই, তারা জমি বর্গা নিয়ে আবাদ করতে বাধ্য হচ্ছেন। আইএফপিআরআইয়ের গবেষণার তথ্যমতে, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের যথাক্রমে ৬৭ দশমিক ৮ ও ৬৪ দশমিক ৯ শতাংশ পরিবারের কোনো ভূমি নেই। এছাড়া ঢাকা বিভাগের ৫৫ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের কোনো ভূমি নেই। রংপুর ও বরিশাল বিভাগের ক্ষেত্রে এ হার ৫৪ দশমিক ৬ শতাংশ করে। রাজশাহী বিভাগের ৫২ দশমিক ১ ও খুলনা বিভাগের ৪৭ শতাংশ পরিবার ভূমিহীন। এসব পরিবারের কৃষির জন্য আলাদা কোনো ভূমি নেই।
গবেষণার বিষয়ে আইএফপিআরআইয়ের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. আখতার আহমদ বণিক বার্তাকে বলেন, ‘গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদের জমির মালিকদের উৎপাদনের অর্ধেক দিয়ে দিতে হয়। এতে তাদের আর তেমন কিছু থাকে না। কিন্তু বিকল্প না থাকায় তারা কৃষিতে যুক্ত থাকে। এখন কীভাবে এসব কৃষককে সহায়তা করা যায়, তা নিয়ে ভাবতে হবে। তবে আমাদের মতো দেশে ভূমি সংস্কার কতটা সম্ভব হবে, সেটি এখনো নিশ্চিত না। যদিও আগে অনেক দেশেই এটা হয়েছে।’
দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথার বিলোপ ও ভূমি মালিকানা সিলিং ১০০ বিঘা নির্ধারণ করা হয়। সে সময় পূর্ববঙ্গে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে স্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্ত করে বর্গাচাষীদের সরাসরি রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু পরে ১৯৬১ সালে আইয়ুব খান সরকার এর পরিমাণ ধার্য করে ৩৭৫ বিঘা বা ১২৫ একর।
মানবজমিনের একটি শিরোনাম “নতুন দল বুধবার, নেতৃত্বে এক ঝাঁক জামায়াতের ছাত্র”
পরিকল্পনা ঠিক থাকলে আগামী বুধবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক দল ঘোষণা করতে চলেছেন। মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে নতুন এই দলের হাল ধরার কথা তথ্য ও সম্প্রচার-সহ বেশ কয়েকটি দফতরের দায়িত্বে থাকা ছাত্রনেতা নাহিদ ইসলামের। তার আগে দু’টি ঘটনা নজর কেড়েছে।
প্রথমত, দু’ভাবে ভাগ হয়ে যাওয়া কোটা-বিরোধী ছাত্ররা টানা আলোচনার পরে নতুন দলের বিভিন্ন পদে যে সব নেতাদের নাম চূড়ান্ত করেছেন, তাদের অনেকেই জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাবেক নেতা। দ্বিতীয়ত, এই দল গঠনের আগেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কিছু মাঝারি পর্যায়ের সমন্বয়ক একটি নতুন ছাত্র সংগঠনও তৈরি করছেন। কালই আত্মপ্রকাশ করতে পারে নতুন এই ছাত্র সংগঠন। তবে নতুন ছাত্র সংগঠনটি নতুন ওই দলটির শাখা হবে কি না, তা এখনই বলতে পারছেন না নেতারা।
রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা গোড়া থেকেই বলে আসছেন, স্বাধীনতা আন্দোলন বিরোধিতার কলঙ্ক নিজেদের মুখ থেকে কিছুতেই তুলতে না-পেরে জামায়াতে ইসলামীই পেছন থেকে কোটা-বিরোধী আন্দোলনের সমন্বয়কদের নিয়ে আনকোরা দলটি তৈরি করছে। কারণ, এখন নির্বাচন হলে সাংগঠনিক শক্তির বিচারে বহু যোজন এগিয়ে থাকা বিএনপি অনায়াসে ক্ষমতা দখল করবে। তাদের ঠেকাতে অন্য ইসলামি দলগুলিকে নিয়ে জোট গড়ার চেষ্টা করেও সুবিধা করতে পারেনি জামায়াত। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রদের নতুন দলটির আর যাই হোক, স্বাধীনতা-বিরোধিতার কলঙ্কটি থাকবে না। বিএনপি-র শাসন মানুষ আগে দেখেছে। এ বারে তাঁরা নতুন দলকে সুযোগ দিতে পারেন। যুদ্ধাপরাধ আদালতে গণহত্যায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে জামায়াত নেতা এ টি এম আজহারুল হকের প্রাণদণ্ড হলেও তা কার্যকর হয়নি। এই রাজাকার শিরোমণির নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করে মঙ্গলবার ইউনূসের দফতর অভিযানের ডাক দিয়েছে জামায়াত।

 Sarakhon Report
Sarakhon Report