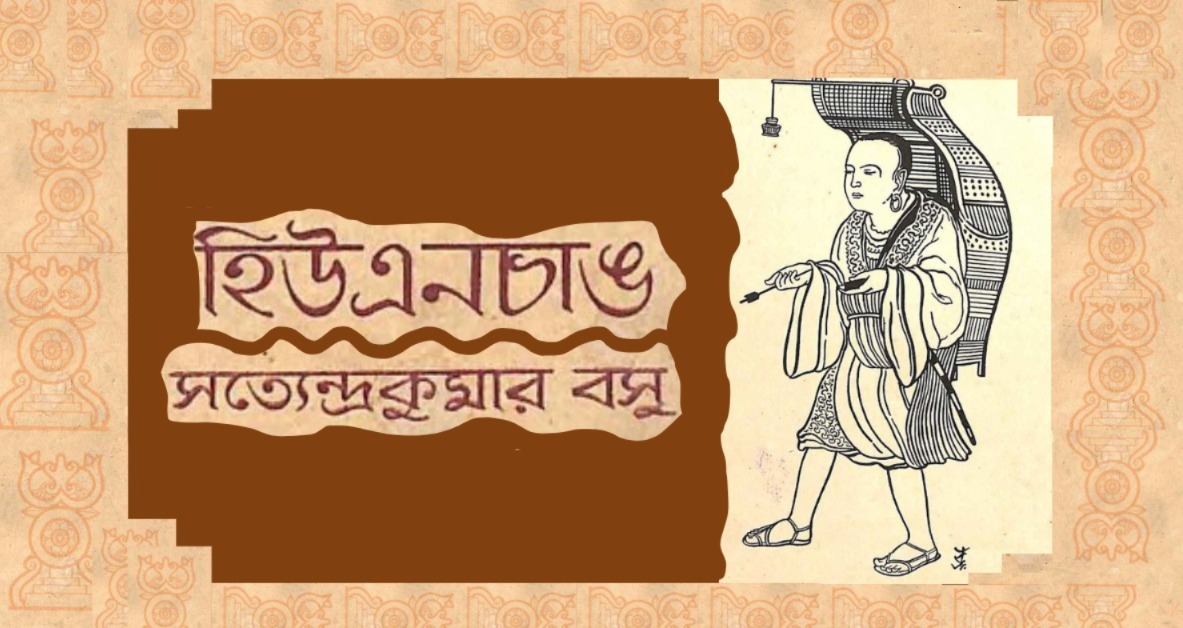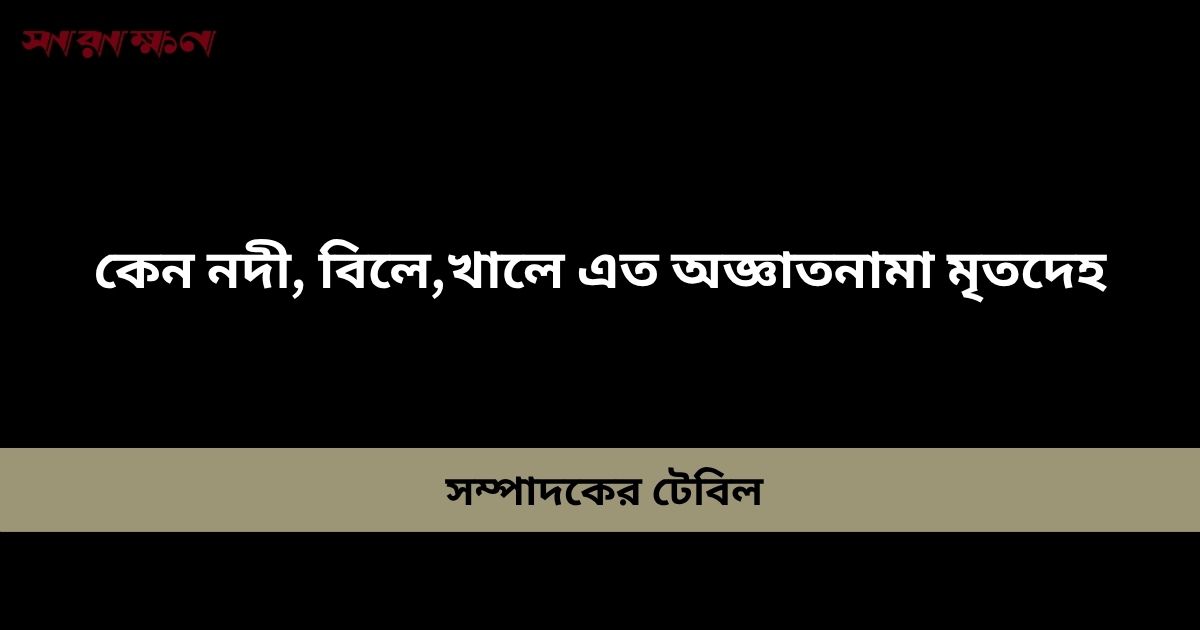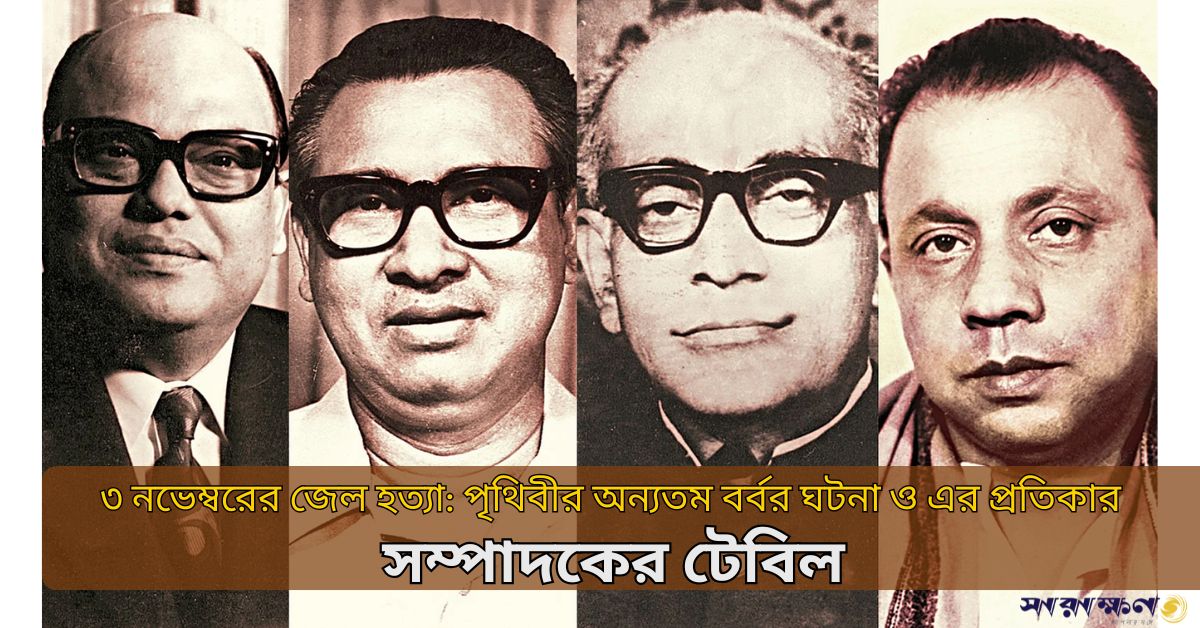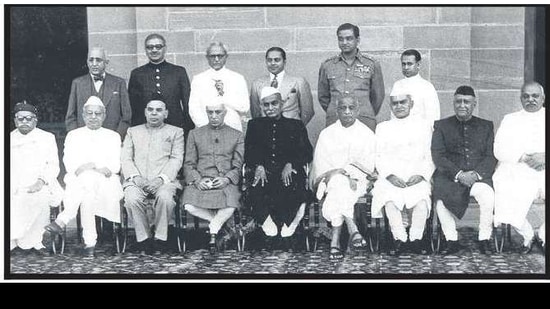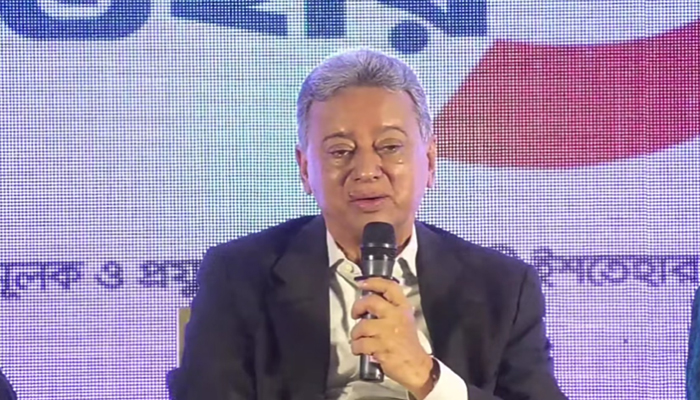ইংরাজের আমলের আগে এদেশের সম্পূর্ণ অরাজকতার যে একটা ছবি মনে আসে, সেটা হয়তো সত্য না হতেও পারে।
হিউএনচাঙএর সময়ে এদেশের মৈত্রেক রাজা ধ্রুবভট্ট হর্ষবর্ধনের জামাতা ছিলেন আর তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। এই রাজার সঙ্গে পরে ইউএনচাঙের পরিচয় হয়েছিল। হর্ষবর্ধনের মত এরও বৌদ্ধপ্রীতি ছিল। হিউ এনচাঙ বলেন, ‘রাজা একটু বোকা আর হঠকারী।
আচার-ব্যবহার মার্জিত নয়, কিন্তু গুণের ও বিদ্যার আদর করেন। অল্পদিন হল তাঁর ত্রিরত্নে ভক্তি হয়েছে আর প্রতি বৎসর সাতদিন ধরে ইনি এক উৎসব করেন। সে সময়ে নানা দেশের ভিক্ষুদের উপাদেয় আহার্য, বস্ত্র, ঔষধ, রত্ন ইত্যাদি বিতরণ করেন।’
এখান থেকে সিন্ধু নদীর ব-দ্বীপ দেখে, বোধ হয় নদীতীর ধরে হিউ এনচাঙ উত্তরে মূলস্থানিপুরে (মূলতানে) এলেন। তার পর তিনি ‘পর্বত’ দেশে (আধুনিক জম্মু) উপনীত হলেন।
এইভাবে হিউএনচাঙের সমস্ত ভারতবর্ষ পরিদর্শন সমাপ্ত হল। তের শত বছর আগে একজন বিদেশী পণ্ডিতের পক্ষে এই ভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় সব বিশিষ্ট স্থানগুলি পরিদর্শন করা যে কী করে সম্ভব হয়েছিল তা আমাদের প্রায় কল্পনার অতীত। তবে মনে হয় যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়লে, ইংরাজের আমলের আগে এদেশের সম্পূর্ণ অরাজকতার যে একটা ছবি মনে আসে, সেটা হয়তো সত্য না হতেও পারে।
সে যা হোক, ভারত-পরিক্রমা সাঙ্গ হলেও হিউএনচাঙের এখনো এদেশে কাজ বাকি ছিল। অনেক শাস্ত্রের অনুলিপি করা বাকি ছিল, আর শাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্যে তিনি নিশ্চয়ই আর একবার তাঁর প্রিয় নালন্দায় যেতে ইচ্ছা করেছিলেন।
কিন্তু সেখানে ফিরবার আগে, বৌদ্ধ-রীতি অনুসারে ‘বর্ষাবাস’ করবার জন্যে তিনি জম্মুতেই দু মাস থাকলেন। এ সময়েও তিনি আলস্যে কাটান নি; এখানকার দুই-তিন জন পণ্ডিতের কাছে ‘মূলাভিধমশাস্ত্র’ ‘সদ্ধর্মসম্পরিগ্রহশাস্ত্র’ আর ‘প্রশিক্ষা-সত্য-শাস্ত্র’ পাঠ করেছিলেন।
(চলবে)
হিউএনচাঙ (পর্ব-১৩৫)

 সত্যেন্দ্রকুমার বসু
সত্যেন্দ্রকুমার বসু