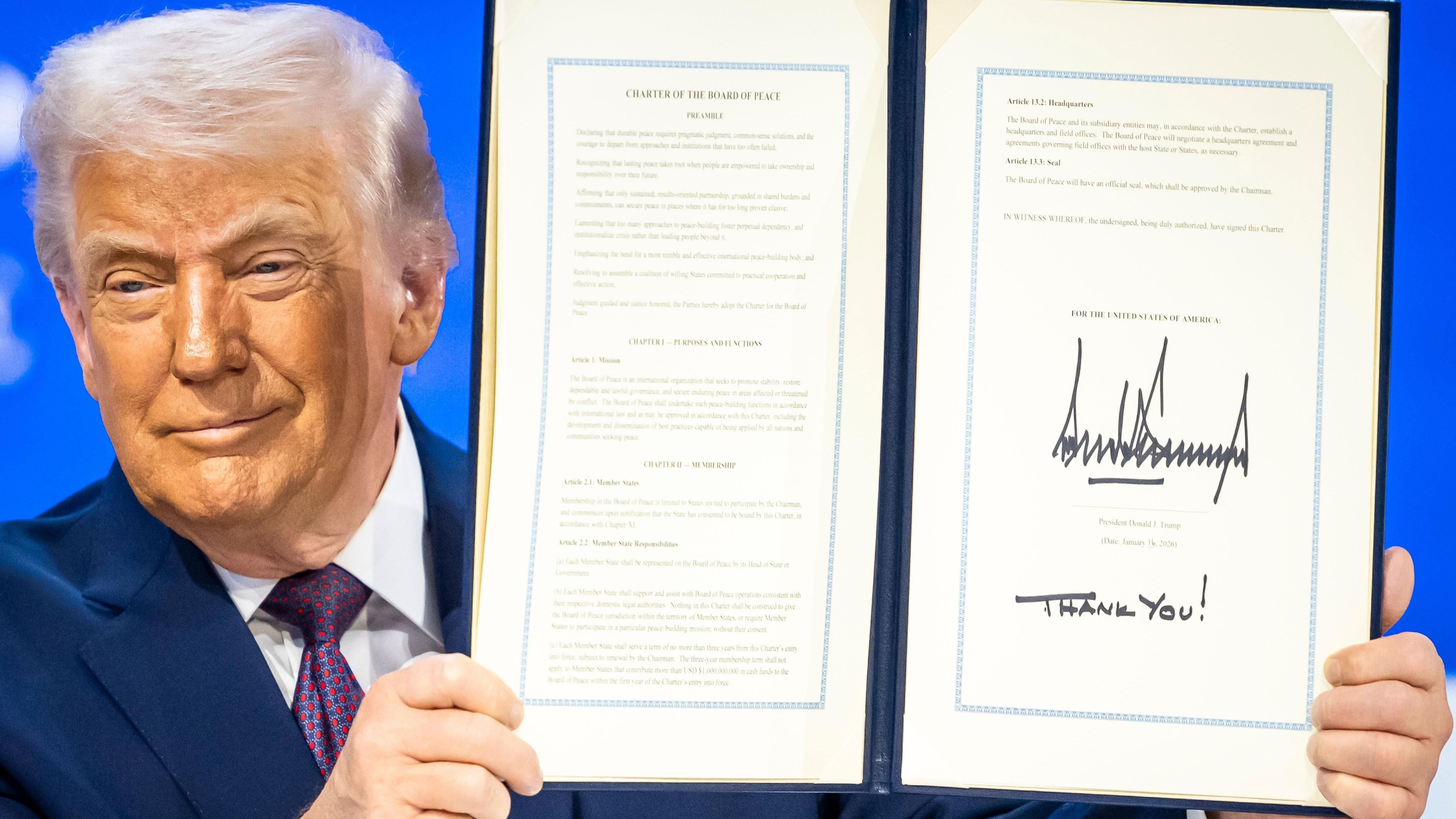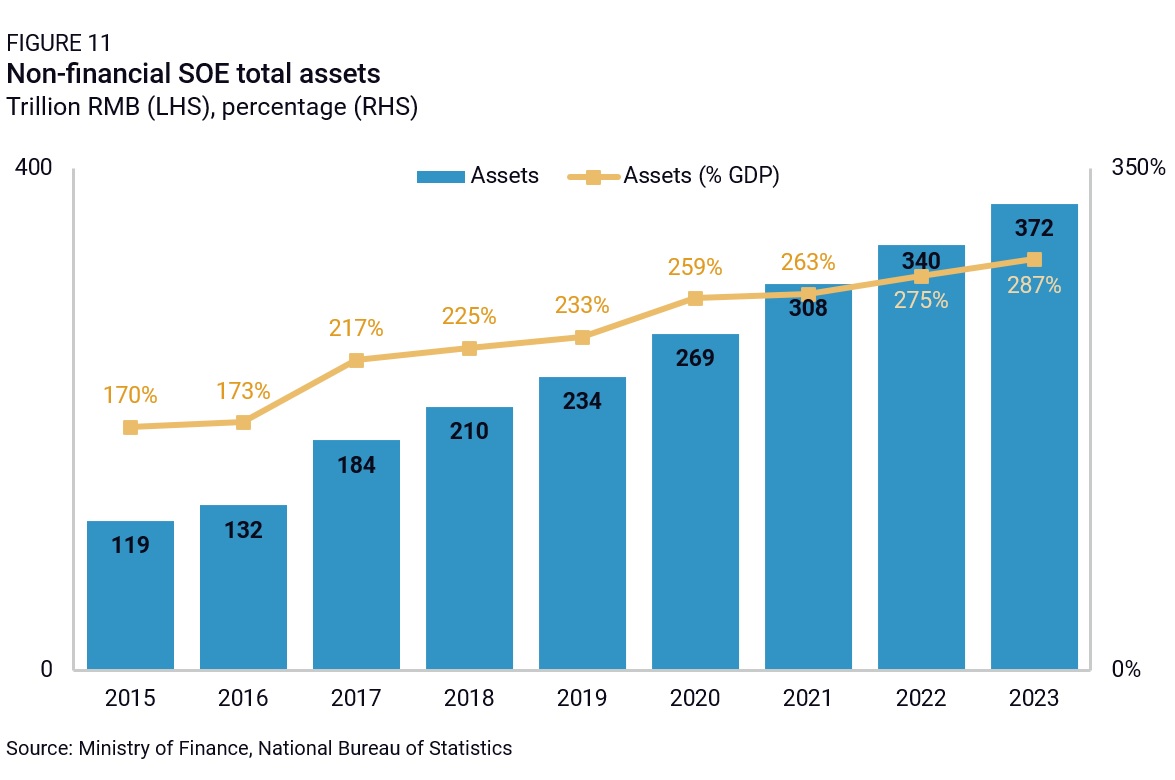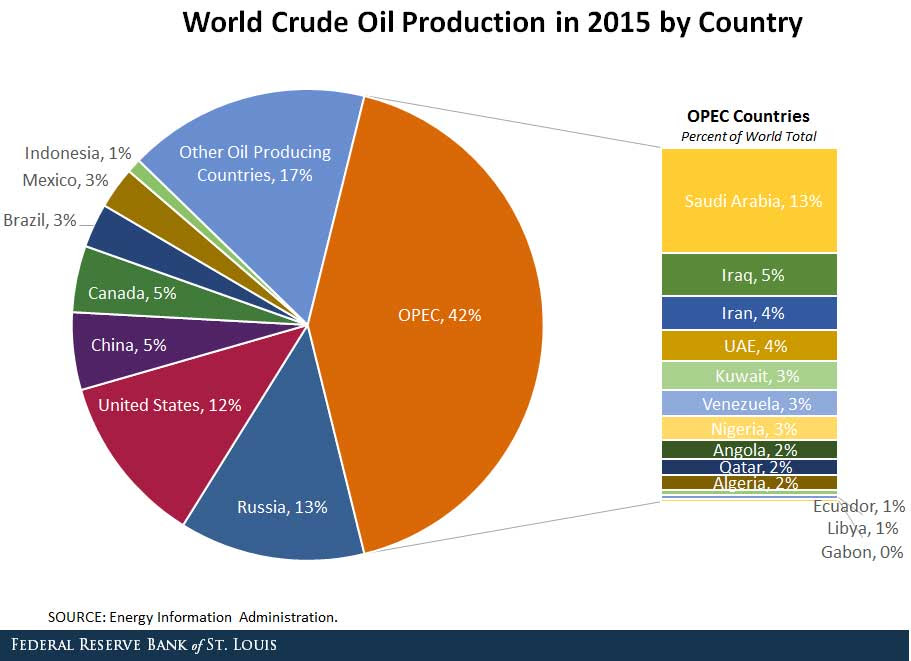বাজারের হাহাকার
ঢাকার মোহাম্মদপুর কাঁচাবাজারে গৃহবধূ সায়মা আক্তার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, “ঈদের আগে যে মিনিকেট ছিল ৭২ টাকা, এখন ৮৫ থেকে ৯০! ছেলেমেয়েদের ডাল–ভাতটাও টিকছে না।” একই ছবিতে সারা দেশে মোটা স্বর্ণা ৫৮ থেকে ৬০ টাকা, মাঝারি পাইজাম ৭০ টাকা ছুয়েছে আর মিনিকেট ৯০ এর ওপর ঘোরাফেরা করছে — এক মাসে সব ধরনের চালের দাম লাফ দিয়েছে।

দাম বাড়ার পেছনের সাতেক ছিদ্র
- ডলার-সংকটে এলসি ভাঙা: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৩ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে গেলে আমদানি বিল মেটাতে সরকারকে কিস্তিতে অর্থ ছাড় করতে হয়, শুল্ক ছাড়াতে সময় গড়ে ২৫ দিন পেছাচ্ছে।
- ২০২৪-এর বন্যায় ক্ষতি: গত আগস্ট ও অক্টোবরে দুই দফা প্লাবনে প্রায় ১১ লাখ টন ধান নষ্ট হয়েছে, যা জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৩ শতাংশ।
- বাম্পার বোরো, তবু মজুত-সিন্ডিকেট: মিলার ও করপোরেট গুদামে ‘উচ্চ দরে আগাম কেনা’ চলায় খোলা বাজারে ধান দাঁড়ায় না — ক্ষেতে দামের চাপ, শহরে আকাশছোঁয়া দর।
ফলে মে মাসে খাদ্যমূল্য-স্ফীতি ১১ শতাংশের ঘরে, যার ৪০ শতাংশেরই দায় শুধু চালের দামে।
‘নীরব দুর্ভিক্ষ’ শঙ্কা
দরিদ্র পরিবারের পাতে চাল–ডাল টিকলেও মাছ, ডিম, সবজি কমে যাচ্ছে। পুষ্টিবিদারা একে ‘সাইলেন্ট ফ্যামিন’ বলছেন—ক্যালরি মেলে, কিন্তু প্রোটিন-ভিটামিন ঘাটতিতে অপুষ্টি বাড়ে। খাদ্য নিরাপত্তার সূচক (FIES)-এ বাংলাদেশ ইতিমধ্যে ‘মডারেট ইনসিকিউর’ স্তরে।

জাপানের উল্টো যাত্রা
দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধানখেত কমিয়ে দাম ধরে রাখার পর, জাপানে ২০২৪-এর তাপদাহে ফলন কমে দর ৭০ শতাংশ বেড়ে যায়। অতঃপর টোকিও ২০২৭ মৌসুম থেকে উৎপাদন বাড়ানোর ঘোষণা দেয়; লক্ষ্য—২০৩০ সালে ৩.৫ লাখ টন রপ্তানি, ঘাটতির বছরে যা ঘরে টেনে এনে দাম সামলানো যাবে।
এই রূপান্তর সফল করতে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হচ্ছে—
- কৃষকের জন্য ‘সেফটি নেট’ ভর্তুকি
- পনেরো হেক্টরের বেশি জমি জুড়ে ব্লক-চাষ
- ড্রোন, এআই ও স্বয়ংক্রিয় রোপণযন্ত্রে খরচ কমানো
তবু জাপানি চাল আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যয়বহুল; বিশ্লেষকেরা বলছেন, নীচু দামে ৩.৫ লাখ টন বিক্রি করা ‘কঠিন চ্যালেঞ্জ’।
বাংলাদেশের জন্য নেওয়া শিখন
- সমবায় ব্লক-চাষ ও যান্ত্রিকীকরণ
প্রতি ৫০–১০০ বিঘা জমি নিয়ে গ্রুপ-লিজে পাওয়ার টিলার ও কম্বাইন হারভেস্টার চালু করলে বিঘা-প্রতি খরচ ১২–১৫ শতাংশ কমবে। - জলবায়ু-সহিষ্ণু ধানের সম্প্রসারণ
বন্যা-সহিষ্ণু ‘ব্রি ধান-৮৪’, খরা-সহিষ্ণু ‘ব্রি ধান-১০৭’ এবং লবণ-সহিষ্ণু ‘ব্রি ধান-৯২’ জাতের বীজে ভর্তুকি জরুরি।

- দাম-স্থিতি তহবিল
জাপানের মতো কেজি-প্রতি ৩০–৫০ পয়সা ‘প্যাডি প্রাইস স্টাবিলাইজার’ মোবাইল-মানি অ্যাকাউন্টে দিলে উৎপাদন বাড়লেও বাজারপতনে কৃষক ভাঙবেন না। - রপ্তানি-বাফার ধারণা
বোরো মৌসুমে অতিরিক্ত দুই লাখ টন চাল কিনে ঘাটতির বছরে বাজারে ছাড়া, আর স্বাভাবিক বছরে নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপে রপ্তানি—দাম দুই দিকেই সামলে যাবে। - ডিজিটাল নজরদারি ও সিন্ডিকেট ভাঙা
জেলা-ভিত্তিক ‘রাইস ড্যাশবোর্ড’ চালু করে মিল ও গুদামে তাৎক্ষণিক মজুত হালনাগাদ বাধ্যতামূলক করলে অস্বচ্ছ মজুতের পথ রুদ্ধ হবে।
চালের দামে অস্বাভাবিক উল্লম্ফনের এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সামনে দুটি পথ—বাড়তে থাকা আমদানি বিলের ওপর নির্ভরতা, অথবা জাপানের আদলে উৎপাদন বাড়িয়ে অতিরিক্ত মজুতকে ‘কুশন’ হিসেবে ব্যবহার করা। দ্বিতীয় পথটি সফল করতে দরকার সমবায়ভিত্তিক যান্ত্রিকীকরণ, নতুন জাত, কৃষক-সুরক্ষা ভাতা ও কঠোর বাজার তদারকি। নইলে স্বল্পআয়ের মানুষের পাতে ভাত কমে যাওয়াই আগামী দিনের কঠোর বাস্তবতা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট