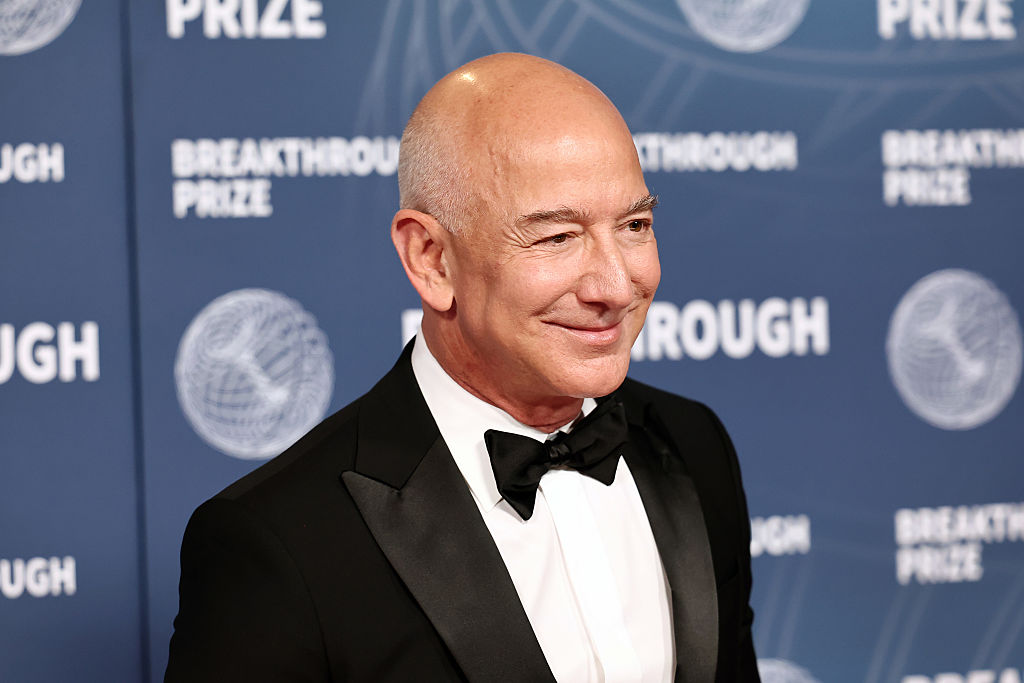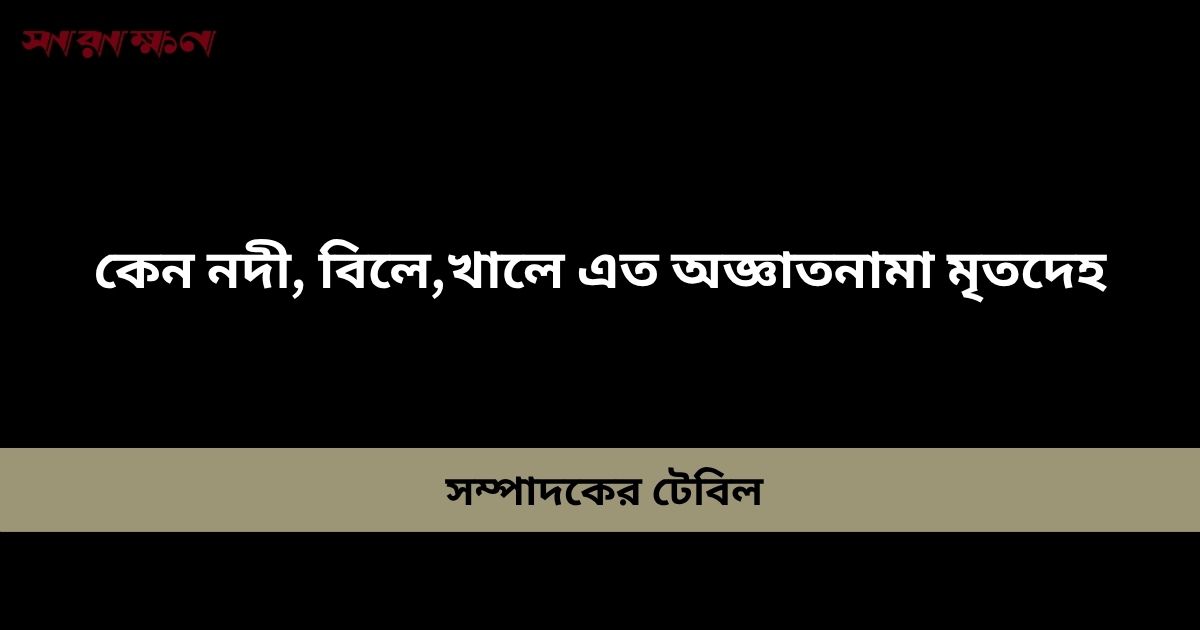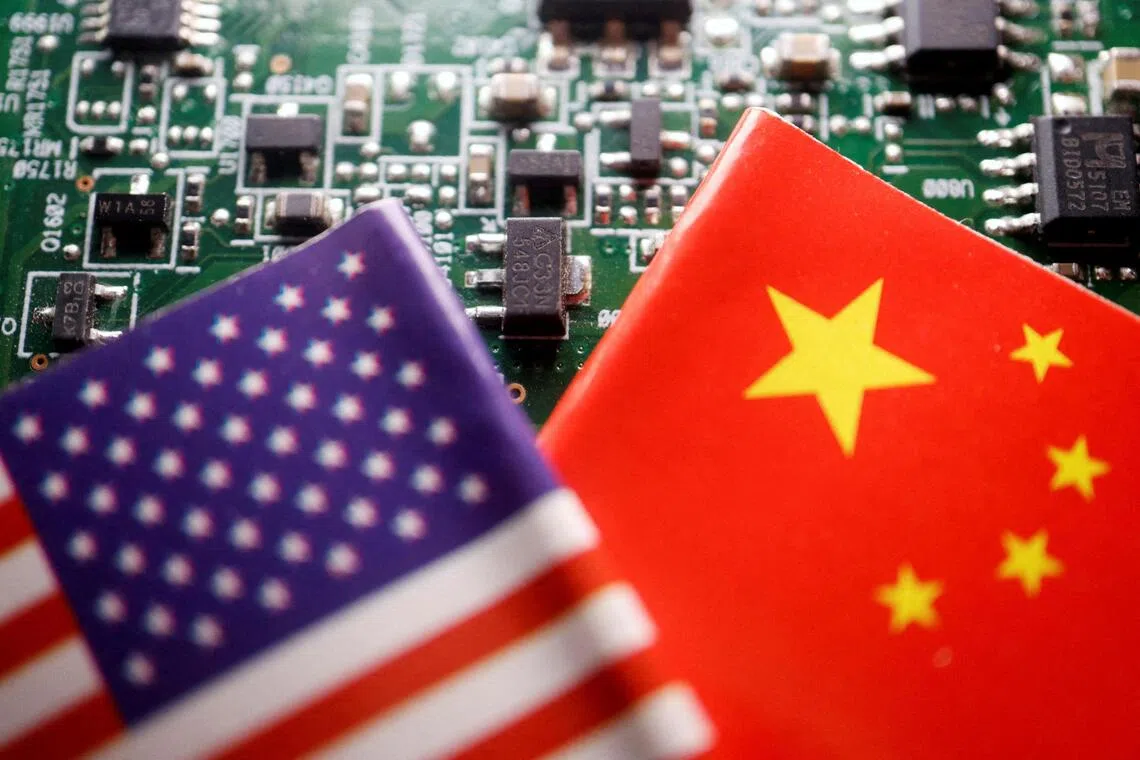নদীর পরিচিতি এবং উৎপত্তি
ভৈরব নদী দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক নদী। এর বয়স প্রায় দুই শত বছর হলেও এর উৎসের ইতিহাস আরও প্রাচীন। এটি গঙ্গা-পদ্মা-বৃদ্ধিত শাখা নদীর অন্যতম প্রবাহ, যা খুলনা, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। এই নদীর দুই তীরজুড়ে গড়ে উঠেছে বহু প্রাচীন জনপদ, হাট-বাজার, নৌবন্দর, কৃষি সভ্যতা ও এক অনন্য নদীকেন্দ্রিক সংস্কৃতি।
দুই তীরের সভ্যতা ও নগরায়ণ
ভৈরব নদীর দুই কূলেই গড়ে উঠেছে অসংখ্য জনপদ—যেমন নওয়াপাড়া, খুলনা শহর, ও আরও অনেক নদীবন্দর। নদীর পানিই ছিল সেচের মূল উৎস। দুই পাড়ের জমি ছিল অতিজলবাহিত ও উর্বর। এখানে ধান, পাট, ডাল, তিল, আখের মতো ফসল উৎপাদিত হত প্রচুর পরিমাণে। ব্রিটিশ আমলে নদীর দুই তীরেই নীলকুঠি গড়ে তোলা হয়েছিল—নীলচাষের দুঃখগাঁথা জড়িয়ে আছে এই নদীর ইতিহাসে।
জলপথে বাণিজ্য ও নৌযোগাযোগ
ভৈরব নদী ঐতিহাসিকভাবে ছিল খুলনা-যশোর অঞ্চলকে কলকাতা, চট্টগ্রাম এমনকি অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর সাথে যুক্ত করার এক প্রধান নৌপথ। ব্রিটিশ আমলে খুলনা বন্দর থেকে কলকাতা পর্যন্ত নৌযান চলত নিয়মিত। ভৈরবের জলপথে নৌকা, পালতোলা বোট, পরে স্টিমার চলত। এতে রপ্তানি হতো ধান, পাট, মাছ, কাঠ, গুঁড়, লবণ, খোল ও মোম। অন্যদিকে ভারত থেকে আসত কাপড়, লোহা, নুন, বিলেতি পণ্য।

ব্রিটিশ আমলের রপ্তানি-আমদানি
ব্রিটিশ শাসনকালে ভৈরব নদী খুলনা ও যশোর অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যিক শিরা ছিল। খুলনা বন্দর হয়ে কলকাতায় পাট রপ্তানি হত এই নদীপথে। নদীর পাড়ে গড়ে ওঠে পাটকল, গুঁড়ের আড়ত, কাঠের গুদাম। শীত মৌসুমে পানির গভীরতা কমলেও বর্ষাকালে নদী হয়ে উঠত প্রাণবন্ত বাণিজ্যপথ।
পাকিস্তান আমলে নদীর গুরুত্ব
পাকিস্তান আমলেও নদীর গুরুত্ব ছিল অক্ষুণ্ণ। খুলনা বন্দর এবং ভৈরব নদীপথে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য যেমন বজায় ছিল, তেমনি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বাণিজ্যও চলত। খুলনা-যশোরের শিল্পোৎপাদন, চাল-গুঁড়-আখের রপ্তানি এই নদীর ওপর নির্ভরশীল ছিল।
বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর
বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভৈরব নদীর গুরুত্ব কিছুটা কমে এলেও এটি এখনও খুলনা অঞ্চলের কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনের সেচের মূল উৎস। খুলনা বন্দরকে মোংলা বন্দরের সঙ্গে, অভ্যন্তরীণ নদীপথকে ভারত-বাংলাদেশ প্রটোকল রুটের সঙ্গে সংযুক্ত করার বড় সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এই নদীকে।
নদীর জলজ সম্পদ
ভৈরব নদীতে একসময় ছিল প্রাকৃতিক মিঠা পানির মাছের আধার। রুই, কাতলা, ইলিশ (উজানে ঢুকে যাওয়া), টেংরা, পুঁটি, শোল, গজার প্রচুর ধরা পড়ত। নদীর তীরের বনাঞ্চল (বিশেষ করে সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায়) ছিল মাছ, কাঁকড়া, মৌচাক, কাঠের উৎস। তবে দূষণ, পলিমাটি জমে যাওয়া ও নাব্যতা হারানোর কারণে এই জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির মুখে।

নৌযোগাযোগ ও অভ্যন্তরীণ বন্দর সংযোগ
ভৈরব নদী খুলনা বন্দরকে যশোর, নওয়াপাড়া, সাতক্ষীরা, পাইকগাছা, সুন্দরবনসহ পশ্চিম বাংলাদেশের অনেক জেলার সাথে যুক্ত করেছিল। এখান থেকে নৌযান চলত কলকাতা, চট্টগ্রাম এমনকি আসাম পর্যন্ত। স্বাধীনতার পর ভারত-বাংলাদেশ প্রটোকল রুটে খুলনা থেকে কলকাতা পর্যন্ত যাত্রী ও পণ্য নৌযান চলাচলের কথাও নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে।
নদীকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ও গান
ভৈরব নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা মানুষের জীবনযাপন ছিল নদীকেন্দ্রিক। কৃষিকাজ, মৎস্য শিকার, নৌযাত্রা, মালামাল আনা-নেওয়া সব কিছুতেই নদী ছিল প্রধান সহায়ক। নদীপাড়ের মানুষ গাইত বাউল, ভাটিয়ালি, পল্লীগীতি। নদীর বুকে পালতোলা নৌকা চলার সময় মাঝিরা গাইত।
“ও ভাটির দিকে যাইও না রে বন্ধু, ভৈরব নদীর টান
প্রাণ নিয়া যাবে টানি, হায় রে মাঝির গান।”
এমন গান নদীর স্রোতের মতোই বয়ে গেছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

নদীর অবক্ষয় ও সম্ভাবনা
বর্তমানে নদীর নাব্যতা কমেছে, দূষণ বেড়েছে, অবৈধ দখল, বাধ, চাষাবাদে রাসায়নিক ব্যবহার এর স্বাভাবিক প্রবাহ নষ্ট করছে। তবুও এই নদী বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জীবনরেখা। খুলনা বন্দর, মোংলা বন্দর, অভ্যন্তরীণ নৌপথ, ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য সব কিছুর জন্যই এই নদীর পুনর্গঠন ও ড্রেজিং অপরিহার্য।
দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের নাড়ি
ভৈরব নদী শুধু একটি নদী নয়—এটি ইতিহাস, বাণিজ্য, জীবনযাপন, সংস্কৃতি আর মানুষের নাড়ির টান। দুই শত বছরেরও বেশি সময় ধরে এই নদী বহমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জীবনে। তার পাড়ে গড়ে উঠেছে সভ্যতা, বাণিজ্য, শিল্প, গান আর মানুষের ভালোবাসা। সঠিক নীতিমালা ও সবার সচেতনতাই পারে এই নদীকে আবার প্রাণবন্ত করে তুলতে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট