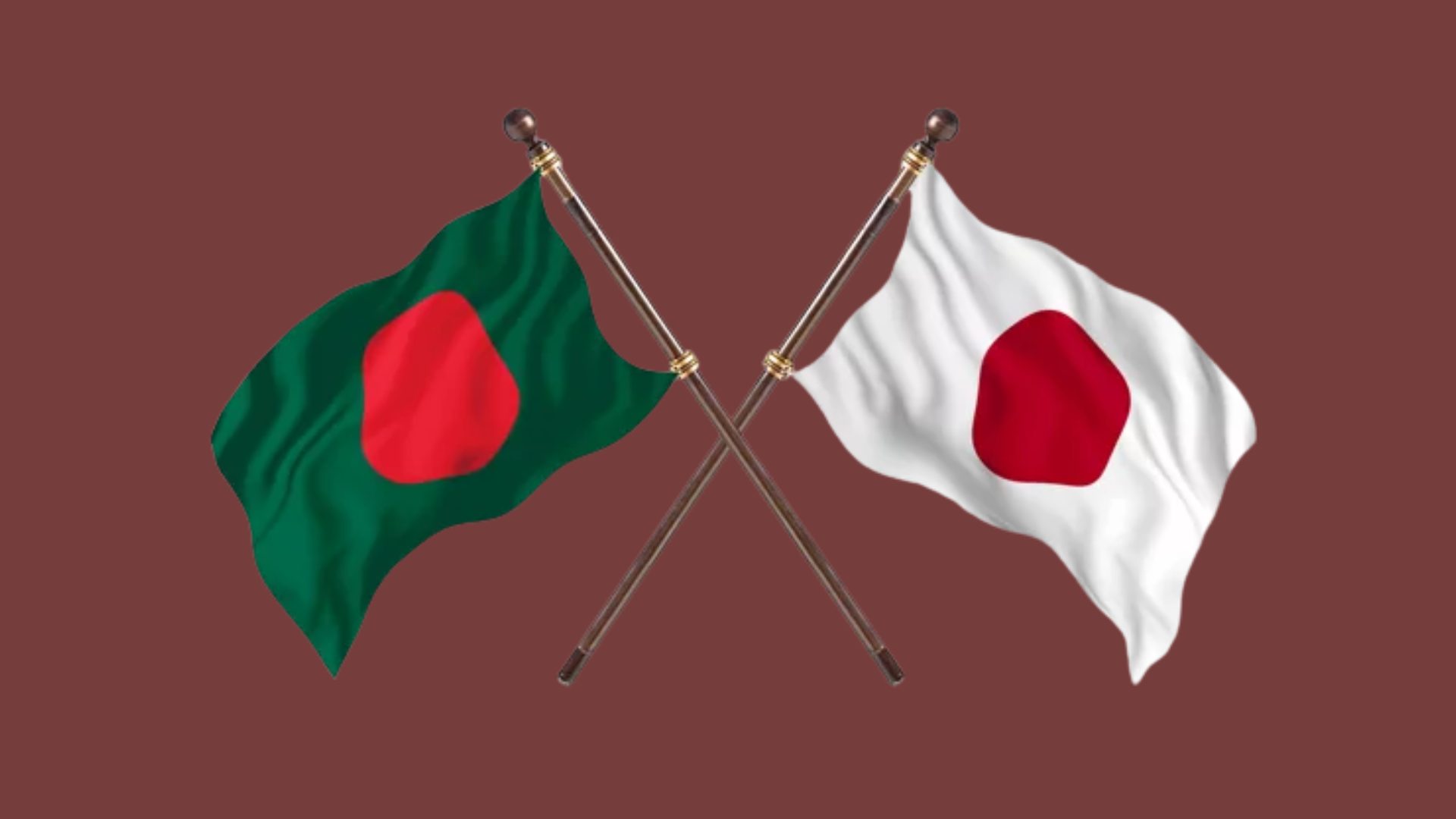দুই প্রেক্ষাপট, দুই মনোভাব
জেনারেশন জেড—যাদের জন্ম ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে—তারা এখন বিশ্ব রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই প্রজন্মের রাজনৈতিক ঝোঁক দেশভেদে ভিন্ন ধারা অনুসরণ করছে। যুক্তরাষ্ট্রে জেনারেশন জেড-এর বহু পুরুষ যেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুঁজিবাদী, ডানপন্থী রাজনীতিকে সমর্থন করছে, সেখানে বাংলাদেশের জেনারেশন জেড পুরুষদের একটি বড় অংশ ধর্মীয় রক্ষণশীলতাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। কেন এই ফারাক? কী ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতির ভিন্নতা এই পার্থক্য সৃষ্টি করেছে?
আমেরিকায় ট্রাম্প-ঝোঁক: অর্থনৈতিক স্বপ্নের রাজনীতি
যুক্তরাষ্ট্রে জেনারেশন জেড পুরুষদের অনেকে ট্রাম্প-পন্থী হয়ে উঠেছে মূলত ব্যক্তিগত অর্জন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং “ওয়োক” সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে। তাদের কাছে ট্রাম্প এমন একজন রাজনীতিক, যিনি আমেরিকান স্বপ্ন—নিজের চেষ্টায় সফল হওয়ার স্বপ্ন—কে বাস্তবায়ন করতে বলেন। তারা মনে করে, সরকার যত কম হস্তক্ষেপ করবে, ব্যক্তি তত বেশি উন্নতি করতে পারবে। পুঁজিবাদের এই আদর্শে তারা মুক্তবাজার, উদ্ভাবন এবং কর কমানোর পক্ষপাতী।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট: ধর্ম ও সামাজিক রক্ষণশীলতা
বাংলাদেশে জেনারেশন জেড-এর পুরুষদের রাজনৈতিক ঝোঁক ভিন্ন এক পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে। অনেকেই স্কুল বা কলেজ জীবনে ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাব এবং পরিবারের সামাজিক রীতিনীতির মাধ্যমে একটি রক্ষণশীল চিন্তাচেতনার মধ্যে বেড়ে উঠছে। বিশেষত, ইন্টারনেট ও ইউটিউবের মাধ্যমে নানা ধর্মীয় বক্তাদের প্রবেশ সহজ হয়েছে, যা তরুণদের ওপর ধারাবাহিক প্রভাব ফেলছে।
এছাড়া, দেশের রাজনৈতিক স্থবিরতা ও দুর্নীতির বাস্তবতায় অনেক তরুণ মনে করে, রাজনৈতিক আদর্শ নয়, ধর্মীয় শাসনই হতে পারে ন্যায়ের উপায়। ফলে তারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে সমর্থন করতে শুরু করেছে।
শিক্ষা ও নাগরিক সচেতনতার ব্যবধান
যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাধীন মত প্রকাশ, বিতর্ক এবং সমালোচনার সংস্কৃতি প্রচলিত। ফলে তরুণরা রাজনৈতিক চিন্তায় বৈচিত্র্য অর্জনের সুযোগ পায়। অন্যদিকে, বাংলাদেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনো অনুশাসননির্ভর, যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত। এ কারণে অনেক তরুণই পারিবারিক ও সামাজিক বিশ্বাসকেই চূড়ান্ত সত্য হিসেবে ধরে নেয়।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বনাম সাংস্কৃতিক পরিচয়
আমেরিকায় জেনারেশন জেড পুরুষরা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিয়ে বেশি চিন্তিত। তাই তারা এমন রাজনীতিককে সমর্থন করে, যিনি চাকরির নিরাপত্তা, কর ছাড় এবং ব্যবসাবান্ধব নীতির কথা বলেন। বাংলাদেশের তরুণদের একটি অংশ অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তার চেয়ে নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রশ্নকে বড় করে দেখে। ফলে তারা ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে সমাজে নৈতিক শৃঙ্খলা প্রত্যাশা করে।
সামাজিক মিডিয়া ও ‘ইকো চেম্বার’ প্রভাব
উভয় দেশে সামাজিক মিডিয়া একটি বড় ভূমিকা পালন করছে। তবে মার্কিন তরুণরা বিভিন্ন চিন্তাধারার একাধিক উৎস থেকে তথ্য পায়, যেখানে বাংলাদেশের তরুণদের একটি বড় অংশ নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় বা আদর্শিক ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল বা ইনফ্লুয়েন্সার-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। এতে একটি ‘ইকো চেম্বার’ তৈরি হয়, যার মাধ্যমে তারা ভিন্ন মত গ্রহণের বদলে আরও রক্ষণশীল হয়ে ওঠে।

সমাজ, পরিবার ও শিক্ষা
জেনারেশন জেড-এর মধ্যে এই ভিন্ন রাজনৈতিক ও আদর্শিক প্রবণতা সমাজ, শিক্ষা, পরিবার ও গণমাধ্যম ব্যবস্থার পার্থক্যের প্রতিফলন। আমেরিকার পুঁজিবাদপন্থী জেন জেড পুরুষদের কাছে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ হলেও, বাংলাদেশের জেন জেড পুরুষরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে ধর্ম, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং নৈতিক শুদ্ধতাকে। এই বিভাজন শুধু আদর্শগত নয়—এটি দুই সমাজের ভিন্ন বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ কল্পনার প্রতিচ্ছবিও।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট