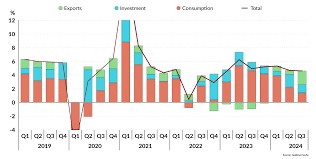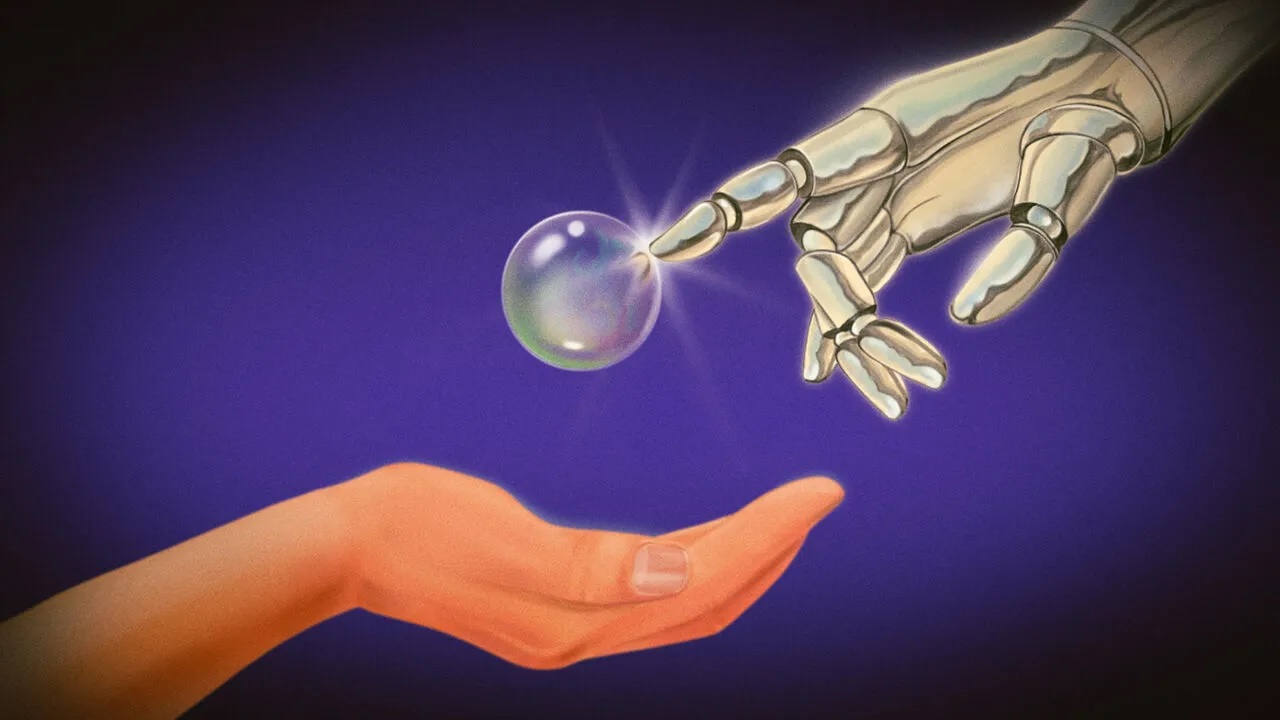২০২৫ সালে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরের সম্ভাবনা ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে। এই চুক্তির মাধ্যমে ভারত ইউরোপের বাজারে তার তৈরি পোশাক ও বস্ত্র (টেক্সটাইল) পণ্য শুল্কমুক্তভাবে রপ্তানি করতে পারবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতের অন্যতম প্রধান বাজার। বর্তমানে বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাধারণ বাণিজ্য সুবিধা (জিএসপি) ব্যবস্থার আওতায় শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাচ্ছে, যা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা হিসেবে কাজ করেছে।
তবে ভারত একই ধরনের শুল্কমুক্ত সুবিধা পেয়ে গেলে ইউরোপীয় বাজারে বাংলাদেশের তুলনায় ভারতের পণ্য প্রবেশে আর কোনো শুল্ক-সংক্রান্ত বাধা থাকবে না। এতে উভয় দেশ সমান প্রতিযোগী হিসেবে দাঁড়াবে এবং প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হবে। ভারতের টেক্সটাইল শিল্প অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, বিনিয়োগে এগিয়ে এবং উৎপাদনে অধিক দক্ষ। তাদের উৎপাদন খরচ কম, বাজার বৈচিত্র্যে অভিজ্ঞতা বেশি। ফলে তারা কম দামে গার্মেন্টস সরবরাহ করতে পারবে এবং ইউরোপের ক্রেতাদের কাছে বাংলাদেশের তুলনায় আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্য একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রথমত, ইউরোপীয় বাজারে বাংলাদেশের বাজার ভাগ (মার্কেট শেয়ার) হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে কম মূল্যের পণ্য—যেমন টি-শার্ট, সোয়েটার, নারীদের সস্তা পোশাক—এসব ক্ষেত্রে ভারতীয় পণ্য প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, মূল্য ও মান—উভয় দিক থেকেই বাংলাদেশের উৎপাদকরা চাপে পড়বেন। শুল্কমুক্ত সুবিধা হারালে, বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতকে আরও উন্নত প্রযুক্তি, দ্রুত উৎপাদন এবং উচ্চ মানের দিকে অগ্রসর হতে হবে। এই উন্নয়নমূলক পদক্ষেপগুলো সময়সাপেক্ষ ও বিনিয়োগনির্ভর, যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।
তৃতীয়ত, যখন ভারত শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে, তখন ইউরোপীয় ক্রেতাদের মধ্যে প্রশ্ন উঠবে—“একই পণ্য যদি ভারত থেকে কম দামে পাওয়া যায়, তবে কেন বাংলাদেশ থেকে কেনা হবে?” এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারলে, অর্ডার সরাসরি ভারতের দিকে সরে যেতে পারে।
এদিকে বাংলাদেশ এখনও জিএসপি সুবিধার আওতায় রয়েছে। তবে ২০২৬ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা হারানোর সম্ভাবনা থাকায় এই সুবিধা ঝুঁকিতে পড়বে। উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তরণ ঘটলে, বাংলাদেশকে নতুন করে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে, এবং হয়তো আগের মতো জিএসপি সুবিধা আর বজায় থাকবে না। অন্যদিকে ভারত যদি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে স্থায়ী শুল্কমুক্ত সুবিধা পেয়ে যায়, তাহলে বাংলাদেশ আগের তুলনায় পিছিয়ে পড়বে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটিই ট্রেড ডাইভারশনের বাস্তবতা—যেখানে বৃহৎ অর্থনীতি তুলনামূলক ছোট অর্থনীতিকে চাপের মুখে ফেলে।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের করণীয় হলো: ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে একটি নিজস্ব দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির উদ্যোগ নেওয়া, যা গার্মেন্টস পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা অব্যাহত রাখবে। একই সঙ্গে প্রয়োজন মান উন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদনের মাধ্যমে ইউরোপীয় মানদণ্ড পূরণ করা, যাতে অ-শুল্ক বাধাও অতিক্রম করা যায়। পাশাপাশি নতুন বাজারের সন্ধান করতে হবে—যেমন দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার উদীয়মান অর্থনৈতিক ব্লকে রপ্তানি সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।
প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে গার্মেন্টস শিল্পে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে এবং আরও দ্রুত ও দক্ষ সরবরাহ চেইন গড়ে তুলতে হবে। কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদন ও সরবরাহ—এই তিন ধাপে গতিশীলতা আনতে হবে।
সর্বোপরি, ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এই চুক্তি কার্যকর হলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প, যা জাতীয় অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি, নতুন প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে। এখনই কার্যকর প্রস্তুতি গ্রহণ না করলে, বাংলাদেশ ইউরোপীয় বাজারে তার প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান হারাতে পারে। এর প্রভাব পড়বে রপ্তানি আয়, কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে। তাই এখনই সময়—রাষ্ট্রীয় কৌশল, শিল্প সমন্বয় ও কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এগিয়ে যাওয়ার।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট