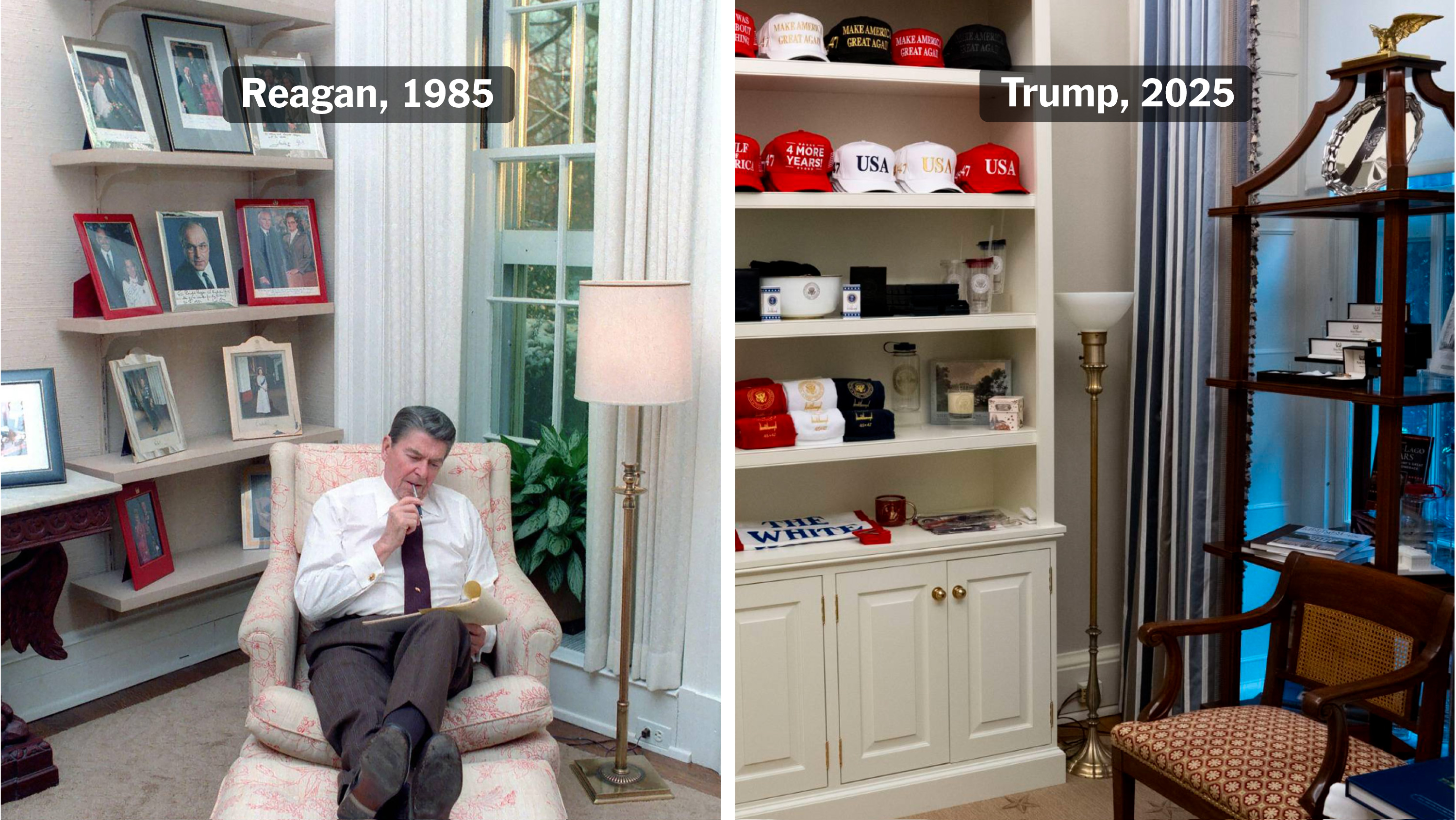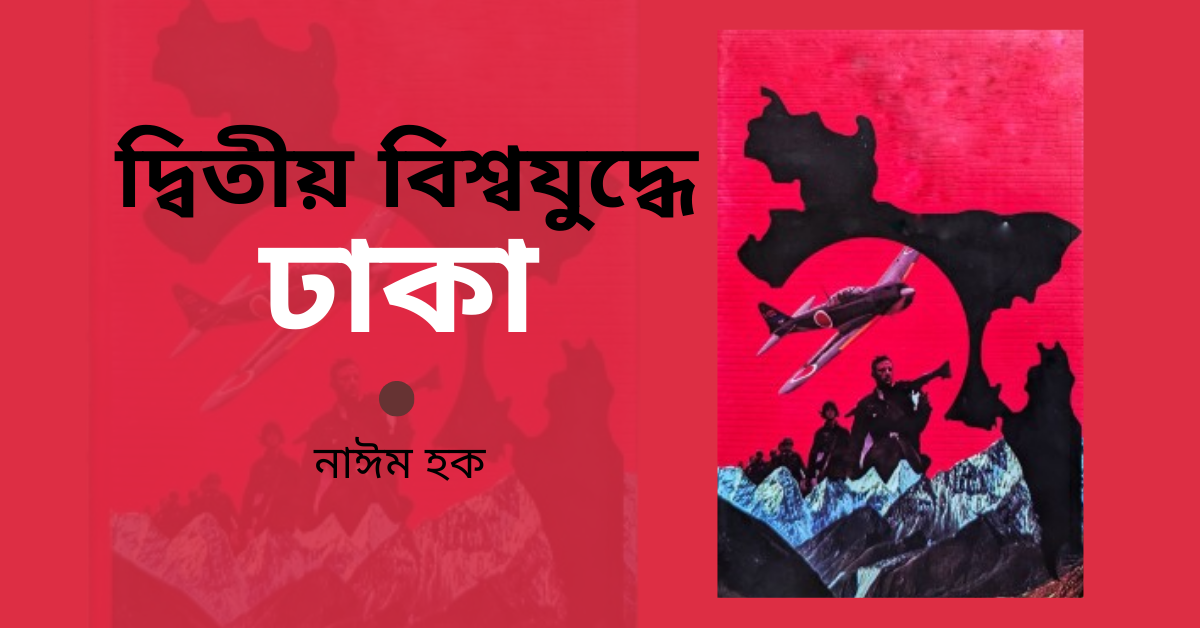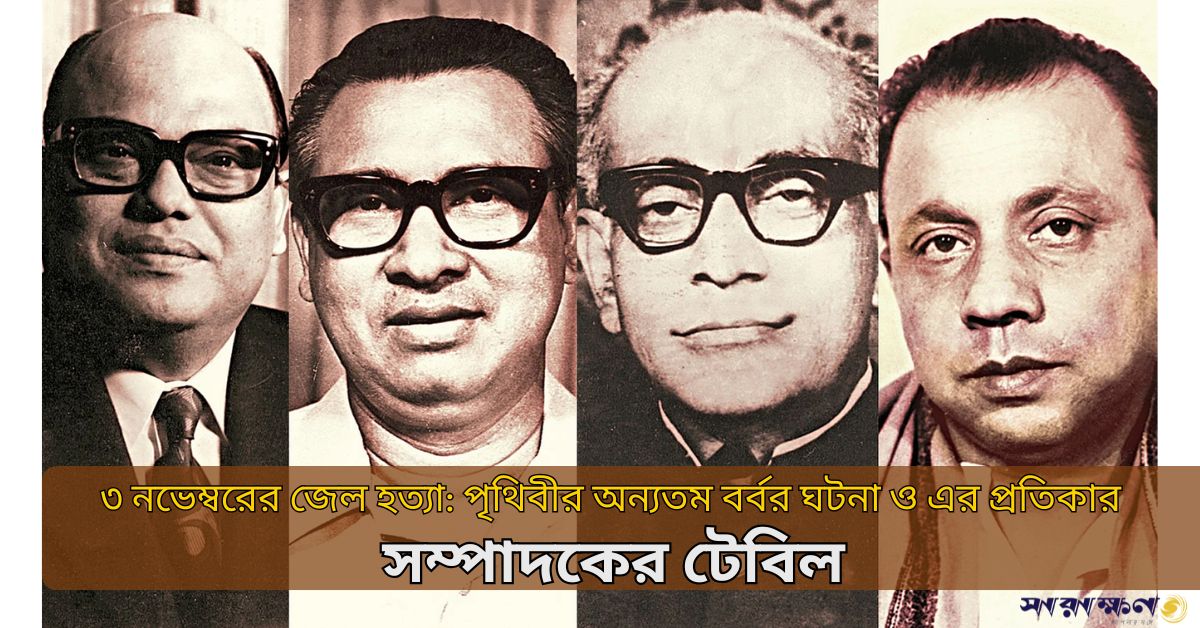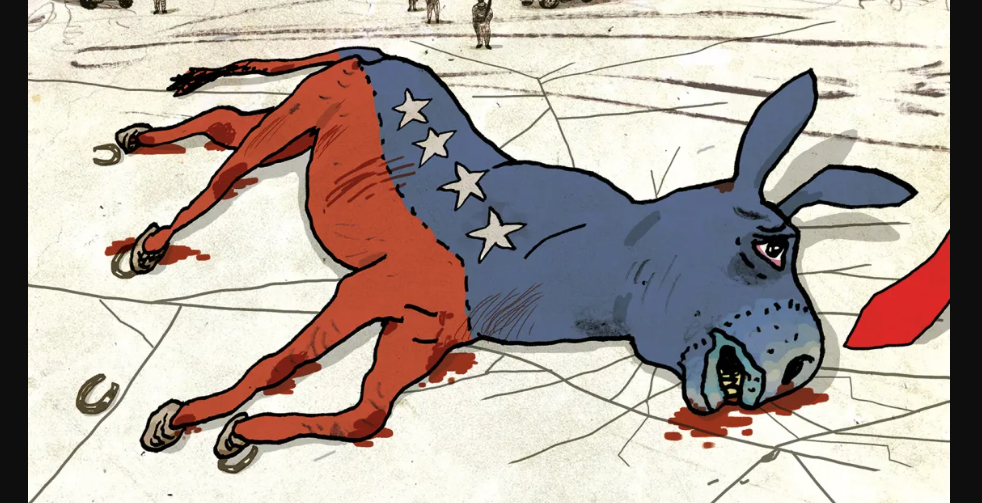চা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান
বাংলাদেশে চা উৎপাদনের ইতিহাস প্রায় ১৮০ বছরের পুরনো। সিলেটের মালনীছড়া চা বাগান থেকে শুরু হয়ে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চা উৎপাদন বিস্তৃত হয়েছে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশে চা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১০৩ মিলিয়ন কেজি, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ উৎপাদনের রেকর্ড। এটি ২০২২ সালের তুলনায় প্রায় ৯.৭ শতাংশ বেশি। এর আগে ২০২২ সালে উৎপাদন হয়েছিল ৯৩.৮৩ মিলিয়ন কেজি।
বাংলাদেশ চা বোর্ড জানিয়েছে, ২০২৪ সালে দেশের মোট উৎপাদন ১০৮ মিলিয়ন কেজি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রতিবছর গড়ে উৎপাদনের হার ৩.৫ থেকে ৪ শতাংশ হারে বাড়ছে।

স্থানীয় বাজারে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি
চা বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শহর হোক বা গ্রাম, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানুষের চা খাওয়ার অভ্যাস দিন দিন আরও দৃঢ় হচ্ছে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে প্রায় ৯২.১৫ মিলিয়ন কেজি চা ভোগ হয়েছে। অর্থাৎ মোট উৎপাদনের প্রায় ৯৫ থেকে ৯৮ শতাংশ চা দেশেই ব্যবহৃত হচ্ছে।
স্ট্যাটিস্টা-এর একটি পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত চায়ের স্থানীয় বাজারে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হবে প্রায় ৮.৫৩ শতাংশ (CAGR)। এই প্রবণতা ইঙ্গিত দেয় যে ভবিষ্যতে দেশের মানুষ চা আরও বেশি পরিমাণে ভোগ করবেন, ফলে চা উৎপাদনের ওপর চাপ আরও বাড়বে।
কেন বাড়ছে চায়ের স্থানীয় চাহিদা?
স্থানীয়ভাবে চায়ের চাহিদা বাড়ার পেছনে কয়েকটি প্রধান কারণ রয়েছে:
জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আর্থিক সক্ষমতা বাড়া: দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিস্তার এবং কর্মজীবীদের সংখ্যা বাড়ছে। ফলে অফিস, দোকান, বাসাবাড়ি—সবখানেই চা একটি সামাজিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।
সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতি: বাংলাদেশের চায়ের সঙ্গে আবেগ ও অভ্যাস জড়িত। অতিথি আপ্যায়ন, বন্ধুবান্ধবের আড্ডা কিংবা ব্যবসায়িক আলোচনায় চা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সহজলভ্যতা ও স্বল্পমূল্য: তুলনামূলকভাবে চা দেশের অন্যান্য পানীয়ের চেয়ে অনেক সস্তা ও সহজলভ্য, ফলে নিম্ন আয়ের মানুষরাও সহজে এটি ভোগ করতে পারেন।
চায়ের দোকান-সংস্কৃতি: শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত রাস্তার পাশে ছোট ছোট চায়ের দোকান সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই দোকানগুলো শুধু চা বিক্রির স্থান নয়, বরং সামাজিক মিলনমেলা হয়ে উঠেছে।
রপ্তানির তুলনায় স্থানীয় বিক্রি কি বেশি লাভজনক?
বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদিত চায়ের মাত্র ১ থেকে ৩ শতাংশ রপ্তানি করা হয়। অর্থাৎ, মোট উৎপাদনের প্রায় ৯৭ থেকে ৯৯ শতাংশ দেশেই বিক্রি হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ সালে মাত্র ১.০৪ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি হয়েছে। অন্যদিকে বাকি অংশ স্থানীয় বাজারে চলে গেছে।
রপ্তানির তুলনায় স্থানীয় বাজারে চা বিক্রি অনেকটাই লাভজনক। কারণ:
- • রপ্তানির জন্য প্রতিযোগিতা বেশি;আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের দার্জিলিং বা শ্রীলঙ্কার সিলন চায়ের তুলনায় বাংলাদেশের চা এখনো ততটা প্রতিযোগী নয়।
- • স্থানীয় চা বাজার চিরস্থায়ী ও স্থিতিশীল;প্রতিদিনের ব্যবহার ও স্বল্প দামের কারণে দেশের অভ্যন্তরে বিক্রির নিশ্চয়তা বেশি।
- • রপ্তানির খরচ বেশি;আন্তর্জাতিক মানের প্যাকেজিং, পরিবহন, শুল্ক ইত্যাদি ব্যয় যুক্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই লাভজনকতা কমে যায়।
তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি বাংলাদেশের চা গুণগত মানে উন্নত করা যায় এবং বাজার সম্প্রসারণের কৌশল নেওয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতে রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হবে।

উৎপাদনের সঙ্গে বাড়ছে চাষ এলাকা
বাংলাদেশে বর্তমানে ১৬৮টির বেশি চা বাগান রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চা উৎপাদন হয় সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে। সম্প্রতি পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও লালমনিরহাটে ছায়া-চাষ পদ্ধতিতে (ছোট পরিসরের চা চাষ) চায়ের উৎপাদন বাড়ছে, যা দেশের চা শিল্পের বিস্তারে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।
রপ্তানিতে অংশগ্রহণ
বাংলাদেশের চা শিল্প বর্তমানে একটি স্থিতিশীল ও ক্রমবর্ধমান খাতে রূপ নিয়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছে, এবং উৎপাদনও সে অনুযায়ী বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও রপ্তানিতে বাংলাদেশ এখনও পিছিয়ে, তবে স্থানীয় বাজারে বিক্রি যে পরিমাণ লাভজনক তা বর্তমান বাজার প্রবণতায় স্পষ্ট।
ভবিষ্যতে উৎপাদন বাড়িয়ে ও গুণগত মান উন্নত করে রপ্তানিতে অংশগ্রহণ বাড়ানো সম্ভব। তবে বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেই চা শিল্প সর্বাধিক লাভজনক ও টেকসই অবস্থানে রয়েছে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট