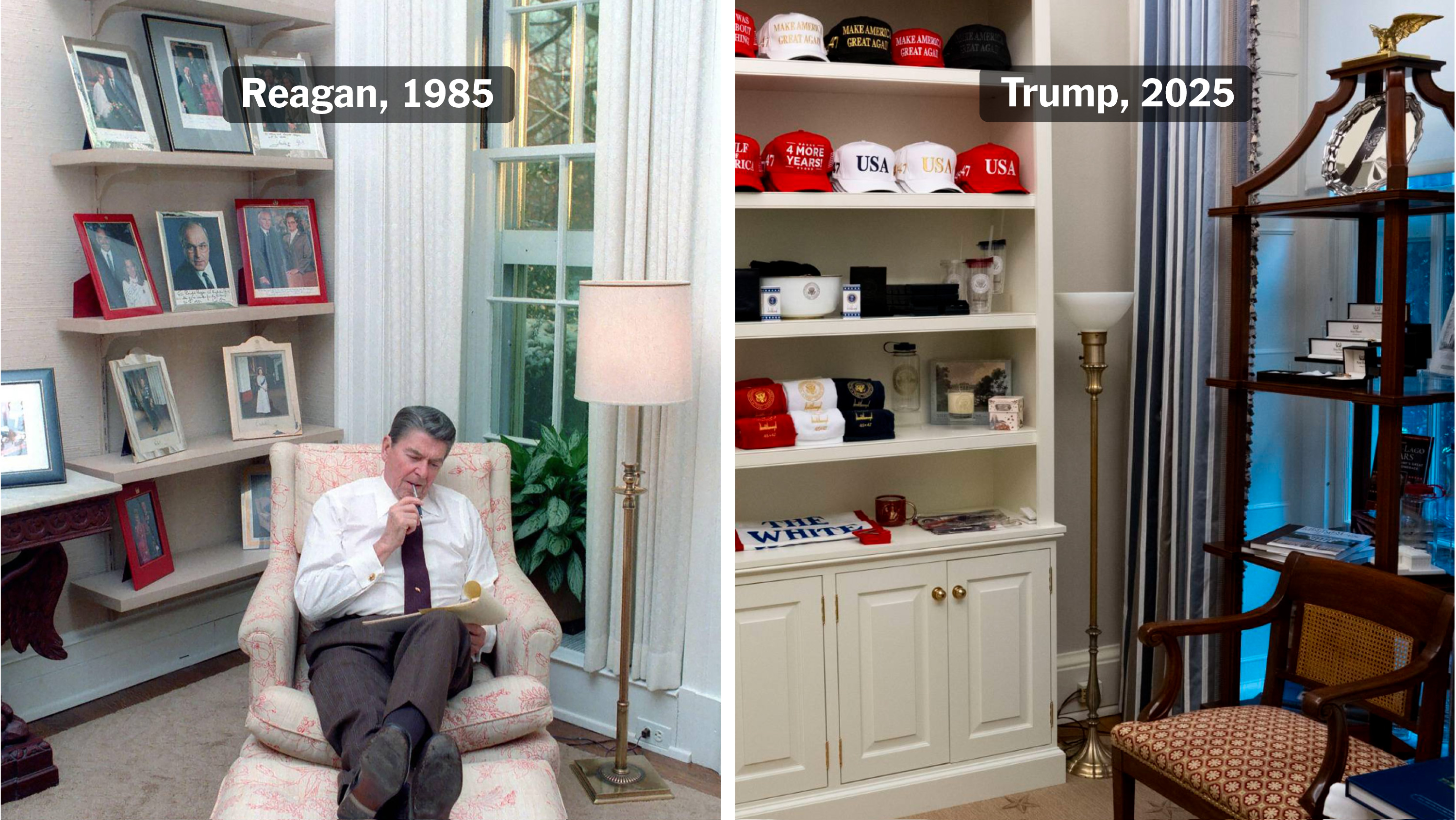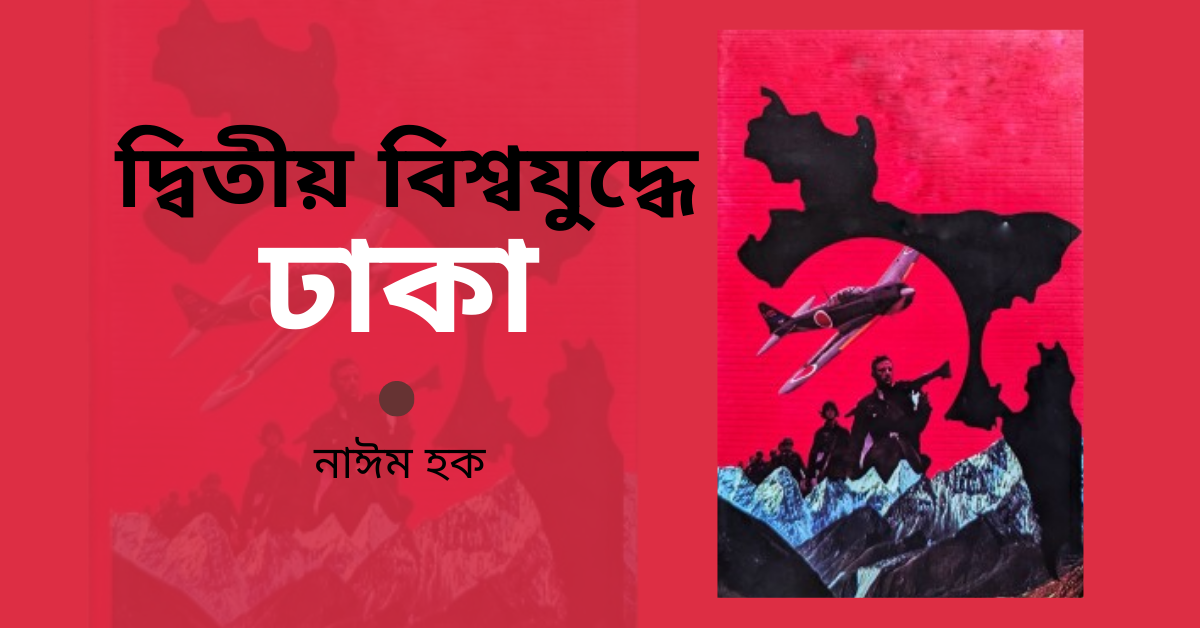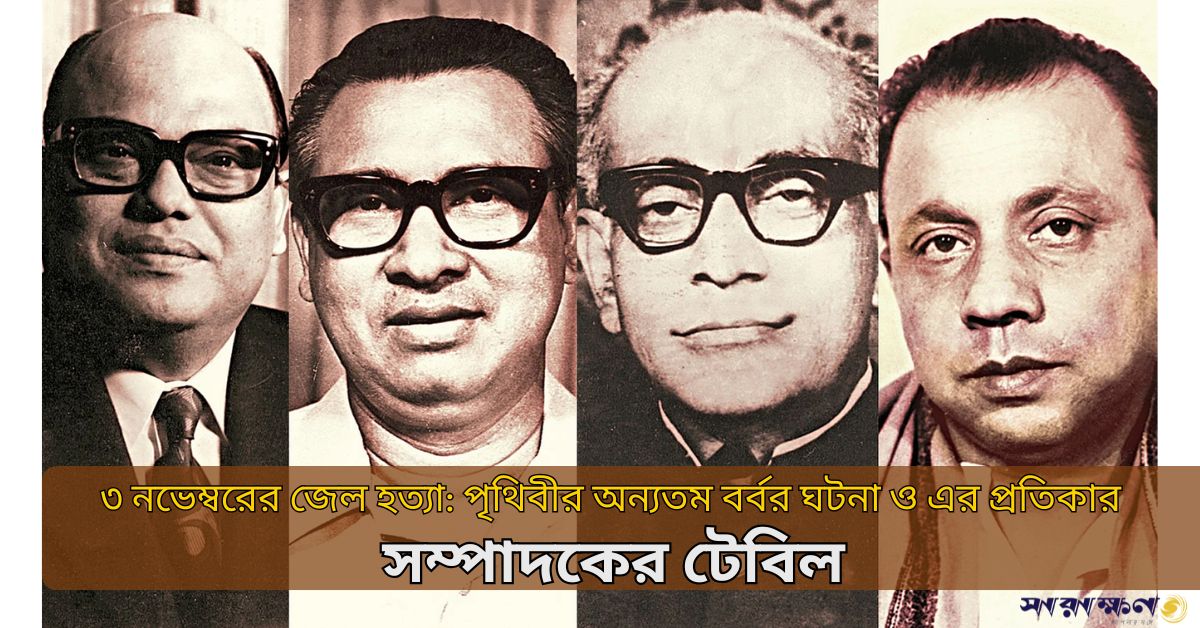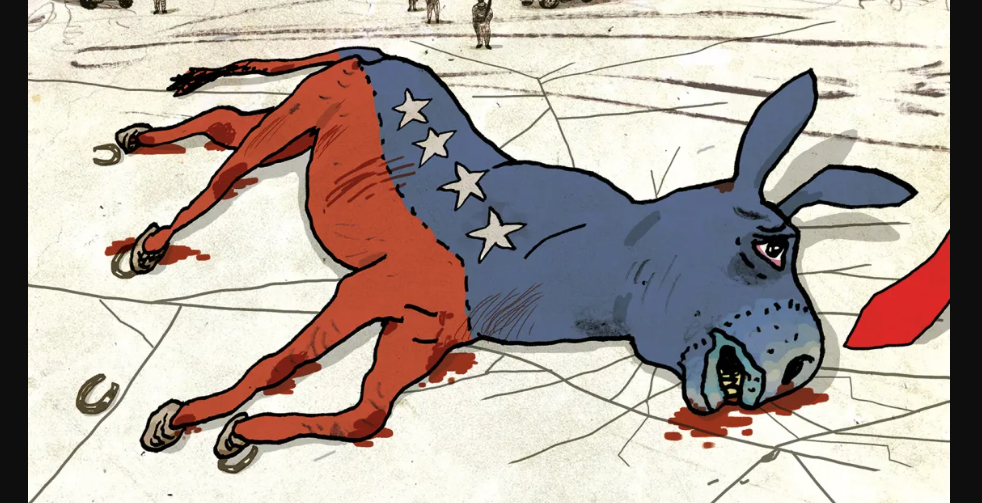উৎস ও প্রাচীন পরিচয়
জলঢাকা নদী একটি আন্তঃদেশীয় নদী, যার উৎপত্তি ভারতের সিকিম রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় হিমালয়ের বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে। প্রাচীনকালে এই নদীকে ‘দেহচু’ নামে ডাকা হতো। তিব্বতি ভাষায় “চু” অর্থে নদী। দেহচু নামটি ছিল সিকিম ও ভুটানের কিছু অংশে প্রচলিত, যার বাংলা অনুবাদ দাঁড়ায় ‘দেহনদী’। পরবর্তীকালে নদীটি পশ্চিমবঙ্গ অতিক্রম করার সময় এর নাম হয়ে যায় ‘জলঢাকা’, যার মানে দাঁড়ায় ‘জলভরা’। এই নামকরণ সম্ভবত নদীর প্রবল জলধারার কারণেই।
নদীর প্রবাহপথ ও বাংলাদেশে প্রবেশ
জলঢাকা নদী ভারতের সিকিম থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা অতিক্রম করে। এরপর নদীটি বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলায় প্রবেশ করে। এই উপরের এলাকা থেকেই নদীর নামের সাথে ‘জলঢাকা’ শব্দটি মিল রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।
ভারতের দুইটি রাজ্য (সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ) কিছু সীমান্তবর্তী অংশে ভুটান এবং বাংলাদেশের একটি বিভাগ (রংপুর) ও অন্তত তিনটি জেলা (নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট) নদীটির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবাহ ও জলধারার শেষ গন্তব্য
বাংলাদেশে প্রবেশের পর নদীটি মূলত নীলফামারীর জলঢাকা, ডোমার ও ডিমলা উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। এরপর এটি লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ ও হাতীবান্ধা উপজেলায় গিয়ে তিস্তা নদীতে মিশে যায়। অর্থাৎ, জলঢাকার পানি শেষ পর্যন্ত তিস্তা নদীতে মিশে বৃহত্তর নদীনীতির অংশ হয়ে পদ্মা-মেঘনা অববাহিকার দিকে চলে যায়।
ব্যবসা ও যোগাযোগে জলঢাকা নদীর ঐতিহাসিক ভূমিকা
প্রাচীনকাল থেকেই জলঢাকা নদী স্থানীয় ব্যবসা, কৃষিকাজ এবং যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম ছিল। নদীটির দুই পাড়ে ছোট ছোট নৌবন্দর ও গঞ্জ গড়ে উঠেছিল, যেমন—ডোমার ঘাট, বোড়াগাড়ী ঘাট ইত্যাদি। চাষীরা নদী দিয়ে সার, শস্য ও কাঠ পরিবহন করত, আর মাছ ব্যবসায়ীরাও নদীপথেই মাছ পাঠাত দূর-দূরান্তে। নদীটি বিশেষত বর্ষাকালে ছোট ট্রলার ও নৌকার মাধ্যমে দুই পাড়ের মানুষের মধ্যে সংযোগ করত।

দুই তীরের জনপদ ও সভ্যতা
জলঢাকার দুই তীরে গড়ে উঠেছে বহু গ্রামীণ জনপদ। নীলফামারীর বোড়াগাড়ী, কেতকিবাড়ি, খগাখড়িবাড়ি, ডোমার, সোনারায় প্রভৃতি গ্রামগুলোর মানুষ নদীকে ঘিরেই জীবন পরিচালনা করে এসেছে। নদী ছিল চাষাবাদ, মৎস্য আহরণ, নৌপরিবহন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উৎস। জলঢাকার তীরে বহু মেলা, নদী উৎসব এবং স্থানীয় গাজীর গানের আসর বসত। এটি একটি লোকজ সংস্কৃতির কেন্দ্রও হয়ে উঠেছিল।
নদীর বর্তমান অবস্থা
বর্তমানে জলঢাকা নদীর অবস্থা অত্যন্ত বিপন্ন। বর্ষাকালে কিছুটা প্রাণ ফিরে পেলেও শুষ্ক মৌসুমে নদীটি প্রায় মৃত হয়ে পড়ে। বালুচরের দখল, নদী খননের অভাব, পাড় ভাঙন ও দখলদারিত্বের ফলে এর স্বাভাবিক প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নদীর গভীরতা কমে যাওয়ায় শুকনো মৌসুমে কৃষিকাজ ও পানির চাহিদা মেটাতে স্থানীয়রা সংকটে পড়ে।

নদীর পানিপ্রবাহের মৌসুমভিত্তিক পরিমাণ
জলঢাকা নদীতে পানির প্রবাহ মৌসুমভেদে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।
- বর্ষাকাল (জুলাই-সেপ্টেম্বর):প্রবাহ সর্বোচ্চ থাকে, জলপ্রবাহের হার প্রায় ২০০-৩৫০ কিউসেক (কিউবিক ফুট/সেকেন্ড) পর্যন্ত পৌঁছায়। এই সময় নদী প্লাবনের ঝুঁকি তৈরি করে।
- হেমন্তকাল ও শীতকাল (অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি):পানি হ্রাস পায়, প্রবাহ কমে প্রায় ৫০-১০০ কিউসেক-এ নেমে আসে। অনেক জায়গায় খালাকৃতির ধারণ করে।
- গ্রীষ্মকাল (মার্চ-জুন):সবচেয়ে কম প্রবাহ থাকে। কোথাও কোথাও পানি একেবারে শুকিয়ে বালুর চর দেখা দেয়।
এই ঋতুভিত্তিক প্রবাহের পরিবর্তনের ফলে কৃষিকাজ, পানি ব্যবহার ও নৌপরিবহনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
হারিয়ে যেতে বসেছে
জলঢাকা নদী শুধু একটি জলপ্রবাহ নয়—এটি ছিল এককালের যোগাযোগের পথ, কৃষি ও বাণিজ্যের আশ্রয়স্থল এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক। কিন্তু বর্তমান অবস্থা সংকটাপন্ন। নদীর দখল, দূষণ ও সংরক্ষণের অভাবে এটি হারিয়ে যেতে বসেছে। এই নদীকে টিকিয়ে রাখতে হলে নিয়মিত খনন, দুই তীরে অবৈধ দখল উচ্ছেদ এবং পানিপ্রবাহ বজায় রাখার কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন। নদীর প্রাণ ফিরলে জীবনের চাকা আবার ঘুরবে নদীতীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট