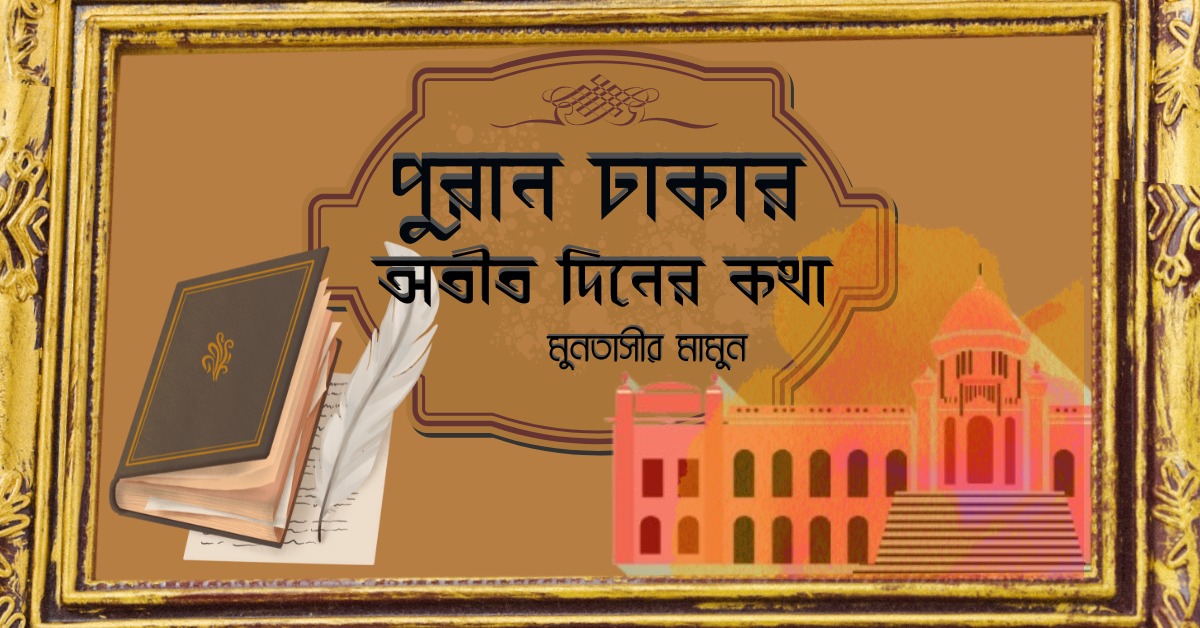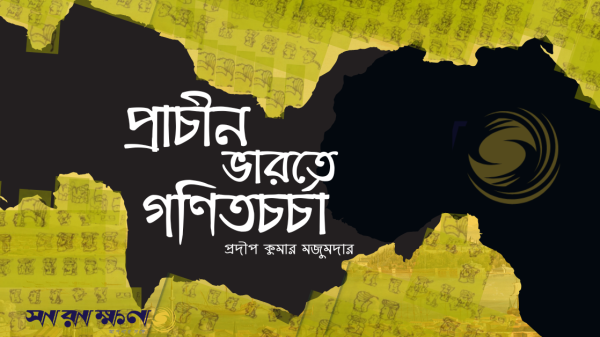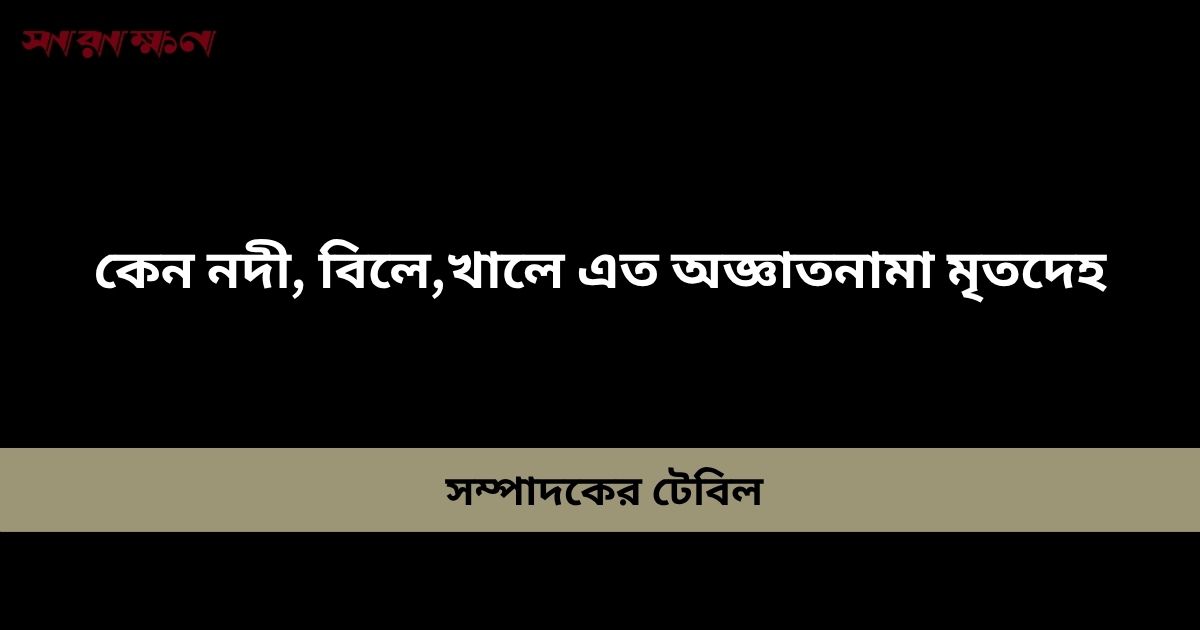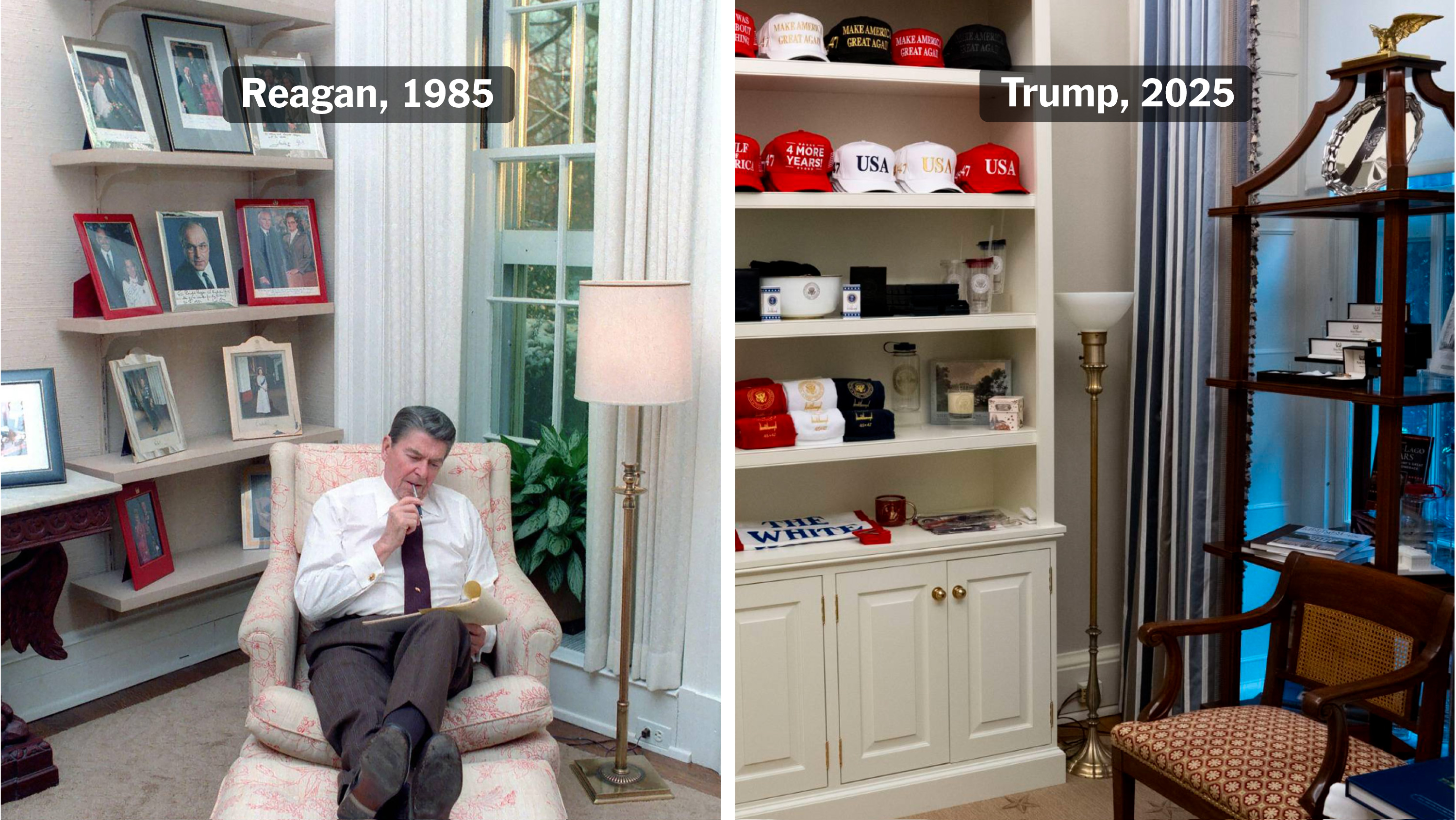বাংলায় ভোঁদড় (স্থানীয় উচ্চারণে ভোদর/ভদর) জলচর মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণী, যাদের প্রধান আবাস নদী, খাল, বিল, ম্যানগ্রোভ বন ও জলাভূমি। বাংলাদেশে ভোঁদড় দিয়ে মাছ ধরা বহু শতাব্দীর লোকজ ঐতিহ্য। কিন্তু প্রজাতির অবস্থা, বিস্তার ও সংখ্যা যেমন বদলাচ্ছে, তেমনি দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে এ বিশেষ মাছ ধরার কৌশলও।
বাংলাদেশ ও বঙ্গ অঞ্চলে ভোঁদড়ের যে প্রজাতিগুলো রয়েছে
১) স্মুথ-কোটেড ভোঁদড় (Lutrogale perspicillata): দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বড় নদী-জলপথে বিপুল সংখ্যক ছিলো। বর্তমানে এদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে গেছে মূলত আইইউসিএন তালিকায় ঝুঁকিপূর্ণ (Vulnerable) প্রাণী অর্থাত্ প্রকৃত সংরক্ষণ না হলে দ্রুত হারিয়ে যাবে । বাংলাদেশে ঐতিহ্যগতভাবে মাছ ধরার কাজে পোষ মানানো হয় এই প্রজাতিকেই।
২) এশিয়ান স্মল-ক্লড ভোঁদড় (Aonyx cinereus): সুন্দরবনসহ এশিয়ার বিভিন্ন ম্যানগ্রোভ ও জলাভূমিতে দেখা যায়। বাংলাদেশের সুন্দরবনে একাধিক দলে উপস্থিতির প্রমাণ রয়েছে।
৩) ইউরেশীয়ান ভোঁদড় (Lutra lutra): ইউরোপ থেকে এশিয়া জুড়ে বিস্তৃত; বাংলাদেশে এখন অত্যন্ত বিরল এবং বিলুপ্তির আশঙ্কায়। স্বাধীনতার পর দেশে উপস্থিতির মাত্র একবার নিশ্চিত প্রমাণ মেলেছে।

বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি সংক্ষেপ
বিশ্বে মোট ১৩ প্রজাতির ভোঁদড় রয়েছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্মুথ-কোটেড ও স্মল-ক্লড প্রজাতি নদী, হাওর ও ম্যানগ্রোভ এলাকায় বাস করে। ইউরেশীয়ান প্রজাতি ইউরোপ-এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে থাকা সত্ত্বেও দূষণ, আবাসস্থল ধ্বংস ও খাদ্যসংকটে বহু এলাকায় কমে গেছে।
বাংলাদেশে কোথায় দেখা যায়
• সুন্দরবন (বিশেষত পূর্বাংশ): স্মল-ক্লড ভোঁদড়ের দল সরাসরি দেখা ও নানা চিহ্নের ভিত্তিতে নিশ্চিত করা হয়েছে।
• দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল—নড়াইল, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও খুলনা: স্মুথ-কোটেড ভোঁদড় পোষ মানিয়ে জেলেরা মাছ ধরায় ব্যবহার করেন। আগে আগে আরো বেশি করতেন।

সংখ্যা: অতীত ও বর্তমান চিত্র
• ২০০–৩০০ বছর আগে: নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই; তবে ভোঁদড়ের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি ছিল এবং ভোঁদড়-সহায় মাছ ধরা বিস্তৃত ছিল।
• সাম্প্রতিক পোষ মানানো ভোঁদড়: ২০২২ সালের এক সমীক্ষায় নড়াইল ও গোপালগঞ্জের ১৫ জেলে পরিবারের কাছে ৩৯টি স্মুথ-কোটেড ভোঁদড় নথিবদ্ধ হয়েছে; গত এক দশকে এই সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে।
• বন্য ভোঁদড়: সুন্দরবনের প্রায় ৩৫১ কিমি জলপথ জুড়ে অন্তত ১৩টি দলে ৫৩টি স্মল-ক্লড ভোঁদড় দেখা গেছে। সারাদেশের মোট সংখ্যার নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া যায় না।
• ইউরেশীয়ান ভোঁদড়: উপস্থিতি অনিশ্চিত; সাম্প্রতিক কিছু ইঙ্গিত থাকলেও সংখ্যা অজানা।
ভোঁদড় দিয়ে মাছ ধরা: পদ্ধতি কী
জেলেরা সাধারণত দুই থেকে তিনটি পোষ মানানো স্মুথ-কোটেড ভোঁদড়কে কোমল দড়ি দিয়ে নৌকার পাশে বেঁধে রাখেন। জাল টেনে এগোনোর সময় ভোঁদড়গুলো পানিতে নেমে মাছ তাড়া করে জালের দিকে ঠেলে আনে। পুরস্কার-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও সংকেত ব্যবহারে এ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। ভোর, সন্ধ্যা বা রাতের আঁধার—এই সময়গুলোতে পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

বর্তমানে ব্যবহারের অবস্থা
পদ্ধতিটি এখন বাংলাদেশে সীমিত আকারে টিকে আছে। নড়াইলের একটি গ্রামে প্রায় পাঁচটি পরিবার এ ঐতিহ্য চালাচ্ছে। খুলনা অঞ্চলে প্রায় বিলুপ্ত; গোপালগঞ্জে কিছু নতুন উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছে। সামগ্রিকভাবে পোষ মানানো ভোঁদড়ের সংখ্যা ও পরিবারের অংশগ্রহণ দ্রুত কমছে।
অতীতে প্রচলিত এলাকা
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী-খালপাড়—বিশেষ করে নড়াইল, খুলনা, বাগেরহাট ও গোপালগঞ্জ—এ এলাকাগুলোর বহু গ্রামে এক সময় ভোঁদড়-সহায় মাছ ধরা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে নড়াইল ও গোপালগঞ্জের কয়েকটি পরিবারে সীমিত আকারে দেখা যায়।
সংকটের মূল কারণ
• আবাসস্থল ধ্বংস ও জলদূষণ
• নদী-খালে মাছের প্রাচুর্য কমে যাওয়া
• আধুনিক ও প্রতিযোগিতামূলক মাছ ধরার কৌশলের বিস্তার
• ভোঁদড় পালনের খরচ, চিকিৎসা ও খাদ্য জোগানের জটিলতা
• জীবিকা পরিবর্তন: অনেক পরিবার বিকল্প পেশায় সরে যাচ্ছে
এই সব কারণে পোষ মানানো ভোঁদড়ের সংখ্যা যেমন কমছে, তেমনি বন্য ভোঁদড়ও একই চাপের মুখে পড়ছে।

সংরক্ষণের করণীয়
• ঐতিহ্য সংরক্ষণ: দক্ষিণ-পশ্চিমে ভোঁদড়-সহায় মাছ ধরা “জীবন্ত ঐতিহ্য” হিসেবে নথিবদ্ধ করা, পরিবারভিত্তিক ভাতা/উদ্দীপনা, প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তা সহায়তা।
• আবাস পুনরুদ্ধার: নদী-খাল পুনঃখনন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, শিকার-নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা এবং মাছের প্রজনন ক্ষেত্র সুরক্ষা।
• বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ: সুন্দরবনে নিয়মিত সমীক্ষা, ক্যামেরা-ট্র্যাপ/ডিএনএ সার্ভে, প্রজাতিভিত্তিক অ্যাকশন প্ল্যান (বিশেষত স্মুথ-কোটেড ও ইউরেশীয়ান) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
• সম্প্রদায়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা: সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি, ঋণ/বিকল্প আয়ের সুযোগ, স্কুলভিত্তিক সচেতনতা কর্মসূচি।
• চিকিৎসা ও উদ্ধার: পোষ মানানো ও বন্য ভোঁদড়ের জন্য ভেটেরিনারি সহায়তা, উদ্ধার-রিহ্যাব সেন্টার ও পুনর্বাসন প্রটোকল।
উপসংহার
বাংলাদেশে তিন প্রজাতির ভোঁদড়ের অস্তিত্ব রয়েছে—স্মুথ-কোটেড, এশিয়ান স্মল-ক্লড ও ইউরেশীয়ান—তবে মোট সংখ্যা অনির্দিষ্ট। সুন্দরবনে স্মল-ক্লড ভোঁদড়ের দল নিশ্চিত হলেও পোষ মানানো স্মুথ-কোটেড দ্রুত কমছে এবং ইউরেশীয়ান প্রায় অদৃশ্য। এখনই সমন্বিত সংরক্ষণ উদ্যোগ না নিলে প্রজাতিগত বৈচিত্র্য যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তেমনি হারিয়ে যাবে আমাদের লোকজ ঐতিহ্য ভোঁদড় দিয়ে মাছ ধরা—যা এই ভূখণ্ডের নদীনির্ভর সংস্কৃতির এক অনন্য অধ্যায়।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট