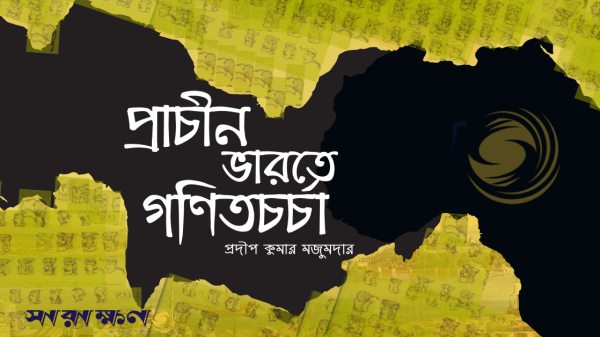২০১৭ সালের গণহত্যা-বিধ্বস্ত প্রত্যাঘাতে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা আজও কক্সবাজার ও ভাসানচরের শিবিরে আটকে আছে। আট বছর অতিবাহিত হলেও কার্যকরি প্রত্যাবাসন হয়নি; মিয়ানমারের রাজনৈতিক অবস্থান ও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত অগ্রিম শর্ত এসব প্রত্যাবাসন পরিকল্পনাকে ধারালোভাবে ঘেঁষে ফেলেছে। ফলে এখন প্রশ্ন—এই অনিশ্চয়তা আরও কয়টি বছর ছড়াবে, নাকি কোনো স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব হবে?
বাংলাদেশ শুরু থেকেই রোহিঙ্গাদের অস্থায়ী আশ্রয় দিয়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা সত্ত্বেও নাগরিকত্ব-নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত গ্যারান্টি না থাকায় প্রত্যাবাসন কার্যকর হয়নি। ফলে শিবিরবাসীর জীবনচক্র দীর্ঘসূত্রি অনিশ্চয়তায় আবদ্ধ হচ্ছে।

রাজনৈতিক পরিবর্তন ও মিয়ানমার বোর্ডের দৃষ্টিভঙ্গি না বদলালে দ্রুত, স্বেচ্ছায় ও নিরাপদ প্রত্যাবাসন কল্পকাহিনিই হয়ে দাঁড়াবে। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো মধ্যস্থতা করলেও বাস্তব নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকার মঞ্জুর না হলে প্রত্যাবাসনের পথ বন্ধই বলে মনে হচ্ছে।
শিবিরে বেড়ে ওঠা কিশোর-কিশোরীরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও নাগরিক পরিচয়ের সুযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন। যদি একই অবস্থা অব্যহত থাকে, তারা স্থায়ী শরণার্থী হিসেবে পরিণত হবে — যে প্রজন্মকে আমরা ‘গাজার প্রজন্মের মতো’ এক চক্রে আটকানো প্রজন্ম হিসেবে দেখতে পারি। এসব তরুণদের মানসিক, সামাজিক ও শৈক্ষিক বিকাশ সংকুচিত হবে।
আন্তর্জাতিক অনুদান কমে আসায় খাদ্য, পানি ও স্বাস্থ্যসেবায় ঘাটতি লক্ষণীয়। আর্থিক সহায়তা হ্রাস পেলে দুর্ভিক্ষ ও জনস্বাস্থ্য সংকটের আশঙ্কা মাথাচাড়া দেবে; শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের ওপর প্রভাব বিশেষভাবে গভীর হবে।
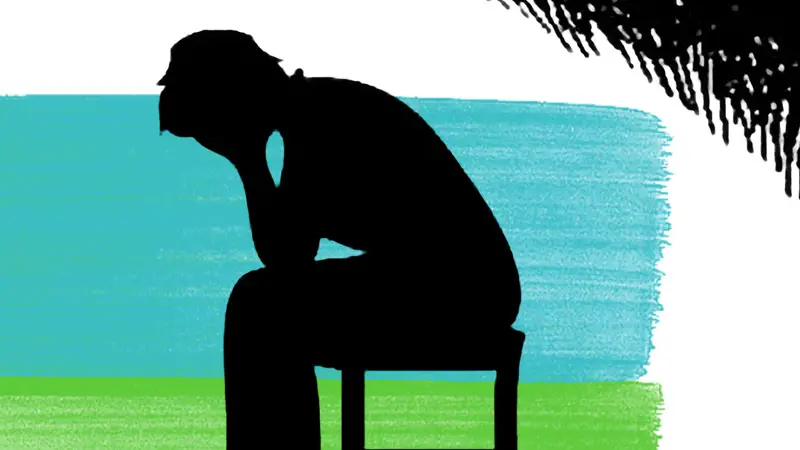
দীর্ঘমেয়াদি বেকারত্ব, হতাশা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মাদক, অপরাধ ও উগ্রতাবাদে জড়িত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। ইতোমধ্যে সীমান্ত অঞ্চলে কিছু অপরাধমূলক ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে—যা আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্যও হুমকি জাগাতে পারে।
সরকার বলছে প্রত্যাবাসনই স্থায়ী সমাধান; কিন্তু বাস্তবে যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে কি স্থানীয়ভাবে অস্থায়ীভাবে মিশিয়ে দেওয়া, নাগরিক সহায়তা ও একটি দীর্ঘমেয়াদি অড-ইনক্লুসিভ নীতি গ্রহণ বা আন্তর্জাতিক শরিকদের সঙ্গে ভাগাভাগি করা ছাড়া আর উপায় অবশিষ্ট থাকবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর রাজনৈতিক, মানবিক ও অর্থনৈতিক সব দিক বিবেচনায় নিতে হবে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট