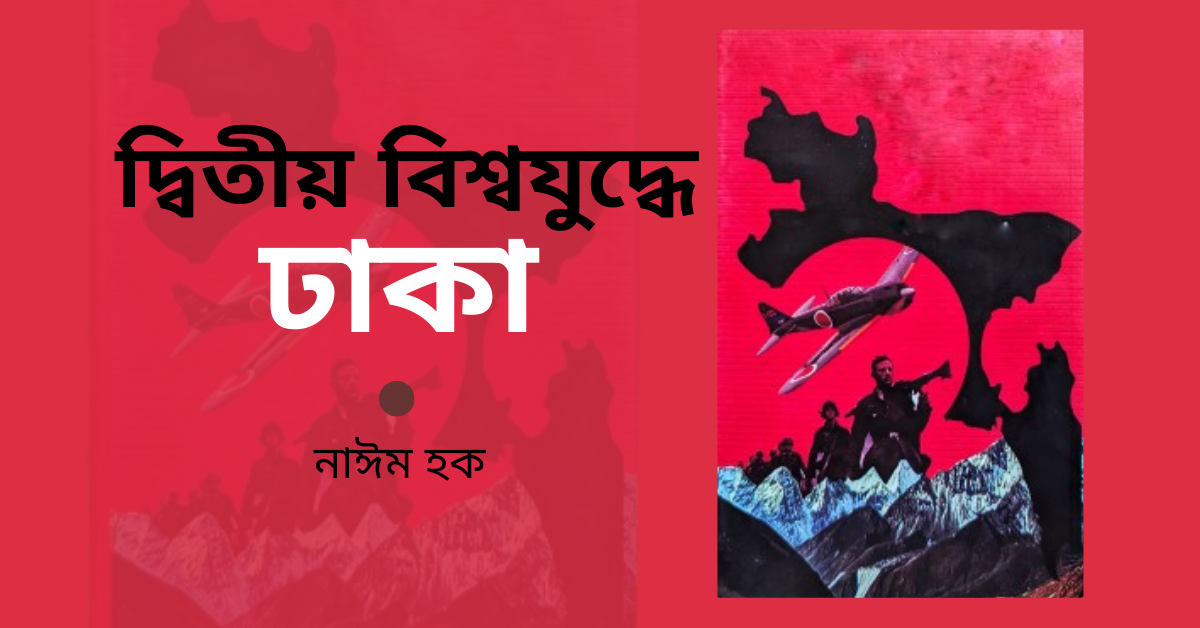বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। কিন্তু শত শত নদীর ভিড়ে কিছু নদী রয়েছে যাদের গুরুত্ব শুধু ভৌগোলিক নয়, বরং ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকও বটে। কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গার বুক চিরে প্রবাহিত মাথাভাঙ্গা নদী তার অন্যতম। পদ্মা থেকে উৎপন্ন হয়ে মাথাভাঙ্গা নদী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশের প্রাণরেখা হয়ে উঠেছে।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
ঔপনিবেশিক আমলে মাথাভাঙ্গা ছিল আঞ্চলিক বাণিজ্যের প্রধান জলপথ। ব্রিটিশ ভারতের কলকাতা বন্দরে কুষ্টিয়া–চুয়াডাঙ্গার পাট, গম, চাল, তামাক এবং মসলাজাত দ্রব্য নৌপথে যাওয়া হতো। পুরোনো নথি ঘেঁটে জানা যায়, ১৮৮০ সালের দিকে নদীর তীরবর্তী এলাকায় অন্তত ২৫টির মতো বড় গুদামঘর ছিল, যেখানে নৌকায় আনা কৃষিপণ্য মজুত হতো।
কুষ্টিয়ার এক প্রবীণ শিক্ষক মজিবর রহমান (৮০) বলছিলেন—
“আমার দাদার সময়েও নৌকা ছিল প্রধান বাহন। মাথাভাঙ্গা নদী না থাকলে কুষ্টিয়ার অর্থনীতি দাঁড়াতই না।”

ভৌগোলিক বিস্তার ও শাখানদীসমূহ
মাথাভাঙ্গা নদীর প্রধান উৎস হলো পদ্মা। পদ্মা থেকে উৎপন্ন হয়ে এটি দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়।
- নবগঙ্গা নদী:ঝিনাইদহ, নড়াইল ও মাগুরার কৃষিজমির সেচের প্রধান উৎস।
- কুমার নদী:মেহেরপুর হয়ে গড়াই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এটি স্থানীয় কৃষকদের কাছে বর্ষাকালের জীবনরেখা।
- চিত্রা নদী:খুলনা ও নড়াইল অঞ্চলে প্রবাহিত হয়ে মৎস্যজীবীদের জীবিকার অন্যতম ভরসা।
এই শাখানদীগুলোর কারণে মাথাভাঙ্গা শুধু একটি নদী নয়, বরং একটি নদীজাল (river network) তৈরি করেছে, যা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতির ভিত রচনা করেছে।
কৃষি ও অর্থনৈতিক অবদান
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় মোট কৃষিজমির প্রায় ৬৫% মাথাভাঙ্গা নদীর পানির ওপর নির্ভরশীল।
স্থানীয় কৃষক আব্দুল খালেক (৫৫), চুয়াডাঙ্গা সদরের বাসিন্দা, জানালেন—
“এই নদী ছাড়া ধান ফলানো যায় না। শীতকালে যখন পানি কমে যায়, তখন সেচের সংকট হয়। কিন্তু নদী থাকলেই জমি উর্বর।”
নদীর পানিতে ধান, গম, ভুট্টা, আখ, পাট থেকে শুরু করে সবজি পর্যন্ত চাষ হয়। মাথাভাঙ্গার পানিতে সেচ পাওয়া যায় বলেই এই অঞ্চলে সবজি চাষে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার তৈরি হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য
মাথাভাঙ্গা নদী ছিল এক সময় মাছের ভাণ্ডার। স্থানীয় জেলে সমিতির হিসেবে, ১৯৮০-এর দশকে এখানে অন্তত ৫০ প্রজাতির মাছ ধরা পড়ত। এর মধ্যে রুই, কাতলা, ইলিশ, মৃগেল, শোল, টেংরা উল্লেখযোগ্য।
জেলে আজগর আলী (৪০), কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা থেকে বললেন—
“আমাদের বাপ-দাদারা এই নদীতে জাল ফেললেই মাছ পেত। এখন নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, মাছও নেই।”
মাছের প্রাচুর্যের কারণে আশপাশের বাজারে প্রতিদিন কয়েক টন মাছ বিক্রি হতো। এখন তা কমে গিয়ে এক-তৃতীয়াংশে নেমে এসেছে।
রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য
নদীকে ঘিরে স্থানীয় সমাজে নানান প্রথা, গান ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। কুষ্টিয়ার বিখ্যাত লালন শাহের গানেও নদীর প্রসঙ্গ এসেছে। নৌকাবাইচ, বর্ষাকালীন মেলা, নদীপাড়ের বিয়ের গান—এসবেই মাথাভাঙ্গা মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সংকট ও পরিবেশগত সমস্যা
কালের পরিক্রমায় নদীর অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে।
পানি প্রবাহ সংকট: শুষ্ক মৌসুমে ভারতীয় অংশে ফারাক্কা ও গঙ্গার বাঁধের কারণে প্রবাহ কমে যায়।
অবৈধ দখল: স্থানীয় প্রভাবশালীরা নদীর দুই পাড়ে দখল করে ঘর-বাড়ি ও বাজার বানাচ্ছে।
বালু উত্তোলন: অপরিকল্পিত বালু উত্তোলনে নদীর তলদেশ ভেঙে পড়ছে।
দূষণ: কৃষিজ রাসায়নিক, পাটকল ও চিনি কলের বর্জ্য নদীতে ফেলা হচ্ছে।
পরিবেশবিদ অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন মতামত দিলেন—
“মাথাভাঙ্গা শুধু নদী নয়, একটি জীবন্ত প্রতিবেশ। এ নদী মরে গেলে পুরো অঞ্চলের কৃষি ও মাছ ধরা ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।”
২০শ শতক ও মাথাভাঙ্গার রূপান্তর
১৯৫০–৭০ দশক পর্যন্ত মাথাভাঙ্গা ছিল উত্তরাঞ্চলের প্রধান পরিবহনপথ। নৌযানেই মালামাল যেত ঢাকায়। কিন্তু সড়ক ও রেলপথ গড়ে উঠায় নদীপথের গুরুত্ব কমতে থাকে।
তবে কৃষি ও সেচের জন্য নদীর গুরুত্ব কমেনি। বরং সময়ের সঙ্গে তা বেড়েছে। নদীর ওপর একাধিক সেতু তৈরি হয়েছে, যা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ করেছে, তবে প্রবাহের গতিপথে পরিবর্তন এনেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেলের (IPCC) গবেষণা বলছে, দক্ষিণ এশিয়ায় আগামী ২০ বছরে নদীভাঙন ও পানি সংকট তীব্রতর হবে। মাথাভাঙ্গা নদীর ক্ষেত্রেও একই পূর্বাভাস রয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে প্রবাহ কমে গিয়ে কৃষক ও জেলেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার বর্ষাকালে হঠাৎ বন্যা হয়ে ফসল নষ্ট হচ্ছে।
সাক্ষাৎকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি
- মেহেরপুরের কৃষাণী রহিমা বেগম (৪৫):
“বর্ষায় নদীর পানি বাড়লে জমি তলিয়ে যায়, শীতে পানি কমে ফসল শুকায়। আমরা দুই দিকেই বিপদে।”
- চুয়াডাঙ্গার স্কুলশিক্ষক রফিকুল ইসলাম (৫০):
“নদী শুধু অর্থনীতি নয়, আমাদের সংস্কৃতিরও অংশ। বাচ্চাদের বইতে নদী নিয়ে কবিতা আছে, কিন্তু বাস্তবে নদী নেই।”
সংরক্ষণ ও করণীয়
নদী রক্ষায় বিশেষজ্ঞরা কয়েকটি পদক্ষেপ জরুরি বলেছেন—
আন্তর্জাতিক নদী ব্যবস্থাপনায় ভারত–বাংলাদেশের সমঝোতা বাড়ানো।
অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও নদী খনন।
পরিবেশবান্ধব কৃষি ও শিল্পবর্জ্য নিয়ন্ত্রণ।
স্থানীয় জনগণকে সচেতন করে নদী সংরক্ষণের আন্দোলন গড়ে তোলা।
মাথাভাঙ্গা নদী আজ এক গভীর সংকটের মুখে। অথচ এটি কেবল একটি নদী নয়, বরং উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারা, সংস্কৃতি, কৃষি ও অর্থনীতির ভিত্তি। যদি এখনই পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে ইতিহাস ও ভূগোলের মানচিত্র থেকে এই নদীর নাম মুছে যেতে পারে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট