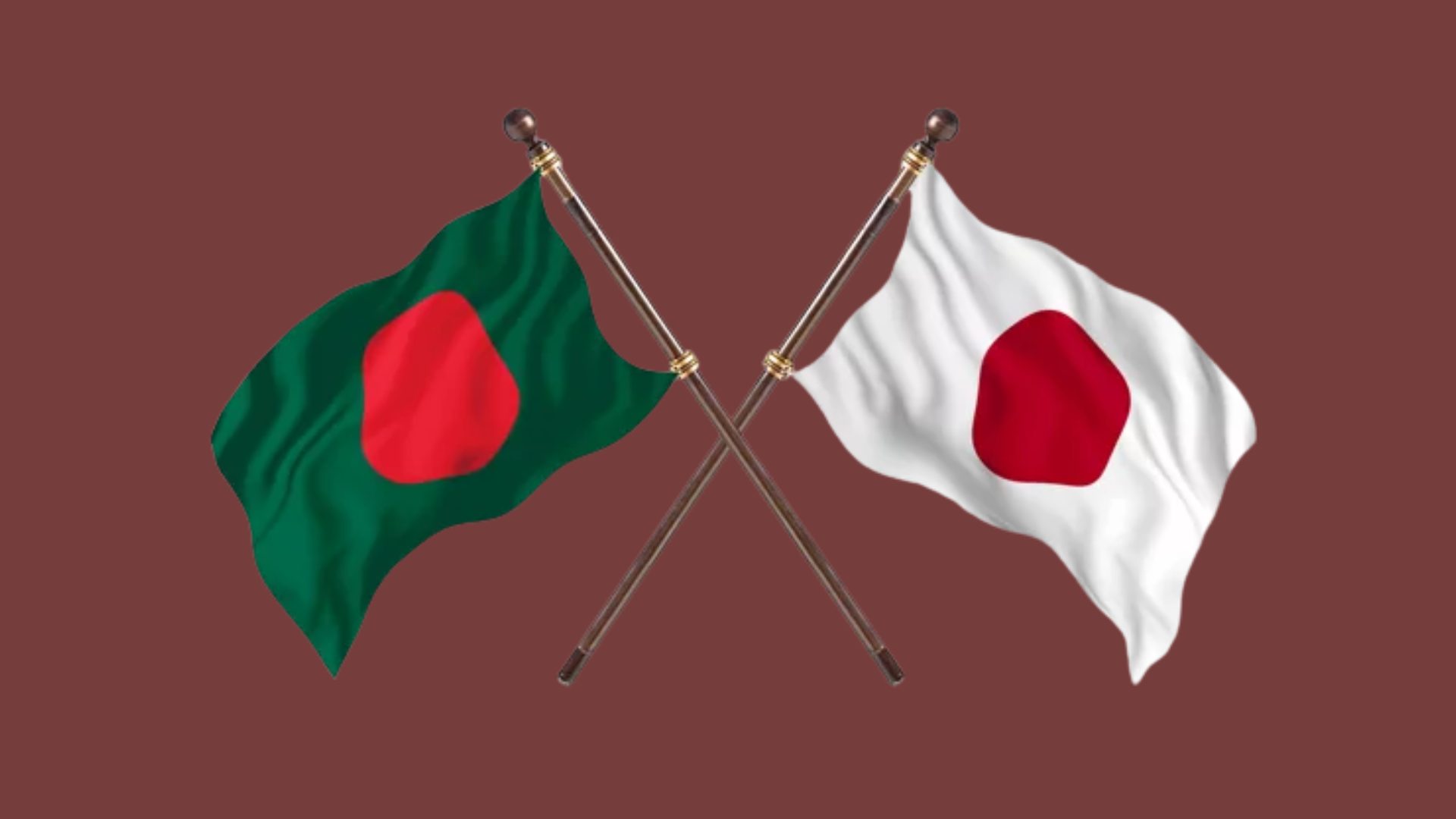২৩ সেপ্টেম্বর, সিঙ্গাপুরে জলক্রীড়ার এক দুর্ঘটনায় জুবিন গার্গের মৃত্যুর চার দিন পর তাঁর দেহ চিরনিদ্রায় শায়িত হয়। দু’টি ময়নাতদন্তসহ চার দিন কেটে গেলেও আসামের মানুষ কোনো সমাপ্তি খুঁজে পাননি। তবু কেউ আসলে সেটি খুঁজছেনও না। কারণ এটি কেবল আরেকটি শুরু—যেখানে ‘জুবিন দা’ নামে পরিচিত যে ঘটনাপ্রবাহ, তা এখন অমর হয়ে উঠছে।
১৯৭২ সালে মেঘালয়ের তুরায় জুবিন বোরঠাকুর নামে জন্ম নেওয়া জুবিন গার্গ শুধু জনপ্রিয় গায়কই ছিলেন না—আরও বহুগুণ বেশি। ২০০৬ সালের ‘গ্যাংস্টার’ চলচ্চিত্রের সেই বহুল জনপ্রিয় গান ‘য়া আলি’-র গায়ক হিসেবেই তাঁকে সীমাবদ্ধ করে দেখা যায় না। আজ, আসামের বাইরে অনেকেই দুটি তথ্য শুনে বিস্মিত হন।
প্রথমত, জুবিন প্রায় ৪০টি ভাষায় ৩৮,০০০-এরও বেশি গান গেয়েছেন। ৫২ বছর বয়সে যাঁর জীবনাবসান, তাঁর এই বিশাল সংগীতভাণ্ডারই আলাদা স্বীকৃতির যোগ্য। কিন্তু এ যুগে কয়েকটি হিট বা জনপ্রিয় সংখ্যার বাইরে মানুষের আগ্রহ কমে গেছে।

কিন্তু নব্বইয়ের দশকের আসামে তা ছিল না। আসামের বিভিন্ন জায়গায় বড় হওয়া, শিল্পমনা পরিবারে জন্ম নেওয়া জুবিন স্কুল-কলেজের দিনগুলোতেও ভরসা রেখেছিলেন সংগীতের ওপর। ১৯৯২ সালে তাঁর প্রথম একক অ্যালবাম ‘অনামিকা’ প্রকাশের পর রাতারাতি তিনি তারকা হয়ে ওঠেন। সহস্রাব্দের সূচনায় এসে তিনি অধিকাংশ আসামবাসীর কাছে আইকনে পরিণত হন। তিনি সংগীত ও চলচ্চিত্র প্রযোজনা শুরু করেন; তখন মৃতপ্রায় অসমীয়া সিনেমাকে নতুন প্রাণ দেন। প্রেম, ভক্তি, বেদনা—আরও নানান বিষয়ে তিনি গান গেয়েছেন।
নিজের গানে এক বিশেষ হামিং-এর ঢং তিনি জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। নীরবে হলেও নিশ্চিতভাবে, জুবিন আসামকে দিয়েছিলেন এক নতুন কণ্ঠ—যেখানে বিদ্রোহ বা বিচ্ছিন্নতাবাদের বদলে স্থিতি ও আধুনিকতা এসেছে, জাত-পাতের বদলে শিক্ষা, দারিদ্র্যের বদলে আশার সঞ্চার হয়েছে। প্রতিটি পরিবর্তনের ছিল তাঁর একটি করে গান, যা মানুষের মনে স্পর্শ করত এবং ধীরে ধীরে তাদের বদলে দিত। কিন্তু মানুষ যেমন দ্বন্দ্বে ভরা, তেমনি ছিলেন জুবিনও।

ভূপেন হাজরিকা ও খাগেন মহন্তদের প্রজন্ম যে ‘পুরনো’ ধারাটি প্রতিনিধিত্ব করত, সেই প্রজন্ম লম্বা চুল, কর্তৃত্ব-বিরোধী ভঙ্গি আর বিপজ্জনকভাবে মুক্তচেতা এক তরুণকে সহজে আইডল হিসেবে মানতে পারেনি। আসলে তিনি তো প্রকাশ্যে কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, অনুষ্ঠানেও মদ্যপান করেছেন, অশালীন ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে কী বদলেছিল, যা তাঁকে আইকনে পরিণত করল? সবকিছু—কেবল জুবিন বাদে। খ্যাতি, অর্থ, অসীম সুযোগ—যা সবচেয়ে মহৎকেও দুর্নীতিগ্রস্ত করতে পারে—সবই তাঁর দিকে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু জুবিন একই রয়ে গিয়েছিলেন।
এতেই আসে দ্বিতীয় তথ্য—যা আজ অনেককে বিস্মিত করছে এবং জুবিনকে নিয়ে কৌতূহলী করে তুলছে। তাঁর শেষযাত্রায় সব শ্রেণি-পেশার হাজারো মানুষ রাস্তায় নেমে সর্বজনীন শোক প্রকাশ করেছেন। অনেকে ২০১১ সালে ভূপেন হাজরিকার শেষযাত্রার সঙ্গে তুলনা টেনেছেন। তবে বিষয়টি ভিড়ের আকার নয়; শোকের গভীরতা ও আবেগের উচ্ছ্বাসই এখানে আলাদা করে ধরা পড়েছে।
আসামের লাখো মানুষের কাছে ‘জুবিন-উত্তর’ পৃথিবী ভাবাই দুষ্কর। তাঁর মৃত্যুর পর আসামে একটি বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ উন্মোচিত হচ্ছে—যা গড়ে উঠছে তিনটি শক্তির সমবায়ে: আসামের মানুষ, রাজ্য সরকার এবং শিল্পীর নিজস্ব উত্তরাধিকার।

আসামের মানুষ তাঁর অকালপ্রয়াণে স্তব্ধ। যদি জুবিন তাঁর জীবনকে পূর্ণতা পর্যন্ত বাঁচতে পারতেন, হয়তো আজকের এই বিরাট তরঙ্গটি এত প্রকট হতো না। মানুষের মাটি, ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয়ের সঙ্গে জড়ানো আবেগের শক্তি তিনি পৃথিবীকে দেখিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত পঙ্ক্তি—“আমার কোনো জাত নেই, কোনো ধর্ম নেই; আমি আগে মানুষ”—কথাটির যেন চাক্ষুষ প্রতিচ্ছবি দেখা গেল, যখন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ ঢল নামিয়ে একসঙ্গে কেঁদে উঠলেন। গণ-শোকের শক্তি গভীর; এটি সমাজ বদলে দিতে পারে। আসাম সরকার বিষয়টি বুঝেছিল এবং তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করে সেই আবেগকে মর্যাদা দিয়েছে। সবাই অন্তর্ভুক্ত বলে অনুভব করেছেন, বোঝা হয়েছে বলে মনে করেছেন। তাঁরা ধাক্কাটা সামলানোর সময় পেয়েছেন এবং ‘জুবিন-উত্তর’ পৃথিবী নিয়ে একসঙ্গে ভাবার, কল্পনা করার অবকাশ পেয়েছেন।
কালাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা, রূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা ও ভূপেন হাজরিকা—এই বিংশ শতকের সাংস্কৃতিক মহীরূহদের পর, জুবিনের মধ্য দিয়ে আসাম নতুন এক পরিচয় খুঁজে পেয়েছে। পথের মানুষের কাছে যেমন তিনি প্রিয় ছিলেন, তেমনি অভিজাত অঙ্গনেও। বলিউডে ক্যারিয়ারের শিখরে থেকেও তিনি আসামে ফিরে এসেছিলেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল—“রাজাকে নিজের রাজ্য ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়।” উলফার হুমকি সত্ত্বেও তিনি বিহু উৎসবে হিন্দি গান গেয়েছেন। আজ সেই উলফাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।
![]()
আজ আসাম নিজেকেই কিছুটা হারিয়েছে। তবু আগের চেয়ে হয়তো আরও পরিপূর্ণ, কারণ এই গায়কের উত্তরাধিকার তাঁর জীবনের সহজ যোগফলের চেয়েও বৃহৎ। তাঁর গানগুলো নতুন অর্থ পাবে, নতুন শ্রোতা খুঁজে নেবে—মানুষ তাঁর ভেতরের নানাদিক আবিষ্কার করবে। তাঁর কাজের পরিধি, ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা হবে; যা শিল্প-সংস্কৃতি থেকে সমাজতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, এমনকি রাজনীতিতেও সঞ্চারিত হবে। প্রতি বছর তাঁর জীবন ও কাজকে ঘিরে আয়োজন হবে। কে জানে, মরণোত্তর আরও কত সম্মান-স্বীকৃতি তিনি পেতে পারেন। কিন্তু ‘জুবিন দা’—সম্ভবত তিনি এসবের তোয়াক্কা করতেন না।
লেখক: শ্রাবণা বড়ুয়া, সহযোগী অধ্যাপক ও পরিচালক, এনকেসিসিইএএস, জিন্দাল স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স। এখানে ব্যক্ত মতামত একান্তই তাঁর নিজের।

 শ্রাবণা বডুয়া
শ্রাবণা বডুয়া