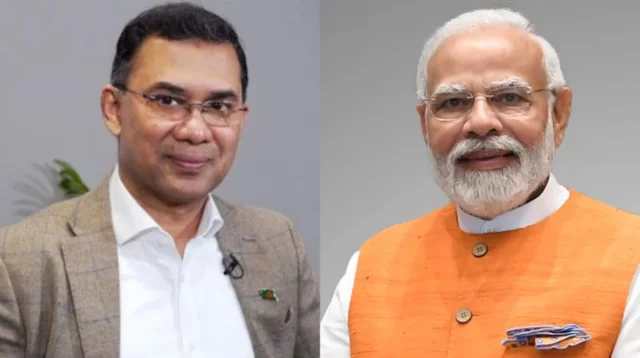এটি সাংবাদিকতা নয়; এটি বাছাই করা গল্প বলা—যেখানে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পাঠকের জন্য আলাদা নৈতিক মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয়।
ভাবুন তো, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটলে যে দাঙ্গা হয়েছিল, সেটিকে যদি পশ্চিমা গণমাধ্যম আইনহীনতা ও গণতন্ত্রের ওপর হামলা না বলে, বরং অর্থ ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক জাগরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করত—ধারণাটাই হাস্যকর। অথচ গ্লোবাল সাউথে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দাঙ্গা—কখনো কখনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে সহিংস হামলাও—পশ্চিমা গণমাধ্যমে নিয়মিতভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত অভিজাতদের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত জনবিদ্রোহ হিসেবে চিত্রিত হয়। তারা এক ধরনের আকর্ষণীয় কিন্তু বিপজ্জনক বয়ানকে নিখুঁত করেছে: যুবনেতৃত্বাধীন “বিপ্লবের” রোমান্টিক গল্প, যা নাকি বিদেশের দমনমূলক ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারগুলোকে উচ্ছেদ করে। গত এক মাসেই মাদাগাস্কার, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে প্রকাশিত খবরে একই ছাঁচ দেখা গেছে। বাংলাদেশে ২০২৪ সালে শেখ হাসিনার পদচ্যুতি বীরোচিত মুক্তি হিসেবে প্যাকেজ করা হয়েছিল; পরিণতিতে ইসলামপন্থী দমন-পীড়ন ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এটি সাংবাদিকতা নয়—এটি বাছাই করা গল্প বলা, যেখানে ঘরের জন্য এক নীতিমালা আর বাইরে অন্য নীতিমালা। ওয়াশিংটনে যে কাজ দেশদ্রোহ বলে ধিক্কৃত, ভঙ্গুর রাষ্ট্রে সেটিই “গণতান্ত্রিক জাগরণ” নামে পুনর্ব্র্যান্ড হয়।
নেপালের উদাহরণ নিন। যখন ভিড় একের পর এক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান—পার্লামেন্ট, সুপ্রিম কোর্ট, মন্ত্রণালয়, ব্যাংক, এমনকি অস্ত্রাগার—পুড়িয়ে দিতে শুরু করল, তখন নির্বাচিত সরকার পড়ে গেল। পশ্চিমা বয়ান-যন্ত্র সঙ্গে সঙ্গে নতুন অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুসিলা কার্কিকে “দুর্নীতিবিরোধী যোদ্ধা” ও জেন-জেড–এর আইকন হিসেবে মহিমান্বিত করল। তাঁর সাংবিধানিক বৈধতার ঘাটতি এবং তাঁর স্বামীর ১৯৭৩ সালের বিমান-ছিনতাইয়ের রেকর্ড প্রায় পাদটীকাতেই ঠাঁই পেল। গুরুত্বপূর্ণ ছিল একটি সহজপাচ্য গল্প: ক্ষুব্ধ তরুণেরা দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন ভেঙে দিয়েছে।

এমন নায়ক বানানোর প্রক্রিয়ায় বয়ানের তুষ্টিকে তথ্যের জটিলতার ওপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়। নেপালের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কেড়ে নেওয়া সেই সমন্বিত অগ্নিসংযোগকে অপরাধমূলক ধ্বংসযজ্ঞ না বলে “যৌবনের আদর্শবাদ” হিসেবে ফ্রেম করা হলো। বাস্তবে, গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে কার্যকর আদালত, সংসদ ও আমলাতন্ত্র লাগে—যে প্রতিষ্ঠানগুলোই ওই গোষ্টিগুলো পুড়িয়ে ছাই করেছে। তাদের ধ্বংসকে মহিমান্বিত করা গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলা নয়, বরং তাকে দুর্বল করা।
দ্বৈত মানদণ্ড শুধু সহিংস অস্থিরতার খবরেই নয়, বিপর্যয়ের খবরেও দেখা যায়। নীতিগতভাবে, শোকাবহ ঘটনার প্রতিবেদনে সংবেদনশীলতা আবশ্যক। বাস্তবে, বিদেশের ট্র্যাজেডি নিয়ে পশ্চিমা কভারেজে প্রায়ই উঁকি দেয় কৌতূহলোদ্দীপক ভয়ারিজম, সাংস্কৃতিক পূর্বধারণা ও চমকপ্রদ উপস্থাপন।
জাপানের ২০১১ সালের ফুকুশিমা বিপর্যয় এক দৃষ্টান্ত: ভুক্তভোগীদের কষ্টকে বিকিরণ-আতঙ্কের কৌতূহলোদ্দীপক গল্পের পটভূমিতে নামিয়ে আনা হয়। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মীদের “নিউক্লিয়ার সামুরাই”, “মানববলিদান” বা “আত্মঘাতী মিশনের নিউক্লিয়ার নিনজা” হিসেবে ছাঁচে ঢালা হয়। অথচ সতর্কতামূলক সরিয়ে নেওয়ার ফলে বিকিরণে কোনো মৃত্যুই ঘটেনি—এই সত্যটি উপেক্ষিত থাকে। চের্নোবিলের সঙ্গে ভয়াবহভাবে বিভ্রান্তিকর তুলনা আতঙ্কই বাড়িয়েছে, স্বচ্ছতা নয়।
কোভিড-১৯ মহামারিও একই পক্ষপাত উন্মোচন করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে, অ-পশ্চিমা বিশ্বের তুলনায় পশ্চিমে সরকারিভাবে বেশি মানুষ মারা গেছে; সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা—দুই ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষে। তবুও পশ্চিমা দর্শকরা সবচেয়ে বেশি দেখেছে ভারত, ব্রাজিল বা আফ্রিকার ছবি। ডেল্টা ধাপে যখন ভারতে দুই মাসের ভয়াবহ ঢেউ বয়ে গেল, পশ্চিমা গণমাধ্যম শ্মশানের জ্বলন্ত চিতা ও হাসপাতালের হাঁসফাঁস করা রোগীর ছবি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিল; এমনকি বিদেশি টিভি দল জরুরি ওয়ার্ডেও ঢুকে পড়ল। কিন্তু যখন নিউইয়র্কে গণকবর খোঁড়া হলো বা পশ্চিমের রাস্তা জুড়ে মরদেহ রাখার জন্য রেফ্রিজারেটেড ট্রাক দাঁড় করানো হলো, তখন সেই চিত্রায়ণ ছিল পরিশীলিত ও সংযত।

আফ্রিকা দীর্ঘদিন ধরেই এ ধরনের পূর্বধারণার ভার বহন করছে। ২০১৪–২০১৬ সালের ইবোলা মহামারিতে ১১,৩২৫ মানুষ মারা গেলেও কভারেজ ভরে ছিল মৃতদেহের ব্যাগ, দাফনের আচার ও হতাশার ছবিতে। পুলিৎজার পুরস্কার গেল এমন এক আলোকচিত্রীকে, যিনি মৃতদেহ সংগ্রহকারীদের অনুসরণ করেছিলেন।মহামারিটি মাত্র তিনটি দেশে সীমিত ছিল—এই তথ্যটি বিশ্বজনতার মনে খুব কমই জায়গা পেল। ফলত, ইবোলাকে “আফ্রিকান” রোগ হিসেবে কলঙ্কিত করা হলো, মহাদেশজুড়ে এক ধরনের কলঙ্ক এঁটে দেওয়া হলো।
এই ধারা যুদ্ধের খবরেও প্রতিধ্বনিত হয়। পশ্চিমা গণমাধ্যম খুব কমই মৃত আমেরিকান বা ইউরোপীয় সৈন্যদের ছবি দেখায়। কিন্তু আফগান, ইরাকি, লিবীয় বা সিরীয় নিহতদের ছবি প্রকাশে তারা কোনো সংকোচ বোধ করে না। ঘরের শোককে ব্যক্তিগত রাখা হয়, বাইরে তা প্রদর্শিত হয়।
নিশ্চয়ই, সব পশ্চিমা গণমাধ্যম একরকম নয়, আর কখনো সখনো দেশীয় ট্র্যাজেডিকেও তারা অতিরঞ্জিতভাবে দেখাতে পারে। তবু বড় ছবিটা পরিষ্কার: যখন সহিংসতা বা বিপর্যয় পশ্চিমের বাইরে ঘটে, তখন সংযম, নির্ভুলতা ও মর্যাদা—এই সাংবাদিকতার নীতিগুলো ঢিলে হয়ে যায়, কখনো পরিত্যক্তও হয়।
এতে সমস্যা কী? সমস্যা হলো, পশ্চিমা গণমাধ্যম একই সঙ্গে বৈশ্বিক গণমাধ্যমও। তাদের ফ্রেম ও ছবি বিশ্বজনমতের ধারণা গড়ে দেয়। যখন অগ্নিসংযোগ ও ভিড়ের সহিংসতা বিদেশে “বিপ্লব” নামে প্যাকেজ করা হয়, তখন তা নৈতিক আড়াল পায়—যা সংস্কার নয়, বরং অস্থিতিশীলতাকে উৎসাহিত করে। যখন মৃত্যু ও বিপর্যয়কে বৈচিত্র্য-খোঁজা, “অপর” বানানো লেন্সে দেখানো হয়, তখন পুরো সমাজগুলো স্টেরিওটাইপে চেপে বসে।

বিশ্বাসযোগ্যতার আসল পরীক্ষাই হলো সামঞ্জস্য। যদি ওয়াশিংটনে কংগ্রেস ভবনে হামলা “বিদ্রোহ” হয়, তবে নেপালে সংসদে হামলাকে “গণতান্ত্রিক জাগরণ” বলে উৎসব করা যায় না। যদি নিউইয়র্কের গণশবদাহের ছবি জনদৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়, তবে নয়াদিল্লির দেহদাহের ছবি বিশ্বমঞ্চে প্রদর্শনেরও কথা নয়।
এই দ্বিখণ্ডিত দৃষ্টি শুধু বাস্তবতা বিকৃত করে না; ঘরে যেটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, বাইরে সেটিকেই বৈধতা দেয়। গ্লোবাল সাউথে যে ধ্বংসযজ্ঞকে ক্ষমা করা হয়, পশ্চিমে একই কাজকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
সময় এসেছে পশ্চিমা গণমাধ্যমের এই দ্বৈত মানদণ্ড ত্যাগ করার। চিন্তাশীল, দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার দাবি—সবখানে একই নিয়ম প্রয়োগ: তথ্যের প্রতি সম্মান, নৈতিক মানদণ্ডে সামঞ্জস্য, আর মানবিক কষ্টের প্রতি সংবেদনশীলতা। নচেৎ যে কভারেজকে সার্বজনীন বলা হয়, তা আসলে সংবাদরূপী সাংস্কৃতিক আত্মমুগ্ধতা ছাড়া কিছুই নয়।
লেখক: ব্রহ্ম চেল্লানি — ভূ-কৌশলবিদ এবং ‘ওয়াটার: এশিয়ার নিউ ব্যাটলগ্রাউন্ড’সহ নয়টি বইয়ের লেখক

 ব্রহ্ম চেল্লানি
ব্রহ্ম চেল্লানি