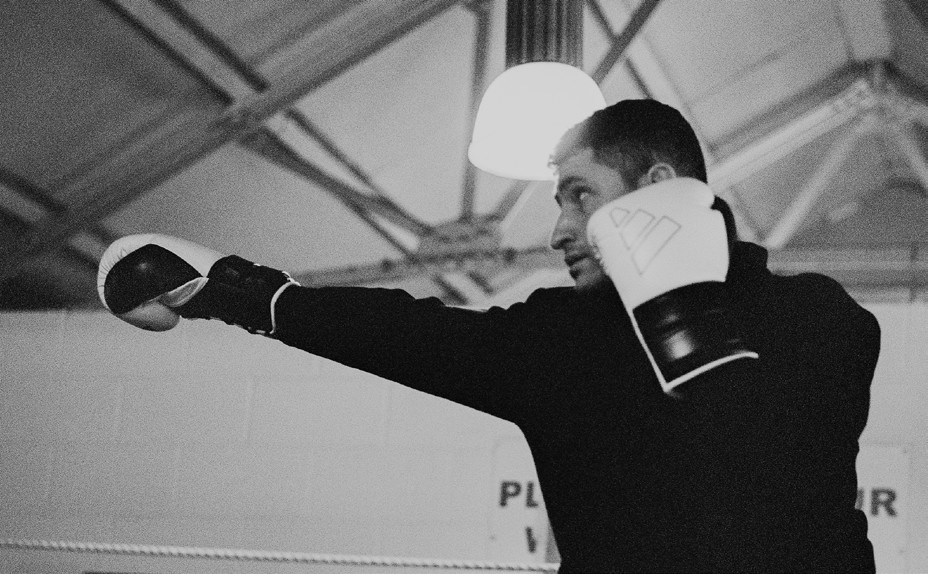প্রাচীন চীনের রাজনীতি, প্রশাসন ও শিল্পচর্চা শুধু তাদের সাম্রাজ্যিক সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল না—এর প্রভাব পড়েছে ইউরোপীয় আলোকায়নের চিন্তাতেও। যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এমেরিটাস মার্টিন পাওয়ার্স দেখিয়েছেন, কীভাবে চীনের ন্যায়বিচার ও শাসনব্যবস্থার ধারণা শিল্পের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল পশ্চিমা সমাজের রাজনৈতিক দর্শনে।
মার্টিন পাওয়ার্স: শিল্প, রাজনীতি ও সমাজের সংযোগ
মার্টিন পাওয়ার্স যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এমেরিটাস ও খ্যাতনামা শিল্প-ইতিহাস-বিদ ও সিনোলজিস্ট। চীনের সামাজিক ন্যায়বিচারের ইতিহাস নিয়ে তার গবেষণা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। তিনি চারটি বইয়ের লেখক, যার মধ্যে দুটি প্রি-মডার্ন চাইনিজ স্টাডিজে লেভেনসন পুরস্কার অর্জন করেছে। তার সাম্প্রতিক গ্রন্থ “চায়না অ্যান্ড ইংল্যান্ড: দ্য প্রি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্রাগল ফর জাস্টিস ইন ওয়ার্ড অ্যান্ড ইমেজ” গ্রন্থে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন কীভাবে ইংরেজ আলোকায়নের চিন্তায় চীনা সাম্রাজ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে।
শিল্পের মাধ্যমে ইতিহাস ও সমাজকে দেখা
পাওয়ার্সের মতে, ইতিহাস বোঝার জন্য শুধু পাঠ্য নয়, দৃশ্যমান শিল্পও একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তিনি বলেন, কোনো ঐতিহাসিক লেখা সবসময়ই সমাজের প্রচলিত ধারণা প্রতিফলিত করে না; কিন্তু শিল্পকর্ম বা চিত্র সাধারণত এমন বার্তা বহন করে যা একটি সম্প্রদায়ের দ্বারা স্বীকৃত ও বোঝা যায়। ফলে চিত্র ও শিল্প সামাজিক ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপাদান হয়ে ওঠে।
তিনি উদাহরণ দেন চীনের এক বিখ্যাত গল্পের। খ্রিষ্টপূর্ব হান রাজবংশের এক প্রধানমন্ত্রী প্রদেশ সফরে গিয়ে দেখেন এক এলাকায় দাঙ্গা চলছে। কিন্তু তিনি হস্তক্ষেপ করেন না, বরং বলেন, “এটি আমার এখতিয়ারের বাইরে; এটি স্থানীয় কর্মকর্তাদের দায়িত্ব।” এই গল্পটি ১২শ শতকের পর থেকে চীন জুড়ে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে—ফুলদানি, কালি-পাত্র, বালিশ থেকে শুরু করে চিত্রকলায়—চিত্রিত হয়েছে এবং ২০শ শতক পর্যন্ত টিকে ছিল। পাওয়ার্সের মতে, এই ধারাবাহিক শিল্পচিত্র প্রমাণ করে, প্রশাসনিক দায়িত্ব ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে চীনে এই ধারণা সমাজজুড়ে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল—যা শুধুমাত্র লিখিত নথি থেকে বোঝা যেত না।

রাজনীতি ও শিল্প: প্রতিফলন নয়, অংশগ্রহণ
পাওয়ার্স মনে করেন, শিল্প শুধুমাত্র রাজনীতির প্রতিফলন নয়; বরং এটি রাজনৈতিক আলোচনার সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। যেমন সংবাদপত্র সমাজ ও রাজনীতির ধারণা প্রকাশ করে, তেমনি শিল্পও করে। যখন কোনো শিল্পকর্মে ধনী ও গরিব, শাসক ও প্রজার মতো দুই ভিন্ন গোষ্ঠীকে একসঙ্গে উপস্থাপন করা হয়, তখন শিল্পীকে সেই সম্পর্কের অর্থ দর্শকের বোধগম্যতায় তুলে ধরতে হয়। এর মাধ্যমেই বোঝা যায় সমাজে শ্রেণি বা শক্তির সম্পর্ক কীভাবে কল্পিত ও প্রকাশিত হয়েছে।
আধিপত্য, সম্মান ও ক্ষমতার চিত্র
অ্যারিস্টোক্রেটিক সমাজে শিল্পে সবচেয়ে সাধারণ দৃশ্যগুলোর একটি হলো—একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির অন্যের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা, প্রায়ই হাত উঁচিয়ে আঘাতের ভঙ্গি করা। নিচের ব্যক্তি সেখানে সম্পূর্ণ অসহায়, শাসকের ইচ্ছার দয়ার ওপর নির্ভরশীল। এই চিত্র কেবল আধিপত্য নয়; এটি “সম্মান” বা “honour”-এর প্রতীক, যা ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কিয়ু The Spirit of Laws গ্রন্থে বর্ণনা করেছিলেন। “সম্মান” এমন এক বিশেষাধিকার, যা মানুষকে কেবল ইচ্ছার ভিত্তিতে কাজ করার ক্ষমতা দেয়—নিয়মের সীমার বাইরে। এই ধারণা পূর্ব ও পশ্চিম—দুই দিকের রাজতান্ত্রিক সমাজেই দৃশ্যমান ছিল।
মার্টিন পাওয়ার্সের বিশ্লেষণ দেখায়, শিল্প শুধু নান্দনিক প্রকাশ নয়; এটি ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতির জটিল আন্তঃসম্পর্কের আয়না। প্রাচীন চীনের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা যেমন তার শিল্পে প্রতিফলিত হয়েছিল, তেমনি সেই ন্যায়ের ধারণা পশ্চিমা সমাজেও আলোকায়নের যুগে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।
#ট্যাগ: চীন, মার্টিন_পাওয়ার্স, রাজনীতি, শিল্প, ইতিহাস, সামাজিক_ন্যায়বিচার, আলোকায়ন, মন্টেস্কিয়ু, সারাক্ষণ_রিপোর্ট

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট