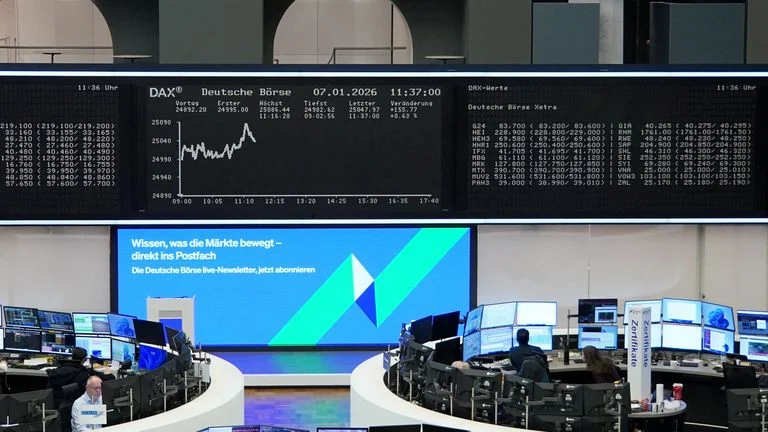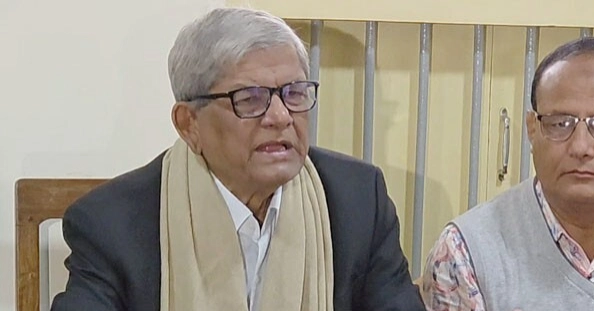মেরি শেলির বিখ্যাত উপন্যাস “ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, অর দ্য মডার্ন প্রমিথিউস” ১৮১৮ সালে প্রকাশের পর থেকেই এটি মানব সৃষ্টির নৈতিকতা, অস্তিত্বের অর্থ এবং ঈশ্বরের ভূমিকা নিয়ে গভীর আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। দুই শতাব্দী পর, পরিচালক গিলেরমো দেল তোরো তাঁর নতুন চলচ্চিত্রে সেই ক্লাসিক গল্পটিকেই ফিরিয়ে এনেছেন এক অন্যরকম আবেগ ও মানবিক ব্যাখ্যায়।
মেরি শেলি থেকে মিলটন পর্যন্ত
মূল উপন্যাসের মতোই দেল তোরোর সংস্করণেও জন মিলটনের “প্যারাডাইস লস্ট”-এর ভাবটি গভীরভাবে প্রবাহিত। শেলির উপন্যাসে যেমন ঈশ্বর, শয়তান ও আদমের প্রতীকী সম্পর্ক ফুটে উঠেছিল, তেমনি দেল তোরোও তাঁর চলচ্চিত্রে সেই ধর্মতাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। চলচ্চিত্রের শুরুতে ও শেষে মিলটনের প্রভাব স্পষ্ট—বিশেষত সেই বাণী, যেখানে সৃষ্ট বস্তু তার সৃষ্টিকর্তাকে প্রশ্ন করে: “আমি কি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম আমাকে সৃষ্টি করতে?”
দেল তোরোর ব্যক্তিগত ‘ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন’

গিলেরমো দেল তোরোর জন্য এই চলচ্চিত্র শুধু একটি রিমেক নয়, বরং এক গভীর আত্মিক যাত্রা। শৈশবে তিনি ১৯৩১ সালের ক্লাসিক সংস্করণে বরিস কারলফ অভিনীত চরিত্রে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই মুগ্ধতা থেকেই জন্ম নেয় তাঁর আজীবনের ভালোবাসা—‘দানব’-এর ভেতর লুকানো মানবিকতাকে খুঁজে বের করা।
এই নতুন “ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন” তাই কেবল এক ভয়ের গল্প নয়; এটি পিতা-পুত্রের সম্পর্ক, পরিত্যক্ত সত্তার বেদনা, এবং মানুষ নামের প্রকৃত দানবের প্রতিফলন।
কাহিনি ও চরিত্র
চলচ্চিত্রের কাহিনি শেলির ১৮শ শতকের জার্মানি ও সুইজারল্যান্ড থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডে। গল্প শুরু হয় উত্তর মেরুর বরফে আটকে পড়া ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসনের জাহাজে (লার্স মিকেলসেন)। একদিন তারা বরফে এক আহত মানুষকে উদ্ধার করে, তিনি ড. ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন (অস্কার আইজ্যাক)।
ভিক্টরের মা মারা যাওয়ার পর মৃত্যু জয় করার বাসনা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এক অস্ত্র ব্যবসায়ী হের হ্যারল্যান্ডার (ক্রিস্টোফ ওয়াল্টজ) তাঁর গবেষণায় অর্থ যোগান দেন, আর এই যাত্রায় যুক্ত হয় এলিজাবেথ (মিয়া গোথ)—এক রহস্যময় নারী। অবশেষে এক রাতে বজ্রঝড়ের মধ্যে মৃতদেহের টুকরো জোড়া দিয়ে জন্ম নেয় তাঁর সৃষ্টি—এক জীবন্ত দানব, যার ভূমিকায় জ্যাকব এলরোর্ডি।
মানবিক দানবের প্রতিচ্ছবি
দেল তোরোর দানব কোনো কুৎসিত দৈত্য নয়—সে বুদ্ধিমান, অনুভূতিশীল ও করুণ। প্রথমে শিশুর মতো নিরীহ এই প্রাণী সমাজের নিষ্ঠুরতায় ধীরে ধীরে রূপ নেয় বেদনার এক প্রতীকে। এলরোর্ডির অভিনয় এখানে অসাধারণ; তার চলনভঙ্গি, দৃষ্টি ও ক্রমবর্ধমান মানবিক হতাশা দর্শকের মনে গভীর ছাপ ফেলে।

সৌন্দর্য ও নিষ্ঠুরতার দ্বন্দ্ব
দেল তোরো বরাবরই সৌন্দর্য ও নির্মমতার মিলনবিন্দু নিয়েই কাজ করেন। “ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন” সেই থিমেরই পরিণত রূপ। সিনেমাটিতে মৃত্যু, ভালোবাসা ও সৃষ্টির অন্তর্নিহিত বেদনা মিলেমিশে গেছে এক অপূর্ব চিত্রভাষায়। কখনো দৃশ্যগুলো এতই সুন্দর যে চোখ সরানো যায় না; আবার কখনো এত নিষ্ঠুর যে তাকানোও কষ্টকর।
ধর্মতত্ত্ব ও পুনর্জন্মের প্রতীক
চলচ্চিত্রে ধর্মীয় প্রতীক সর্বত্র—দানবকে ক্রুশাকৃতিতে দাঁড় করানো, তার আত্মোপলব্ধিতে “প্যারাডাইস লস্ট” পাঠ, এবং স্রষ্টার মুখে উচ্চারিত ‘It is finished!’—সবকিছুই মানবসৃষ্টির দেবতাসুলভ আকাঙ্ক্ষাকে নতুন করে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
তবুও দেল তোরো উভয় চরিত্রের প্রতিও তিনি সহানুভূতিশীল। ভিক্টরের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেমন তার পতনের কারণ, তেমনি দানবের যন্ত্রণা মানবতার প্রতীক। চলচ্চিত্রের শেষ অংশে এই দুই সত্তার ভাগ্য মিশে যায় এক করুণ অথচ কোমল সমাপ্তিতে।
গিলেরমো দেল তোরোর “ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন” শুধু
#ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন #গিলেরমো_দেল_তোরো #অস্কার_আইজ্যাক #জ্যাকব_এলরোর্ডি #মেরি_শেলি #সিনেমা_বিশ্লেষণ #সারাক্ষণ_রিপোর্ট

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট