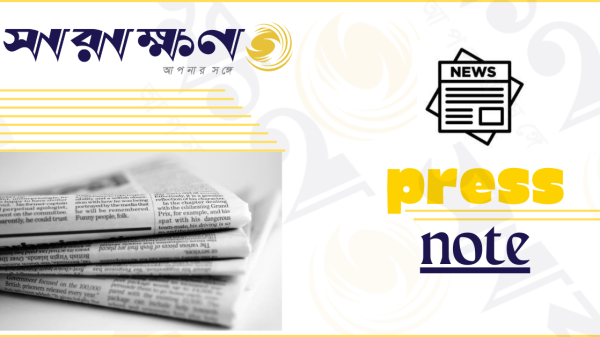সারাক্ষণ ডেস্ক
প্রথম আলোর একটি শিরোনাম “সারা দেশে ট্রেন চলাচল বন্ধ, ভোগান্তিতে যাত্রীরা”
রেলওয়ের রানিং স্টাফদের কর্মবিরতিতে সারা দেশে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। গতকাল সোমবার মধ্যরাতের পর থেকেই রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।
সকালে রাজধানীর কমলাপুর স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় অনেক যাত্রীকে বসে থাকতে দেখা গেছে। তাঁদের অনেকেই ট্রেন চলাচল বন্ধের খবর জানতেন না। সকাল সোয়া ৯টার দিকে স্টেশনে অনেক যাত্রীকেই ট্রেনের খবর জানতে আসতে দেখা যায়। ট্রেন চলবে না জেনে অনেকেই স্টেশন ছেড়ে চলে যান। তবে বয়স্ক ও নারীদের স্টেশনেই অপেক্ষা করতে দেখা গেছে।
রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, পঞ্চগড়, দিনাজপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় যাত্রীদের বসে থাকার খবর জানা গেছে। অনেকে বিকল্প পথে যাত্রা শুরু করেছেন।
মূল বেতনের সঙ্গে রানিং অ্যালাউন্স যোগ করে পেনশন এবং আনুতোষিক সুবিধা দেওয়ার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন রানিং স্টাফরা।গত বুধবার চট্টগ্রামে পুরোনো রেলস্টেশনে সংবাদ সম্মেলন করে ২৭ জানুয়ারির মধ্যে দাবি মানার শর্ত দেয় রেলওয়ে রানিং স্টাফ ও শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন। অন্যথায় ২৮ জানুয়ারি থেকে রেল চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দেয় তারা।
এই রানিং স্টাফরা হলেন গার্ড, ট্রেনচালক (লোকোমাস্টার), সহকারী চালক ও টিকিট পরিদর্শক (টিটিই)। তাঁরা সাধারণত দীর্ঘ সময় ট্রেনে দায়িত্ব পালন করেন। দৈনিক আট ঘণ্টার বেশি কাজ করলে বেসিকের (মূল বেতন) হিসেবে বাড়তি অর্থ পেতেন তাঁরা। এ ছাড়া অবসরের পর বেসিকের সঙ্গে এর ৭৫ শতাংশ অর্থ যোগ করে অবসরকালীন অর্থের হিসাব হতো।
দৈনিক ইত্তেফাকের একটি শিরোনাম “বাজারের আস্থাহীনতায় দর হারাচ্ছে ‘ভরসার’ বহুজাতিক কোম্পানিও”
অনেকটা নিশ্চিত ভালো মুনাফা পেতে বিনিয়োগকারীরা বহুজাতিক কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, শেয়ার বাজারের গভীরতা বাড়াতে বড় ভূমিকা রাখে এই বহুজাতিক তথা ভালো কোম্পানিগুলো। কিন্তু বাজারের আস্থাহীনতায় দর হারাচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। দর কমে গত এক বছরের মধ্যে এখন সর্বনিম্ন অবস্থানে এই কোম্পানিরগুলোর শেয়ারদর। গতকাল রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ার বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) মূল্যসূচকের পতনে ভূমিকা রেখেছে তালিকাভুক্ত বহুজাতিক কোম্পানিগুলোও।
এদিন ডিএসইতে তালিকাভুক্ত ১৩টি বহুজাতিক কোম্পানির মধ্যে ১২টির দরই কমেছে। কিন্তু কেন কমছে বহুজাতিক কোম্পানির শেয়ারদর? বাজার বিশ্লেষকরা বলেছেন, দেশে গত বছর জুলাই-আগস্টে আন্দোলনের পাশাপাশি অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করায় সামগ্রিকভাবে অন্যান্য খাতের মতো নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে দেশে ব্যবসা পরিচালনা করা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর আয় ও মুনাফায়। এছাড়া, অনেক ব্যাংক এখন ১২ শতাংশ পর্যন্ত সুদ দিচ্ছে। ফলে বিনিয়োগকারীরা শেয়ার না কিনে ব্যাংকে টাকা রাখছে। দেশি-বিদেশি অনেক বড় বিনিয়োগকারী ডলার সংশ্লিষ্ট সম্পদে বিনিয়োগ করছে। আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ক্রিপ্টো কারেন্সির দর বাড়তির দিকে। তারা বলেছেন, গত আগস্টে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) পুনর্গঠন করা হলেও বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে সংস্থাটি দৃশ্যমান কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে গত ৫ আগস্টের পর বিদেশি বিনিয়োগ কিছুটা বাড়লেও গত নভেম্বর ও ডিসেম্বরে আবার কমেছে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বহুজাতিক কোম্পানির শেয়ারদরেও।
বাজারের লেনদেনের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ডিএসইতে গতকাল লেনদেনকৃত মোট ৪০৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে মাত্র ৭৫টির, কমেছে ২৬১টির। আর অপরিবর্তিত রয়েছে ৬৭টির দর। এর মধ্যে তালিকাভুক্ত ১৩টি বহুজাতিক কোম্পানির মধ্যে ১২টির দরই কমেছে। দর কমা বহুজাতিক কোম্পানিগুলো হলো: ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কো. (ব্যাটবিসি), বার্জার পেইন্টস্, গ্রামীণফোন, লাফার্জহোলসিম, ম্যারিকো, বাটা, ইউনিলিভার, রবি, রেকিড বেনকাইজার, লিন্ডেবিডি ও হাইডেলবার্গ সিমেন্ট। অন্যদিকে দর বেড়েছে মাত্র সিঙ্গারবিডি বাংলাদেশ লি.-এর। ডিএসইর তথ্য বলছে, কোম্পানিগুলোর শেয়ারদর এখন গত এক বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে অবস্থান করছে। গতকাল ডিএসইতে লেনদেন শেষে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কো. বাংলাদেশ লি. -এর সমাপনী দর ছিল ৩৪৫ টাকা ২০ পয়সা, বার্জার পেইন্টসের ১৮১৫ টাকা ৮০ পয়সা, গ্রামীণফোনের ৩৩০ টাকা ১০ পয়সা, লাফার্জহোলসিমের ৪৯ টাকা ৮০ পয়সা, ম্যারিকোর ২৩০৪ টাকা ৬০ পয়সা, বাটা সুর ৮৭৬ টাকা ৭০ পয়সা, ইউনিলিভারের ২৫২৫ টাকা, সিঙ্গারের ১০৭ টাকা ৮০ পয়সা, রবির ২৭ টাকা ৬০ পয়সা, রেকিড বেনকাইজারের ৪১০৮ টাকা ৭০ পয়সা, হাইডেলবার্গ সিমেন্টের ২০৯ টাকা, আর এ কে সিরামিকসে্র ২২ টাকা ১০ পয়সা ও লিন্ডে বাংলাদেশের ৯৭৬ টাকা ২০ পয়সা। অন্যদিকে এক বছর আগে এই সময়ে কোম্পানিগুলোর শেয়ারদর ছিল, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কো. বাংলাদেশ লি. -এর ৫১৮ টাকা ৭০ পয়সা, বার্জার পেইন্টসের ২০০০, গ্রামীণফোনের ৩৮৭ টাকা, লাফার্জহোলসিমের ৭৭ টাকা ৮০ পয়সা, ম্যারিকোর ২৬০০, বাটার ১০২৫ টাকা, ইউনিলিভারের ৩৩৭০ টাকা, সিঙ্গারের ১৬১ টাকা, রবির ৩৫ টাকা ৭০ পয়সা, রেকিড বেনকাইজারের ৫২১৮ টাকা ১০ পয়সা, হাইডেলবার্গ সিমেন্টের ৩৭১ টাকা, আর এ কে সিরামিকসে্র ৪২ টাকা ৬০ পয়সা ও লিন্ডে বাংলাদেশের ১৮০০ টাকা।
বণিক বার্তার একটি শিরোনাম”বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি নেমেছে ১ দশমিক ৪১ শতাংশে”
কয়েক বছর ধরেই দেশের বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি বেশ মন্থর। গত ছয় মাসে তা আরো মন্থর হয়ে এসেছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই থেকে নভেম্বর) দেশের বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ বেড়েছে মাত্র ১ দশমিক ৪১ শতাংশ। এর আগে গত অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩ দশমিক ৪৬ শতাংশ।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৪ সালের জুন শেষে বেসরকারি খাতে ব্যাংক ঋণের স্থিতি ছিল প্রায় ১৬ লাখ ৪১ হাজার ২২৯ কোটি টাকা। নভেম্বর শেষে ঋণের এ স্থিতি বেড়ে ১৬ লাখ ৬৪ হাজার ৩২৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। সে হিসাবে পাঁচ মাসে বেসরকারি খাতে ঋণ স্থিতি বেড়েছে মাত্র ২৩ হাজার ৯৫ কোটি টাকা। আর ঋণ প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ১ দশমিক ৪১ শতাংশ।
ব্যাংক কর্মকর্তারা জানান, বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহ এর আগে এতটা মন্থর হয়ে আসতে দেখা যায়নি। নভেম্বরের পরও এ চিত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি। বরং এখন ঋণের যে প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে এরও বড় অংশ এসেছে অনাদায়ী সুদ ও সুদহার বৃদ্ধির প্রভাবে।
শুধু পাঁচ মাসের হিসাবে নয়, বরং নভেম্বর পর্যন্ত এক বছরের পরিসংখ্যানেও বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ কমে আসার চিত্র দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এক বছরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৭ দশমিক ৬৬ শতাংশ। যদিও চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর) জন্য ঘোষিত মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ৯ দশমিক ৮ শতাংশ ধরা হয়েছিল।
বেসরকারি খাত ঋণবঞ্চিত হলেও ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ নেয়া বেড়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) সরকারের ব্যাংক ঋণ বেড়েছে ৩ দশমিক ২৪ শতাংশ। যেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ে সরকারের ব্যাংক ঋণ কমেছিল ৬ শতাংশের বেশি। আর ২০২৩ সালের নভেম্বরের তুলনায় ২০২৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সরকারের ব্যাংক ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২০ দশমিক ৫১ শতাংশ।
মানবজমিনের একটি শিরোনাম “কেন বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় অত্যাবশ্যক?”
তিনটি বিভাগ নিয়ে অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র গঠিত। আর সেগুলো হলো: আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। দুঃখজনক ও আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের জন্য স্ব স্ব সচিবালয় থাকলেও বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় নেই। বিদ্যমান পুরো সচিবালয় তো শাসন বিভাগ তথা নির্বাহী বিভাগের পারপাস সার্ভ করে। অপরদিকে আইন বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় থাকবে বলে খোদ সংবিধান স্পষ্ট করে বলেছে। সংবিধানের ৭৯(১) অনুচ্ছেদ বলেছে, ‘সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকিবে’। কিন্তু বিচার বিভাগের জন্য কোনো স্বতন্ত্র সচিবালয় নেই। অতীতের কোনো সরকারই তা করেনি বা করতে দেয়নি।
বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ করা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ও আছে। নির্বাহী থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আংশিক বাস্তবায়ন করা হয় ২০০৭ সালে। ওই বছর এক অধ্যাদেশ জারি করে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা হয়। কিন্তু বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ অদ্যাবধি নেওয়া হয়নি। সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদ স্পস্ট করে বলেছে, ‘রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।’ সংবিধান ও ঐতিহাসিক মাসদার হোসেন মামলায় সর্বোচ্চ আদালতের দেয়া রায়ের আলোকে স্বতন্ত্র ও পৃথক বিভাগ হিসেবে গড়ে উঠতে বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় অতি জরুরি। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও সর্বোপরি নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচার বিভাগকে রক্ষার জন্য বিচার বিভাগের আলাদা সচিবালয় প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি।
সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অধঃস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকবে হাইকোর্ট বিভাগের। ১০৯ অনুচ্ছেদ স্পষ্ট করে বলেছে, ‘হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন সকল [আদালত ও ট্রাইব্যুনালের] উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকিবে।’ সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদের মর্ম অনুযায়ী অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ হাইকোর্ট বিভাগের একচ্ছত্র অধিকার। সাংবিধানিক এই বাধ্যবাধকতা সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ (full fledged) বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। তাই সংবিধানের ৭৯ অনুচ্ছেদে যেভাবে সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকার কথা বলা হয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় নিশ্চিতের লক্ষ্যে পৃথক অনুচ্ছেদ সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা উচিৎ যাতে কোনো রাজনৈতিক সরকার এই বিষয়টিকে কোনোভাবেই অবজ্ঞা করতে না পারে।
বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের মামলার সংখ্যা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধস্তন আদালতের বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কারণে সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রির কর্মপরিধি অতীতের তুলনায় ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অবস্থা ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলেও বিচার বিভাগের জন্য পৃথক একটি সচিবালয় স্থাপন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। তাই সার্বিক বিশ্লেষণে কেবলমাত্র পৃথক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই অধস্তন আদালতের বিচারকগণের শৃঙ্খলা, বদলি, পদোন্নতি, ছুটি ও অন্যান্য বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মাসদার হোসেন মামলার আলোকে বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা ও পৃথকীকরণ নিশ্চিত করা সম্ভব। বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় না থাকার কারণে দীর্ঘদিন ধরে বিচার বিভাগে অনেকটা দ্বৈত শাসন চলে আসছে যা বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতার মূলে আঘাত হানে।

 Sarakhon Report
Sarakhon Report