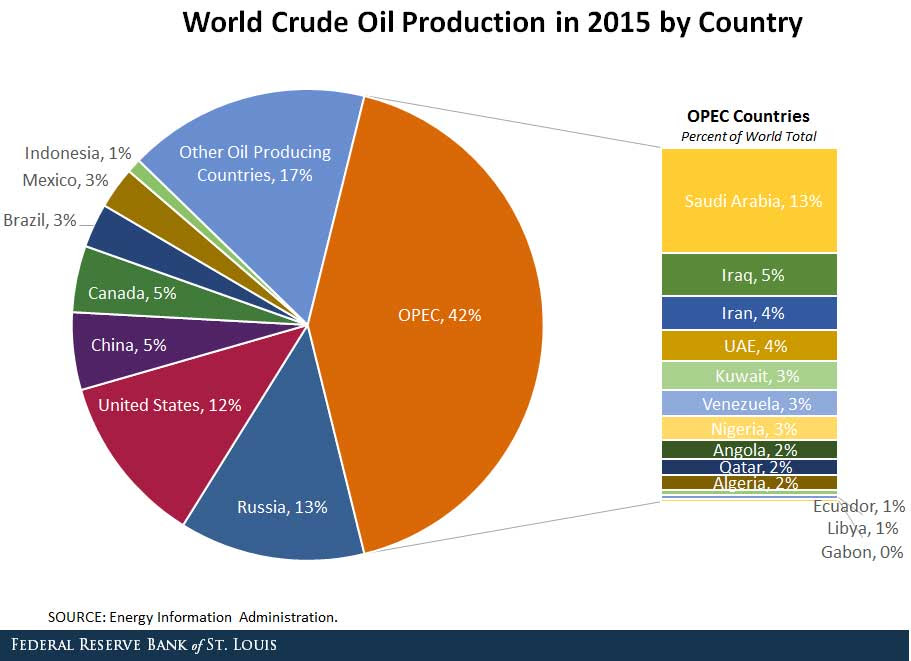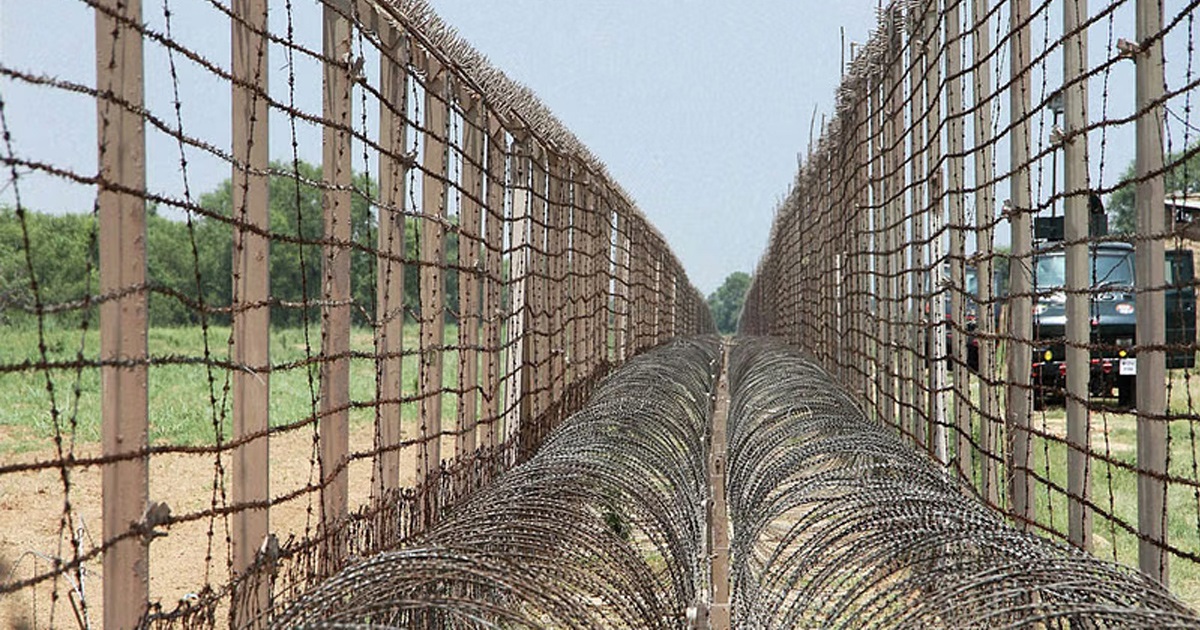নীলাঞ্জন সিরকার
ভারতের জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সবশেষ শাসন করেছিল ১৯৯০-এর দশকে। সেই সময়কার “ধূলিময় শহর” দিল্লির চেহারা এখন পুরোপুরি পাল্টে গেছে। এখন দিল্লি বিশাল এক মহানগর, যেখানে ভারতের নানা প্রান্ত ও বিদেশ থেকেও মানুষের আগমন ঘটে—জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের (এনসিআর) মূল কেন্দ্র হিসেবেই। ২০০০-এর দশকের শুরুর দিকে কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের নেতৃত্বে দিল্লির অবকাঠামো ও পরিবেশে ব্যাপক পরিবর্তন আসে—প্রশস্ত রাস্তা, শহরের সবুজায়ন ইত্যাদি। আরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বে আম আদমি পার্টি (এএপি) ২০১৩ সালে প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় আসে, মূলত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির কারণে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির অসন্তোষের ঢেউকে কাজে লাগিয়ে।
আজকে এএপি-র পরাজয়ের প্রধান কারণ হলো মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির ভোটারদের দলত্যাগ। এমনকি কোনো একসময়ে অপ্রতিরোধ্য বলে বিবেচিত কেজরিওয়ালও নিজের আসন হারিয়েছেন। ক্ষমতায় আসার পরে এএপি নিজেকে কিছুটা রূপান্তরিত করে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণির কথা মাথায় রেখে বিনামূল্যে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, সরকারি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে সংস্কার ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি দেয়। একইসঙ্গে “দুর্নীতিমুক্ত” ভাবমূর্তি বজায় রেখে ও “বিকল্পধর্মী” রাজনীতির বার্তা দিয়ে কিছুটা মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমর্থনও ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মদ লাইসেন্সে দুর্নীতি নিয়ে বিতর্ক, কিছু নেতা-মন্ত্রীর বিলাসিতার অভিযোগ এবং ২০২০ সালে ক্ষমতায় ফেরার পর তৈরি হওয়া এক ধরনের স্থবিরতা—সব মিলিয়ে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তরা এএপি-কে ছেড়ে চলে গেছেন।

এএপি মূলত “দিল্লি মডেল”-এর মাধ্যমে ভর্তুকি ও সরকারি সুবিধাকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করে। এই পরাজয় তাদের ভাবমূর্তিতে বড় ধাক্কা দেবে। কিন্তু দিল্লি এমন একটি জায়গা যেখানে মাথাপিছু আয় প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা (ভারতের মধ্যে তৃতীয় সর্বোচ্চ রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল) এবং ভোটারের অর্ধেকের বেশি উচ্চ/সাধারণ জাতিভুক্ত। এমন একটি শহরে এ ধরনের মডেল চালু রাখা কঠিন, এবং দিল্লির এই জনমিতিই এএপি-র পরাজয়ের অন্যতম কারণ। দিল্লিতে জয় পেতে হলে যে কোনো দলকেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ভোটারের সমর্থন পেতে হবে। এই শ্রেণির মনোভাবের পরিবর্তন দেখা যায় বিশেষ করে পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিল্লিতে, যেখানে ৭০টির মধ্যে ২১টি আসন অবস্থিত। পাঞ্জাবি ও হরিয়ানভি-ভাষী জনগোষ্ঠীর আধিক্য এ অঞ্চলে; এরা ব্যবসায়িক প্রবণতা সম্পন্ন, আর্থ-সামাজিকভাবে উন্নতি-অন্বেষী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। পাঁচ বছর আগে, এএপি এই অঞ্চলে ২১টির মধ্যে ২০টি আসনে জিতেছিল। কিন্তু এবার তারা ১৮টিতে হেরেছে।
এই এলাকায় বসবাসকারী লোকজন সাধারণত জাতীয় নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী মোদি ও বিজেপিকে সমর্থন করে এসেছেন। এএপি আশা করেছিল বিধানসভা নির্বাচনে এই ভোটারদের এক বড় অংশকে নিজের পক্ষে আনতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি যেখানে ৫৭% ভোট পেয়েছিল, পরের বছর অর্থাৎ ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেই ভোট ৩৯%-এ নেমে গিয়েছিল। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি আবার ৫৭% ভোট পায়, আর ২০২৫ সালের রাজ্য নির্বাচনে তাদের সম্ভাব্য চূড়ান্ত ভোটশেয়ার প্রায় ৪৬% বলেই মনে হচ্ছে। অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচনে এখনো বিজেপির ভোট কিছুটা কমলেও, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের ক্রমবর্ধমান এএপি-বিরোধী মনোভাবই দিল্লির নিয়ন্ত্রণ বিজেপির হাতে তুলে দিয়েছে।

দিল্লির রাজনীতি যেভাবে আলাদা বৈশিষ্ট্য বহন করে, এই ফলাফল অবশ্যই সারা দেশে একটি প্রতিধ্বনি তুলবে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এএপি-র বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতা, যার মধ্যে সুপ্রিমো আরবিন্দ কেজরিওয়ালও আছেন, কারাবরণ করেছেন। কিন্তু এটি এএপি-র জন্য সহানুভূতির আবহ তৈরি করতে পারেনি; বরং তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হয়েছে অনেকের কাছে। পরিচয়-ভিত্তিক রাজনীতির প্রশ্নে এএপি একটি ‘নরম হিন্দুত্ব’ লাইন নিয়েছে, যেখানে কেজরিওয়াল নিজেই কিছু মন্তব্য করেছেন; মুখ্যমন্ত্রী অতিশি আবার আরেক ধাপ এগিয়ে ‘কঠোর হিন্দুত্ব’-এর প্রয়াস চালিয়ে কিছুটা হাস্যকর অবস্থায় পড়েছেন। নেতারা নিজেদের (কেননা কারাবরণের আশঙ্কা প্রবল ছিল এবং নির্বাচিত সরকারের চেয়ে লেফটেন্যান্ট গর্ভনর বেশি ক্ষমতা পাচ্ছিল) বাঁচানোর চেষ্টায় ব্যস্ত থাকায় দিল্লির মৌলিক সমস্যাগুলো বরাবরই অধরা থেকে গেছে। একসময় ‘বিকল্পধর্মী রাজনীতি’ দিয়ে নিজেদের গড়ে তোলা দলটি ক্রমে অন্য সবার মতো হয়ে উঠেছে। এর প্রভাব পড়বে গুজরাট ও পাঞ্জাবের মতো রাজ্যগুলিতেও, যেখানে এএপি ইতোমধ্যেই কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে।
২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে আমরা যে কটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন দেখেছি—হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, আর এখন দিল্লির দিকে তাকালেও দেখা যায়, এই জয়গুলোর পেছনে প্রধানমন্ত্রী মোদির ভূমিকা তুলনামূলকভাবে কম। বিজেপির যেসব অপ্রত্যাশিত জয় হয়েছে সেগুলো অনেকটাই সংগঠনের মজবুত ভিত্তি ও দক্ষতার কারণে—প্রার্থী বাছাইয়ে, ভোটারদের সংগঠিত করার ব্যাপারে, এবং নিজেদের প্রধান ভোটব্যাংক অটুট রাখার প্রশ্নে দলটি খুব কম ভুল করে। তবে এটি বিজেপির জন্য এক নতুন ধরনের রাজনীতি। এক অদ্ভুত দ্বৈরথ হলো, এমনভাবে রাজ্য জিতলে প্রধানমন্ত্রী মোদির ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা নাটকীয় বা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাড়ে না। দীর্ঘদিন “ব্র্যান্ড মোদি” নির্ভর করে চলা দলটি ধীরে ধীরে নতুন এক পরিচয়ের দিকে এগোচ্ছে (যদিও সেটি ঠিক কী রকম হবে, এখনো স্পষ্ট নয়)। অন্যদিকে বিজেপির অবশ্যই বুঝতে হবে, দিল্লির চাহিদা কী এবং এই ২১শতকের বৈশ্বিক মহানগরীকে তারা কীভাবে পরিচালনা করবে।
- নীলাঞ্জন সিরকার, আহমেদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস-এর সহযোগী অধ্যাপক।

 Sarakhon Report
Sarakhon Report