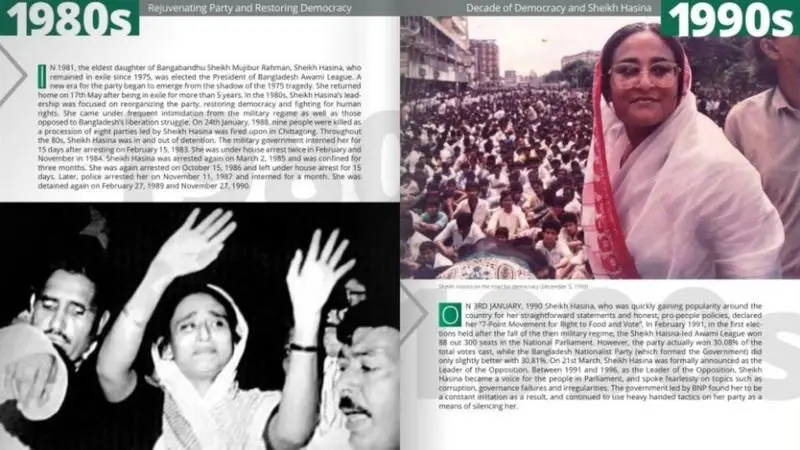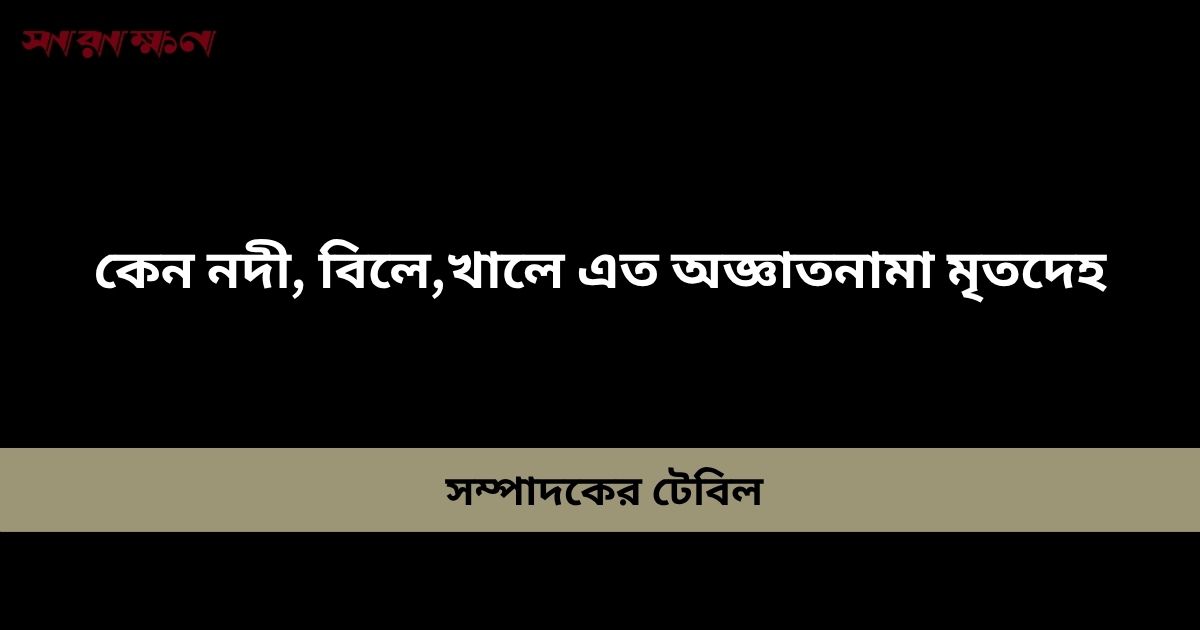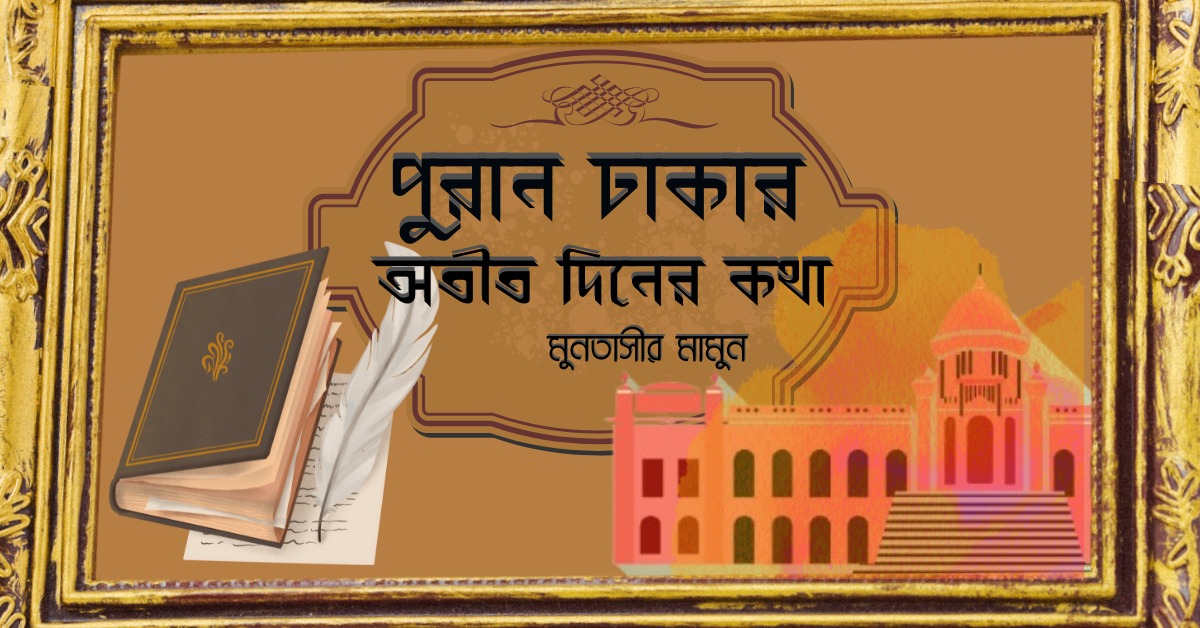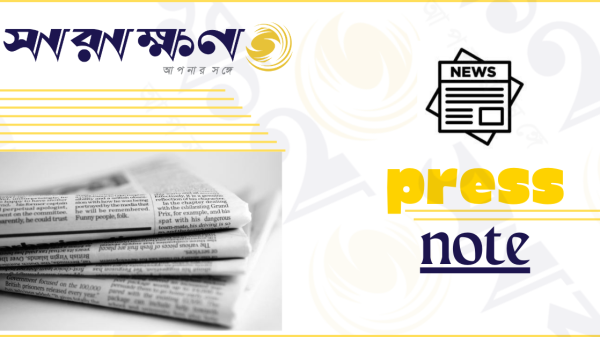বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দুই শতক আগে যে বিশাল ম্যানগ্রোভ বন বিস্তৃত ছিল, তা আজ আর কল্পনাও করা যায় না। ইতিহাসের পাতা ও ঔপনিবেশিক আমলের জরিপ থেকে জানা যায়, প্রায় ২০০ বছর আগে বাংলাদেশের উপকূলজুড়ে ম্যানগ্রোভ বন ছিল আনুমানিক ২০,০০০–২২,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায়। এই বনের সবচেয়ে বড় অংশ ছিল সুন্দরবন, যা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ভাগ করা। তখনকার সুন্দরবন বাংলাদেশের অংশে প্রায় ১১,০০০–১২,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত ছিল। শুধু খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা নয়, বরিশাল বিভাগের দক্ষিণাঞ্চল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা জেলার উপকূলীয় চর এবং সন্দ্বীপ, হাতিয়া, মহেশখালী, কুতুবদিয়া দ্বীপগুলিতেও ম্যানগ্রোভ প্রভাবিত বনাঞ্চল ছিল। মেঘনা নদীর মোহনা ও শাখা নদীর চরগুলোতে তখন নদীর পলি, নোনা ও মিঠা পানির মিশ্রণ—সব মিলিয়ে এক অনন্য জীববৈচিত্র্যময় পরিবেশ গড়ে তুলেছিল।
এই বনে তখন বাস করত অসংখ্য প্রাণী। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা ছিল ৫০০–৬০০ এর মতো বলে অনুমান করা হয়। বিশাল পাল করে চিতল হরিণ বনের ভেতরে ঘুরে বেড়াত, বুনো শূকর, গন্ধগোক্র, বনবিড়াল, মেছোবাঘের মত স্তন্যপায়ী প্রাণীর আধিপত্য ছিল। সরীসৃপের মধ্যে নোনা জলের কুমির ছিল প্রচুর, এমনকি একসময় মিঠা জলের ঘড়িয়ালও দেখা যেত। নদী ও মোহনার পানিতে গাঙ্গেয় ও ইরাবতী ডলফিনের বাস ছিল স্বাভাবিক। পাখিদের মধ্যে মাছরাঙা, বক, শামুকখোল, জলপিপি, পানকৌড়ি সহ অসংখ্য জলপাখি প্রজনন করত। জলজ জীববৈচিত্র্যে ছিল শাপলাপাতা মাছ, রুপচাঁদা, ভেঁটকি মাছ, পঞ্চাশের বেশি কাঁকড়া প্রজাতি, শামুক, ঝিনুক। এ বন বাংলাদেশের উপকূলের প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ঠেকাত এবং উপকূলীয় মানুষের জীবিকা, খাদ্য ও কাঠের উৎস হিসেবে কাজ করত।

কিন্তু এই বন উজাড় হতে শুরু করে ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে। ১৮৫৩ সালে ব্রিটিশ সরকার সুন্দরবনকে রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা করলেও, কাঠ কাটার লাইসেন্স দিয়ে রাজস্ব আদায় শুরু করে। নদী ও চরাঞ্চলে নীলচাষ, ধানচাষ, লবণ উৎপাদনের জন্য ম্যানগ্রোভ কেটে ফেলা হয়। ঊনিশ শতকের শেষ দিকে নতুন নতুন চরে বসতি স্থাপন, বাঁধ নির্মাণ ও কৃষি সম্প্রসারণ আরও তীব্র হয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ সামলাতে উপকূলীয় চর ও দ্বীপগুলোতে ব্যাপক বন নিধন ঘটে। ১৯৬০–৮০ এর দশকে সেচ প্রকল্প, নদীশাসন ও চিংড়ি চাষের বিস্তার ম্যানগ্রোভের ওপর শেষ বড় আঘাত হানে।
ম্যানগ্রোভ ধ্বংসের প্রধান কারণ ছিল কৃষি সম্প্রসারণ—ধানক্ষেত, চিংড়ি ঘের ও লবণ খামার গড়ে তুলতে বন কাটা। নদীর বাঁধ ও সেচ প্রকল্পের কারণে মিঠা জলের প্রবাহ কমে যায়, ফলে বনের লবণাক্ততা বাড়ে এবং গাছ মারা যায়। বাণিজ্যিক লগিংয়ে সুন্দরবনের কাঠ নৌকা, বাড়ি ও রেলস্লিপার নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, নদীভাঙন ও নতুন চর জয় করার আকাঙ্ক্ষা বন উজাড়কে ত্বরান্বিত করে। এ ছাড়া শিল্প দূষণ, নদীতে বর্জ্য ফেলা ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক ব্যবহার ম্যানগ্রোভের মাটি ও পানি দূষিত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের তীব্রতাও ধ্বংসের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে।

ফলে দুই শতকে বাংলাদেশ তার ম্যানগ্রোভ বনের অর্ধেকেরও বেশি হারিয়েছে। FAO এবং বন অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ১৮০০–১৮৫০ সালে যেখানে ২০–২২ হাজার বর্গকিলোমিটার বন ছিল, ১৯৫০ সালে তা প্রায় ১৫–১৬ হাজার বর্গকিলোমিটারে নেমে আসে। ১৯৯০ সালের মধ্যে তা প্রায় ৭ হাজার বর্গকিলোমিটারে নেমে আসে। ২০২০–২৪ সালের হিসেবে বাংলাদেশের অংশে সুন্দরবন প্রায় ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার। অর্থাৎ দুই শতকে প্রায় ৭০ শতাংশ বনাঞ্চল হারিয়ে গেছে।
বর্তমানে সুন্দরবন বাংলাদেশের একমাত্র বড় ম্যানগ্রোভ বন। এর প্রায় ৫২ শতাংশ সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষিত, এবং এটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। তবে সংরক্ষিত এলাকা হলেও সমস্যার শেষ নেই। নদী শাসনের কারণে পলি সরবরাহ কমে গেছে, ফলে মাটি ক্ষয় হচ্ছে। নদীর মিঠা জল প্রবাহ কমে গিয়ে লবণাক্ততা বাড়ছে, যা গাছের মৃত্যুর হার বাড়িয়ে দিচ্ছে। শিল্প দূষণ—বিশেষ করে খুলনা-মোংলার শিল্প এলাকা থেকে আসা বর্জ্য নদীতে ফেলে সুন্দরবনের পানি ও মাটি দূষিত করছে। স্থানীয় মানুষ জীবিকার জন্য অতিমাত্রায় মাছ, কাঁকড়া ও মধু সংগ্রহ করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন সিডর, আইলা, বুলবুল ও আম্পান এই বনের অনেক অংশ ধ্বংস করেছে, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ক্রমাগত হুমকি।

প্রাণবৈচিত্র্যও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা ৫০০–৬০০ থেকে নেমে এসেছে প্রায় ১১৪ (২০১৮ সালের হিসাব)। চিতল হরিণ এখন প্রায় ৭০–৮০ হাজারে সীমিত। নোনা জলের কুমির কয়েক হাজার থেকে ১৫০–২০০-এ নেমে এসেছে, এবং গাঙ্গেয় ও ইরাবতী ডলফিনও ক্রমশ বিলুপ্তির পথে।
বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন—যদি এই ধারা বজায় থাকে, তাহলে ৫০–১০০ বছরের মধ্যে সুন্দরবনের বড় অংশ বিপন্ন হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠ যদি ১ মিটার বাড়ে, তাহলে সুন্দরবনের ১৫–২০ শতাংশ এলাকা স্থায়ীভাবে নিমজ্জিত হতে পারে। নদীর পলি না এলে মাটি ক্ষয় অব্যাহত থাকবে এবং নতুন ম্যানগ্রোভ গাছ জন্মাবে না।
এখনো সময় আছে সুন্দরবন ও বাংলাদেশের বাকি ম্যানগ্রোভ বন বাঁচানোর। সমাধান হিসেবে দরকার নদীর মিঠা জল প্রবাহ ফিরিয়ে আনা, সীমিত ও টেকসই চিংড়ি চাষ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় নিশ্চিত করা, শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা, জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা তৈরি করা এবং বাংলাদেশ–ভারতের মধ্যে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা। এই কাজগুলো না করলে আমরা হারিয়ে ফেলব আমাদের উপকূলের প্রাকৃতিক ঢাল, জীববৈচিত্র্য এবং লাখো মানুষের জীবিকা—যা একবার হারালে আর কখনো ফিরে আসবে না।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট