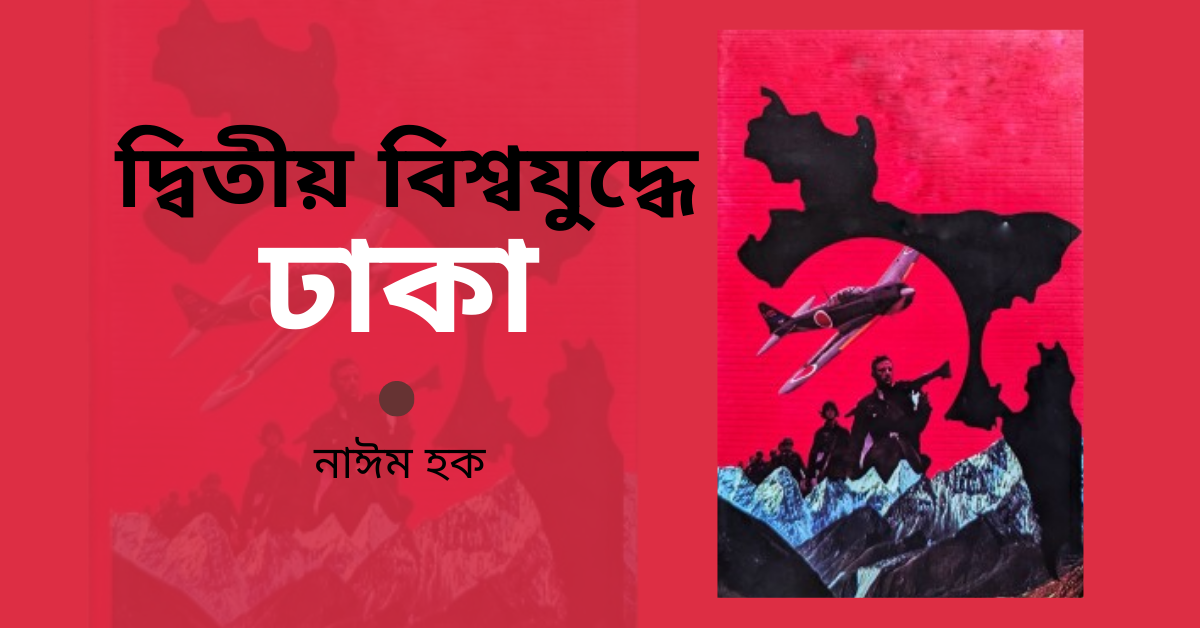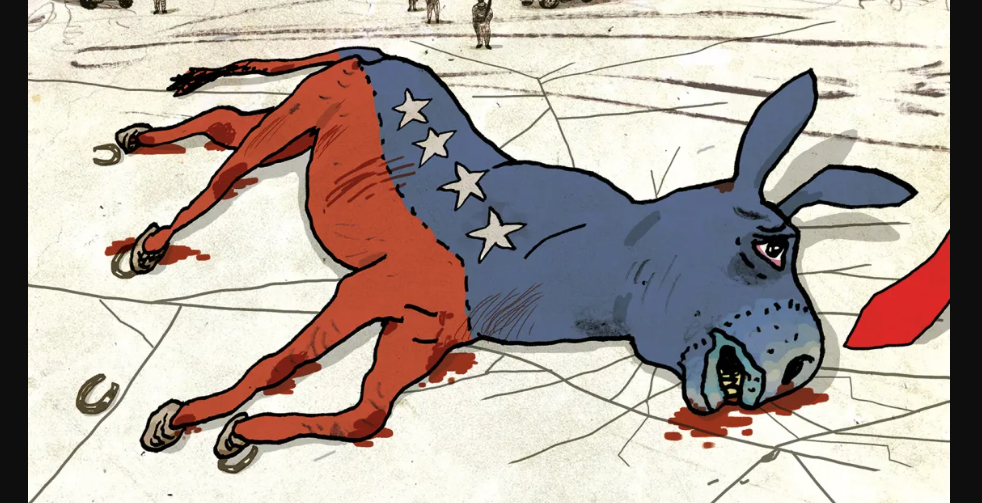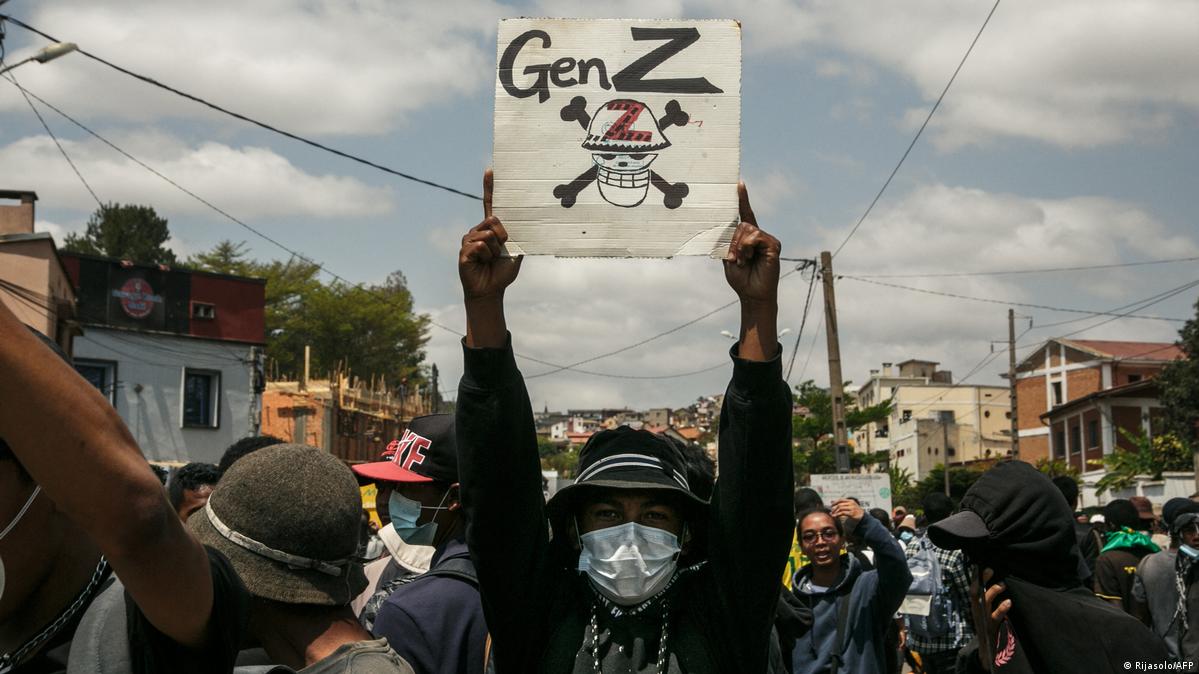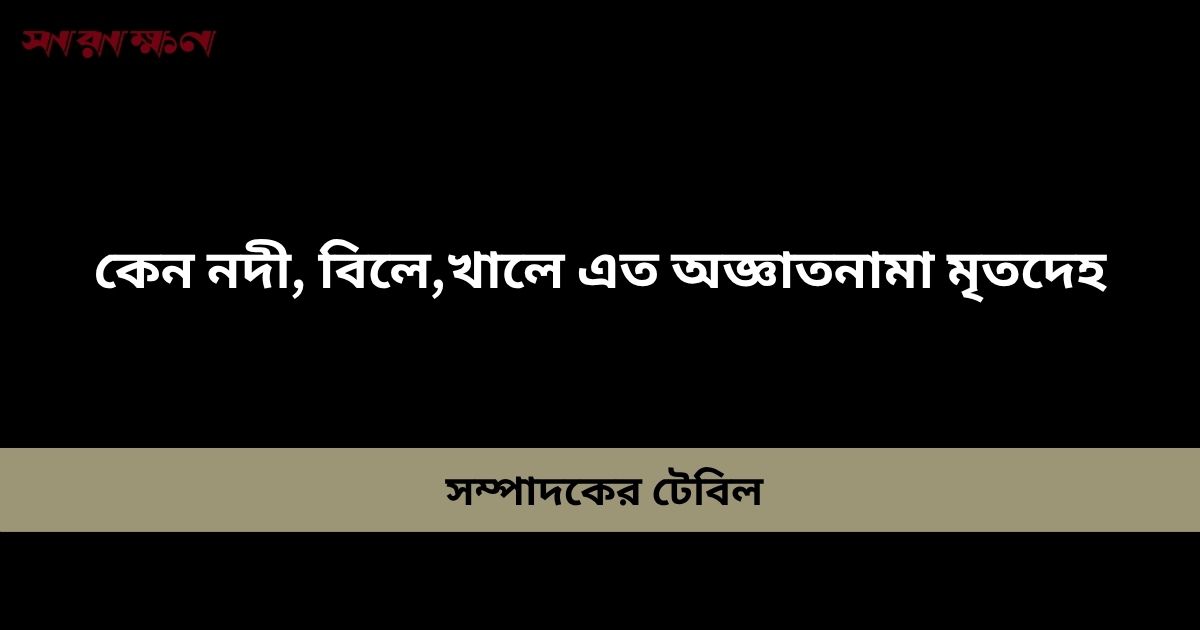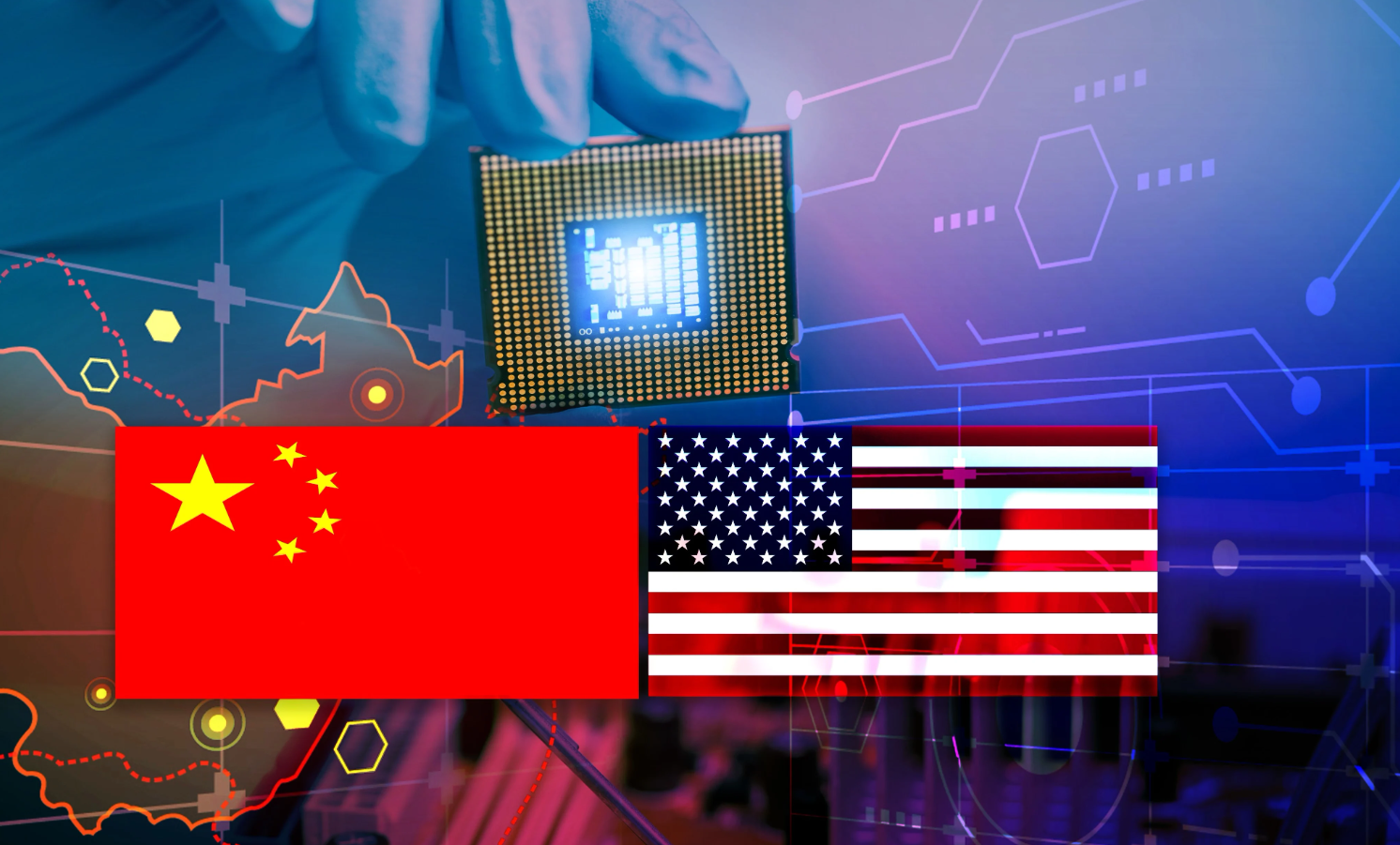কুমার নদ চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া এলাকা থেকে উৎপত্তি লাভ করে, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও কুষ্টিয়ার সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়ে মাগুরার কাছে নবগঙ্গা নদীতে মিলিত হয়। নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২৪‑১৪৪ কিলোমিটার এবং গড় প্রস্থ ৭৫‑১০৭ মিটার। শীতল ও কালো পানির জন্য এটি স্থানীয়ভাবে “কালোবিল” নামে পরিচিত ছিল।
নদীগুলোর যোগাযোগ চেইন ও অঞ্চল সংযোগ
চুয়াডাঙ্গা → ঝিনাইদহ → মাগুরা → রাজবাড়ী
কুমার নদী মাথাভাঙ্গা থেকে শুরু করে নবগঙ্গা–চিত্রা অববাহিকায় প্রবাহিত হয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ নদীপথ হিসেবে ব্যবহৃত হতো।
রাজবাড়ী পর্যন্ত রুট: কুমার → নবগঙ্গা → গড়াই → পদ্মা → ঢাকার গোলন্দো বা আরিচা ঘাট এবং খুলনা–মংলা বন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এই নদীপথ আন্তঃজেলা এবং জেলা থেকে মহানগরমুখী যাতায়াতকে সহজ করে তুলেছিল।

গত দুই শতকের ব্যবসা ও যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু
বর্ষা মৌসুমে নদীর পানিতে ভরা থাকায় চাল, আটা, পাট, মাছ, কাঠ, ইট, মাটি ইত্যাদি পণ্য সহজে বড় বাজার ও বন্দরে পরিবহন করা যেত।
মানব যোগাযোগের দিক থেকেও নদী ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবানীগঞ্জ, ঝিনাইদহ, মাগুরা থেকে খুলনা ও ঢাকার দিকে যাত্রী ও ডাকপত্র পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হতো।
শৈলকুপা, নগরকান্দা, বাখুন্ডা, মুকসুদপুরসহ অনেক বাজার ও ঘাট এই নদীর পাশে গড়ে উঠেছিল। নদীই ছিল তাদের জীবনদায়ী যোগাযোগ রুট।

ব্যবহৃত যোগাযোগ মাধ্যম
১. দেশি নৌকা, কোষা ও ডিঙ্গি
ছোট দূরত্বে কৃষক ও পথচারীরা ফল, মাছ ও গ্রামীণ পণ্য আদান-প্রদানে এগুলো ব্যবহার করত।
২. বড় পালতোলা নৌকা ও স্পিডবোট
১৯শ শতক থেকে ২০শ শতকের মাঝামাঝি পর্যায়ে চালু হয় এবং বড় মালবাহী পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত হতো।
৩. স্টিমার ও ইঞ্জিনচালিত লঞ্চ
ঝিনাইদহ ও মাগুরা অংশে স্টিমার ও লঞ্চ পরিষেবা ছিল। খুলনা ও আরিচা ঘাটের সঙ্গে সংযোগ ছিল এবং যাত্রী ও মাল পরিবহন নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী চলত। নদীর গভীরতা ৩০‑৪০ ফুট হওয়ায় এসব চলাচল সম্ভব ছিল।

নদীর বন্দর সংযোগ
যদিও কুমার নদীর সঙ্গে বড় কোনো সমুদ্রবন্দর যুক্ত ছিল না, তবুও নগরবন্দর যেমন খুলনা, নারায়ণগঞ্জ বা গোয়ালন্দের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ ছিল।
শৈলকুপা, নগরকান্দা, মুকসুদপুর ও বাখুন্ডা ঘাট থেকে নদীপথে জেলা সদর ও শহরগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।
গ্রাম থেকে শহরে মানুষ ও পণ্য পরিবহন তুলনামূলকভাবে সস্তা, দ্রুত ও সুবিধাজনক ছিল।
স্টিমার রুটের স্মৃতি
ঝিনাইদহ ও মাগুরা অংশে ১৯৬০‑৭০ এর দশক পর্যন্ত স্টিমার ও বড় ইঞ্জিনচালিত নৌযান চলাচল করত।
মাঝিপাড়া ও শহরঘাট থেকে খুলনা এবং আরিচা ঘাট পর্যন্ত রুট ছিল।
অনেকেই স্মরণ করেন, সেই সময়ের স্টিমার যাত্রা ছিল আনন্দময় ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ। ঘাটে নৌকা থামার সময় পল্লীগীতি, ভাটিয়ালি সুরে গান বাজত—যা নদীজীবনের অংশ ছিল।

মাছের বৈচিত্র্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব
কুমার নদীতে ছিল রুই, কাতলা, মৃগেল, বোয়াল, কালবাউস, শিং, গজার, কৈ, মাগুর, শোল, পুঁটি ইত্যাদি মাছের প্রাচুর্য।
এই মাছগুলো স্থানীয় বাজারে বিক্রির পাশাপাশি দূরবর্তী শহরেও পাঠানো হতো।
মাছ ধরার সরঞ্জাম হিসেবে খাঁড়া জাল, চাপেলি, ঘুনি, দাড় জাল ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো। গ্রামের অনেক মানুষের জীবিকা নদীকেন্দ্রিক ছিল।
এখন: সংকটাপন্ন নদী ও বাস্তবতা
জি‑কে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর কুমার নদীর প্রবাহ কমে যায় এবং অনেকাংশে এটি একটি খালের রূপ নেয়।
বর্তমানে নদীর অধিকাংশ অংশ দখল ও দূষণের শিকার। অবৈধ স্থাপনা, ইটভাটা, বর্জ্য নিষ্কাশন, এবং মধ্যরাতে বালু উত্তোলন নদীর নাব্যতা ও সৌন্দর্য ধ্বংস করেছে।
২০১৬ সালে কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প অনুমোদন পেলেও তার বাস্তবায়ন এখনও অসম্পূর্ণ। নদীর ঐতিহ্য ও জীববৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন সুসংগঠিত পরিকল্পনা ও জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ।
কুমার নদী দুই শতকেরও বেশি সময় ধরে গ্রামীণ জীবন, বাজার, মানুষের চলাচল ও মাছসম্পদের অন্যতম ভিত্তি ছিল। আজও এর ঐতিহ্য ও গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট