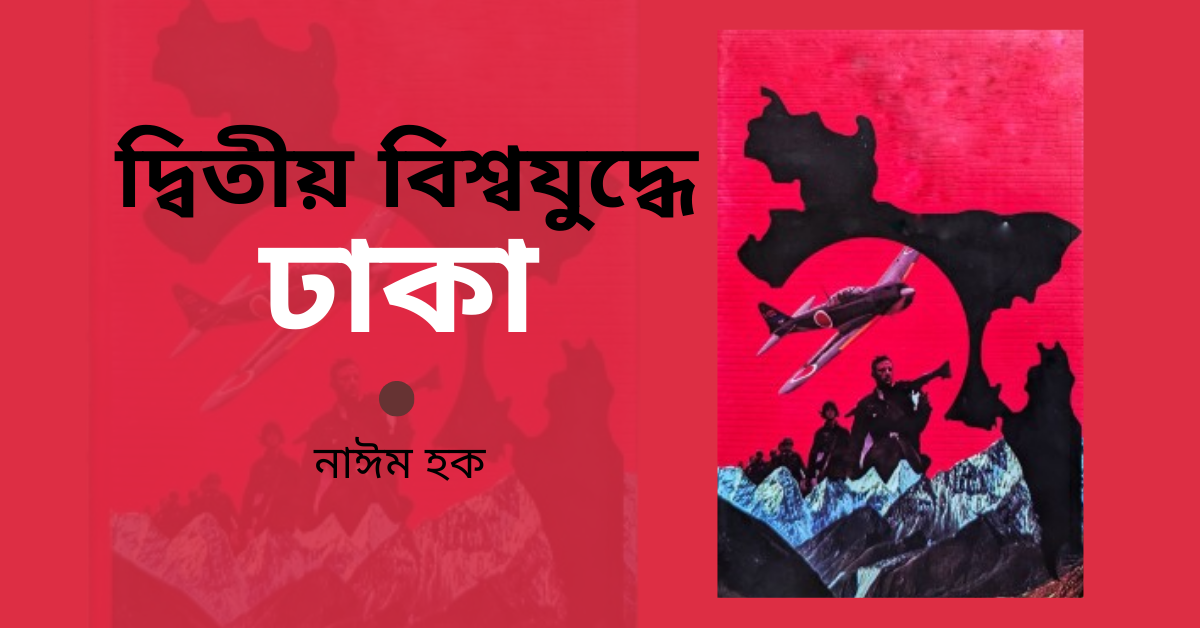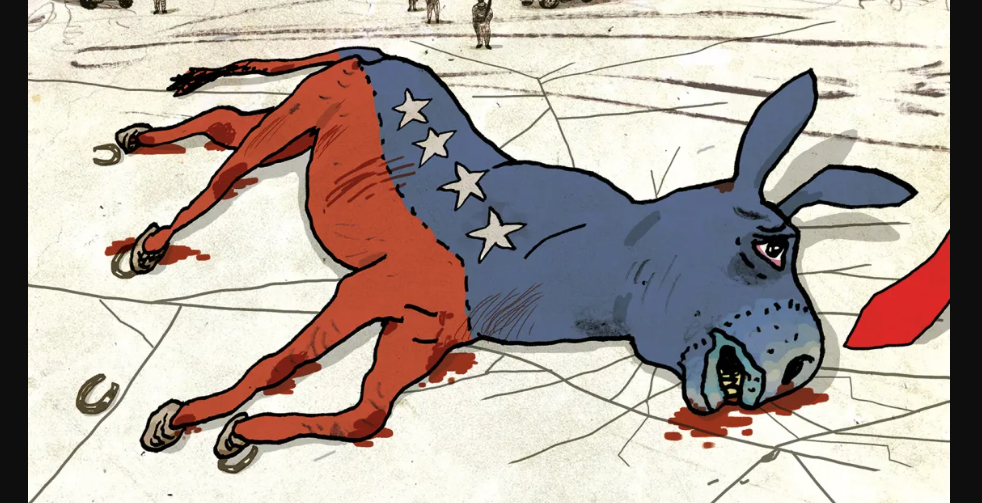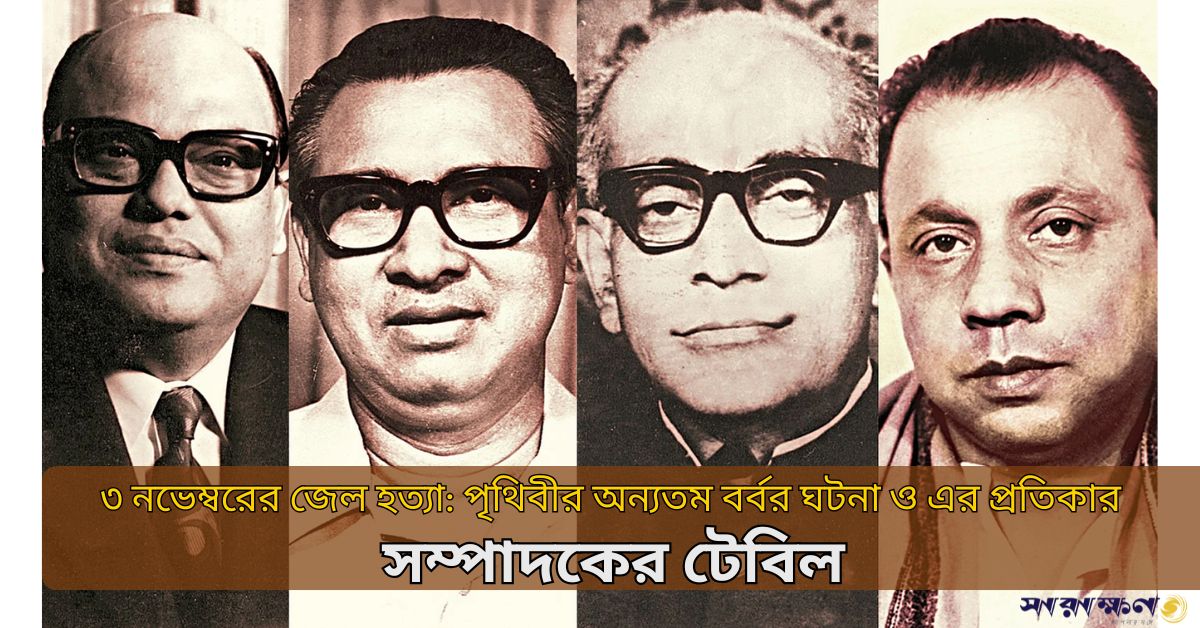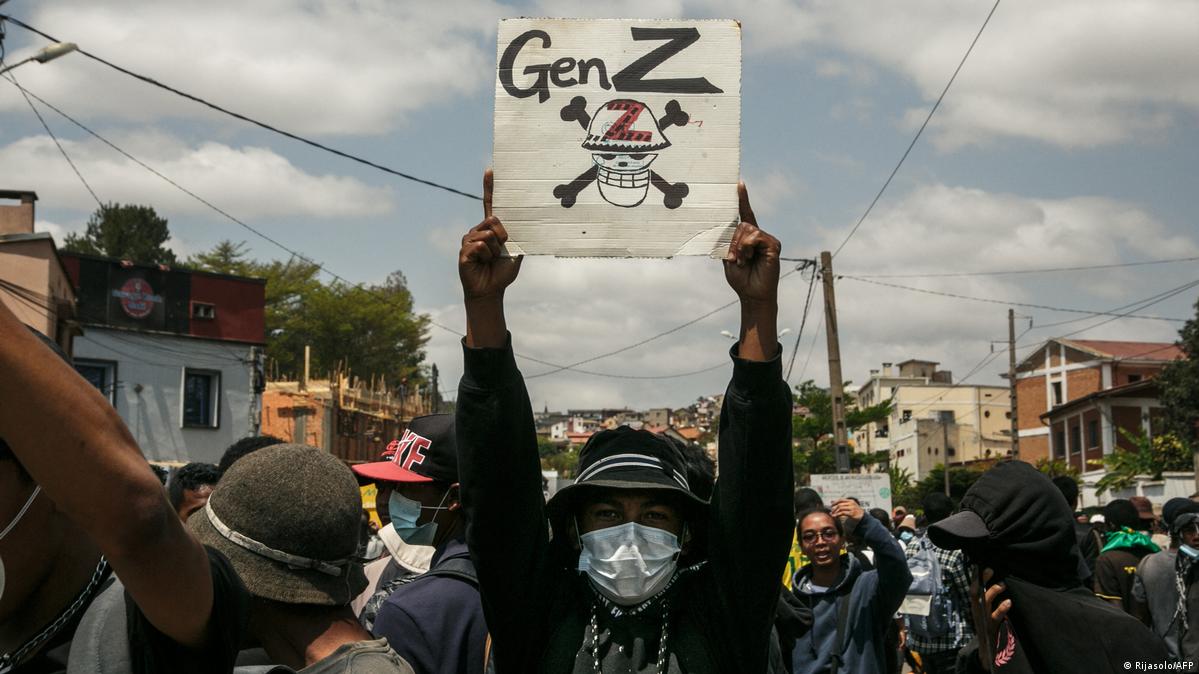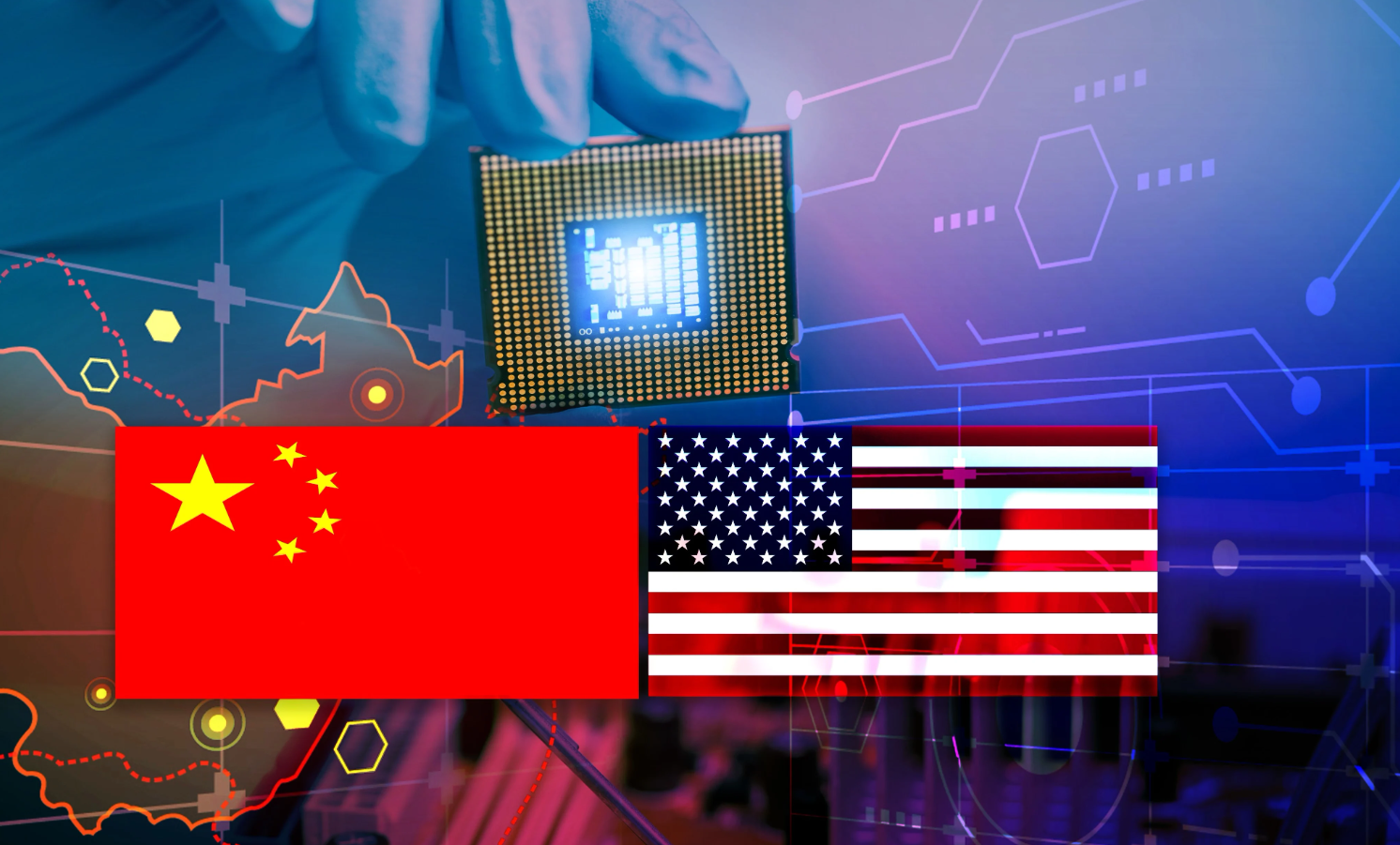প্রতিষ্ঠা ও প্রাচীন পটভূমি
শামবাজার ঢাকার অন্যতম প্রাচীন ব্যবসাকেন্দ্রগুলোর একটি। এর উৎপত্তির সঠিক সাল নির্ধারণ করা কঠিন হলেও গবেষকদের মতে, এটি মুঘল আমলের শেষদিকে বা ব্রিটিশ শাসনের শুরুর দিকে গড়ে ওঠে, আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। ‘শামবাজার’ নামটির উৎস নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, এটি ‘শাহমবাজার’ থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে, আবার কেউ বলেন, পারস্য থেকে আগত ব্যবসায়ীদের ‘শাম’ অঞ্চল (প্রাচীন সিরিয়া-ইরান-ইরাক অঞ্চলকে তৎকালীন সময়ে ‘শাম’ বলা হতো) থেকে আগত হওয়ার কারণেই এর নাম হয় ‘শামবাজার’। এই বাজার ছিল নদীনির্ভর ব্যবসার একটি কেন্দ্র, যেখানে বুড়িগঙ্গা ও সূত্রাপুর খাল সংলগ্ন অবস্থানের কারণে নদীপথে ব্যবসা সহজতর হয়েছিল।
ঔপনিবেশিক আমলে শামবাজারের স্বর্ণযুগ
উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের শুরুর দিকে শামবাজার ঢাকার অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। এই বাজার তখন বৃহত্তর পূর্ববঙ্গের অন্যতম পাইকারি কেন্দ্র হয়ে ওঠে। চাল, ডাল, মসলা, পাট, কাঁচা চামড়া, তামাক, কাঠসহ নানা পণ্যের পাইকারি বেচাকেনা হতো এখানে। ব্রিটিশ আমলে বুড়িগঙ্গার মাধ্যমে নবাবগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, বরিশাল এবং এমনকি ফরিদপুর অঞ্চল থেকেও নৌপথে পণ্য আসত এই বাজারে। এ সময়েই শামবাজার ঘাট এবং বাজারটির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ব্যবসায়ী মহলে।
অতিরিক্তভাবে শামবাজার ছিল হিন্দু ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারদের একটি কেন্দ্রস্থল। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত এখানেই ছিল কলকাতা থেকে আগত অনেক নামকরা ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতির বাসস্থান। এ অঞ্চলে স্থাপিত হয় কিছু উল্লেখযোগ্য ভবন, যেমন শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির, দানবীর বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাস বসাকের স্মরণে নির্মিত পান্থশালা ইত্যাদি।

পাকিস্তান আমলে ব্যবসার রূপান্তর
১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর হিন্দু ব্যবসায়ীদের বড় একটি অংশ ভারতে চলে যাওয়ায় শামবাজারের ব্যবসায়িক কাঠামোতে পরিবর্তন আসে। তবে নবাগত মুসলমান ব্যবসায়ীরা এখানে নতুনভাবে ব্যবসা গড়ে তোলেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে শামবাজারে চাল, গম, তেল, খেজুর, পেঁয়াজসহ খাদ্যপণ্যের বৃহৎ পাইকারি বাজার গড়ে ওঠে। এ সময় এটি ঢাকার বাজার নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পায়।
শামবাজারেই চালু হয় পুরান ঢাকার অন্যতম বিখ্যাত শামবাজার রাইস মিল, যা চাল ও ভাঙা চাল সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। সত্তরের দশকের আগপর্যন্ত শামবাজার ছিল ঢাকা শহরের অন্যতম অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি।
ধ্বংসের শুরু: নদী হারানো ও নগরায়নের চাপ
আশির দশকের পর থেকে শামবাজারের পতনের সূচনা ঘটে। এর প্রধান কারণ ছিল বুড়িগঙ্গা নদীর দখল ও দূষণ এবং সূত্রাপুর খালের শুকিয়ে যাওয়া। নদী ও খালের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নৌপথে পণ্য পরিবহন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ব্যবসার গতি ধীরে ধীরে মন্থর হতে থাকে। পাশাপাশি রাজধানীর উন্নয়ন পরিকল্পনায় পুরান ঢাকা উপেক্ষিত থেকে যায়, যার ফলে রাস্তার সংকীর্ণতা, যানজট, অপরিকল্পিত স্থাপনা এবং পাইকারি বাজারে আধুনিক লজিস্টিক সুবিধার অভাব ক্রমেই শামবাজারকে পিছিয়ে দেয়।
এছাড়াও নবাবপুর, গুলিস্তান, কারওয়ানবাজার, শান্তিনগর ইত্যাদি অঞ্চলে নতুন পাইকারি বাজার গড়ে ওঠায় ব্যবসার কেন্দ্রীকরণ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে শামবাজার তার পুরনো ঐতিহ্য হারাতে শুরু করে।

বর্তমান অবস্থা
বর্তমানে শামবাজার আর আগের মতো বিশাল পাইকারি বাজার না থাকলেও এটি এখনো ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ খুচরা ও আংশিক পাইকারি বাজার হিসেবে টিকে আছে। এখানকার প্রধান পণ্য এখন মূলত চাল, ডাল, তেল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন এবং মৌসুমি কিছু মসলা। কিছু মিল এখনও সক্রিয় রয়েছে, তবে সেই আগের জৌলুস আর নেই।
বাজার এলাকাটি এখন দখলদারিত্ব, যানজট, অপরিকল্পিত দোকান এবং স্যানিটেশন সমস্যায় জর্জরিত। এখানে আধুনিকীকরণের কোনো পরিকল্পনা নেই, অথচ এটি ঢাকার বাজার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ ধ্বংসপ্রাপ্ত নিদর্শন।
স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করেন, সরকার চাইলে শামবাজার সংরক্ষণ করে একটি ঐতিহ্যবাহী পাইকারি ও খুচরা বাজারে রূপান্তর করা সম্ভব, যেখানে প্রাচীন বাজার সংস্কৃতির ঐতিহ্য টিকে থাকবে এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধাও যুক্ত হবে।
শামবাজার শুধু একটি বাজার নয়, এটি ছিল এক সময়ের ঢাকার অর্থনৈতিক কেন্দ্র। বুড়িগঙ্গা নদী ও খালের সৌজন্যে যে বাজারটি গড়ে উঠেছিল, আজ তা হারিয়ে যাচ্ছে নগরায়নের অব্যবস্থাপনা ও ঐতিহ্য রক্ষার অভাবে। এই বাজারের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের জন্য এক ধরনের নগর নৃতত্ত্বের স্মারক। শামবাজারকে ঘিরে যদি সংরক্ষণমূলক পরিকল্পনা নেওয়া হয়, তবে এটি আবার হতে পারে পুরান ঢাকার প্রাণকেন্দ্র, যেমনটি একসময় ছিল।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট